বছরখানেক আগেও করোনা মহামারী ছিল বিশ্বজুড়ে। আতঙ্কে বাঁচছিল মানুষ। কারণ রোগের ওষুধ জানা ছিল না। জানা ছিল না প্রতিষেধক টিকা। তবু সেরেছেন বহুজন। করোনা–জয়ী হয়ে অভিনন্দিত হয়েছেন সাধারণ মানুষের মাঝে। এ প্রসঙ্গেই এমন এক বিস্ময়–কন্যার কথা স্মরণে আসে যাঁর গোটা জীবনটাই ছিল করোনা যুদ্ধের মত আশঙ্কায় পরিপূর্ণ! জীবন–সাগরে হ্যারিকেনের মাঝে, প্রখর বুদ্ধি ও সাহসিকতার ভিত্তিতে দাঁড় টেনে একাকী পার করেছেন তিনি একের পর এক প্রতিকূলতাকে! কিন্তু তাইতেই ক্ষান্ত হননি। প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজেকে ডাক্তাররূপে। মানবসেবায় ঢেলেছেন প্রাণ। জন্মের দীর্ঘ একশ চুয়ান্ন বছর পরেও তবু ক’জন জানে তাঁর কথা! সে যুগের অজস্র গুণীজনের কথা কথিত হয়েছে বারে বারে। শুধু নেপথ্যে থেকে গেছেন ডাক্তার হৈমবতী সেন (Haimabati Sen), যাঁর সমগ্র জীবনটাই ছিল অশুভ থেকে শুভর দিকে এগিয়ে যাওয়ার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা।
আরও পড়ুন- নিবন্ধ: ভারতের প্রথমা বাঙালি ডাক্তার
জন্ম হয়েছিল ১৮৬৬ সালে, পূর্ববঙ্গের খুলনার ঘোষ পরিবারে। জন্মসূত্রে বাংলার মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বংশধর ছিলেন তিনি। ছিলেন অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকেই তিনি অবাঞ্ছিত। বিশাল বিত্তবান বাবার প্রথম সন্তানের আগমন–লগ্নে প্রচুর হোম–যজ্ঞ হয়েছিল প্রাসাদে। সবাই চেয়েছিল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী একটি ছেলে। এমন সময় হেমের জন্ম হলে আশাহত হন সকলে। সবাই হেমের মাকে দুষতে থাকে। দুঃখী জননী ঘরে মুখ লুকোন। শিশু হেম পড়ে থাকেন একা। শুধু বাবা প্রসন্নকুমার ঘোষ খুশি হন। তাঁর আদেশে একমাস ঢাক ঢোল সানাইয়ের উৎসব হয় রাজপ্রাসাদে। এরপর হৈমবতী ওরফে ‘হেম’-এর ভাই হলে মা তাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ছোট্ট হেমের বাবা স্নেহভরে মেয়ের নাম দেন ‘চুন্নিবাবু’। সকলকে সে নামে ডাকতে বলে জানিয়ে দেন, যেন মেয়ে বলে কেউ তাঁকে অবহেলা না করে। ছেলেবেলা থেকেই ডাকাবুকো হেম ছেলেদের শার্ট–প্যান্ট পরে বাহিরমহলে তাঁর ভাইদের মাঝেই বড় হতে থাকেন। অন্দরের মহিলারা কেউ খবর রাখেন না তাঁর।

শ্রুতিধর হেম স্কুলে ভাইদের মাঝে থেকে তাদের চেয়ে দ্রুত আয়ত্ত করতে থাকেন পড়াশোনা, শুধুই শুনে। এমন সময় এক স্কুল ইন্সপেক্টরের নজরে পড়ে তাঁর এই অসামান্য ক্ষমতা। তাঁর আগ্রহে হেমের বাবার অনুমতি নিয়ে আরম্ভ হয় পড়ালেখা, অন্দরমহলের চোখের আড়ালে। কিন্তু শীঘ্রই ধরা পড়েন বালিকা। বীতশ্রদ্ধ আত্মীয়–স্বজনেরা জোর করে তাঁর বিবাহ দেন মাত্র সাড়ে নয় বছরে, এক পঁয়তাল্লিশ বছরের তেজবরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। নিজের চেয়ে পাঁচগুণ বড় মাতাল লম্পট স্বামীর ঘর করতে এসে একরাতে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয় হেমের। সদ্য বিবাহিতা নাবালিকা নিজের ঘরের বিছানার এক কোণে জবুথবু হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আবিষ্কার করেন তাঁর লম্পট দুশ্চরিত্র স্বামীটিকে এক বেশ্যার সঙ্গে, তাঁরই ঘরে। আর্তনাদ করে ওঠেন হেম, তবু সে নিরস্ত হয় না। বেশ্যা নারীটি মানা করলে সে জানায় যে এভাবেই সে তালিম দিতে চায় তার নাবালিকা স্ত্রীকে। মূর্ছিতা হয়ে পড়েন হেম। জ্ঞান ফিরলে হন মানসিক বিকারগ্রস্ত। বাপের বাড়ি পাঠানো হয় তাঁকে। সেখানে বাবাকে সব বলেও নিস্তার পান না। ওঝার ঝাড়ুও পিঠে সইতে হয় তাঁকে। ইতিমধ্যে কঠিন লিভারের রোগে স্বামীর জীবনাবসান হলে দশ বছর বয়সে বিধবা হন হৈমবতী।
বীতশ্রদ্ধ আত্মীয়-স্বজনেরা জোর করে তাঁর বিবাহ দেন মাত্র সাড়ে নয় বছরে, এক পঁয়তাল্লিশ বছরের তেজবরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে। নিজের চেয়ে পাঁচগুণ বড় মাতাল লম্পট স্বামীর ঘর করতে এসে একরাতে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয় হেমের। সদ্য বিবাহিতা নাবালিকা নিজের ঘরের বিছানার এক কোণে জবুথবু হয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। হঠাৎ শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। আবিষ্কার করেন তাঁর লম্পট দুশ্চরিত্র স্বামীটিকে এক বেশ্যার সঙ্গে, তাঁরই ঘরে।
বৈধব্যের সাজে বাপেরবাড়ি ফিরলে জোটে ভৎসনা, গঞ্জনা ও ধিক্কার। যাতনার ভারে জর্জরিত হেম খুঁজতে থাকেন বেরনোর পথ। অবশেষে ভাইয়েদের সাহায্যে লুকিয়ে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। তলব এলে আবার যেতে হয় শ্বশুরবাড়িতে। সেখানেও সব কাজ সাঙ্গ করে অভিধান সঙ্গী করে নিজে নিজেই পড়াশোনা চালাতে থাকেন। কিন্তু সে স্বস্তিটুকুও বেশিদিন জোটে না। শ্বাশুড়ি মারা গেলে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িতা হন। ওদিকে মা বাবারও পর পর জীবনাবসান হয়। বাবা হেমের জন্য যথেষ্ট অর্থ রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার থেকেও পান না এক কানাকড়ি। ভাইয়েরা দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়।

কথায় বলে, জীবন গল্পের চেয়েও বেশি রোমাঞ্চকর! বালবিধবা হেমের অভিভাবকহীন একাকী জীবনে যে উত্থান–পতনের উথালপাথাল চোখে পড়ে, তা যত রোমহর্ষক, ততই বিস্ময়কর! ছোটবেলায় নিজেকে ‘টম বয়’ বলে অভিহিত করা হেম কিন্তু সমস্ত প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁর চলার গতি অব্যাহত রাখেন। সব কিছুর মধ্যে জাগিয়ে রাখেন তাঁর আরও উচ্চশিক্ষার জ্ঞান পিপাসাটিকে। কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ‘হোম’-এ থেকে বিধবারা পড়াশোনা করে, সে খবর পেয়ে রওনা দেন কলকাতার পথে। কিন্তু দুর্গামোহন দাস ও শিবনাথ শাস্ত্রী সেদিনই লন্ডন যাচ্ছেন বলে জোটে না সাহায্য বা আশ্রয়। পথ চলতে পাতানো মানুষের সাহায্যেই তাঁর জীবনের গতি। অতঃপর যে সজ্জন ছেলেটির সঙ্গে তিনি এসেছিলেন, বাধ্য হয়ে ফিরতে হয় তারই সঙ্গে ঢাকায়, তার যৌথ পরিবারের বাড়িতে। সেখানেও টিকতে পারেন না। পালাতে হয় অন্যখানে। এভাবে বেশ কিছু মাস নানা ঘাটে, নানা অপরিচিত অস্বস্তিকর মানুষের মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে আবার এসে পৌঁছন কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে। তখন অল্প কিছু মেয়েরা মেডিক্যালে পড়ালেখা করছে দেখে চিকিৎসা–বিদ্যা শিখে স্বাধীন জীবন কাটানোর আগ্রহ প্রকাশ করেন হেম। কিন্তু এ শহরে তিনি একাকিনী থাকবেন কোথায়? অতএব পরিস্থিতির কাছে নতিস্বীকার করতে হয় তাঁকে। তাঁদের কথামত পুনর্বিবাহ করেন হেম, ব্রাহ্মধর্ম–প্রচারক কুঞ্জবিহারী সেনকে। স্বামী ছিলেন বেকার, অতএব বৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করে বৃত্তি নিয়ে হেম ভর্তি হন মেডিকেল কলেজে। আরম্ভ হয় তাঁর জীবনের আরেক নতুন অধ্যায়।
কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ‘হোম’-এ থেকে বিধবারা পড়াশোনা করে, সে খবর পেয়ে রওনা দেন কলকাতার পথে। কিন্তু দুর্গামোহন দাস ও শিবনাথ শাস্ত্রী সেদিনই লন্ডন যাচ্ছেন বলে জোটে না সাহায্য বা আশ্রয়। পথ চলতে পাতানো মানুষের সাহায্যেই তাঁর জীবনের গতি। অতঃপর যে সজ্জন ছেলেটির সঙ্গে তিনি এসেছিলেন, বাধ্য হয়ে ফিরতে হয় তারই সঙ্গে ঢাকায়, তার যৌথ পরিবারের বাড়িতে। সেখানেও টিকতে পারেন না। পালাতে হয় অন্যখানে। এভাবে বেশ কিছু মাস নানা ঘাটে, নানা অপরিচিত অস্বস্তিকর মানুষের মাঝে ঘুরপাক খেতে খেতে অবশেষে আবার এসে পৌঁছন কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে।
শুরু হয় অধ্যয়ন জীবন। কিন্তু ঝড়ের ঝাপটা চলতেই থাকে। স্বামী আয় করেন না, সংসারে সাহায্যও করেন না। এদিকে একের পর এক সন্তান–সন্ততির মা হতে থাকেন হেম। নিজের বৃত্তির আয়ে কোনোক্রমে সংসার চালিয়ে, বাড়ির সব কাজ সামলে চলতে থাকে তাঁর পড়াশোনা। বহুদিন একাহারে কাটে। বহুমাস এক কাপড়ে যেতে হয় কলেজে। অবশেষে কখনও হার–না–মানা হেম মেডিক্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। প্রায় প্রতিটি বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে তিনি সমস্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এইবার আরম্ভ হয় আরেক অশান্তি। অর্ধেক নম্বরের জন্য গোপালচন্দ্র দত্তকে পিছনে রেখে স্বর্ণপদকের অধিকারিণী হেমকে মেয়ে বলে স্বর্ণপদক দিতে চায় না ছেলেরা। চলে ক্লাস বয়কট, হাঙ্গামা, পিকেটিং। এমনকি হেমকে মেরে ফেলার হুমকিও বাদ যায় না। ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট ও মেজর সার্জেন জে. বি. গিবনস অবশ্য বেঁকে বসেন ও হেমকেই দিতে চান তাঁর প্রাপ্য পদকটি। অবশেষে লেফটেন্যান্ট গভর্নর অবধি কথা গড়ালে তাঁর কথায় মিটিং ডাকা হয়। হেম জানান যে তিনি স্বর্ণপদক চান না। তার বদলে নিখরচায় সার্টিফিকেট কোর্সে ঢুকে আরও উচ্চশিক্ষার সুবিধা পেতে চান। তাঁর কথামতো পুনঃ বৃত্তি দিয়ে তাঁকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয়। প্রায় সব বিষয়ে প্রথম স্থানের রৌপ্যপদক নিয়ে পূর্ণ সাফল্যে তিনি মেডিকেলের গণ্ডি পার করেন।
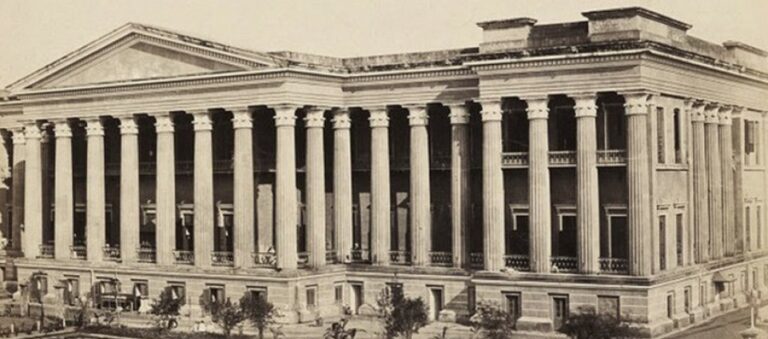
কিন্তু এত কিছুর পরও যুদ্ধ থামে না হেমের জীবনে। এমন রেজাল্ট থাকতেও চাকরি জোটে না কলকাতায়। বৃত্তি বন্ধ, অর্থসংকট, পর পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিশেহারা হন হৈমবতী। এমন সময় হঠাৎ চুঁচুড়ায় গেলে, সেখানকার স্থানীয় মানুষদের আগ্রহে তৈরি লেডি ড্যাফেরিন মহিলা হাসপাতালে চাকরি মেলে। শুরু হয় সাহসিনী ডাক্তার হেমের মানবসেবা, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। এবার ঘরে-বাইরে একাকিনী নারীকে ঘিরে ধরে নতুন ধাঁচের সামাজিক, কূটনৈতিক ও যৌন নিগ্রহের ভয়। কিন্তু ভয়কে ডরাতে শেখেননি হৈমবতী। তাই কিছুই দমাতে পারে না তাঁকে। সবকিছুর মাঝে একাগ্রভাবে করে যেতে থাকেন রুগীর সেবা। সে সময়ের পর্দানসীন নারীরা হাসপাতালে আসতে অনিচ্ছুক হলে তাদের বাড়ি গিয়ে দেখে আসতেন। সম্ভ্রান্তের কাছে অর্থ নিতেন। অভাবীকে দেখতেন বিনি পয়সায়। কাজ করে যেতেন ঘড়ির কাঁটার মতন। নিজের ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে ঘর–বার সামলে কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লেও হাসপাতালে রুগি দেখা থেকে কেউ তাঁকে বিরত করতে পারত না। একবার নিজে গর্ভবতী অবস্থায় হাসপাতালের তিন চারটে কঠিন ডেলিভারি কেসে বেশি পরিশ্রম করেছিলেন বলে তাঁর নিজের জঠরে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সন্তানটিকে জন্ম দিতে প্রচুর কষ্ট পেয়েছিলেন তিনি।
এমন রেজাল্ট থাকতেও চাকরি জোটে না কলকাতায়। বৃত্তি বন্ধ, অর্থসংকট, পর পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে দিশেহারা হন হৈমবতী। এমন সময় হঠাৎ চুঁচুড়ায় গেলে, সেখানকার স্থানীয় মানুষদের আগ্রহে তৈরি লেডি ড্যাফেরিন মহিলা হাসপাতালে চাকরি মেলে। শুরু হয় সাহসিনী ডাক্তার হেমের মানবসেবা, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। এবার ঘরে-বাইরে একাকিনী নারীকে ঘিরে ধরে নতুন ধাঁচের সামাজিক, কূটনৈতিক ও যৌন নিগ্রহের ভয়।
সব জ্বালা মুখ বুজে সয়েছেন। এমনকি স্বামীর দুর্ব্যবহার ও লাথির প্রহারও। পরিণত বয়সে, কুঞ্জবিহারীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিধবা হয়ে আরেক নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করেন হেম। আশ্রয় দিতে থাকেন ওই অঞ্চলের অনাথ অভাগা শিশু, বালক বালিকা ও বালবিধবাদের— নিজের ঘরে, নিজের কাছে। হেমের রাজত্বে ছিল না কোনও দুঃখের ঠাঁই। হাসপাতাল চত্বরে বা তার আশেপাশে যে যেখানে যাকে অসহায় পেত, এসে পৌঁছে দিয়ে যেত তাঁর কাছে। তারা থাকত তাঁর দেখাশোনায় কিছুদিন, কিছুমাস ও বছরও। অনেককে পরে তিনি হোমে পাঠিয়েছেন, অনেক বাল্য–বিধবা মেয়েদের দিয়েছেন পুনর্বিবাহ, ব্রাহ্মমতে। এইভাবে প্রায় তিনশ জনের দেখাশোনা করেছিলেন তিনি। দিয়েছিলেন তাদের নতুন জীবন। এ কাজ করতেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন হেম। কিন্তু ভয় কারে কয় সে কথা ছিল না তাঁর জানা। ছিলেন তিনি চির সংগ্রামী, অগ্রগতির দিশারী!
সাতষট্টি বছর বয়সে, ৫ আগস্ট ১৯৩৩ সালে তাঁর জীবনাবসান হয়। কথায় বলে, তীব্রবুদ্ধি, মনোবল ও সাহসিকতার বলে মানুষ সুমেরু লঙ্ঘন করতে পারে। নিজ জীবন দিয়ে এ প্রবাদকে সত্যি করে দেখিয়ে গেছেন সে যুগের কিংবদন্তি মহিলা ডাক্তার হৈমবতী সেন!
*তথ্যঋণ- The Memoirs of Dr. Haimabati Sen: From Child Widow to Doctor-Translated by Tapan Raychaudhuri; Edited by Geraldine Forbes, Tapan Raychaudhuri; Introduced by Geraldine Forbes; Roli Books; New Delhi 110048; First Published 2000.
*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Wikimedia Commons
বিশ্বভারতী থেকে ভূগোলে স্নাতকোত্তর ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট।
পেশায় লেখক। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত বাংলা ও ইংরেজি পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশ। তা ছাড়া পনেরটি বাংলা ও একটি ইংরেজি বই প্রকাশিত। বিবেকানন্দ-নিবেদিতা গবেষক। এই বিষয়ে এবং আরো অন্যান্য বিষয়ে আমন্ত্রিত বক্তৃতা দিয়ে থাকেন।


























3 Responses
প্রণাম জানাই ডক্টর সেনকে 🙏 এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কেউ যে লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন ভাবা যায় না। ধন্যবাদ চিরশ্রী দি, এমন একটা মানুষের কীর্তি সম্পর্কে অবহিত করার জন্য।
খুব ভাল প্রসঙ্গ ও লেখা। সেই সময়ের কাদম্বিনী গাঙ্গুলির নামটিই পরিচিত। কিন্তু পাশাপাশি হৈমবতী সেন, আনন্দীবাই যোশী, রুকমাবাই রাউথ এরকম বেশ কজন স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তাদের একজনের কথা অনেকে জানলেন।
শ্রেয়সী তার লেখায় এই সময়টাকে ধরবে, সকলের কথা শোনাবে, এই আশায় রইলাম।
ধন্যবাদ জানাই প্রান্তিক ও ভাস্করদাকে, আমার লেখায় সুচিন্তিত সুন্দর মতামত দেওয়ার জন্য। খুব ভালো লাগলো। 🙏