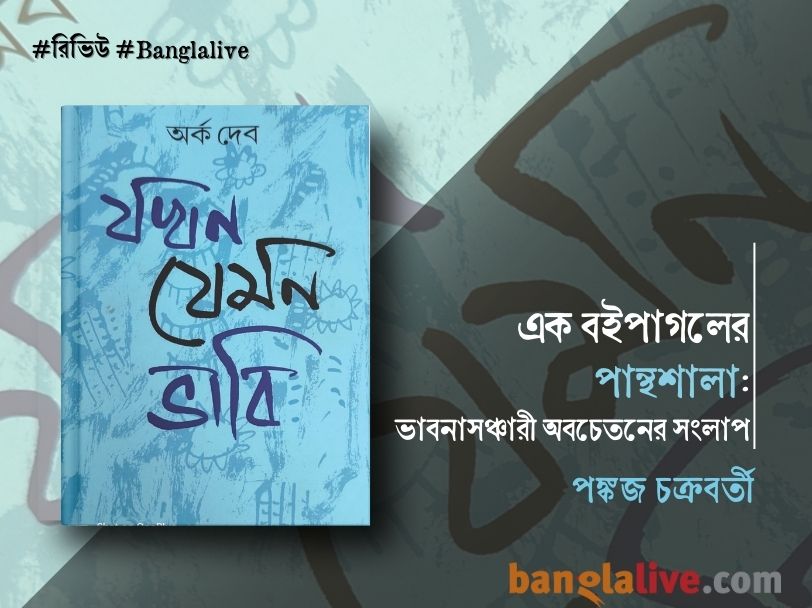বইয়ের নাম: যখন যেমন ভাবি (Book Review)
লেখক: অর্ক দেব
প্রকাশক: ঋত
প্রচ্ছদ: মৃণাল শীল
প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০২৪
বিনিময় মূল্য: ৪০০.০০
সেভাবে ভাবতে গেলে, এমন অনেক বই আছে যা পড়ে ফেলতে প্রয়োজন লোকাল ট্রেনের জানলার ধারের সিট। যেখানে পাওয়া যাবে সর্বজনে ব্যক্তিগত পরিসর। সেই বই একটু একটু করে পড়তে হয়। গোগ্রাসে গিলতে নেই। চোখ বুজে, আবারও খানিকটা, ক্রমান্বয়ে অথবা এলোমেলো। মাঝেমধ্যে না পড়লেও চলে এমন, কিন্তু মন্থন জরুরি। সেই মন্থনে মিশে যায় লেখকের জীবন এবং পাঠকের জীবন। তৈরি হয় সহবাসের গোপন সম্পর্ক। আর থাকে অপ্রত্যাশিত কিছু মুহূর্ত। মফস্বলের বাপুজি কেকে হঠাৎ মোরব্বা পেলে যেমন হয়। অর্ক দেবের ‘যখন যেমন ভাবি’ তেমনই একটি বই। একটি তরুণ বয়সের পক্ষে যা হতে পারে তার চেয়েও উঁচু। তীব্র এক উটের গ্রীবা তছনছ করে দেয় আমাদের স্থিতি। মনে হয় ভাবা হয়নি এতদিন। আর অবাক হয়ে দেখি আমাদের মধ্যে অর্ক এই বয়সে অনায়াসে পেয়েছেন সেই স্বপ্নলোকের চাবি। (Book Review)
এক উটের গ্রীবা তছনছ করে দেয় আমাদের স্থিতি।
অর্কর এই বইটির কেন্দ্রে আছে গান, আরেকটু স্পষ্ট করে বললে রবীন্দ্রনাথের গান। অবশ্য শুধু গান নয়, গান থেকে কবিতা, মফস্বলের জীবন, সিনেমা, লোডশেডিংয়ে হঠাৎ এক টুকরো অকারণ চাঞ্চল্য, সাম্প্রতিক ঘটনার সামাজিক ও রাজনৈতিক বয়ান সবই এসেছে। এমনকি পুজোর দিনে সকাল থেকে রাত্রি কয়েকজন ফুড ডেলিভারি পার্টনারের মুখোমুখি হয়ে অর্ক দেখে ফেলেছেন ঝলমলে উৎসবের রাতে এই শহরের বুকে কতখানি অন্ধকার জমে আছে। পড়তে পড়তে মনে হয় এই লেখাগুলি জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা বলা। কেউ শুনুক তেমন কোনও অভিপ্রায় নেই, কেউ জানুক তেমন কোনও আকাঙ্ক্ষাও নেই। শুধু একটি গোপন ডায়েরি কোনওক্রমে ধুলো ঝেড়ে সিন্দুক থেকে বেরিয়ে এসেছে বাসাবদলের আগে। (Book Review)
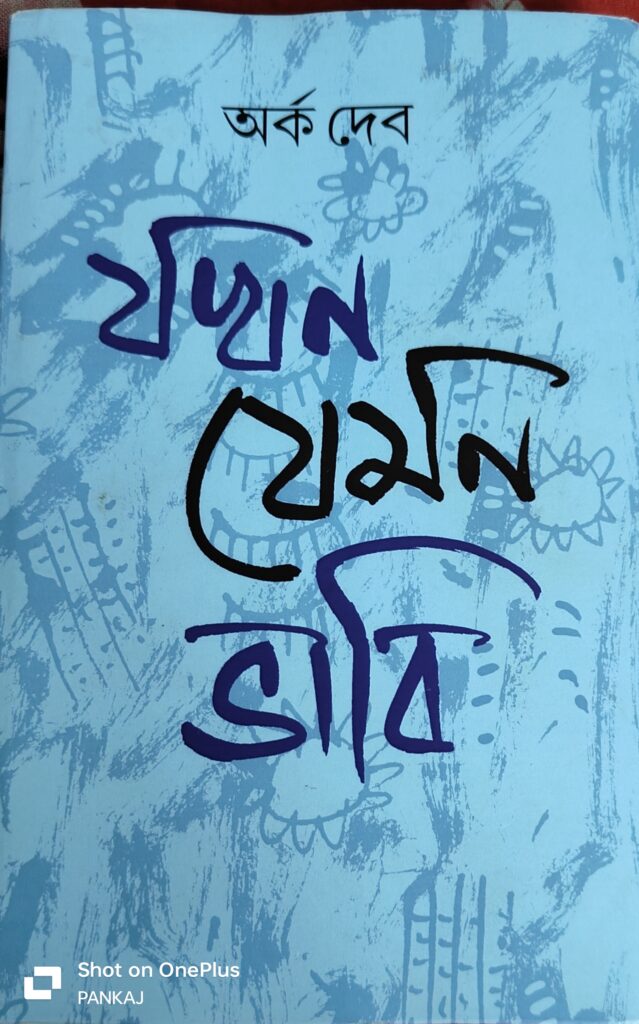
কে এই লেখাগুলি লিখেছেন? পাঠক অর্ক দেব, না লেখক অর্ক নাকি সাংবাদিক অর্ক দেব? আসলে এখানে রয়ে গেছে একই সঙ্গে লেখকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের অভিপ্রায়। যদিও গ্রন্থনাম বলে লেখাগুলি খানিক এলোমেলো চরিত্রের, রেফারেন্সবিহীন। কিন্তু পাঠক এখানে অনায়াসেই পাবেন ভাবনার এমন অনেক উপাদান যা আরেকটু বিস্তারে একটি পৃথক গ্রন্থের দাবি করতে পারে। এই লেখা ব্যক্তিগত কিন্তু সামাজিক। কোথাও কোথাও আছে স্বগতকথন। নিজের মুখোমুখি দাঁড়ানো একা কথা বলার জন্য। স্বগত কিন্তু কখনও কখনও সোচ্চার। কোনও দাবি নেই কিন্তু প্রশ্নাতীত সমর্পণও নেই। আছে নাছোড় ‘ভাবনার আলিপন’, পলাতকা স্মৃতির ছায়া। (Book Review)
আসলে এখানে রয়ে গেছে একই সঙ্গে লেখকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের অভিপ্রায়। যদিও গ্রন্থনাম বলে লেখাগুলি খানিক এলোমেলো চরিত্রের, রেফারেন্সবিহীন।
মোট ৩৮ টি ছোট ছোট গদ্য দিয়ে সাজানো এই বই দিনযাপনের এক ঘনিষ্ঠ জার্নাল। ভাবনার নিবিড়তা যাকে অর্ক বলেছেন ‘বড়জোর অহেতুক চিন্তার ডুবজলে অবগাহনের ইশারা।’ সেইসঙ্গে এই লেখাগুলিতে আছে দিনের প্রশ্ন এবং রাতের প্রশ্রয়। এখানে একজন সাংবাদিক সংশয় নিয়ে দেখছেন, একজন পাঠক চিন্তার বিস্তার করে চলেছেন এবং তারপর একজন লেখক লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। যেখানে সংবাদের তাৎক্ষণিকতার মুহূর্তগুলিকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন অর্ক। তাই ‘উল্টোপাল্টা ঘুড়ির মাঞ্জা’ নামে কিস্তিতে কিস্তিতে এই লেখা প্রকাশিত হলেও অর্কর পরিমার্জনা নিবিড় ঐকতান তৈরি করেছে। (Book Review)
আসলে অর্ক মফস্বলের পাঠক তো, অভাবের সুযোগে সে পানপাত্র থেকে সবটুকুই শুষে নিয়েছে জীবনের। তাই এই গ্রন্থ এক আজীবন পাঠকের। অর্ক মফস্বলের সেই পাঠক যেখানে আয়োজনের চেয়ে অপ্রতুলতা বেশি। সেখানে জানালার পাশের রোদ আর দুপুরের নির্জনতা, চায়ের দোকান, লোকাল ট্রেন, হল্ট স্টেশনের রূপকথা থেকে জীবন কুড়োতে হয়। (Book Review)
আসলে অর্ক মফস্বলের পাঠক তো, অভাবের সুযোগে সে পানপাত্র থেকে সবটুকুই শুষে নিয়েছে জীবনের।
কত বিচিত্র আর বিপরীত উপাদানে ভরা অসামান্য এই বইটি। বিষয় থেকে বিষায়ান্তরে যেতে যেতেই আমরা টের পাই এর নিয়ন্ত্রক শক্তি আসলে স্মৃতি। আরও স্পষ্ট করে বললে এক অলৌকিক গন্ধের স্মৃতি। একে নস্টালজিয়া বললে ভুল হবে তার কারণ বিগত জীবনের হালহকিকত নিয়ে কোনও ভাল-মন্দের একরৈখিক বিচার এখানে নেই। বরং এই বইয়ের সর্বত্র রয়েছে নানা প্রশ্নের ভঙ্গিমা। কিন্তু তাকে সমসাময়িকতার বাজারে ছেড়ে রাখা হয়নি বরং চিরন্তন প্রশ্নটিকে অর্ক প্রতিমুহূর্তে জুড়ে দিয়েছেন। তাই বিস্মিত হতে হয় এই দেখে বহু যুগের ওপার হতে অর্ক কীভাবে কুড়িয়ে নিচ্ছেন উপন্যাসের চরিত্র, গানের শব্দ, এমনকি লোকাল ট্রেনের নিরুচ্চার শব্দগুলিকে। জয় গোস্বামীর লেখালেখির পঞ্চাশ বছর পর নিজেকে প্রকাশ্যতা(লেখা প্রকাশের) থেকে সরিয়ে নেওয়ার একটি সংবাদ তথ্য থেকে অর্ক অনায়াসে পৌঁছে গেছেন তৃতীয় অবসরের দার্শনিক অভিপ্রায়ে। (Book Review)
একত বিচিত্র আর বিপরীত উপাদানে ভরা অসামান্য এই বইটি। বিষয় থেকে বিষায়ান্তরে যেতে যেতেই আমরা টের পাই এর নিয়ন্ত্রক শক্তি আসলে স্মৃতি।
প্রায় প্রতিটি ভোটেই রক্তাক্ত লাশ দেখা আমাদের নিয়তি। সেই শোকের আবহ থেকে অর্ক চলে আসেন ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত পুত্রের পিতার প্রসঙ্গে আর সেখান থেকেই চলে যান রুদালির বানিজ্য-ক্রন্দনে। কিন্তু আশ্চর্যজনক অর্ক তাঁর জীবন দিয়ে ধরে ফেলেন ‘সমষ্টির ক্রন্দনে ব্যক্তিগত নিভৃত শোকের’ কোনও স্থান নেই। তাই সদ্য বিবাহিত মেয়ের বাপের বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য কান্নার আসরে গৃহস্থ মহিলারা কীভাবে এগিয়ে দেন ‘শোকের হাজিরাখাতা! অশ্রুঁফোটার রাজনীতি’ অর্ক ছাড়া কে আর আমাদের জানাতেন? রবীন্দ্রনাথের একটি গানের থেকে আরও অজস্র গানে অর্ক খুঁজে ফেরেন নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগার অভিপ্রায়। জীবনানন্দের ‘শঙ্খমালা’ কবিতার একাডেমিক পাঠে যে ক্ষতি আমাদের হয়েছে তার উপশম দেবে অর্কর এই গ্রন্থের চতুর্থ লেখাটি। সেখানে জীবনানন্দের শব্দ আর সেই সূত্রে চলে আসে, লোকাল মানুষের গান, বর্ধমানের ভাগচাষীর সুর এবং লালন। (Book Review)
এই বইয়ের একটি অবিস্মরণীয় লেখা ‘কার চোখের চাওয়ার হাওয়ায়’। সুফি দর্শনে চোখ মনের আয়না। তাই কোনও সুফি সন্তের পদে নয়ন বা আঁখি শব্দটি এলে গায়কেরা অনেকক্ষণ ধরে সেই শব্দটির আদরযত্ন করেন। এই সূত্রেই অর্ক বাবা শেখ ফরিদি, আমির খসরু থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ‘নয়ন’ শব্দটি ধরে যেভাবে কয়েক শতাব্দী পথ হেঁটেছেন সেই তুলনামূলক পথটি ঈর্ষণীয়। একটি কবিতা হাজার বছর ধরে লিখে চলেছেন একজন আদি কবি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অর্ক যে পাঠ পরিধি অর্জন করেছেন তা তুলনাহীন এবং বিস্ময়কর। (Book Review)
আরও পড়ুন: এই গ্রামদেশ, স্বপ্নাদেশে লিখিত কবিতা
স্মৃতির গন্ধ বা গন্ধের স্মৃতি নিয়ে একটি চমৎকার লেখা শেষ করার পর মনে হল সারা পৃথিবী জুড়ে এর চিরন্তন জাল ছড়িয়ে আছে। আর তাই যে গন্ধ কে ইউরোপীয় দার্শনিকেরা কোনও মূল্য দেননি সেই গন্ধের মূল্য নিয়ে অর্ক যোগ করে দিচ্ছেন বোদলেয়ার আর রবীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দকে- যাঁর কবিতায় কলমির গন্ধ, ধানের গন্ধ চাল-ধোয়া হাতের গন্ধ আর মৃত্যুর গন্ধ লগ্ন হয়ে আছে। ব্যবহারিক হাত আর লেখার হাত কত আলাদা। লেখার হাত নিজের মর্জির মালিক। (Book Review)
শারীরিক হাতের জন্য হয়তো যত্ন লাগে কিন্তু লেখার হাতের জন্য লাগে প্রস্তুতি। লাগে নির্জনতা। যা সমরেশ বসু থেকে হারুকি মুরাকামি সকলেই রপ্ত করেছেন। এমনকি আমরা জানি ‘ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচুড’ লেখা মাঝ দুপুরে শেষ হলেও মার্কেজ বসেছিলেন আরও তিন ঘণ্টা লেখার টেবিলে প্রতিদিনের অভ্যাসে। সেও তো লেখার হাতের প্রতি সম্ভ্রমেই। অথচ আজকের সাংস্কৃতিক বাঙালি তার লেখার হাত নিয়ে যে গর্ববোধ করেন তার পেছনে যে তিক্ত বিদ্বেষপূর্ণ আড়ম্বর আছে তাকে তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন অর্ক ‘সে যখন তখন নামিয়ে দিতে পারে নাটক নভেল। পারে, তাই সে নিয়মিত লেখে না, যে লেখে তাঁকে হ্যাটা করে। (Book Review)
অধ্যাবসায়কে ছোটো চোখে দেখে। ট্যালেন্ট তার মামাদাদু, সে বসবে আর লেখার ফুলকি উড়বে।’ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু বলা যায় বুদ্ধদেব বসু সম্ভবত এদের জন্যই লেখার ইস্কুল কথাটি ভেবেছেন। আরেকটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন অর্ক যা সূক্ষ্ম অর্থে একটি দার্শনিক অভিপ্রায়ই বটে। যে বই কেনে সে কি পাঠক? বরং অর্ক মনে করেন যে ঘুরে দেখে বই কিনে এনেছিল আর যে বই পড়ছে তারা এক ব্যক্তি হলেও আসলে আলাদা লোক। প্রথমজন বড়জোর সংগ্রাহক নিভৃত পাঠকের চাকরবাকর বলা যায়। আর দ্বিতীয়জন তার প্রয়োজন নির্জনতা, ভাবনার জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা। একটি দূরত্ব রচনা সমাজ এবং প্রয়োজনের সংসারে। (Book Review)
এসব যদি হয় পাঠক মনের প্রশ্ন তাহলে দেখব সাংবাদিক মনের প্রশ্নগুলিও কম সংবেদনশীল নয়। সেখানে পায়ে হাঁটা প্রতিবাদের পথ আছে, প্যালেস্টাইন আছে, খাদ্য সুরক্ষার প্রশ্ন আছে, আছে গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরার বিপ্লবের প্রশ্ন। সেইসব রচনায় প্রশ্ন সমসাময়িক কিন্তু উত্তরগুলি ভবিষ্যতের জন্য জরুরি বার্তা। আর এভাবেই দেখে ফেলেন অর্ক ফুড ডেলিভারি পার্টনারের রেটিং অসহায়তা এবং তার পাশেই দেশ বিদেশের ফুটবল দাসদের কথা যারা এজেন্টের মাধ্যমে ভারতে বা নেপালে চালান হয়ে যায়। খেলোয়াড় হিসেবে শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারে তারা অবৈধ। খেলার জন্য চুক্তিবদ্ধ নয় বরং তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সস্তা শ্রমের বাজারে। তাই মফস্বলে আমরা কালো বন্ধুটিকে যখন চিমা বলেছি, দেখিনি তার নিচে কতখানি শ্রম, রক্তপাত হয়ে চলেছে।
এসব যদি হয় পাঠক মনের প্রশ্ন তাহলে দেখব সাংবাদিক মনের প্রশ্নগুলিও কম সংবেদনশীল নয়।
রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই গ্রন্থে সবচেয়ে বেশি এসেছে যাঁর কথা তিনি জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথের গান আর জীবনানন্দের কবিতা যেন অর্কর অবচেতনের শুশ্রূষা। নিবিড় বেদনার পুলক। তাই কথায় কথায় অর্ক চলে যান জীবন থেকে জীবনানন্দে। শুধুমাত্র ‘ক্ষমতা আমাকে দেখে’ এবং ‘দুর্গাদ্রষ্টার পর্যটন’ এই দুটি অসামান্য লেখার জন্য অর্ক পাঠকের স্মৃতিতে থেকে যাবেন দীর্ঘদিন। (Book Review)
এই লেখাগুলির প্রধান চালিকাশক্তি নিশ্চিত মফস্বলের স্মৃতি। স্মৃতি কিন্তু নস্টালজিয়া নয়। তার কারণ অর্ক কোথাও দাঁড়িয়ে কোনও ভাল মন্দের বিচার করেননি। নিদান দেননি। শুধু একটি সূত্র থেকে আরেকটি উপক্রমের দিকে চলে গেছেন। যখন পিছন ফিরে তাকাই তখন বুঝতে পারি অনেক বিপর্যয়, অনেক ঘটনার কালিমা পেরিয়ে আমাদের আসতে হল। একটা গোটা নব্বই দশক যার সাক্ষী। শুধু একটা দশকই কী পরিমাণ মূল্যবোধের অপচয় সামলেছে, নিজেকে প্রস্তুত করেছে অর্ক তা দেখান প্রায় আঙুল তুলে। পাশাপাশি একটি আঙুল ঠিক নিজের দিকে। একজন সৎ মানুষের যা কর্তব্য। তাই এই গ্রন্থ পড়ার পর মনে হয় ‘আকাল আমাদিগের সর্বাঙ্গে।’ বুঝতে পারি, কেন এই লেখার প্রথম পাঠক হিসেবে রাত জেগে অপেক্ষা করতেন জয় গোস্বামী। এই লেখা আসলে এক বইপাগলের পান্থশালা। এক ধূসর তেলেনাপোতার চরাচর। তীব্র জ্বরে আক্রান্ত এক পাঠকের খোলসের ভিতর লুকিয়ে আছেন একজন সত্যদ্রষ্টা লেখক। বহুমুখী ও তীব্র, অতল এবং অপ্রত্যাশিত। (Book Review)
জন্ম ১৯৭৭। লেখা শুরু নব্বইয়ের দশকে। পঞ্চাশের বাংলা কবিতার আতিশয্যর বিরুদ্ধে এযাবৎ কিছু কথা বলেছেন। ভ্রমণে তীব্র অনীহা। কিংবদন্তি কবির বৈঠকখানা এড়িয়ে চলেন। এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ - বিষণ্ণ দূরের মাঠ চার ফর্মার সামান্য জীবন, উদাসীন পাঠকের ঘর, লালার বিগ্রহ, নিরক্ষর ছায়ার পেনসিল, নাবালক খিদের প্রতিভা। গদ্যের বই- নিজের ছায়ার দিকে, মধ্যম পুরুষের ঠোঁট। মঞ্চ সফলতা কিংবা নির্জন সাধনাকে সন্দেহ করার মতো নাবালক আজও।