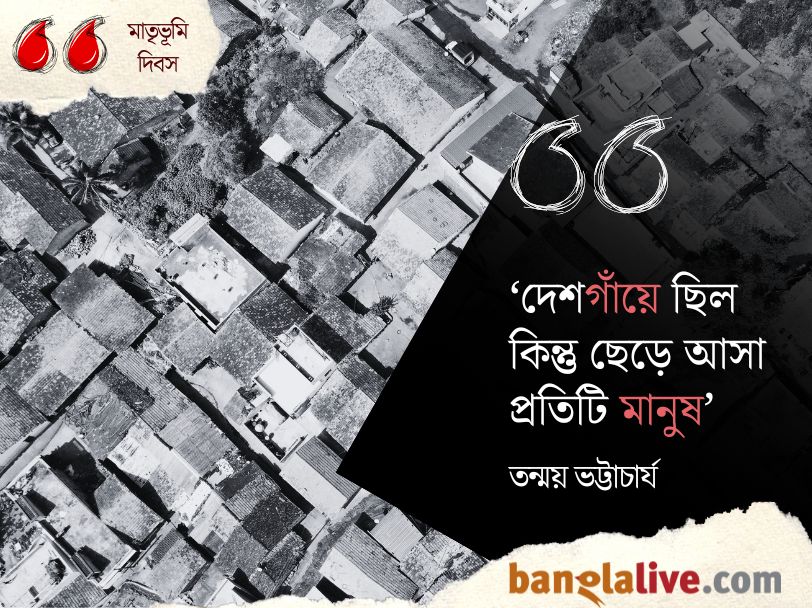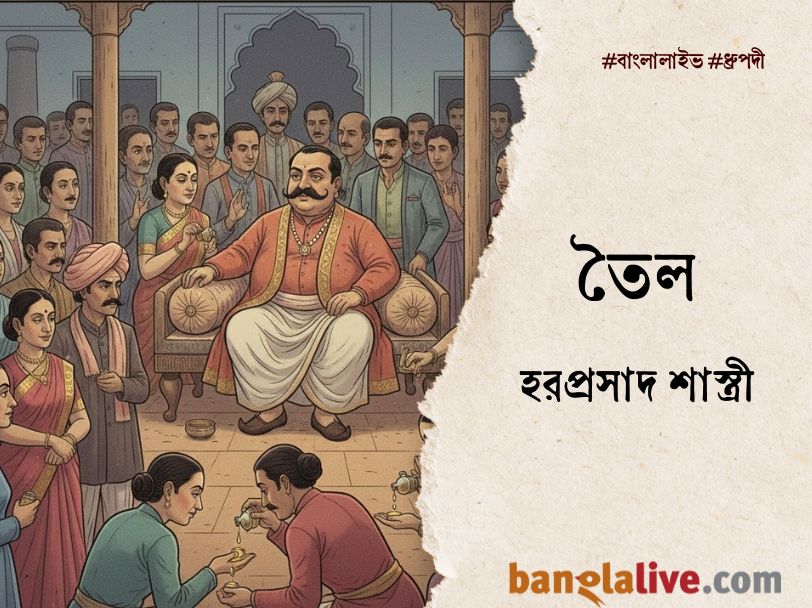(Motherland)
‘দেশ’ শব্দে, আমাদের কল্পনায় সাধারণভাবে ভেসে ওঠে একটি মানচিত্র। আসমুদ্রহিমাচল ভারতের ছবি। ৩,২৮৭,২৬৩ বর্গ কিলোমিটারের এক ভূখণ্ড। তারই মধ্যে ‘নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান/ বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান’, যেমনটি লিখেছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। কিন্তু অভিধান আরও কয়েকটি অর্থ তুলে ধরে— ‘নিজের গ্রাম’, ‘জনপদ’ ইত্যাদি। বৃহত্তম ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে ক্ষুদ্রতম স্বগ্রাম— ‘দেশ’ শব্দটি এই ব্যাপক বিস্তৃতি পেল কীভাবে? এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ইংরাজি ‘কান্ট্রি’ শব্দটি। এ-ও, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র— উভয় দিকেই ঝুঁকে। ছেড়ে-আসা গ্রাম তথা ১৯৪৭-পরবর্তী উদ্বাস্তু দৃষ্টিভঙ্গিতে, তথাকথিত সেই ‘দেশ’-এর স্পন্দনই বোঝার চেষ্টা করব আমরা। (Motherland)

(Motherland) এ-কথা অনস্বীকার্য, বর্তমান ভারতের একত্ররূপ যখন কল্পনাতীত ছিল, ভিন্ন-ভিন্ন জনপদ তথা রাজ্য যখন ছিল স্বাধীন ও স্বশাসিত, সেইসমস্ত জনপদ অভিহিত হত ‘দেশ’ হিসেবেই। ক্রমে, ঔপনিবেশিক যুগে ভারত ‘এক’ হয়ে উঠলেও, ‘দেশ’-এর মৌলিক অর্থটুকু বদলায়নি। আর তা যদি হয় নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে যেমন তা সত্য, তেমনই ছোটো কোনও গ্রামের ক্ষেত্রেও। এ-বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চালানো যায় অন্য দিক দিয়েও। ‘দেশ’ প্রকৃতপক্ষে নিজের ঠিকানা। বিদেশে কোনও ভারতীয় নিজের দেশের পরিচয় দিতে গিয়ে ভারতের নাম নেন, কেননা বৈশ্বিক প্রেক্ষিতে ভারতের সুবাদেই চিহ্নিত হবেন তিনি। আবার পশ্চিমবঙ্গীয় কোনও ব্যক্তি ভারতের অন্য প্রদেশে গেলে, তাঁর দেশ হয়ে ওঠে এই রাজ্য। একইভাবে, পশ্চিমবঙ্গের ভেতরেও, বর্ধমান জেলার কেউ অন্য জেলায় গেলে, তিনি বর্ধমানকে দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বর্ধমানের ভেতরে, ‘দেশ’ হয়ে ওঠে থানা বা ব্লক বা গ্রাম। এভাবেই, পরিসর যত বদলাতে থাকে, দেশ তত নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। জন্ম নেয় ‘দেশগাঁ’ শব্দবন্ধ। কখনও-কখনও দেশ-পরিচয় হয়ে ওঠে ব্যক্তির আত্মপরিচয়ও। সেই দেশে অবস্থিত বাস্তুভিটে হয়ে ওঠে ‘দেশের বাড়ি’। আর কে-না জানে, যতই প্রবাসজীবন হোক, শিকড়টুকু গেঁথে ওই দেশের বাড়িতেই। যাঁরা শিকড়ের সঙ্গে সংলগ্ন, বাস্তবে বা মানসিকভাবে, তাঁরাই বুঝবেন এর গুরুত্ব। (Motherland)
কৃষ্ণরাম ও সত্যেন্দ্রনাথের সূত্রে যখন সাহিত্য-মানচিত্রে উঠে এসেছিল নিমতা: তন্ময় ভট্টাচার্য
আমাদের আলোচনা দেশের সেই আদি ও প্রাথমিক পরিচিতি নিয়েই। গ্রাম, থানা, বড়োজোর জেলার বাইরে পৌঁছোয় না তার সীমা। ব্যক্তির ঠিকানার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে ওঠে তাঁর দেশ-পরিচয়। এর সুবিধা হল, ব্যক্তির নির্দিষ্ট জন্মস্থান তথা বিচরণভূমিকেও চিহ্নিত করা যায় সহজে। দেশছাড়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সে-পরিচয় আবেগ বয়ে আনে। আনে দীর্ঘশ্বাস ও ফিরে যাওয়ার বাসনা। দেশ যেন এক সুদূরের হাতছানি, পরিচয়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, অথচ ফেরার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। সে-বাধাই আরও তীব্র করে তোলে দেশের স্মৃতি। উচ্চারণভেদে হয়ে ওঠে ‘দ্যাশ’। যেমনটি ঘটেছিল পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসা অজস্র পরিবারের ক্ষেত্রে। (Motherland)
দেশের এই স্থিতিস্থাপকতা, জেলা থেকে গ্রামে চলাচল, প্রকৃতপক্ষে পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির নিজের ভেতরেই নেমে যাওয়া। গ্রামে পৌঁছে, ভিটের দাওয়ায় বসে খানিক জিরানোর আহ্লাদ।
(Motherland) ১৯৪৭-এর বাংলাভাগ ও তার পরবর্তী দু-আড়াই দশকের ঘটনাবলিতে, অজস্র মানুষ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আশ্রয় নিয়েছিলেন ভারতে। ছেড়ে এসেছিলেন ভিটেমাটি, জমি-জিরেত, আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের। হারিয়েছিলেন জীবিকাও। সব হারানোর যে-বেদনা, তার বিপরীতে স্মৃতিতে ফুটে উঠত নিরাপদ অবস্থানকালীন সুখের দিনগুলি। জন্ম, শৈশব-কৈশোর, যৌবনের বিস্তীর্ণ অধ্যায়। দেশ-সংক্রান্ত আবেগের উৎস মূলত সেইসব স্মৃতিই। তারও আগে, নিজভূমিতে থাকাকালীনই দেশের পরিচয়ে পরিচয় দিতেন তাঁরা। ‘দেশ কোথায়?’— এ-প্রশ্নের উত্তরে কেউ বলতেন ময়মনসিংহ, কেউ রাজশাহী, কেউ সিলেট। ঢাকা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, খুলনা, যশোর, বরিশাল সহ এমন কত ‘দেশ’ যে ছড়িয়ে ছিল তৎকালীন পূর্ববঙ্গের ভূখণ্ডে, তার ঠিকানা নেই। সেই ‘দেশ’ ভেঙে গভীরতর দেশেও যাওয়া চলত। জেলা থেকে সাবডিভিশন, সেখান থেকে থানা, সেখান থেকে গ্রাম। তবে তা প্রাথমিক পরিচিতিটুকু দেওয়ার পরবর্তী ধাপ। ধরা যাক, কেউ দেশ ময়মনসিংহ শোনার পর, জানতে চাইল— ‘ময়মনসিংহের কোথায়?’ তখন ধাপে-ধাপে বাকি অংশগুলি জানানো। দেশের এই স্থিতিস্থাপকতা, জেলা থেকে গ্রামে চলাচল, প্রকৃতপক্ষে পরিচয় প্রদানকারী ব্যক্তির নিজের ভেতরেই নেমে যাওয়া। গ্রামে পৌঁছে, ভিটের দাওয়ায় বসে খানিক জিরানোর আহ্লাদ। (Motherland)

উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে চলে আসার পরও সেই দেশ-পরিচয়টুকু ছাড়তে পারেননি তাঁরা, বরং আঁকড়ে ধরেছিলেন আরও। একই দেশের তথা জেলার মানুষদের একত্রবাসের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন কলোনিতে। কোনও-কোনও কলোনি আবার শুধুমাত্র একই জেলার মানুষদের নিয়ে গড়ে ওঠা। এমনকি, দেশ-সূত্রে পূর্বপরিচিতরা একসঙ্গে জমি কিনে বাসা বানিয়েছেন— পাওয়া যায় এমন উদাহরণও। ফলে, দেশ ছেড়ে এসেও এক ভিন্ন ‘দেশ’ গড়ে তোলার এই প্রচেষ্টা— এ-ও কি কম গুরুত্বপূর্ণ! (Motherland)
গঙ্গাবক্ষে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা, সাক্ষী ছিল বালি-দক্ষিণেশ্বর: তন্ময় ভট্টাচার্য
(Motherland) বাংলা সাহিত্যে— কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক বা গানে উদ্বাস্তু-সূত্রে ‘দেশ’-এর কথা ফিরে এসেছে বারবার। সে-শব্দব্যবহার যেমন দেশভাগ নামক ঘটনাটিকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত, তেমনই ফেলে-আসা দেশ তথা গ্রামের দিকেও ইঙ্গিত করে ক্ষেত্রবিশেষে। তাঁদের অর্থাৎ দেশ-ছেড়ে আসা প্রথম প্রজন্মের স্মৃতিতে ভারত কি ‘অপর’ হয়েই থেকে গেল? তর্কসাপেক্ষ এই চিন্তা ছেড়ে কবিতায় উঁকি দিই। দেবদাস আচার্য যখন লেখেন— ‘তখন আমি খুব ছোটো ছিলাম, যখন দেশত্যাগী হই’, এই দেশত্যাগ নেপথ্য-অর্থ পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আসা নয়, বরং নিজের ভিটে-গ্রাম-জেলা হারানো। উত্তম দাশের কবিতায় ‘এক কাপড়ে দেশত্যাগ’-এরও অভিমুখ সেদিকেই। উৎপলকুমার বসুর কবিতায় ‘দেশ কেন ছেড়ে এলি?’—এ-প্রশ্নে শ্লেষের আড়ালে অসহায়তা ও কোণঠাসা অবস্থানটি চিহ্নিত করা যায় সহজেই। কিরণশঙ্কর দাশগুপ্ত উদ্বাস্তুদের উদ্দেশে বলেন
‘তবু এলি দেশ ছেড়ে এ কোন বিদেশে’, সেকালের উদ্বাস্তুদের চিন্তাভাবনার প্রকৃতি স্পষ্ট। আবাল্য কাটানো ‘দেশ’ ছেড়ে, একপ্রকার বাধ্য হয়েই ভারতীয় ভূখণ্ডে আসা, এ একপ্রকার বিদেশযাত্রাই। কেন না তাঁরা ব্রিটিশ ভারত বা পূর্ব পাকিস্তান— এ-সমস্ত রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের তুলনায় স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন জেলা বা গ্রাম-পরিচয়েই। (Motherland)
কিরণশঙ্করের পঙক্তিতে কি এই ইঙ্গিতও লুকিয়ে, যে, যতই কষ্ট হোক, দেশের ‘কমফর্ট জোন’ ছেড়ে বিদেশে আসা বিবিধ দিক দিয়েই প্রতিকূল! আবার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাস্তবের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ারই পক্ষপাতী— ‘সীমান্তের ওইদিকে আমার জন্মভূমি,/ এইদিকে আমার দেশ।’
জন্মভূমি ও বাসভূমির এই টানাপোড়েন প্রথম প্রজন্মের বহু উদ্বাস্তুকে দীর্ণ করেছে। ফেলে-আসা ভূমি নতুন রাষ্ট্র অর্থাৎ ‘বাংলাদেশ’ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও, স্মৃতিকাতর অনেকে সে-দেশকে আপন করে নিয়েছেন, ফিরতে চেয়েছেন জন্মভিটেয়। অংশুমান করের কবিতায় তারই প্রতিফলন— ‘…ঠাম্মা বারবার বলে উঠত/ দ্যাশ, দ্যাশ, আমাগো বাংলাদেশ।’ বর্তমান নিবন্ধকারের কাছেও, নবতিপর পিতামহী একাধিকবার ‘দ্যাশ’-এ যাওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছিলেন। ‘দ্যাশ’ অর্থ কিন্তু সেখানে বাংলাদেশ নয়; বাংলাদেশের যে-কোনও জায়গায় গেলে ইচ্ছা পূর্ণতা পেত না তাঁর। সে-দেশ ছিল নির্দিষ্টভাবে কিশোরগঞ্জের বর্শিকুড়া গ্রাম। সে-ইচ্ছা সফল হয়নি আর। কিন্তু ছাব্বিশ বছর বয়সে ভিটে ছেড়ে আসা এক নারীর ছয়টি দশক পরেও সেখানে ফেরার বাসনা প্রমাণ করে, ভৌগোলিকভাবে মানুষ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে একাধিক দেশের বাসিন্দা হতেই পারে, কিন্তু যে-দেশ লালন করে মনের ভেতরে, তার গণ্ডি যতই ক্ষুদ্র হোক-না কেন, দেশের ছবি বলতে প্রাথমিকভাবে ভেসে ওঠে সেই গাঁ-ঘরই, কোনও রাষ্ট্রের মানচিত্র নয়। (Motherland)
বছর তিনেক আগে, বর্তমান নিবন্ধকার একটি বৌভাতের নিমন্ত্রণপত্র দেখে চমকে উঠেছিলেন। পাত্র, অনূর্ধ্ব-তিরিশ, জন্ম-কর্ম সব পশিমবঙ্গেই। পাত্রের মা-বাবারও তাই। তারও আগের প্রজন্ম উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে। সেই নিমন্ত্রণপত্রে, পাত্রের বিভাগে লেখা— ‘দেশ: পূর্ব বাংলা, ঢাকা’।
বছর তিনেক আগে, বর্তমান নিবন্ধকার একটি বৌভাতের নিমন্ত্রণপত্র দেখে চমকে উঠেছিলেন। পাত্র, অনূর্ধ্ব-তিরিশ, জন্ম-কর্ম সব পশিমবঙ্গেই। পাত্রের মা-বাবারও তাই। তারও আগের প্রজন্ম উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে। সেই নিমন্ত্রণপত্রে, পাত্রের বিভাগে লেখা— ‘দেশ: পূর্ব বাংলা, ঢাকা’। যেখানে তাঁর জন্ম ও বাসস্থান, সেই ঠিকানা লিখিত ‘নিবাস’ হিসেবে। অপরপক্ষে, পাত্রীর ক্ষেত্রে ‘দেশ: এ দেশ’। আপাতভাবে পড়ে মনে হতেই পারে, এ-নিবাস যেন সাময়িক, মূল ঠিকানা তো ঢাকাই! প্রকৃতপক্ষে, ভারতের নাগরিক হয়েও, মনে-মনে ওপার বাংলার স্মৃতি লালন করে চলেছে সেই পরিবার; যার সঙ্গে উত্তরাধিকার ছাড়া আর-কোনও যোগই নেই তৃতীয় প্রজন্মের। শুধু এই একটি নয়, এমন আরও অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে উদ্বাস্তু পরিবারগুলিতে। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা একে দ্বিচারিতা ভেবে ক্রোধ প্রকাশ করতেই পারেন, তবে এর মধ্যে স্মৃতিকাতরতা ছাড়া আর-কোনও উপাদান নেই; বাস্তবেও তাঁরা ভারতরাষ্ট্রেরই অনুগত। কিন্তু মনে পড়া? ঐতিহ্য? উত্তরাধিকার? শিকড়? কোনও চোখরাঙানি কি এগুলির বদল ঘটাতে পারে! (Motherland)

তর্ক উঠতে পারে— এক দেশে আশ্রয় নিয়ে, সেখানকার নাগরিক হয়েও অন্য দেশের প্রতি দুর্বলতা কতটা সমর্থনযোগ্য? এর উত্তর ‘দেশ’ শব্দটির বৈচিত্র্য ও প্রয়োগের মধ্যে লুকিয়ে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কেউ-কেউ শব্দটি একমুখী করতে চাইলেও, তাঁদেরও নিজস্ব ‘দেশ’ আছে, আছে শিকড়ও। চাইলে অগ্রাহ্য করাই যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র দেশের সমষ্টিতে গড়ে ওঠা বৃহৎ একটি দেশ আসলে ভারসাম্যের দিকেই নির্দেশ করে। আর উদ্বাস্তুদের কথা ধরলে, তাঁদের ‘দেশ’-কেন্দ্রিক স্মৃতিচারণের অবস্থান ভারতের বিপ্রতীপে নয়; তা একান্তই ব্যক্তিগত, মনের কোণে লুকিয়ে রাখা এক সজল-শ্যামল আবেগ। যে-দেশের কোনও পতাকা নেই, মুদ্রা বা মানচিত্র নেই, তাঁরা এককভাবে সে-দেশেরও প্রতিনিধি। আর-সব মুছে ফেলা যায়, স্মৃতিকে রোধিবে কে! (Motherland)
ঋণ:
তন্ময় ভট্টাচার্য সম্পাদিত, দেশভাগ এবং, সৃষ্টিসুখ, ২০২২
গৌরব দাস
শিরোনাম ঋণ: অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
ছবি সৌজন্য- ক্যানভা ডট কম-এর কপিরাইট ফ্রি ছবি
জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।