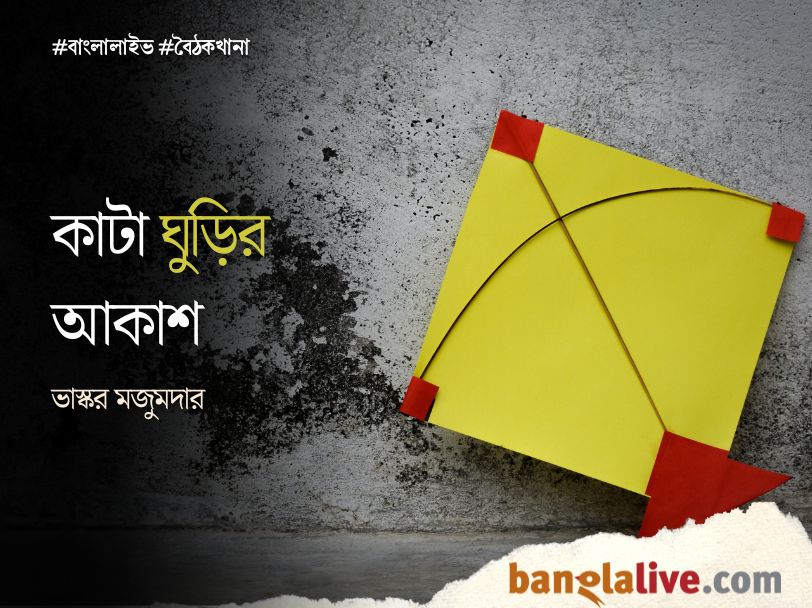(Vishvakarma Puja)
‘রুঠে খাবোঁ কো মনালেঙ্গে
কটি পতঙ্গো কো থামেঙ্গে
ও হায় জজ়বা
সুলঝা লেঙ্গে উলঝে রিস্তো কা মানঝা…’ (Vishvakarma Puja)
তারপর তুরতুর করে ঘুড়িটা বাড় নিল। আমি হাঁ করে দেখছি আমার উড়িয়ে-দেওয়া ঘুড়ি কেমন আকাশের ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে। এত দূর ঘুড়ি ওড়ানো সম্ভব? টুবলুদা হলে সব সম্ভব। ওর হাতে যে-কোনও ঘুড়ি বহু দূর আকাশে উড়তে পারে। এখন ঘোর দুপুর। আজ কী একটা ছুটির দিন। (Vishvakarma Puja)
আরও পড়ুন: আরন্ধের রাঁধাবাড়া কি বর্ষাশস্যের থ্যাংক্সগিভিং?
এতক্ষণ কোয়ার্টার্সের এই ন্যাড়া ছাদে অনেক লোক ছিল। তারা সব খেতে গেছে। আরেকটু পর সব আসবে। আমি স্নান-খাওয়া সেরে এসেছি আর টুবলুদার ঘুড়ি ওড়ানোর এত ভীষণ নেশা যে ও নাওয়া-খাওয়া ভুলে যেত এই ঘুড়ির মরসুমে। তখন বর্ষা জুলাইতে মোটামুটি শেষ হয়ে যেত। আগস্টে আকাশ বেশিরভাগ সময় ঝকঝকে। ১৫ই আগস্ট থেকে বিশ্বকর্মা পুজো অবধি কে-ব্লকের ন্যাড়া ছাদে আমাদের ঘুড়ি ওড়ানো চলত। (Vishvakarma Puja)
আমরা তখন ফাইভ-সিক্স, টুবলুদারা খুব বেশি হলে টুয়েল্ভ। শিশুরা তারুণ্য ও তরুণেরা যৌবনের দীক্ষা পেত ওই ছাদেই। কারও প্রথম বিড়ি-সিগারেট, কারও প্রথম বটতলার বই ও বইয়ের মধ্যেকার লোভনীয় ছবি দেখার অভিজ্ঞতা সেই ছাদে হয়েছিল। ঘুড়ি ওড়ানো শেখার ক্লাসও চলত। কী করে ঘুড়ি বাড়তে হবে, ঘুড়ি চিনতে হবে, কোন কাগজের ঘুড়ি মজবুত, কোন সুতো ভাল কিংবা ভাল সুতো না থাকলে মাঞ্জার ব্যবস্থা নিজেদের কীভাবে করে নিতে হবে, সেই সব আদান-প্রদান চলত আমাদের ছাদে। (Vishvakarma Puja)

মাঞ্জার জন্য আঠা, কাচের গুঁড়ো এমনকি রেসকোর্সের মাঠ থেকে শেয়ালের গু-এর যোগাড়– সব আমরা করে নিতাম। ছোটদের প্রথম তালিম চলত লাটাই ধরার কাজে। তারপর ঘুড়িতে অল্প, অল্প বাড় দেওয়া আর কেউ নিজে থেকে ঘুড়ি ওড়াতে শিখে গেলে অবশ্যই তার ভাগ্যে পুরস্কার স্বরূপ দু’এক টান সিগারেট জুটত! মানে পুরো সিগারেট নয়। দাদারা টান দিতে দেবে দু’এক বার- ওইটুকুই! এবারে সিগারেট কীভাবে ট্যাপ করে খেতে হবে সেগুলো অনেক ওপরের শিক্ষা। আমরা তখনও অতটা পৌঁছাইনি। (Vishvakarma Puja)
তখন বিশ্বকর্মা পুজো আমাদের জীবনে একটা নব আনন্দ এনে দিত। যদিও মা বলত, ‘ওগুলা রিশকাআলা গো পূজ়া’ তবু এই পুজোয় আমাদের অংশগ্রহণ থাকত। সেটা যে শুধু ঘুড়ির জন্য তা নয়। খানিকটা রান্না-পুজোর জন্যেও। যদিও আমরা কাঠবাঙাল তাও কোয়ার্টার্সে এবং মুচিপাড়ার যে বাড়িতে আমরা এক সময় ভাড়া থাকতাম সেখানে ওরা রান্না-পুজো করত। বাসন্তী কাকিমার বাড়ি আমরা খেতাম সব্জি ডাল, পাঁচ-ছ’রকমের ভাজা যার মধ্যে নারকেল ভাজা বেশ লাগত, পান্তা ভাত আর এক সরু টুকরো ইলিশ মাছ। ওদের বাড়িতে কেউ ঘরবাড়ির দালালি করত, কেউ ড্রাইভারি- ওদের সচ্ছলতা হয়তো কম ছিল, কিন্তু আন্তরিকতা ছিল আকাশ ছোঁয়া। (Vishvakarma Puja)
“জয়াদির বাড়িতে রান্না-পুজোর আয়োজন ছিল এলাহি। চার পাঁচ রকমের মাছ, ভাজাভুজি, দু’রকমের ভাত, চাটনি এমনকি পায়েস অবধি।”
বাসন্তী কাকিমার ছেলেপুলে ছিল না। উনি ওই রান্না পুজোর খাবার আমাকে কখনও কখনও নিজে হাতে খাইয়ে দিতে চাইতেন। সেইরকম রান্না-পুজো অনেক পরে খেয়েছি কোয়ার্টার্সের জয়াদির বাড়িতে। বড় মজার মানুষ ছিল জয়া ভট্টাচার্য। স্বামীর মৃত্যুর পর সরকারি চাকরি পেয়েছিল। সঙ্গে ফ্যামিলি পেনশন। কিন্তু গোপনে আরেকটি বিয়ে করেছিল জয়াদি। সকালে অফিস যেত শাঁখা-সিঁদুরহীন বৈধব্য বেশে আবার সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে, গা ধুয়ে সিঁথি ভরতি করে জয়াদি সিঁদুর পরে নিত। শাঁখা-পলা গলিয়ে নিত দুই হাতে! জয়াদির বাড়িতে রান্না-পুজোর আয়োজন ছিল এলাহি। চার পাঁচ রকমের মাছ, ভাজাভুজি, দু’রকমের ভাত, চাটনি এমনকি পায়েস অবধি। (Vishvakarma Puja

এই জয়াদির এক সময় ব্রেনস্ট্রোক হল। মাথার অপারেশন হল পিজিতে। ডাক্তার বলল সেরে উঠবে। কিন্তু চার-পাঁচ মাস বিছানা বন্দি থাকার পর একদিন দুপুরে, খালি বাড়িতে, জয়াদি মারা গেল। (Vishvakarma Puja)
না, সে-বছর বিশ্বকর্মা পুজো কোয়ার্টার্সে বন্ধ হয়নি। তখন কোয়ার্টার্সের যত ড্রাইভার অর্থাৎ সরকারি দপ্তরের যাঁরা গাড়ি চালাতেন তাঁরা এক জোট হয়ে একটা বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করতেন। কিন্তু তারও আগে কোয়ার্টার্সের অফিস ঘরে একটা ছোট্ট বিশ্বকর্মা ঠাকুর এনে পুজো হত। এখানে পুজোর ব্যবস্থা করত ইলেকট্রিশিয়ান, প্লাম্বার আর সুইপারের কাজ-করা লোকেরা। (Vishvakarma Puja)
‘আরও পড়ুন: মাটির শরীরে তুলির টান
পুজোর দিন ফলমূল প্রসাদ হলেও পরদিন থাকত ভাত আর খাসির মাংসের বিরাট আয়োজন। তবে সেটা অফিসের লোক ও তাদের পরিবারের জন্য। অফিসের লোকেরা একে অপরের পরিচয় দিত ‘স্টাপ’ হিসেবে। খাসির মাংসের দিন সন্ধ্যাবেলা অফিসের অনেকের চোখ লাল থাকত। টলে পড়ে যেতে অবশ্য কাউকে কখনও দেখিনি। রমেশ কাকুর ছেলে মুকেশ ছিল আমার বন্ধু। ওই অফিস ঘরে ছিল ওদের থাকার ব্যবস্থা। রমেশ কাকু কোয়ার্টার্সে সুইপিঙের কাজ করতেন। ওইটুকু ঘর, যেটা সকালে কোয়ার্টার্সের অফিসঘর আর বিকেলে হয়ে উঠত ওদের সংসার, সেখান থেকে পড়াশোনা করে মুকেশ মাধ্যমিকে স্টার পেয়েছিল। (Vishvakarma Puja)
আমার মা বিশ্বকর্মা পুজোকে ‘রিশকাআলা গো পূজ়া’ বললেও আমরা পুজোর দিন বাচ্চাকাচ্চারা ঠাকুর দেখতে বেরোতাম মায়ের সঙ্গেই। টালিগঞ্জ পাড়ার কোয়ার্টার্সে আমাদের বসবাস, অতএব আমাদের উদ্দেশ্য থাকত প্রথমে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর বিশ্বকর্মা ঠাকুর দেখা, তারপর টেকনিশিয়ান স্টুডিওর ভেতরের তিনটে বিশ্বকর্মা ঠাকুর দেখা, শেষে এন.টি ওয়ানের বিশ্বকর্মা দেখে বাড়ি ফেরা। পথের সব রিকশা স্ট্যান্ডের পুজোগুলোতে আমরা দাঁড়াতাম আর যেখানে পারতাম গরম গরম খিচুড়ি সাঁটাতাম। খিচুড়ি খাওয়ার ব্যাপারে ‘রিশকাআলা গো পূজ়ায়’ অংশগ্রহণ করতে আমার মায়ের কোনও দ্বিধা ছিল না। (Vishvakarma Puja)
“যত দোষ রিকশাওয়ালাদের। তাদের সব উৎসব হাসির খোরাক। বিশ্বকর্মা যেন বাঙালি সংস্কৃতিতে আজও জাতে ওঠেননি! বাঙালি এখনও সে-পুজো বিষয়ে নাক কোঁচকায়।”
আরেকটু বড় হয়ে গিয়েছি যখন, পমপমের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, ওদের বাড়িতে খুব যাতায়াত আর ওদের বাড়ির তীজ, কৌরভা চথ, ছটপুজো, শনিবারের খিচুড়ি- সব কিছুর মধ্যে ঢুকে পড়েছি তখন ওদের পরিচিত একজন ছিলেন ‘জমিনের কাকু’ বলে আমাকে কাকিমা পরিচয় করাতেন, যার সঙ্গে মানে পমপমদের আর সেই কাকুদের এক জায়গায় জমি কেনা ছিল, সেই কাকুর কাঠের দোকানে আমার বিশ্বকর্মা পুজোর নেমন্তন্ন থাকত। ওখানে নেমন্তন্ন মানে খাসির মাংস আর ভাত। মহাতৃপ্তি করে খেয়ে বাড়ি ফিরতাম। সেটা বিশ্বকর্মা পুজোর পরের দিন। (Vishvakarma Puja)
ফেরার সময় দেখতাম সেই রিকশাওয়ালারা মহানন্দে ভ্যানে করে ঠাকুর ভাসাতে যাচ্ছে। ভ্যানের পাশে একটি রিকশায় এক ভদ্রলোক বসে একটা সিন্থেসাইজার মতো জিনিসে গান বাজাচ্ছে ‘দো ঘুট মুঝে ভি পিলা দে শরাবি/দেখ ফির হোতা হ্যায় ক্যায়া…’ আর ভাসানিরা উদ্দাম নৃত্য করছে। কখনও কখনও আবার চিৎকার করে বলছে, ‘বোলো বিশ্বকর্মা মাঈ কী জয়য়য়য়য়য়!’ (Vishvakarma Puja)

মা যেটা বলত এখন সেরকম ছবি অনেক চোখে পড়ে। এখন বিশ্বকর্মা পুজোর আগে সমাজ মাধ্যমে দেখি এক মত্ত রিকশাওয়ালা রিকশা থেকে উল্টে পড়ে আছে— সেই ছবি। ওটা বিশ্বকর্মা পুজোর আগমন বার্তার কৌতুকময় ছবি। কী অপূর্ব শিক্ষা আমাদের! এদিকে দুর্গা পুজো-কালী পুজো বা দিওয়ালিতে কত মানুষ যে মদ খেয়ে ফেরে তার হিসেব নেই। (Vishvakarma Puja)
যত দোষ রিকশাওয়ালাদের। তাদের সব উৎসব হাসির খোরাক। বিশ্বকর্মা যেন বাঙালি সংস্কৃতিতে আজও জাতে ওঠেননি! বাঙালি এখনও সে-পুজো বিষয়ে নাক কোঁচকায়। এ-ব্যাপারে তার আকাশ এখনও পরিষ্কার নয়। (Vishvakarma Puja)
তেমনই এক আকাশের তলায় বসে আছি আমি আর টুবলুদা। হঠাৎ মেঘের ভ্রুকুটি আমাদের ঘুড়ি-ওড়ানোতে বাধা দিচ্ছে। মন খারাপ হয়ে আসছে। টুবলুদা, অপূর্ব সুন্দর দেখতে আমার এই দাদাটি পড়াশোনায় তত ভাল না। ওর খোলা আকাশ আর ঘুড়ি ভাল লাগে। কিন্তু বাড়িতে তা মানে না। টুবলুদা প্ল্যান করছে বম্বে পালিয়ে যাবে একদিন। ওখানে ফিল্মে চান্স নেবে। আর আমার কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে আমাদের তো এরকম আর ঘুড়ি ওড়ানো হবে না টুবলুদা বম্বে পালিয়ে গেলে! (Vishvakarma Puja)
সে যা হোক, টুবলুদার বম্বে যাওয়া হয়নি, মাঝ রাস্তা থেকে ফিরিয়ে এনেছিল বাড়ির লোক। আমারও আর তেমন ছাদে ওঠা হয়নি। আরও হয়নি কারণ কোয়ার্টার্সের অরূপদা ওই ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল। সেটাও ছিল একটা বিশ্বকর্মা পুজোর দিন। সারা কোয়ার্টার্সে তীব্র শোকের ছায়া নেমে এসেছিল। আর আমরা জীবনের আকাশে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়েছিলাম একেক জন। (Vishvakarma Puja)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ভাস্কর মজুমদার লেখেন মূলত প্রবন্ধ, উত্তরসম্পাদকীয় নিবন্ধ, কলাম ও ছোটগল্প। যৌনসংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক মানুষ, স্কুলশিক্ষা, শাস্ত্রীয়সঙ্গীত, নৃত্য ও সিনেমা তাঁর বেশিরভাগ লেখার বিষয়। অনুবাদকর্মের সঙ্গেও তিনি বহু বছর যুক্ত। সম্প্রতি কলকাতা দূরদর্শনের পক্ষ থেকে তাঁর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।