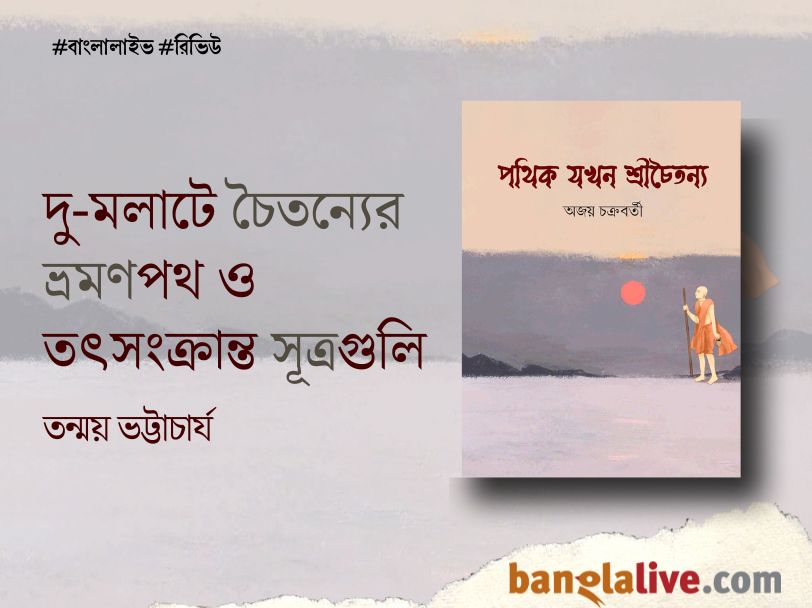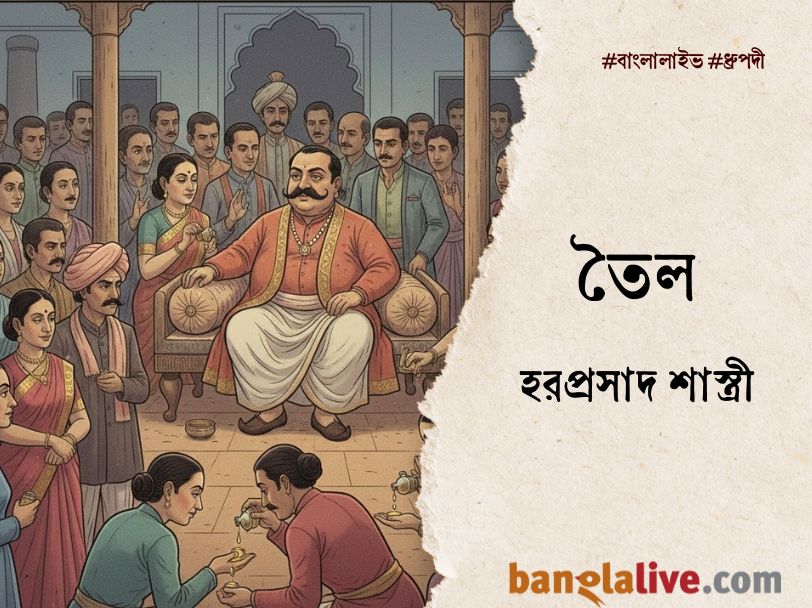(Chaitanya)
বইয়ের নাম: পথিক যখন শ্রীচৈতন্য
লেখক: অজয় চক্রবর্তী
প্রচ্ছদ: দিবাকর চন্দ
প্রকাশক: ব্ল্যাকলেটার্স
বিনিময় মূল্য: ৩০০ টাকা
ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ। বাংলায় তখন হুসেন শাহ-র রাজত্ব। সেই পটভূমিতে নবদ্বীপে নিমাই-এর উত্থান, প্রচার-প্রসার, সন্ন্যাসগ্রহণ ও নীলাচলযাত্রা এবং পরবর্তীতে ভ্রমণ। তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের ভূগোল, ইতিহাস ও সমাজকে বুঝতে গেলে নিমাই তথা চৈতন্য ও তাঁর পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝা জরুরি— এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে চৈতন্যচরিত কাব্যগুলিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ উঠে এসেছে বারংবার। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে আলোচনা পল্লবিত হয় বিভিন্ন দিকে, যার অন্যতম চৈতন্যের ভ্রমণপথ। সেই সংক্রান্ত আলোচনারই নবতম সংযোজন অজয় চক্রবর্তী লিখিত বই ‘পথিক যখন শ্রীচৈতন্য’। (Chaitanya)
চৈতন্যজীবনী বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলি হল বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’, জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’, লোচনদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘চৈতন্যচরিতামৃত’। শেষেরটি ছাড়া বাকি সবগুলিই ষোড়শ শতকে লিখিত। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের ভূগোল ইতিপূর্বে বিপ্রদাস পিপিলাই-এর ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে (১৪৯৫) খানিকটা উঠে এলেও, তার অনেক স্থান-বিবরণী প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্তীতে সংযোজিত বলে মনে করেন গবেষকরা। চৈতন্যচরিতগুলিতে সেই অভিযোগের আঙুল ওঠে না। বিশেষ করে বৃন্দাবনদাস যখন ‘চৈতন্যভাগবত’ লিখছেন (১৫৪৮), তাতে উল্লিখিত স্থানগুলি যে সমকালে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তা সন্দেহাতীত। পরবর্তী কাব্যগুলিও সেই ধারাই বহন করেছে। ফলে, বিপ্রদাস পিপিলাই ও মুকুন্দ চক্রবর্তীর দুই মঙ্গলকাব্যের মধ্যবর্তী চৈতন্যচরিতগুলি তৎকালীন ভূগোল ও স্থানমাহাত্ম্যের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। (Chaitanya)
আরও পড়ুন: কলোনির রাহুল, রাহুলের কলোনি: এক অচ্ছেদ্য বোঝাপড়া
অজয় চক্রবর্তীর গ্রন্থটির ভরকেন্দ্রও সেই স্থানই, বইয়ের নাম থেকেই তা স্পষ্ট। ‘পথিক যখন শ্রীচৈতন্য’— সন্ন্যাসগ্রহণের আগে ও পরে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে চৈতন্যের ভ্রমণবৃত্তান্ত উঠে এসেছে এই বইয়ে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থের অংশ হিসেবে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। হিতেশরঞ্জন সান্যাল, বিমানবিহারী মজুমদার, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী সহ অনেকেই এ-বিষয়ে আলোকপাত করেছেন, বিভিন্ন দ্বন্দ্বগুলি বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র চৈতন্যের ভ্রমণ-কেন্দ্রিক বই বাংলাভাষায় বিরল। সেখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আলোচ্য গ্রন্থটি। (Chaitanya)
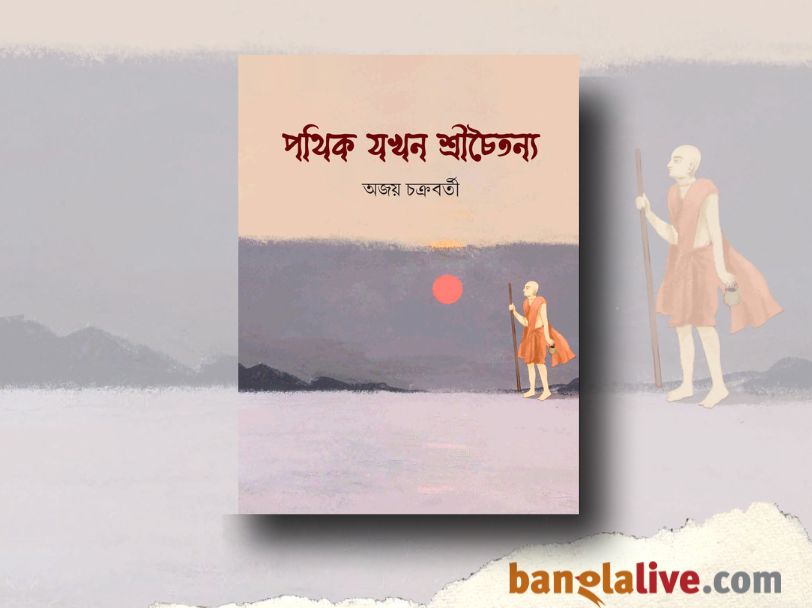
লেখক এ-বইয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সমগ্র বিষয়টি ধরতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের ‘কাঁহা গেলে তোমা পাই’ স্মর্তব্য। সেখানেও বিভিন্ন কথোপকথনের মধ্যে দিয়েই বুঝতে চাওয়া হয়েছিল বইয়ের মূল বিষয়কে। এই জাতীয় উপস্থাপনা সুখপাঠ্য, কেন-না তথ্য ও বিশ্লেষণের ওপরে একধরনের কাহিনিধর্মিতার পরত থাকে, যা সাধারণ পাঠকের আকর্ষণ ও মনোযোগ ধরে রাখে। আবার নন-ফিকশন হিসেবে বিচার করতে বসলে এই উপস্থাপনা পাঠককে জায়গায়-জায়গায় মূল বিষয় থেকে সরিয়ে দেওয়ার সম্ভাবনাও রাখে। অজয় নিপুণ হাতে সেই রাশ টেনে রাখলেও, বর্ণনার মধ্যে কাহিনিধর্মিতার চলন মাঝেমধ্যে আলোচ্য বিষয় থেকে নজর ঘুরিয়েছে, যদিও তা কাঠামো নির্মাণের পক্ষে একপ্রকার উপকারী। তবে তথ্য, আলোচনা ও তার বিশ্লেষণের যে-অভ্যস্ত গদ্যভাষা, তা এই উপস্থাপনায় অনুপস্থিত। (Chaitanya)
“লেখক মূলত প্রধান কয়েকটি চরিতকাব্যকে আশ্রয় করেই লিখেছেন, ফলে তার বাইরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে।”
নবদ্বীপের পটভূমি, চৈতন্যের উত্থান, বিকাশ ও বিস্তারকে যথাযথভাবে ধরার চেষ্টা করেছেন অজয়। সন্ন্যাসজীবনের পূর্বে নবদ্বীপের বাইরে শ্রীহট্ট ও গয়ায় ভ্রমণ, পরবর্তীতে নীলাচল, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গভ্রমণের বিবিধ প্রসঙ্গ চরিতকাব্যগুলির ওপর নির্ভর করে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। সেইসঙ্গে উঠে এসেছে যাত্রার উদ্দেশ্য ও পশ্চাদ্পটও। ফলে শুধুমাত্র ভ্রমণপথের বর্ণনা হয়ে থাকার পরিবর্তে সম্পূর্ণতা পেয়েছে বইটি। (Chaitanya)
বিশেষ করে চৈতন্যের দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ সংক্রান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা প্রশংসনীয়। এছাড়াও সর্বত্রই বর্ণনা বা প্রেক্ষিতের পাশাপাশি চরিতকাব্য থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন অজয়, যা বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়। সেইসঙ্গে মূল উৎসগুলির রূপের সঙ্গেও পাঠক পরিচিত হতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষে বিস্তৃত আলোচনা, গবেষকদের উদ্ধৃতি বিষয়ের গভীরে যেতে সাহায্য করে। তা ছাড়া, বর্তমান নবদ্বীপকে চেনার প্রাথমিক উপাদান হিসেবেও এই বই গুরুত্বপূর্ণ। (Chaitanya)
“নদী ধরে যাত্রাপথে স্থানগুলিতে হাজির হওয়া অসম্ভবও নয়। কিন্তু সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও চরিতকাব্যে অনুল্লেখ-হেতু এ-বিষয়ে আরও আলোচনা ও গবেষণা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থে তা ধরা গেলে, উপকৃত হতেন পাঠকই।”
তবে বেশ-কিছু বিষয় বা স্থান উল্লিখিত হলেও, তার বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করেননি লেখক। অথচ, তা গ্রন্থভুক্ত হলে চৈতন্যের কার্যকলাপের পাশাপাশি আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ হত। যেমন কুমারহট্টে (বর্তমান হালিশহর) অবস্থিত চৈতন্যডোবা— কথিত আছে, গুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান সেখানে। (Chaitanya)
আরও পড়ুন: ক্রোড়পত্র: ‘দেশগাঁয়ে ছিল কিন্তু ছেড়ে আসা প্রতিটি মানুষ’
চৈতন্য ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সেখানে গিয়ে গুরুর জন্মভিটের মাটি সংগ্রহ করেন ও সেখানে একটি ডোবা জন্ম নেয়। অদূরে, গঙ্গাতীরে অবস্থিত চৈতন্যঘাটও। এছাড়াও পানিহাটি ও বরানগরে চৈতন্যের আগমন ও ‘লীলা’-র বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে চরিতকাব্যগুলিতে, যা অজয়ের লেখায় অনুপস্থিত। পানিহাটিতে চৈতন্যের আগমন, রাঘব পণ্ডিতের ভিটেয় যাত্রা, বরানগরে ভাগবতাচার্য্যের গৃহে গমন ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচিত হলে তা বইয়ের বিষয়ের প্রেক্ষিতে যথোপযুক্ত হত। (Chaitanya)
এমনকি, নব্বই বছর ধরে প্রতিবছর চৈত্র মাসে চৈতন্যের নৌকাযোগে পানিহাটি থেকে বরানগর যাত্রা উদযাপিত হয়, অংশ নেন অগণিত ভক্ত, যা একপ্রকার চৈতন্যের ভ্রমণপথেরই উদযাপন। সমকালের এই উৎসবটি গ্রন্থভুক্ত হওয়া নিতান্তই জরুরি ছিল। (Chaitanya)
“চৈতন্যের বঙ্গভ্রমণ পথ-সংক্রান্ত বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের যে-ফারাক, তা লেখক ছুঁয়ে গেলেও আরও বিস্তৃত বর্ণনা ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ কাম্য ছিল।”
লেখক মূলত প্রধান কয়েকটি চরিতকাব্যকে আশ্রয় করেই লিখেছেন, ফলে তার বাইরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়েছে। যেমন একটি সমস্যা— বেশ-কিছু জায়গায় চৈতন্য গিয়েছিলেন বলে স্থানীয় জনশ্রুতি, অথচ চরিতকাব্যগুলিতে তার উল্লেখ নেই। এই সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন হিতেশরঞ্জন সান্যালও। শেওড়ফুলি, বৈদ্যবাটী, কোন্নগর ইত্যাদি হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদগুলিতে চৈতন্যের উপস্থিতির মিথ প্রচলিত। নদী ধরে যাত্রাপথে স্থানগুলিতে হাজির হওয়া অসম্ভবও নয়। কিন্তু সম্ভাব্যতা সত্ত্বেও চরিতকাব্যে অনুল্লেখ-হেতু এ-বিষয়ে আরও আলোচনা ও গবেষণা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থে তা ধরা গেলে, উপকৃত হতেন পাঠকই। (Chaitanya)
“তবে বইটির আপাত-আখ্যানধর্মিতাই যে সেই গভীরতায় প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক, তা অনুমেয়। ফলে, চৈতন্যের ভ্রমণ-বিষয়ে কৌতূহলী অথচ অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে বইটি বিশেষ উপকারী।”
একইভাবে, চৈতন্যের বঙ্গভ্রমণ পথ-সংক্রান্ত বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের যে-ফারাক, তা লেখক ছুঁয়ে গেলেও আরও বিস্তৃত বর্ণনা ও যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ কাম্য ছিল। বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছিলেন— ‘বাঙ্গালী লেখকেরা শ্রীচৈতন্যের বাংলাদেশ-পরিভ্রমণ-বিষয়েই যখন এক মত হইতে পারেন নাই, তখন তাঁহার দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-বর্ণনায় যে তাঁহাদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ থাকিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।’ এই কারণেই নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থে পাঠক গভীর আলোচনার প্রত্যাশী হতেই পারেন! (Chaitanya)
এছাড়াও, পরিশিষ্ট অংশে বা অন্যত্র নিত্যনন্দের ভ্রমণপথ বা ধর্মপ্রচারের স্থানগুলি নিয়ে আলোচনা থাকলে (যার তালিকা জয়ানন্দ তাঁর কাব্যে বিস্তারে দিয়েছেন) সমকালের ভূগোল ও জনপদের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বোঝাপড়ার পরিসর আরও বিস্তৃত হত। মূল বিষয় চৈতন্য-কেন্দ্রিক হলেও, নিত্যানন্দের সংযোজন খুব অপ্রাসঙ্গিক হত না এ-বইয়ে। (Chaitanya)
আরও পড়ুন: রতন থিয়াম: থিয়েটার, সময় আরও অনেক কথা
তবে বইটির আপাত-আখ্যানধর্মিতাই যে সেই গভীরতায় প্রবেশের পথে প্রতিবন্ধক, তা অনুমেয়। ফলে, চৈতন্যের ভ্রমণ-বিষয়ে কৌতূহলী অথচ অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে বইটি বিশেষ উপকারী। এই জাতীয় বিষয় সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার আধারে লিখিত হয় বলে, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে ভাষা ও উপস্থাপনাগত দূরত্ব থেকেই যায়। নির্দিষ্ট শ্রেণির মধ্যেই ঘোরাফেরা করে বইগুলি। অজয় চক্রবর্তীর ‘পথিক যখন শ্রীচৈতন্য’ সেই সীমিত গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর পাঠকসমাজকে মাথায় রেখে লেখা। (Chaitanya)
আগ্রহ জাগানোর পক্ষে এই উপস্থাপনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আলোচ্য বিষয়ের ‘প্রাইমার’ হিসেবে বইটি সমাদর লাভ করুক, চৈতন্যের ভ্রমণ ও তৎসংক্রান্ত ভূগোলচর্চা গুরুত্ব পাক আরও— তাহলেই সার্থক হবে এই প্রয়াস। সর্বোপরি, বাংলার সমাজেতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়-পাঠে ইন্ধন জোগানোর জন্য লেখক ও প্রকাশককে অভিনন্দন। (Chaitanya)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।