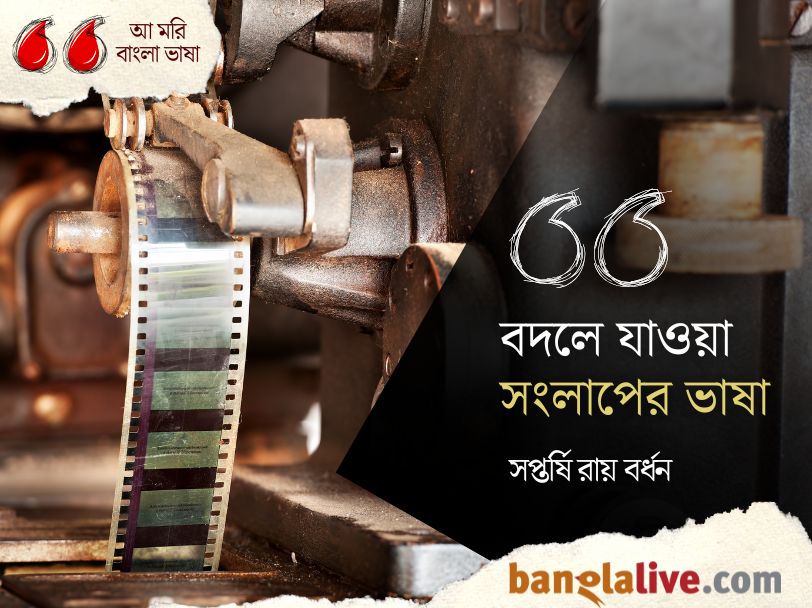আ মরি বাংলা ভাষা
(Bengali Dialogue)
ভাষা এক বহতা নদী। অর্থাৎ ভাষা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, মুখে মুখে বিবর্তিত হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় নতুন শব্দ যুক্ত হয়, উচ্চারণ বদলে যায়, কিংবা বদলে যায় তার প্রয়োগ। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন নিত্য নৈমিত্তিক। সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রের সংলাপ প্রসঙ্গে বলেছিলেন “সাহিত্যের কাহিনীতে কথা যে কাজ করে, চলচ্চিত্রে ছবি ও কথা মিলিয়ে সে কাজ হয়।” বাংলা ছবিতে, সবাক কালের ইতিহাসে, সংলাপবিহীন বা স্বল্প সংলাপ ছবির দৃষ্টান্ত এতটাই কম যে তাঁর মতে “বেশির ভাগ ছবিতেই আমরা বাস্তবধর্মী সংলাপ শুনি, বা শোনার চেষ্টা করি।” এবং দর্শক হিসেবে সেইসব সংলাপ আমরা মনের মধ্যে সাদরে লালন করি, প্রয়োজনে তা কাজে লাগে প্রাত্যহিক জীবন যাপনে। (Bengali Dialogue)
টকি হিসেবে নির্মিত প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র ‘জামাই ষষ্ঠী’। ১৯৩১ সালে মুক্তি পায়। এ ছবির সংলাপ লিখেছিলেন পরিচালক অমর রায় চৌধুরী খোদ নিজের হাতে। তারপর একটা দীর্ঘ আট দশকের পথ হেঁটে সিনেমা এসে দাঁড়ায় বিংশ শতাব্দীর উপান্তে। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটকের ভাষায় বাংলার যে মেটামরফোসিস হয়েছে, তার থেকে মুক্তি পায়নি চলচ্চিত্রের সংলাপও। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ফিল্মি সংলাপ বাংলা ভাষার রূপ এবং প্রয়োগে বদলে গিয়েছে। (Bengali Dialogue)
সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটকের ভাষায় বাংলার যে মেটামরফোসিস হয়েছে, তার থেকে মুক্তি পায়নি চলচ্চিত্রের সংলাপও।
বাংলা সিনেমার কারিগরেরা প্রথাগতভাবে সিনেমার গল্পের জন্য অবগাহন করেছেন বাংলা সাহিত্যের মহাসাগরে। কী নেই সেখানে? রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিম থেকে শুরু করে প্রফুল্ল রায়, বনফুল, শরদিন্দু, সত্যজিৎ, সুনীল, তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, সুবোধ ঘোষ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বিমল কর, শিবরাম চক্রবর্তী, পরশুরাম, সমরেশ বসু, বিভূতিভূষণ, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, আশাপূর্ণা দেবী, লীলা মজুমদার– এরকম বহু প্রথিতযশা লেখক, সাহিত্যিকদের বলা বাংলা ও বাঙালি জীবনের পাঁচমেশালি গল্প সিনেমার রসদ জুগিয়েছে। সংলাপ লিখিয়েদের, সুচারু লেখনীর টানে সেসব সাহিত্যকীর্তি পেয়েছে পর্দার ভাষা। চিত্রনাট্টের উপাদানে, ক্যামেরার কারুকৃতি ও সম্পাদনা যোগ করেছে সিনেমার আঙ্গিক। (Bengali Dialogue)
আরও পড়ুন: শব্দ তুমি চিত্রকল্প বিধি
বইয়ের পাতা থেকে চোখ তুলে সিনেমার পর্দায় চোখ রেখেছে দর্শক; না পড়ে, এবার “বই” দেখার পালা। নিউ থিয়েটার্স এবং তার কর্ণধার বি.এন.সরকার এই ব্যাপারে অগ্রগণ্য। তিনি বুঝেছিলেন বাঙালিকে যদি সিনেমায় মজাতে হয় তবে সাহিত্য নির্ভর ছবি বানাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যদি কোনও সাহিত্যিককেই দেওয়া যায় সংলাপ লেখার দায়িত্ব তবে তিনি আর যাই করুন না কেন “মারব এখানে আর লাশ পড়বে শ্মশানে” জাতের সংলাপ লিখবেন না। (Bengali Dialogue)

বাংলা সাহিত্য থেকে নেওয়া গল্পের স্বাদু চিত্রনাট্য রূপান্তরের কাজ তিনি সঁপেছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকদের উপরে। পরের দিকে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ, অখিল নিয়োগী, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সর্বোপরি সত্যজিৎ স্বয়ং সংলাপ লেখার কাজ করেন। এখানে নির্বাক যুগের মধু বসু, সাধনা বসুর “গিরিবালা” ছবিটি উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ নাকি ঐ ছবিতে ব্যবহৃত “মেয়েমানুষ” শব্দ বদলে “গিন্নি মা” ব্যবহার করার উপদেশ দিয়েছিলেন, অর্থাৎ ভাষাকে আরেকটু পরিশীলিত করতে বলেছিলেন। (Bengali Dialogue)
সাহিত্য নির্ভর ছবি বানাতে হবে এবং সেক্ষেত্রে যদি কোনও সাহিত্যিককেই দেওয়া যায় সংলাপ লেখার দায়িত্ব তবে তিনি আর যাই করুন না কেন “মারব এখানে আর লাশ পড়বে শ্মশানে” জাতের সংলাপ লিখবেন না।
এর ফলে বইয়ের পাতা থেকে উঠে আসা চরিত্ররা তাদের চলনে বলনে কাহিনি সূত্র থেকে বিচ্যুত হল না ঠিকই কিন্তু এতদসত্ত্বেও “সাহিত্যের গল্প” আর “ছায়াছবির গল্প” এ দুইয়ের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম তফাৎ থেকেই গেল। দিনের শেষে সিনেমাকে একটা পপুলার আর্ট হিসেবে দর্শকের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করতেন পরিচালক আর তার জন্য, বাকি পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে সংলাপের মাল মশলা প্রয়োগের প্রতি থাকত তাঁর সজাগ দৃষ্টি। অবশ্য এ দোষে শুধু বাংলা নয়, অন্যান্য ভারতীয় ছবিও দুষ্ট! (Bengali Dialogue)
তিরিশ, চল্লিশের দশকে বাংলা ছবির প্রধান শ্রেণি বিভাগ করা যেত সামাজিক, ধর্মমূলক ও পৌরাণিক- এই তিন ভাগে। সেই সময়ের পরিচালক, প্রযোজকদের কাছে এই নতুন কথা বলা বিনোদন মাধ্যম নিয়ে উৎসাহ যেমন কম ছিল না, তেমনই এর ব্যবসায়িক সাফল্য নিয়ে ছিল দ্বন্দ। অতএব বাংলা রঙ্গমঞ্চের মঞ্চসফল চেনামুখ অভিনেতা অভিনেতৃদের দিয়ে বাজিমাত করবার একটা প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল প্রথম থেকেই। সুতরাং সংলাপের বৈচিত্র্য থাকলেও তা হয়ে যেত মঞ্চের আধারে অভিনয়– কোথাও যেন তৈরি করত এক ধরণের অতিনাটকীয়তা। (Bengali Dialogue)
সংলাপের বৈচিত্র্য থাকলেও তা হয়ে যেত মঞ্চের আধারে অভিনয়– কোথাও যেন তৈরি করত এক ধরণের অতিনাটকীয়তা।
সেদিক থেকে বিমল রায়ের “উদয়ের পথে” একটি নতুন পথের মোড় বলা যেতে পারে। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের মতে তখন মন দিয়ে ডায়লগগুলি শুনত দর্শক। এমনকি অনেক বাঙালির “উদয়ের পথে” এর ডায়লগগুলো মুখস্থ ছিল। যেমন পরবর্তীকালে “শোলে” এর ডায়লগ অনেক ভারতীয় মুখস্থ করেছিলেন। “এখানে মনে রাখতে হবে ভারতীয়রা যেমন সিনেমা দেখে তেমনি কিন্তু শোনেও এবং ডায়ালগগুলো মনে রাখে। আমাদের দেশে শ্রুতি সংস্কৃতি খুব শক্তিশালী। তুলসিদাসের রামায়ণ খুব কম লোকেই পড়ে, কিন্তু অনেকেই শুনে মনে রাখে। (Bengali Dialogue)
আরও পড়ুন: দেবরাজ রায় : এক সাদাকালো সময়ের ছবি
রামায়ণকথা, লোককথাগুলো আসলে শ্রুতি পথেই মানুষের কাছে আসে। সিনেমা আসলে আরবান ফোকলোর বা শহুরে লোকনাট্য। তাই সেই সময়ে সিনেমা এই নীতিটাকে গ্রহণ করেছে।”
স্বাধীনতাত্তোর বাংলা ছবির সংলাপে ভাষার প্রয়োগে দেখা যায় রূপান্তর। দেশভাগ এবং তাকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েন তার ছাপ এসে পড়ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে। স্বাভাবিকভাবেই এপারের বাংলা ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়ে ওপার বাংলার কথ্য ভাষা যার মিশেলে তৈরি হয় “মাসিমা মালপো খামু” জাতীয় সংলাপ। নিমাই ঘোষের “ছিন্নমূল” ছবিতে “বাঙাল” ভাষা উদ্বাস্তু মানুষগুলোর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে যেন ঢুকে পড়ল শহর কলকাতার “এদেশিয়” মহল্লায়। এরই মাঝে ১৯৫৫ সালে “পথের পাঁচালি” সংলাপ বহুল চিত্রনাট্যের থেকে মুখ ঘুরিয়ে তৈরি করেছিল সিনেমার এক নতুন ভাষা। নৈঃশব্দ্য, সীমিত আবহ আর ন্যূনতম সংলাপ জুড়ে পল্লিবাংলার ছবি আঁকা হল সাদা-কালো সেলুলয়েডে। পণ্ডিত মশাই হিসেবে তুলসি চক্রবর্তীর “এই সেই জলস্থান মধ্যবর্তী” মনের মাঝে থেকে গেলেও “পথের পাঁচালি” আদপে দৃশ্য নির্ভর সিনেমা- যা দেখে আমরা অপু-দুর্গার নিশ্চিন্দিপুরকে চিনি। (Bengali Dialogue)
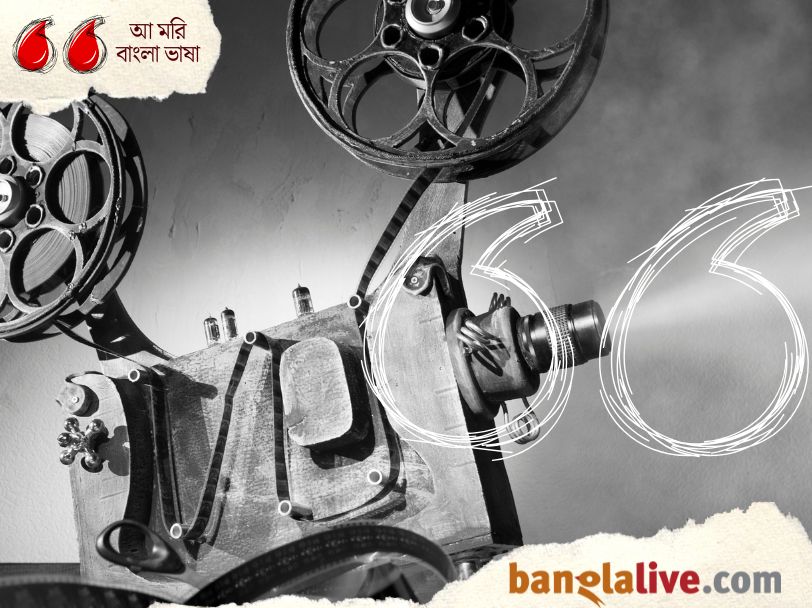
ষাট এবং সত্তরের দশক আসলে এক অর্থে বাংলা ছায়াছবির স্বর্ণময় একটা পর্যায়। সিনেমার কারিগরি ও পরিকাঠামোগত উন্নতির সমান্তরালে এসেছিলেন অসংখ্য নতুন পরিচালক, অভিনেতা, কাহিনিকার, গীতিকার, সুরকার। দর্শক বিনোদন মাধ্যম হিসেবে নাটক এবং বেতারের পাশাপাশি গ্রহণ করেছে সিনেমাকে– সে বাংলা হোক, বা হিন্দি বা হলিউডি এবং সব থেকে বড় কথা সিনেমা একটি ব্যবসায়িক বিকল্প হিসেবে পরিগণিত হতে শুরু করেছে। (Bengali Dialogue)
বাংলা ছবির সংলাপে ভাষার প্রয়োগে দেখা যায় রূপান্তর। দেশভাগ এবং তাকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক টানাপোড়েন তার ছাপ এসে পড়ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে।
দেশভাগের চালচিত্রে ঋত্বিক ঘটকের ছবি “সুবর্ণরেখা”, “মেঘে ঢাকা তারা” এবং “কোমল গান্ধার” সিনেমার এক নতুন ভাষা তৈরি করে। শহুরে বাংলার সঙ্গে গ্রাম্য ডায়ালেক্ট জুড়ে “রাইত কত হ’ল, উত্তর মেলে না” এখনও মনের ভিতরে সাড়া জাগায়; রোগগ্রস্ত নিতার আর্তি “দাদা আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম” তৈরি করে এক অদ্ভুত অনুরণন। (Bengali Dialogue)
উত্তমকুমারের বাংলা ছবিতে আসা আরেকটা টার্নিং পয়েন্ট। সংলাপের ভাষার সঙ্গে যোগ হয় তাঁর নায়কোচিত উপস্থাপনা যা আসলে সেই সব সংলাপের তীক্ষ্ণতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। “নায়ক” ছবিতে “আমি তো আছি, ইজিনট দ্যাট এনাফ” বা “আই ওয়ান্ট টু গো টু দ্যা টপ, টু দ্যা টপ, টু দ্যা টপ” এভাবেই দাগ কেটে গেছে দর্শকের মনে। আসলে সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে সত্যজিত রায়ের প্রায় সব ছবিতেই সংক্ষিপ্ত সংলাপ বা বাক্যবন্ধের সঙ্গে একেবারে কথ্য বাংলার একটা অদ্ভুত ফিউশান ঘটে গেছে। অন্য ছবি বাদ দিয়ে, শুধু গুগাবাবা আর ফেলুদার দু-জোড়া ছবি, যা এই সব মজাদার আকর্ষণীয় সংলাপের আঁতুড়ঘর, দেখলেই পাওয়া যায় তার সম্যক পরিচয়। “তৃতীয় সুর আর ষষ্ঠ সুর”, “আর বিলম্ব নয়”, “জানার কোনও শেষ নাই, জানার চেষ্টা বৃথা তাই”, “মগজ ধোলাই”, “যন্তর মন্তর ঘর”, “মগজাস্ত্র”, “তংগ মাত করো”, “কাঁটা কি এরা বেছে খায়”, “এটা আমার”, “এদিকে চারশ, এদিকে চারশ”, “লালমোহন, মোহনলাল, মগনলাল সব লালে লাল”– এরা আমাদের ডিকশনারিতে প্রবেশ করেছে অনায়াসে। যেমন জায়গা করে নিয়েছে ১৯৮৬ সালের “আতঙ্ক” ছবির “মাস্টারমশাই আপনি কিন্তু কিছুই দেখেননি” অথবা “দাদার কীর্তি” এর “প্র্যাক্টিকাল ক্লাস”! (Bengali Dialogue)
আরও পড়ুন: প্রতিবেশী: চলচ্ছবির প্রতিবেশীরা
এখানে একটা জিনিস বলা দরকার। সময়ের নিরিখে শালীন এবং অশালীনের সংজ্ঞা বদলে যায়। অর্থাৎ আজ সংলাপে যে ভাষা ব্যবহার করলে ব্যাপারটা ভাল দাঁড়ায় কিন্তু করা যাচ্ছে না, কারণ তা হয়তো বা পেরিয়ে যাবে শালীনতার আরোপিত সীমা, আজ থেকে এক দশক পরে সে হয়তো অনায়াসে ঢুকে পড়েছে কোনও রকম ভ্রু কুঞ্চনের পরোয়া না করেই। ১৯৭৫ সালের ২১শে মার্চ শক্তি সামন্তের “অমানুষ” রিলিজ করলে, তার গান সুপার হিট। বাকি সব গানগুলি বেতারে শোনা গেলেও “বিপিন বাবুর কারণ সুধা, মেটায় জ্বালা মেটায় ক্ষুধা” গানটি বাজানো হত না। এর অন্যতম কারণ প্রথম অন্তরার শেষে একটি “শালা” যা পুরো গানটিকে নির্বাসনে পাঠায়। (Bengali Dialogue)
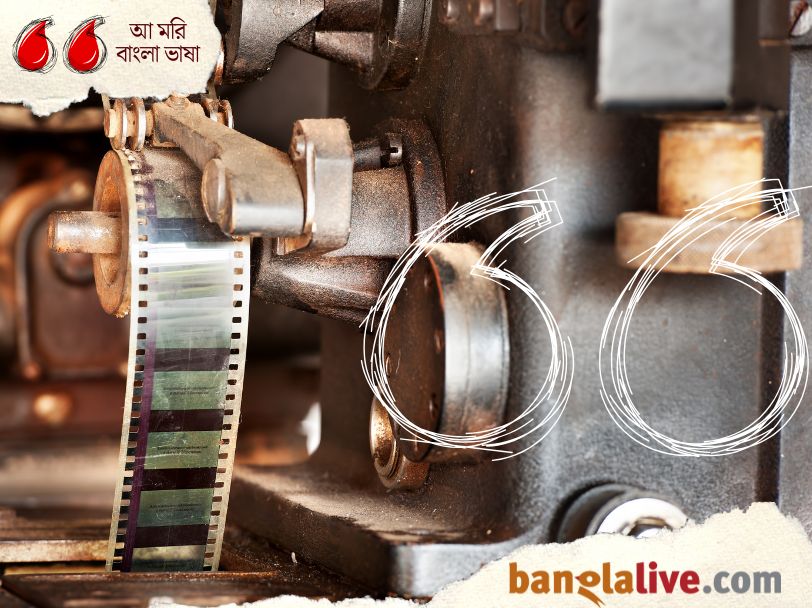
সুতরাং সামাজিক পরিবর্তনের স্রোত ভাষার রক্ষণশীলতাকে ভাঙবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সর্বোপরি বাংলা ছবির মান আশির দশকের ওপারে যে সাঙ্ঘাতিক পতনের ইতিহাস গড়েছে তার সঙ্গে সমান তালে নেমে এসেছে সংলাপের ভাষা। ঋত্বিক চলে গিয়েছিলেন আগেই। ক্রমশ শেষ হয় সত্যজিৎ-মৃণাল-তরুণ-তপন যুগ। ফিল্মের মতো শক্তিশালী আরেকটি গণমাধ্যম টেলিভিশন, যার প্রসার বাড়তে থাকে আশির দশক থেকেই। সুতরাং তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হয় সিনেমাকে। এবং একটা সময়ে দেখা যায় কম বাজেটের, নরবরে চিত্রনাট্য আর অভিনয় নিয়ে তৈরি ছবিতে ভরে গেছে বাংলার সিনেমা হল। এই বাজারি ছবির অন্যতম উপাদান গান এবং উচ্চ গ্রামে বাঁধা ডায়লগ। “শত্রু”, “লাঠি”, “বাবা কেন চাকর”, “মানুষ কেন বেইমান”, “বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না” এরকম ছবির শো-এ হয়তো দর্শকের অভাব ঘটেনি, কিন্তু কলকাতার টালিগঞ্জ স্টুডিওপাড়ার যে খুব প্রাপ্তি ঘটেছে– তাও নয়। (Bengali Dialogue)
কিন্তু সর্বোপরি বাংলা ছবির মান আশির দশকের ওপারে যে সাঙ্ঘাতিক পতনের ইতিহাস গড়েছে তার সঙ্গে সমান তালে নেমে এসেছে সংলাপের ভাষা।
এর পরের সময়ে ঋতুপর্ণ ঘোষ, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গাঙ্গুলি, কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায়, মৈনাক ভৌমিক এরকম বেশ কিছু পরিচালক আসেন টালিগঞ্জে ছবি করবার জন্য। ডিজিটাল কারিগরির হাত ধরে অনেক উন্নত হয় সিনেমা তৈরির পুরো পদ্ধতি। গল্পের প্লটে আসে নতুন চিন্তাধারার ছোঁয়া। একটু একটু করে সংলাপের ভাষায় মেশে হিন্দি আর ইংরেজি। স্মার্টফোন আর কম্পিউটারের কিবোর্ডে অভ্যস্ত বাঙালির লেখার ভাষার প্রতিফলন ঘটে যায় সিনেমার সংলাপে। এরপরের স্তরে ওয়েব সিরিজ এসে যেন বাকি আগলটুকুও ভেঙে দেয়। জীবনের বাস্তবকে ছবির পর্দায় প্রতিফলিত করতে গিয়ে চিত্রনাট্য জুড়ে এখন চলেছে একধরণের ভাষা সন্ত্রাস যেখানে আছে বাংলিশের বুলি, অপভাষার নিরন্তর আনাগোনা, দ্ব্যর্থক শব্দের খেলা। (Bengali Dialogue)
আরও পড়ুন: সত্যজিতের সিনেমায় রেল : ফিরে দেখা
মোটামুটিভাবে সাহিত্যশ্রয়ী মেলোড্রামাকে একটা সময়ের পরে বাঙালি পাত্তাই দেয়নি সেভাবে। আর দেয়নি বলেই হয়তো ফেলু মিত্তির, ব্যোমকেশ বক্সী, শবর দাশগুপ্ত আর রাজা রায়চৌধুরীর বাইরে কোনও নতুন দুঃসাহসী চরিত্র কি বাঙালির দরকার হয়েছে? কলকাতা কেন্দ্রিক জীবনে হয়তো সেই চর্বিত চর্বণেই সে খুশি। আসলে দর্শক হিসেবে চাহিদা না থাকলে হয়তো বা মান উন্নীত হওয়ার দায়ও থাকে না কোনও বিনোদনের। (Bengali Dialogue)
সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।