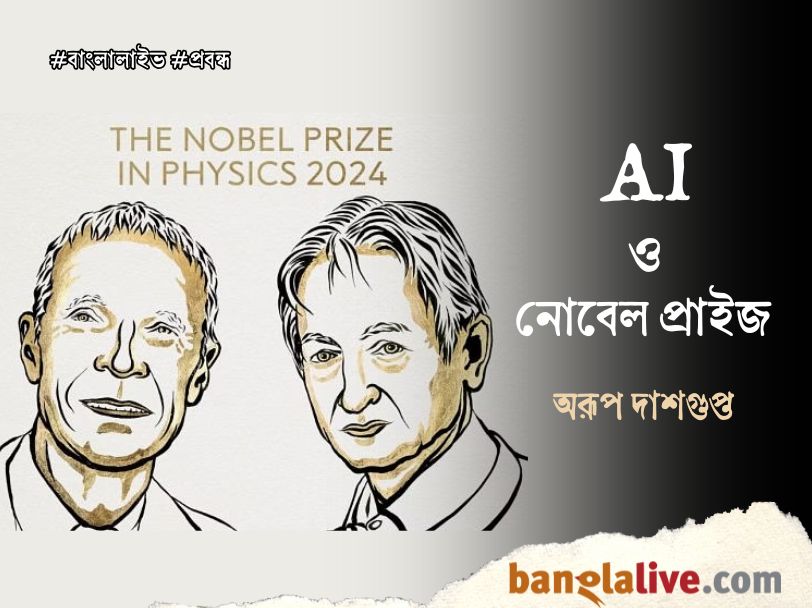পদার্থবিজ্ঞানে ২০২৪ সালের নোবেল (Nobel Prize) পুরস্কার পেল জন হপফিল্ড এবং জিওফ্রে হিন্টন। যাঁদের কাজের বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI.(Artificial Intelligence)
ব্যাপারটা বেশ আশ্চর্যজনক, কারণ নোবেল পেলেন পদার্থবিজ্ঞানে আর গবেষনার বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI যা কী না মৌলিক বিজ্ঞান বা বেসিক সায়েন্স নয়, সম্পূর্ণ প্রযুক্তি নির্ভর বিষয় বা টেকনোলজি বেসড সায়েন্স। তাহলে কি এখন থেকে নোবেল কমিটি বেসিক সায়েন্সের গবেষনা ছেড়ে টেকনোলজির আবিষ্কারে পুরস্কার দেওয়ার দিকে মন দেবে! যদিও এ ঘটনা নতুন কিছু নয়, আগেও অন্তত একবার হয়েছে।
পদার্থবিজ্ঞানে ২০২৪ সালের নোবেল পুরস্কার পেল জন হপফিল্ড এবং জিওফ্রে হিন্টন। যাঁদের কাজের বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI.
২০১৪ সালে ইসামু আকাসাকি, হিরোসি আমানো এবং সুজি নাকামুরা নীল রশ্মি নির্গতকারী এলইডি আবিষ্কারের জন্য ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন অথচ ১৯৬২ সালে নিক হলোন্যাক প্রথম লাইট এমিটিং ডায়োডের কথা বলা সত্ত্বেও নোবেল পুরস্কার পাননি।
একইরকম ভাবে এআইয়ে কাজ করে ফিজিক্সে নোবেল প্রাইজ পাওয়াটা কিন্তু বেশ সন্দেহজনক। এ নিয়ে চারপাশে প্রশ্নও উঠছে। তাহলে কি এআই ফিজিক্সের অঙ্গ হয়ে গেল, নাকি এবার থেকে প্রযুক্তি বিদ্যাতেও নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে।
একটু বিস্তারিতভাবে ভেবে দেখা যাক এআইয়ে নোবেল দেওয়ার পেছনে যুক্তিই বা কী আর সেই যুক্তি আদৌ গ্রহণযোগ্য কী না।
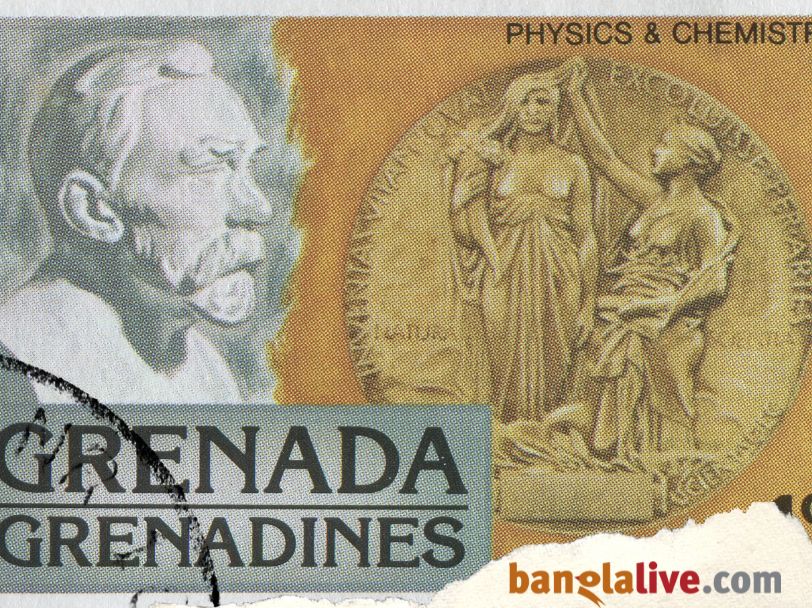
কারণ AIতে নোবেল দেওয়ার পিছনে কিন্তু বাজার অর্থনীতি চাঙ্গা করার একটা বড় চেষ্টা আছে।
২০২৩ সালের বিখ্যাত আমেরিকান কনসালটেন্সি কোম্পানি ম্যাককিনসির একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, অদূর ভবিষ্যতে শুধু জেনারেটিভ এআই (জেনারেটিভ এআই- এআই যখন নিজে নিজেই ডিসিশন নিতে পারে) হয়তো প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতিতে কমপক্ষে ৪.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার অবদান করবে। আবার আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত সংস্থা IMF একইরকম রিপোর্টে সতর্ক করছে যে অদূর ভবিষ্যতে এই এআই’ই বিশ্বব্যাপী প্রায় ৪০% চাকরি খেয়ে নিতে পারে। তাহলে এটা পরিষ্কার যে এআই একদিকে যেমন বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে তেমনই অন্যদিকে শ্রমবাজারকে শেষ করে দেবে। সাধারন মানুষ চাকরি হারাবে আর মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সম্পত্তি বাড়তে থাকবে। সেই যুক্তিতেই এআই এ নোবেল প্রাইজ দেওয়া বাজার অর্থনীতিকে আরও চাঙ্গা করার একটা প্রচেষ্টা মাত্র।
এটা পরিষ্কার যে এআই একদিকে যেমন বাজার অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে তেমনই অন্যদিকে শ্রমবাজারকে শেষ করে দেবে।
অনেকেই হয়তো বলবেন বা বলছেন যে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি প্রথম বাজারে আসার পরেও এইরকম সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু বুঝতে হবে পিসি’র প্রভাব সমাজে যতটা পড়েছিল ইন্টারনেট তার থেকে বেশ কয়েকগুণ বেশি প্রভাব ফেলেছে আর এআই এদের থেকে সামগ্রিক প্রভাব আরও কয়েক শতগুন বেশি ফেলবে। যাইহোক এসব কথায় পরে আসব। এখন দেখা যাক এআই আর ফিজিক্সের মধ্যে আদৌ মেলবন্ধন সম্ভব কী না। আর তা জানার আগে দেখা যাক প্রাথমিক ভাবে AI কীভাবে কাজ করে আর হঠাৎ করে AI নিয়ে বিশ্ব জুড়ে এত লাফালাফিই বা শুরু হয়েছে কেন।
আরও পড়ুন: ডিপফেক-মানবসভ্যতার মারিয়ানা ট্রেঞ্চ?
এআইয়ের রমরমা শুরু এনভিডিয়া নামের একটি আমেরিকান কোম্পানির হাত ধরে। সম্প্রতি মাইক্রোসফ্টকে পেছনে ফেলে এনভিডিয়া বাজার মূলধনের দিক থেকে অ্যাপেলের ঠিক পরে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোম্পানি হিসাবে চিহ্নিতও হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে এর সঙ্গে এআইএর সম্পর্ক কোথায়।
আসলে এনভিডিয়ার এআইয়ের উত্থান একে অপরের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে। একটু বিস্তারে জানা যাক।
কম্পিউটারে আমরা যে রঙিন ছবি বা ভিডিও দেখি তাকে প্রসেস করার জন্যে আগে একধরণের ইলেক্ট্রনিক সার্কিট বোর্ড ব্যবহার করা হত যাকে বলা হত ভিডিও কন্ট্রোলার। তার কম্পিউটারের মেইন সিপিইউ আর মেমোরির থেকে আলাদা নিজস্ব মেমরি এবং প্রসেসর থাকত।

যেহেতু ভিডিও গেমে বা যেকোনও ভিডিওতে কম্পিউটার স্ক্রিনের ছবি ক্রমাগত বদলাতে থাকে তাই স্মুথ মুভমেন্টের জন্য খুব দ্রুততার সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে স্ক্রিনকে নতুন করে আঁকতে হয় বা রিফ্রেশ করতে হয়। কী কী নতুন করে আঁকতে হবে বা কী কী রঙ ব্যবহার করতে হবে এইরকম কয়েক হাজার বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে কয়েক লাখ ইন্টারাকশন একসঙ্গে বা প্যারাল্যালি প্রসেস করতে হয়, যা করতে খুব পাওয়ারফুল, ফাস্ট প্রসেসিং পাওয়ারের সিপিইউ এবং দ্রুত রিড-রাইট করার মতো মেমরির প্রয়োজন হয়। স্ক্রিনে আমরা যে মুহুর্তে যে ছবি দেখি সেটা স্ক্রিনে পাঠানোর আগে মেমরিতে তৈরি করা হয়। এটা করার জন্য মেমরিতে স্ক্রিনের সমান রিজোলিউশনের আর সাইজের একটা জায়গাকে স্ক্র্যাচ প্যাডের মতো করে ব্যবহার করা হয়।
লক্ষাধিক পিক্সেলের প্রতিটি পিক্সেলের রং, উজ্জ্বলতার গ্র্যাডিয়েন্ট আর তার ডিরেকশনের সমষ্টিগত রূপ দিয়েই তৈরি হয় একেকটা ছবি।
যেমন ধরা যাক ২৫৬০ X ১৪৪০ রিজোলিউশনের একটা স্ক্রিন মানে ২৫৬০ টা হরাইজোনটাল লাইন আর 1440 টা ভার্টিকাল লাইনের একটা মেশ। আর তার প্রত্যেকটা ক্রস পয়েন্ট বা ছেদবিন্দুকে বলে পিক্সেল। এইরকম লক্ষাধিক পিক্সেলের প্রতিটি পিক্সেলের রং, উজ্জ্বলতার গ্র্যাডিয়েন্ট আর তার ডিরেকশনের সমষ্টিগত রূপ দিয়েই তৈরি হয় একেকটা ছবি। এবার ছবি যখন নড়াচড়া করে তখন তার নড়াচড়ার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্ক্রিনের প্রতিটি পিক্সেলের রং, উজ্জ্বলতা বদলে বদলে তাকে প্রথমে মেমরিতে তৈরি করে ততক্ষণাৎ স্ক্রিনকে রিফ্রেশ করতে করতে আঁকতে আঁকতে যেতে হয় এবং এই কাজটা করতে হয় সাংঘাতিক দ্রুততার সঙ্গে। এটাকে বলা হয় রেন্ডারিং।
আরও পড়ুন: বিজ্ঞানে মিলায় বস্তু : জন্মদিনে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে
প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এটা তো টিভিতে বা কম্পিউটার স্ক্রিনেও হয়, তাহলে এতে এআইয়ের কী ভূমিকা? তফাতটা হচ্ছে টিভিতে বা কম্পিউটার স্ক্রিনে ভিডিওটা আগের থেকে ঠিক করা থাকে, আর এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে যখন সিস্টেমকে ডিসিশন নিতে হয় পরবর্তী ছবি কেমন হবে তখন প্রয়োজন হয় এআইয়ের। তাই ছবি আঁকার সাথে সাথে সিস্টেমকে অনেক সময় সম্ভাব্য পরবর্তী পরিস্থিতির মধ্যে থেকে সঠিক সিদ্ধান্তটা নিতে হয়, যার জন্য প্রয়োজন অত্যন্ত ফাস্ট প্রসেসিং পাওয়ারের সিপিইউ আর তার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দ্রুত লেখা-পড়া করতে পারে এমন মেমরি।
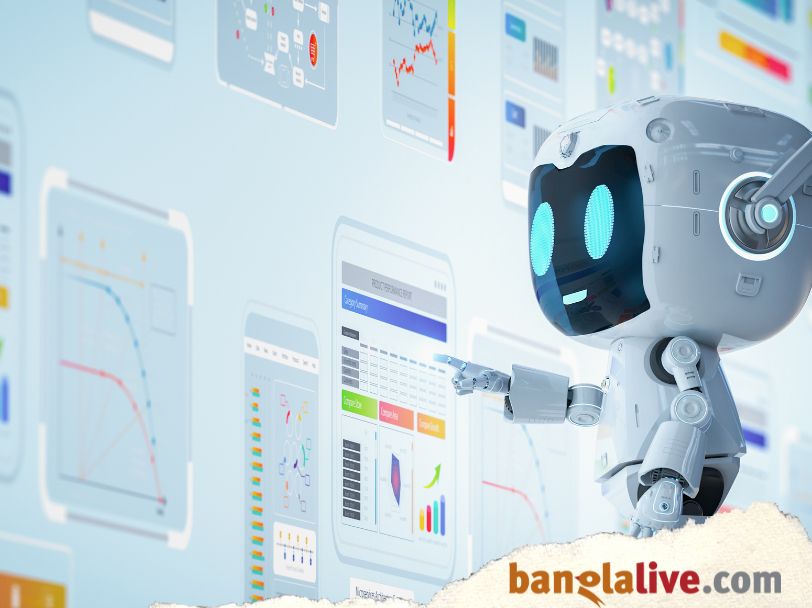
এইরকম একটা ইলেট্রনিক সার্কিট তৈরির প্রথম চেষ্টা করে জাপানের টোসিবা কোম্পানি ১৯৯৪ সালে, নাম দেয় জিপিইউ বা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট। কিন্তু বাজার মাত করে দেয় ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে আনা এনভিডিয়ার জিইফোর্স-২৫৬ নামে জিপিইউ চিপ। জিইফোর্স-২৫৬ এতটাই ক্ষমতা সম্পন্ন যে এই জিপিইউ প্রতি সেকেন্ডে এক কোটি পলিগন প্রসেস করতে সক্ষম ছিল যা এখন এনভিডিয়ার নতুন জিপিইউ জিইফোর্স-আরটিএক্স-৪০ সিরিজে সেকেন্ডে কুড়ি কোটি পলিগন প্রসেস করতে সক্ষম। আসলে যেকোনও ত্রিমাত্রিক বা 3D ছবি অনেকগুলি পলিগন জুড়ে তৈরি হয়। যেমন একটা ত্রিভূজ বা চতুর্ভূজ তিনটে বা চারটে লাইন জুড়ে তৈরি তেমনই বহু সংখ্যক লাইন জুড়ে নানান শেপের পলিগন তৈরি হয়। এনভিডিয়া শুধু জিপিইউ বাজারে আনল না সঙ্গে নিয়ে এল সিইউডিও বা কুডা নামের একটা সফ্টওয়ার আর্কিটেকচার (কম্পিউট ইউনিফায়েড ডিভাইস আর্কিটেক্চার) যার মাধ্যমে প্রোগ্রাম লিখে জিপিইউকে নানান কাজ করার ইন্ট্রাকশনস্ পাঠানো সম্ভব।
এনভিডিয়ার নতুন জিপিইউ জিইফোর্স-আরটিএক্স-৪০ সিরিজে সেকেন্ডে কুড়ি কোটি পলিগন প্রসেস করতে সক্ষম।
প্রথম দিকে এই কুডা আর্কিটেক্চারের ব্যবহার মূলত কম্পিউটার গেমিং সফ্টওয়্যার লেখার জন্যে ব্যবহার হলেও ২০১২ সালে জিওফ্রে হিন্টন প্রথম জিপিইউয়ের প্রসেসিং পাওয়ার কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক কম্পিউটেশনে ব্যবহার করেন। আমাদের মস্তিষ্কে যেমন অনেকগুলো নিউরোনকে সাইন্যাপস দিয়ে জোড়া দিয়ে এক একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় কম্পিউটারেও তাই। এক একটা নিউরোনে কোনও একটা বিষয়ের যাবতীয় তথ্য ধরা থাকে। ঠিক যেমন খোপ খোপ করা একটা বাক্স। বাক্সটির নাম যদি উত্তমকুমার হয় তাহলে বাক্সের প্রত্যেকটা খোপে আলাদা আলাদা করে উত্তমকুমারের চরিত্রের, রূপের বা গুণের যাবতীয় তথ্য রাখা থাকে আর পুরো বাক্সটা উত্তমকুমারকে রিপ্রেজেন্ট করে। এইরকম একেকটি খোপ যদি একটা নিউরোন হয় তাহলে এরকম অনেকগুলো নিউরোনকে এক একটা নির্দিষ্ট শেপে এবং অর্ডারে জুড়ে একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি হয়। এইরকম এক বা একাধিক নিউরাল নেটওয়ার্ক জুড়ে এক একটা ঘটনা বা অভিজ্ঞতা পুনর্নির্মাণ করা হয়।
কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ককে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব। যা AI এর ক্ষেত্রে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
২০১২ সালে, হিন্টনই প্রথম দেখান যে এনভিডিয়ার জিপিইউয়ের উপর কুডা ব্যবহার করে কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ককে ছবি চিনতে শেখানো যায়। অর্থাৎ কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ককে ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব। যা AI এর ক্ষেত্রে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।
হিন্টনের এই যুগান্তকারী কাজ এনভিডিয়াকে দেখিয়ে দেয় যে তাদের জিপিইউ ব্যাবহার করে গেমিং সফ্টওয়্যার ছাড়াও অন্যান্য দ্রুত প্রসেস করার সফ্টওয়্যার তৈরি করা সম্ভব। এর আগে, এনভিডিয়ার CUDA প্রধাণত উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটিং যেমন সিটি স্ক্যান, আর্থিক মডেলিং এবং অ্যানিমেশনের জন্য ব্যবহৃত হত।
সুতরাং হিন্টনের পরীক্ষাগুলি কেবল এআইয়ে বিপ্লব আনেনি, তারা এনভিডিয়াকে তার নিজস্ব প্রযুক্তির সম্পূর্ণ শক্তি বুঝতেও সাহায্য করেছে।

হিন্টনের এই কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের কাজই মূলত, আধুনিক AI এর বিল্ডিং ব্লক।
১৯৪০-এর দশকে ওয়ারেন ম্যাককুলোচ এবং ওয়াল্টার পিটস্ মানুষের মস্তিষ্কের সঙ্গে মিল রেখে সাইবানেটিক্সে প্রথম স্নায়ু কার্যকলাপের মডেল হিসাবে নিউরাল নেটওয়ার্কের ধারণা প্রস্তাব করেছিলেন।
তবে হ্যাঁ, ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত ব্যবহারিক অ্যাপ্লিকেশন সীমিত ছিল, যতক্ষণ না জন হপফিল্ড, হপফিল্ড নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন। এই হপফিল্ড নেটওয়ার্ক বলে আমাদের মস্তিষ্কের নিউরাল নেটওয়ার্ক কীভাবে বায়োফিজিক্সের নিয়ম ব্যবহার করে কোনও অসম্পূর্ণ তথ্য থেকে কোনও কিছুর সম্পূর্ণ রূপ অনুমান করতে পারে আর ঠিক সেইভাবেই কী করে কৃত্তিম নিউরালে তা ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটা বিড়ালের ছবি ঝাপসা হয়, তবে এই মডেল দিয়ে কম্পিউটার অনুমান করতে পারে যে এটি আসলে কেমন হওয়া উচিত।
আরও পড়ুন: চুম্বক আবিষ্কারের কাহিনী
AI এর ক্ষেত্রে এটা একটা বিশাল পদক্ষেপ হলেও যথেষ্ট ছিল না, কারণ বিড়াল তো চেনা গেলো কিন্তু মাছ দেখলে বিড়াল কী করবে বা রেগে গেলে সেই বিড়াল কেমন মুখ করবে তা তো AI জানে না। তাই গবেষনা শুরু হল কীভাবে AI ভবিষ্যদ্বাণী করবে বা নিজে নিজেই নতুন কোনও প্রাসঙ্গিক তথ্য দেবে।
এইখানেই হাজির হলেন জিওফ্রে হিন্টন তাঁর বোল্টজম্যান মেশিন নিয়ে। হিন্টনের এই বোল্টজম্যান মেশিন নিউরাল নেটওয়ার্কের মাঝে একটা লেয়ার বা স্তর গুঁজে দিলেন যাকে বলা হল লুকানো বা হিডেন লেয়ার।
হিন্টনের এই বোল্টজম্যান মেশিন নিউরাল নেটওয়ার্কের মাঝে একটা লেয়ার বা স্তর গুঁজে দিলেন যাকে বলা হল লুকানো বা হিডেন লেয়ার।
শুরু হল এইসব বিভিন্ন লেয়ারে থাকা নিউরাল নেটওয়ার্কদের ট্রেনিং দেওয়া। যতরকম সম্ভাব্য তথ্য সম্ভব তাদের শেখানো হল আর এই ট্রেনিং দেওয়া তথ্য বা ডেটা গুঁজে দেওয়া হল বাক্সের সেই খোপগুলোতে। এর ফলে কন্ট্রোলিং সফ্টওয়্যার সামনের পিছনের বা আশেপাশের বিভিন্ন নিউরাল নেটওয়ার্কের থেকে ডেটা নিয়ে নানান সম্ভাব্য পরিস্থিতি তৈরি করতে সক্ষম হল আর তার উপরে সম্ভাব্যবতার সূত্রাবলী বা ল’জ অফ পসিবিলিটিজ ব্যবহার সেই কন্ট্রোলিং সফ্টওয়্যার সঠিক পরিস্থিতি বা সম্ভাবনা নির্ধারণ করতে সক্ষম হল।
শুরু হল কুডার মাধ্যমে জিপিইউতে কোনও একটা নিউরাল নেটওয়ার্কের সম্ভাব্য নানান এক্সটেনডেড স্টেটের ট্রেনিং দেওয়া আর সেই স্টেটগুলো থেকে ভবিষ্যৎবাণী করা বা নতুন সম্ভাব্য পরিস্থিতি উপস্থাপন করা। যাকে আমরা জেনারেটিভ AI বলি। তাই এখন একটা ছবিতে একটা বিড়াল কেমন হবে তা শনাক্ত করার সাথে সাথে, একটা কম্পিউটার AI দিয়ে এখন অনুমান করতে পারে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যে বিড়ালটি দেখতে কেমন হতে পারে।
এখন একটা ছবিতে একটা বিড়াল কেমন হবে তা শনাক্ত করার সাথে সাথে, একটা কম্পিউটার AI দিয়ে এখন অনুমান করতে পারে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যে বিড়ালটি দেখতে কেমন হতে পারে।
এত অব্দি তো সব ঠিক আছে। কিন্তু এতক্ষণ যেসব কাজ বা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হল তা তো সবই টেকনোলজি আর অঙ্ক! এর মধ্যে ফিজিক্স কোথায়? যদিও হপফিল্ড এআইতে নিউরাল নেটওয়ার্কের ব্যবহার করেছিল বায়োফিজিক্স থেকে মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে জেনে। কিন্তু তা হলেও এআইকে ফিজিক্স বলা যায় না।
পরবর্তীতে হিন্টন ডেটা প্রসেস করার জন্য আর যেকোনও পরিস্থিতির ভবিষ্যতের স্টেট প্রেডিকশন করার জন্যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফিজিক্স আর কম্পিউটেশনাল ফিজিক্স ব্যবহার করলেও এআইকে কিন্তু ফিজিক্স বলা যায় না। AI সবসময়েই একটা প্রব্লেম সলভিং টেকনোলজি বেসড টুল, যার মধ্যে কোনও ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা নেই, আছে শুধুই অঙ্ক। নোবেল কমিটির চার্টারে অঙ্ক বা টেকনোলজিতে পুরস্কার দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই।
হপফিল্ড এআইতে নিউরাল নেটওয়ার্কের ব্যবহার করেছিল বায়োফিজিক্স থেকে মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে জেনে। কিন্তু তা হলেও এআইকে ফিজিক্স বলা যায় না।
আসলে AI নিয়ে ২০২০ সালের আগে থেকেই আমেরিকার সফ্টওয়্যার কোম্পানিগুলো বাজার ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু বিশ্বাস এবং গ্রহণযোগ্যতার অভাব বাঁধ সাধছিল। এমতাবস্থায় কোভিড প্যান্ডেমিক একটা বিশাল সুযোগ নিয়ে এল। সরাসরি শ্রমের নির্ভরতা আর মানুষের সঙ্গে সংস্পর্শ কমাতে AI এর উপর নির্ভরশীলতা বাড়াতে বাধ্য হল, কোভিডের জন্য কিছুটা স্বাভাবিক নিয়মেই লোকের চাকরি যেতে আরম্ভ হল। আস্তে মানুষ AI Based service-এর উপর নির্ভরশীল হল। এই সুযোগে ধনতান্ত্রিক সমাজ মানবশ্রম কমিয়ে ফেলল অতিরিক্ত লাভের লোভে। অটোমেশন ইন্ডাস্ট্রি বহুদিন নতুন কিছু না আনতে পেরে AI Based Automation-কে আঁকড়ে ধরল। ফলে বৃহৎ শিল্পের উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল ক্ষুদ্রশিল্পগুলো বন্ধ হতে শুরু করল আর ফলে নিম্নবিত্ত সমাজে বেকারত্ব বাড়তে শুরু করল।

আস্তে আস্তে এআই, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এই না জানা থাকলে চাকরিতে টিকে থাকা কঠিন হতে শুরু করবে। আবার এআই বা সেই সংলগ্ন অন্যান্য বিষয় শিখতে গেলে যে ধরনের অংক বা ভাষায় দখল দরকার তা আজকালকার শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বত্র সবার কাছে অ্যাক্সেসিবল নয়। আসলে এআই নিজেই নিজের শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রসঙ্গত চ্যাট-জিপিটি’র মতো সফ্টওয়্যার যেমন ছাত্রছাত্রীদের কিছু না শিখেই সহজে ফেক-জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করছে যা অত্যন্ত লোভনীয় ঠিক তার ফলে একটি ছেলে বা মেয়ে যখন ইন্ডাস্ট্রীতে চাকরি করতে আসছে তখন দেখা যাচ্ছে বা যাবে যে তার যেকোন একটা বিষয়ে যতটা জানা দরকার তার কিছুই সে জানে না। এরফলে তৈরি হবে প্রচুর সঠিকভাবে শিক্ষা না পাওয়া ডিগ্রীধারী ছেলেমেয়ে। আর সঠিক ট্রেনিং পেতে গেলে ছাত্রছাত্রীদের যে ধরণের ইনস্টিটিউটে যাওয়া দরকার তা অ্যাফোর্ড করার ক্ষমতা সমাজে খুব অল্পসংখ্যক ছেলেমেয়েদের পক্ষেই সম্ভব হবে।
প্রসঙ্গত চ্যাট-জিপিটি’র মতো সফ্টওয়্যার যেমন ছাত্রছাত্রীদের কিছু না শিখেই সহজে ফেক-জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করছে
এআই ব্যবহার করতে না পারলে বা সঠিক এমপ্লয়ী না পেলে ছোট ছোট কোম্পানি বন্ধ হতে শুরু করবে বা করেছে।
একটু চোখ কান খোলা রাখলেই বোঝা যাবে কোন কোন ধরনের কোম্পানি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর কাদের প্রফিট বাড়ছে। AI সবরকম কোম্পানির কাছে কম খরচায় বেশি মার্জিনে ব্যবসা করার সুযোগ এনে দিয়েছে। এটাকেই আরও জোড়দার করা আর সাধারণ মানুষ আর কোম্পানিগুলোর AI এর উপর ভরসা বাড়ানোর জন্যে এই নোবেল একটা নতুন পদক্ষেপ। আগামী দিনগুলোতে পৃথিবী জুড়ে শ্রমজীবী মানুষ কাজ হারাবে, ধনী আরও ধনী হবে আর গরীব আরও গরীব হবে। হিউম্যান রিসোর্সের ভ্যালু কমবে, হিউম্যানফেস-লেস AI based “perfect service” পাওয়ার জন্যে কনসিউমার অনেক বেশি খরচা করবে।
হিউম্যান রিসোর্সের ভ্যালু কমবে, হিউম্যানফেস-লেস AI based “perfect service” পাওয়ার জন্যে কনসিউমার অনেক বেশি খরচা করবে।
বেশিরভাগ ডেভেলপিং বা আন্ডার ডেভেলপ্ড ইকোনমি লো স্কিল বেসড সা্র্ভিস ওরিয়েন্টেড হয়ে যাবে। যারফলে যেকোনও সমাজের শিরদাঁড়া অর্থাৎ আস্তে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আস্তে আস্তে হারিয়ে যাবে বা ছোট হতে থাকবে। বেঁচে থাকবে গরীব, নিম্নবিত্ত এবং ধনী সম্প্রদায়। উন্নতিশীল দেশে বাড়বে অর্থনৈতিক বৈষম্য। অবশেষে “উন্নত” জীবনযাত্রার আশায় শুরু হবে মাস মাইগ্রেশন। সারা বিশ্ব একটা ইকোনমিক ডিজাস্টারের সম্মুখীন হবে।
আসলে এটা একটা নতুন খেলনার মতো, কনজিউমারকে নতুন কিছু না দিতে পারলে বাজার চাঙ্গা হবে না তাই AI কে পরবর্তী বিজ্ঞান বলে এস্টাব্লিস করার জন্য AIকেও ফিজিক্সের সঙ্গে জুড়ে নোবেল দিয়ে দেওয়া হল।
অলংকরণ- আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
পড়াশোনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিয়ো ফিজিক্স বিভাগে। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন তথ্য প্রযুক্তিকে। প্রায় এগারো বছর নানা বহুজাতিক সংস্থার সাথে যুক্ত থাকার পর উনিশশো সাতানব্বইতে তৈরি করেন নিজের তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। বর্তমানেও যুক্ত রয়েছেন সেই সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে। কাজের জগতের ব্যস্ততার ফাঁকে ভালবাসেন গান-বাজনা শুনতে এবং নানা বিষয়ে পড়াশোনা করতে। সুযোগ পেলেই বেড়াতে বেরিয়ে পড়েন আর সেই অভিজ্ঞতা ধরে রাখেন ক্যামেরায়।