(National Science Day)সেদিন বিকেলের চা-টা খাওয়ার পরে আমাদের ‘জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের তাৎপর্য’ নিয়ে চিন্তা ক’রছিলাম আর এরকম গভীর চিন্তার ফলে একটু ঝিমুনি এসেছিল, হঠাৎ কে যেন ব’লে উঠল, “কী ব্যাপার, এই ভরবিকেলে ঘুমানো হচ্ছে?” চমকে তাকিয়ে দেখলাম পানুদা মানে ইন্সটিট্যুটে আমার পাঁচবছরের সিনিয়র প্রফেসর ডক্টর প্রণবেন্দু রায়। বললাম, “তুমি? কখন এলে? এসো, এসো, কতদিন পরে তোমায় দেখলাম! চা বলছি।”(National Science Day)
ভাষাবিজ্ঞানী সুনীতিকুমার: পবিত্র সরকার
“দাঁড়া, সামনে ল্যাপটপ নিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়ছিস তাই কি নিয়ে এত চিন্তামগ্ন সেটা আগে বুঝি।”
“আর বলো কেন, ‘জাতীয় বিজ্ঞান দিবস’ নিয়ে লিখতে হবে কিন্তু কীভাবে যে শুরু করবো কে জানে!”
“ও ‘জাতীয় বিজ্ঞান দিবস’। সেটা কবে?”
“আরে! আঠাশে ফেব্রুয়ারি, আবার কবে!”
“কেন?”
“আবার? ‘রমণ এফেক্ট আবিষ্কার’, তার ফলে প্রথম এশিয়ান হিসাবে সি ভি রমণের বিজ্ঞানে নোবেল পাওয়া, এসবের জন্যেই তো দিনটা ঠিক করা হয়েছে।”
“কীসের এফেক্ট?”(National Science Day)
নিউক্লিয়স আর ইলেক্ট্রনরা এ-ওকে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে ধরে থাকে। প্রত্যেক এলিমেন্টের পরমাণুতে ইলেক্ট্রনগুলো নিউক্লিয়স থেকে কত দূরে দূরে থাকতে পারে তা ঠিক করা আছে, ফলে তাদের কত কত শক্তি থাকতে পারে সেটাও নির্দিষ্ট।
“কী আপদ! আচ্ছা বলছি। দুনিয়ার সবকিছু খুব ছোট্ট-ছোট্ট জিনিস দিয়ে তৈরি, তাদের নাম ‘মলিকিউল’, বাংলায় ‘অণু’, এরা আবার একটা বা অনেকগুলো আরও ছোটো ‘অ্যাটম’ বা ‘পরমাণু’ দিয়ে তৈরি, যেমন টিউবলাইটের ভিতরের মার্কারির বাষ্পের অণুতে একটা করে পরমাণু, আর জলের অণুতে একটা করে অক্সিজেন আর দুটো করে হাইড্রোজেন পরমাণু।(National Science Day)
বিজ্ঞানে মিলায় বস্তু : জন্মদিনে বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে: শেখর গুহ
পরমাণুর মধ্যে একটা নিউক্লিয়স থাকে, তাতে কতগুলো পজিটিভ চার্জড প্রোটন আর নিউক্লিয়স ঘিরে ঠিক ততোগুলো ইলেক্ট্রন, তাদের চার্জ নেগেটিভ। প্রতিটা এলিমেন্ট বা মৌলপদার্থের, যেমন লোহা, সোনা, অক্সিজেন, বা হাইড্রোজেনের পরমাণুতে নির্দিষ্ট সংখ্যার প্রোটন থাকে, হাইড্রোজেনে একটা, অক্সিজেনে আটটা, এইরকম। নিউক্লিয়স আর ইলেক্ট্রনরা এ-ওকে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে ধরে থাকে। প্রত্যেক এলিমেন্টের পরমাণুতে ইলেক্ট্রনগুলো নিউক্লিয়স থেকে কত দূরে দূরে থাকতে পারে তা ঠিক করা আছে, ফলে তাদের কত কত শক্তি থাকতে পারে সেটাও নির্দিষ্ট। কেমন হচ্ছে?”
“চমৎকার! চালিয়ে যা।”(National Science Day)
পরমাণুতে ইলেক্ট্রনকে নিউক্লিয়স থেকে দূরে সরাতে গেলে আলো ঢোকাতে হবে, আর প্রত্যেক এলিমেন্টের পরমাণুতে এই দূরত্বগুলো নির্দিষ্ট বলে প্রত্যেক এলিমেন্ট কয়েকটা নির্দিষ্ট রঙের আলো ‘খেয়ে’ নিতে পারে, তাতে ইলেক্ট্রনগুলো দূরে যায়, আবার আগের জায়গায় ফিরে এলে তারা ওই ওই রঙের আলোগুলো ফিরিয়ে দেয়।
“আলোর শক্তি দিয়ে এই শক্তি বাড়ানো যায়। আলোর শক্তি তার রঙের উপরে নির্ভর করে, লালের থেকে যত বেগনির দিকে যাওয়া যায়, আলোর শক্তি ততই বাড়ে। লালের নীচে ‘ইনফ্রা-রেড’ নামে অদৃশ্য আলো। পরমাণুতে ইলেক্ট্রনকে নিউক্লিয়স থেকে দূরে সরাতে গেলে আলো ঢোকাতে হবে, আর প্রত্যেক এলিমেন্টের পরমাণুতে এই দূরত্বগুলো নির্দিষ্ট বলে প্রত্যেক এলিমেন্ট কয়েকটা নির্দিষ্ট রঙের আলো ‘খেয়ে’ নিতে পারে, তাতে ইলেক্ট্রনগুলো দূরে যায়, আবার আগের জায়গায় ফিরে এলে তারা ওই ওই রঙের আলোগুলো ফিরিয়ে দেয়। একে বলে ওই এলিমেন্টের ‘স্পেক্ট্রাম’, যা দিয়ে এলিমেন্টটা আছে কী না নির্ভুলভাবে বোঝা যায়। আবার অণুরা বিভিন্ন নিউক্লিয়স বরাবর স্প্রিঙের মতো কাঁপতে পারে, এই কাঁপার শক্তি কী কী হতে পারে সেটাও আবার অণুর জন্যে নির্দিষ্ট, এদের জন্যে ইনফ্রা-রেড আলো লাগে, তাই দিয়ে বোঝা যায় কোন অণু আছে।”
“কিন্তু ‘রমণ এফেক্ট’ কোথায়?”(National Science Day)
অন্য চোখে— বিজ্ঞানসাধক রাজেশ্বরী: নীলার্ণব চক্রবর্তী
“সব অণুকে কিন্তু এভাবে বোঝা যায় না। যাদের মধ্যে শুধু দুটো একই পরমাণু যেমন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি, বা যেসব অণুর মধ্যে একটা নিখুঁত সামঞ্জস্য আছে, যেমন বেঞ্জিন, একেবারে পার্ফেক্ট হেক্সাগন, তাদের এরকম কাঁপন থেকেও আলো বেরয় না। তাদের কীভাবে ‘দেখা’ যাবে সেটা গত শতকের বিশের দশকে বিজ্ঞানীদের কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল। ১৯২২ থেকে আমাদের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ্ সায়েন্সে রমণ বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে দিয়ে আলো পাঠিয়ে গবেষণা করছিলেন। ১৯২৮ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তিনি দেখলেন বেঞ্জিনের মধ্যে দিয়ে নীল আলো পাঠালে যে আলোটা গিয়েছিল সেটা ছাড়াও আরও দুটো খুব আবছা আলো বেরিয়ে আসছে, একটা একটু সবুজের দিকে মানে কম শক্তির আলো আর অন্যটা, একটু বেগনির দিকে, মানে বেশি শক্তির আলো। তাছাড়া, এই দুই আলো প্রধান আলোর থেকে যতটা শক্তিতে বেশি বা কম, সেই তফাৎ ঠিক বেঞ্জিনের অণুর কাঁপনের শক্তি যা হওয়ার কথা, তাই। যে চাবিকাঠি খোঁজা হচ্ছিল সেটা পাওয়া গেল! এব্যাপারে রমণ আরও পরীক্ষা করে ২৮শে ফেব্রুয়ারি একেবারে নিশ্চিত হলেন। পরে দেখা গেল হাইড্রোজেন ইত্যাদিদের জন্যেও এই নতুন ধরণের স্পেক্ট্রাম পাওয়া যায়। এই কাজের জন্যে ১৯৩০ সালে রমণ নোবেল প্রাইজ পেলেন। হল?”(National Science Day)
১৮৯৫ সালের নভেম্বরে যেদিন জগদীশ বোস মাইক্রোওয়েভ তৈরি করে কলকাতার টাউন হলে ছোটলাটের গা ফুঁড়ে, দুটো ঘর পেরিয়ে রিমোটে বন্দুক চালিয়েছিলেন
“কিন্তু এরকম ঘটনা কি আমাদের দেশে আর ঘটেনি? ১৮৯৫ সালের নভেম্বরে যেদিন জগদীশ বোস মাইক্রোওয়েভ তৈরি করে কলকাতার টাউন হলে ছোটলাটের গা ফুঁড়ে, দুটো ঘর পেরিয়ে রিমোটে বন্দুক চালিয়েছিলেন, বা ১৯২৪ সালে যেদিন সত্যেন বোসের সেই পেপার ছেপে বেরল যাতে উনি দেখালেন আলো আসলে কণিকা আর এমন কণিকা যাদের চরিত্র হল দল বেঁধে থাকা, তাতেই আলোর সবকিছু বোঝা যায়। সেগুলো ভুলে যাব? সেগুলো নোবেল প্রাইজ পায়নি বলে? আজ তো সবাই স্বীকার করছে না পাওয়া অন্যায় হয়েছে?”
“সায়েন্স ডে কটা হবে? তিনটে? কোনও দেশে হয়?”(National Science Day)
“আমাদের তো তিনটে সায়েন্স অ্যাকাডেমী, সেটা কোন দেশে হয়? আর বিজ্ঞান দিবস ঘটা করে পালন করছি, অন্যদিকে স্কুলে ডারউইনের বিবর্তনবাদ তুলে দেওয়া হচ্ছে, অ্যাস্ট্রোলজি আর অ্যাস্ট্রোনমিকে একসঙ্গে পড়ানো হচ্ছে, রিসার্চে ফান্ডিং ক্রমাগত কমানো হচ্ছে, সরকারি স্কুল একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, এগুলো কী? অন্যদেশে ‘সায়েন্স ডে’ থাকে না কিন্তু বিজ্ঞান যার উপরে দাঁড়িয়ে থাকে, লেখাপড়া আর গবেষণা, তার উপরে খরচ করে।”
“আমরা কি বিজ্ঞান নিয়ে কিছুই ক’রিনি?”(National Science Day)
বিজ্ঞানের যেটা প্রধান জোর, প্রশ্ন করার ইচ্ছে বা অধিকার, সেটাই তো ক্রমাগত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।
“কে বলল? আজ আমরা যেখানে এসেছি সেটাই তো তার প্রমাণ। কিন্তু ভেবে দেখ, তার প্রায় সবটাই আসলে কি টেক্নোলজি বা প্রযুক্তি নয়? বিজ্ঞানের যেটা প্রধান জোর, প্রশ্ন করার ইচ্ছে বা অধিকার, সেটাই তো ক্রমাগত কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আর শুধু আমরা কেন, পৃথিবীর যে দিকে চাই সেদিকে তো এই অন্ধকার ঘনাতে দেখছি। বিজ্ঞানের আজ বড় সংকটের দিন এসেছে। আমরা সব ভুলে যাচ্ছি, ভুলে যাচ্ছি।”(National Science Day)
চমকে জেগে উঠলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আর স্বপ্নে পানুদার সঙ্গে কথা বলছিলাম। তাছাড়া আর কি হতে পারে? পানুদা তো গতবছর মারা গেছেন।(National Science Day)
আলোকময় দত্ত ২০১৭ সালে সিনিয়র প্রফেসর পদে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজা রামান্না ফেলো হিসাবে সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তিন বছর অতিবাহিত করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক।




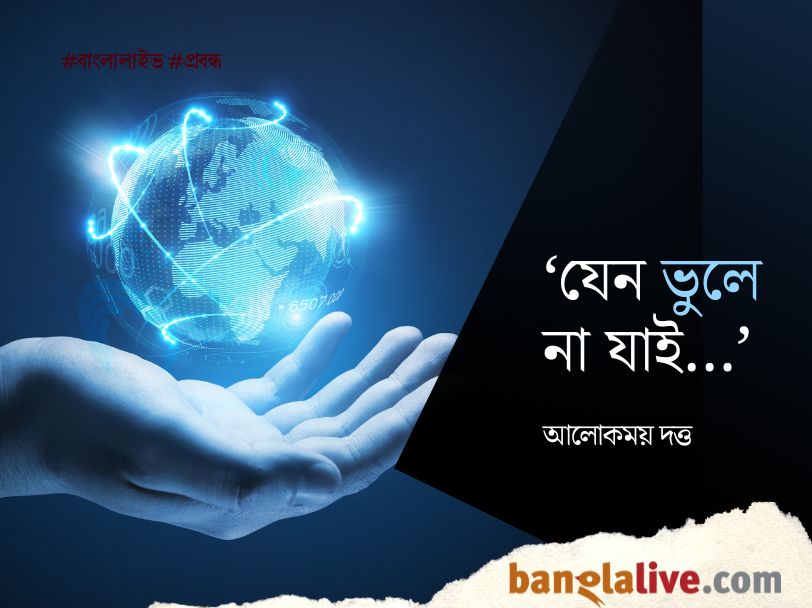





















One Response
Please keep on writing and motivate future generation for studying science.