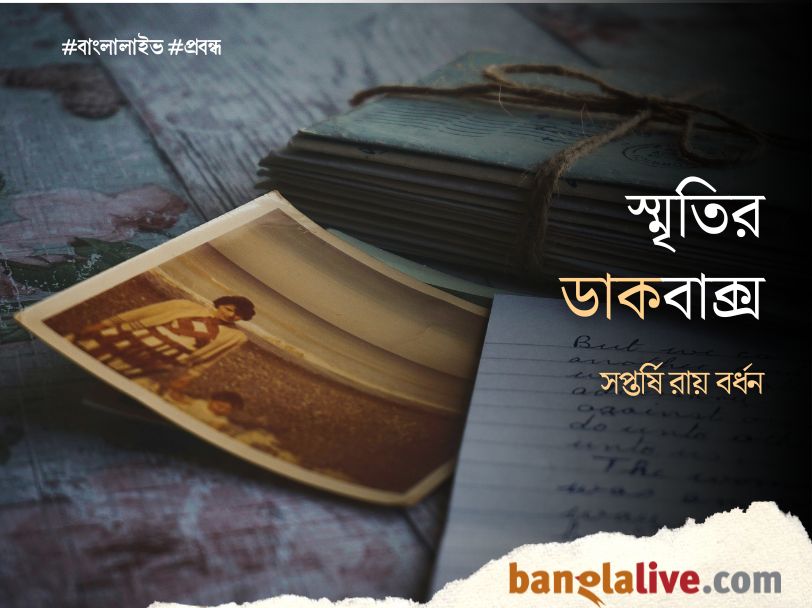(Post Box)
“হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক
তাদের হলুদ ঝুলি ভ’রে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
কতকালের পুরানো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে ওই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি”
কোভিডের সময়েই বাড়ি পরিস্কারের ধুম পড়েছিল। বাড়ির চৌহদ্দির মাঝে ইতি-উতি যত্রতত্র জমে থাকা না-খোলা বাক্স, না-মোছা তাক, না-পড়া বই– আরও অনেকগুলো ‘না’-এর মাঝে পড়েছিল চিঠির গুচ্ছরা অভিমানি অসূর্যম্পশ্যার মতো। হয়তো বা পড়েই থাকত ওভাবে যদি না, না-কাজের অবকাশে তাদের দিকে দৃষ্টি যেত খানিক, প্রকাশ পেত তারা প্যান্ডোরার বাক্সের এক কোণ থেকে। (Post Box)
বেশ নাদুস-নুদুস এক বাণ্ডিল চিঠি। গিঁটের আগল খুলে দিতে সম্মিলিত আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ল তারা এধারে-ওধারে। সরকারি শীল-মোহরের ছাপ তাদের শরীরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সবুজ বা আকাশী নীল, খাম বা তিন ভাঁজের ইনল্যান্ড লেটার, ফ্যাকাশে হলুদ পোস্ট কার্ড, লাল-নীল ডোরাকাটা এয়ারগ্রাম, তার সঙ্গে রঙিন লিফাফা, গোলাপি, লাল বা সবুজ– অন্দরে শুভেচ্ছাবার্তার কার্ড, যার গায়ে লেগেছে সময়ের পাঁশুটে রঙ। (Post Box)
এসেছিল যার কাছ থেকে, সেও কবে হারিয়ে গিয়েছে সময়ের কোলে। স্মৃতি-বিস্মৃতির ঝাঁপি খুলে আজ তারা মুক্তির স্বাদ পায়। মনের মাঝে তুফান তোলে। (Post Box)
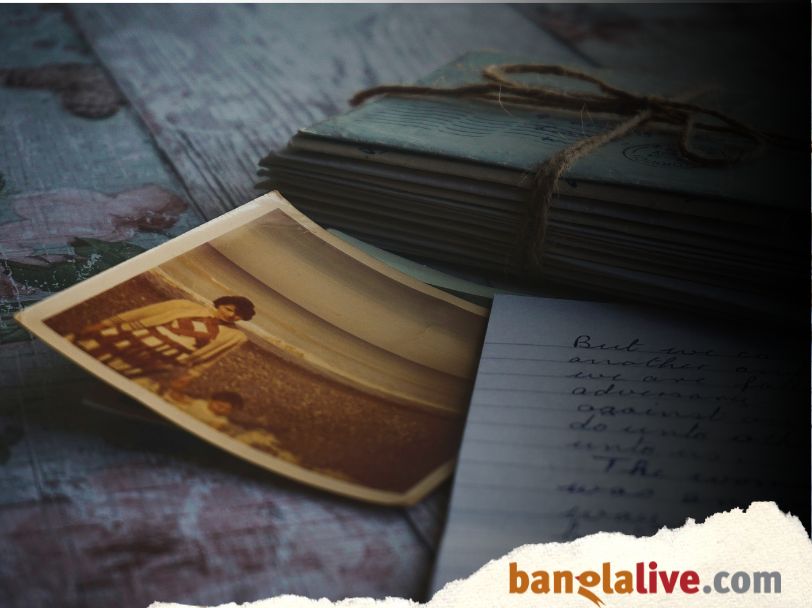
চিঠির পরতে পরতে খুঁজে পাই বন্ধুদের। পাই তাদের জীবনের যাত্রাপথের খবর, মনের হদিশ। কত হারিয়ে যাওয়া কথা, ফেলে আসা মুহূর্তরা বাঙময় হয়ে ওঠে। কত সূর্যাস্ত, কত সন্ধ্যা, কত নিশি পেরিয়ে যাওয়ার হদিশ পাই চিঠির লাইনে– কখনও বেঁকাতেড়া বেলাইনে। কখনও লেখনীর আঁচড়ের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকে কোনও ভুল বা না-বলা-কথা। (Post Box)
আত্মীয় পরিজনের কাছ থেকে নিতান্তই সাংসারিক, বৈষয়িক কথার ভার বয়ে আনা কোনও চিঠি, যার শেষ পাতে ভালবাসা, প্রীতি, স্নেহাশীর্বাদ– সেও উঁকি দেয়। পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো পাওয়া গেল দুটি চিঠি, যা ডাকবাক্সে ফেলা হয়নি। সংকোচের আস্তরণের নীচে তারা থেকে গেছে বাক্সের এক কোণায়। (Post Box)
“তখন আমাদের জীবন হয়তো বা এত কেজো হয়ে ওঠেনি। জীবনের গতিতে ছিল মন্দাক্রান্তা ছন্দ। সেই আপাত গতিহীনতার সঙ্গে সঙ্গত রেখেই চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়া ছিল আমাদের সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।”
হিসেব করে দেখা গেল, আশির দশকের গোড়া থেকে নব্বইয়ের মাঝামাঝি- একটা দীর্ঘ সময়ে চিঠিগুলো এসেছিল। কৈশোর পেরিয়ে যৌবন– বড় অদ্ভুত সে সময়। আজকের সঙ্গে তার ভীষণ অমিল। চিঠির পাতা জুড়ে তখন এই যে আলাপন, শব্দহীন কথোপকথন– এর জন্য থাকত এক নিরন্তর অপেক্ষা। এক মুহূর্তে ফিরে আসা বা ফিরিয়ে দেওয়া নয়– দুয়ের মধ্যে থাকত এক-যোজন সময়ের বিস্তার, দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়ার ইতিহাস। (Post Box)
সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, রাগ-অনুরাগ, পাওয়া না পাওয়া নিয়ে হৃদয়ের আকুতি জানিয়ে কালির আঁচড়ে সাদা কাগজের বুকে ফুটে উঠত অন্তরঙ্গ আলাপন। ‘বলেছিলে তাই চিঠি লিখে যাই, কথা আর সুরে সুরে, মন বলে তুমি রয়েছ যে কাছে, আঁখি বলে কতদূরে…’ জগন্ময় মিত্রের গাওয়া এ গানটি যেন সুদূর থেকে ভেসে আসা কোনও মনোলগ। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বেজে চলছে নিরন্তন। সুরেলা এ চিঠির ছত্রে ছত্রে বিরহ আর ভালবাসা মাখামাখি হয়ে আছে। (Post Box)
তখন আমাদের জীবন হয়তো বা এত কেজো হয়ে ওঠেনি। জীবনের গতিতে ছিল মন্দাক্রান্তা ছন্দ। সেই আপাত গতিহীনতার সঙ্গে সঙ্গত রেখেই চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়া ছিল আমাদের সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। প্রায় ১৫০ বছরের পুরনো ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা দেশব্যাপী তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করেছিল দেড় লক্ষেরও বেশি ছোট, বড় ডাকঘরের মাধ্যমে। ডাকহরকরাদের পিঠে চিঠি আর টাকার বোঝা পৌঁছে যেত স্থান থেকে স্থানান্তরে যার দিনযাপনের কথা লিখেছিলেন কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায়। ডাকপিয়নের আবির্ভাব আরও কয়েক যুগ পরে। সাধারণ অথবা রেজিস্টার্ড চিঠি, মানি অর্ডার, টেলিগ্রাম, পার্সেল, বিদেশি ডাক– সবই পরিবাহিত হত এই সুবিশাল পরিকাঠামোর মাধ্যমে। (Post Box)
বৈদ্যুতিন বার্তা বিনিময়ের জায়গাটুকু দখল করেছিল টেলিফোন, টেলেক্স বা টেলিপ্রিন্টার যা হয়তো অধিকাংশ মানুষের হাতের নাগালে ছিল না। অতএব চিঠি এবং তার প্রত্যুত্তরের জন্য ছিল এক অধীর প্রতীক্ষা যা উন্মাদনার, উত্তেজনার বা কখনও উৎকণ্ঠার। নিদাঘ, নিঝুম দুপুরে ডাকপিয়নের সাইকেলের ঘণ্টা ঘোষণা করত তার আগমণ বার্তা। জানালার আড়ালে আন্দোলিত হত কোনও হৃদয়। বন্ধ লেটার বক্সের ছোট্ট কাচের গবাক্ষে দৃশ্যমান না- খোলা চিঠির আভাস সঞ্চার করত এক অনাবিল আনন্দের। তবে কি প্রতীক্ষার সাগর ডিঙিয়ে এল সেই চিঠি? আসলে আমাদের সকলের হৃদয়েই হয়তো বা বসত করে “ডাকঘর” এর অমল যে নিরন্তর অপেক্ষা করে থাকে কবে বাদল কিম্বা শরৎ হরকরা বয়ে নিয়ে আসবে রাজার লেখা চিঠি। (Post Box)
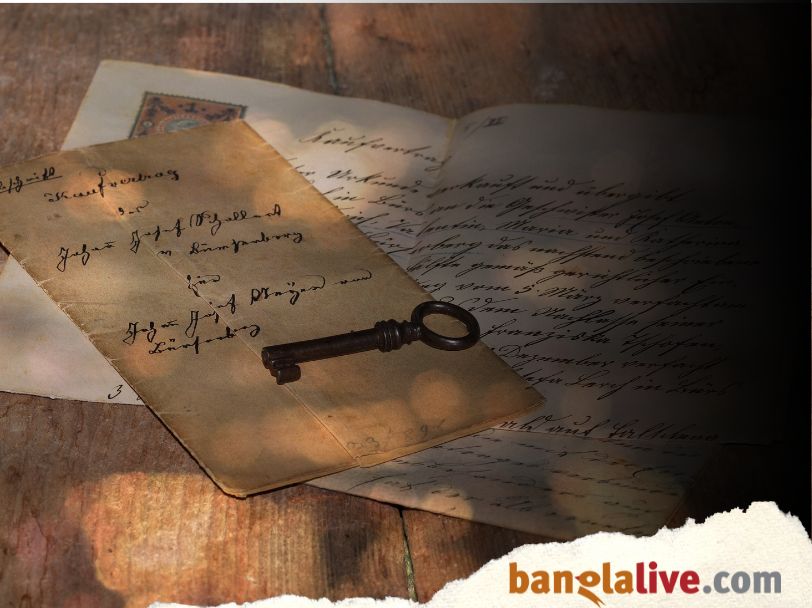
দুর্গা দশমীর দিনে লাল কালিতে দুর্গানাম লেখার পরেই শুরু হত সদ্য কেনা পোস্টকার্ডের দেড়খানা পাতায় শুভ বিজয়ার প্রণাম, স্নেহাশীর্বাদ বিনিময়ের পালা। আমার জন্য বরাদ্দ ঐ আধখানা পাতা। বিজয়ার শুভেচ্ছা দেওয়া- নেওয়া নাকি চলতে পারে দীপাবলির আগে অবধি অতএব সেই সময়ের মধ্যে চিঠি না পেলে বা দেরিতে পেলে চলত মান অভিমানের পালা। আমার মাতামহের মেজোমেজদিদি থেকে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে– এ পারে আসা হয়নি তাঁর, বলা ভাল, শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে আসতে চাননি তিনি। যেহেতু বাঙলা দেশের ডাক আন্তর্জাতিক পরিষেবার অন্তর্গত, অতএব তা পৌঁছুতে লাগত খানিক বেশি সময়। সেইজন্য ভুল বোঝাবুঝি ঠেকাতে মাতামহ তাঁর প্রথম চিঠিটি লিখতেন মেজোদিদিকে।
“কয়েকদিন আগে রাতের কলকাতায় চোখে পড়ল ১৮৭৬ সালে তৈরি “Dead Letter Office”। আলোয় উদ্ভাসিত তার লাল ইমারত। আসলে এটা হল পথহারা চিঠিপত্রের অন্তর্জলি যাত্রার শেষ পৈঠা। অন্তর্জাল আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কাছে পরাজিত ডাক ব্যবস্থার বুঝি এবার সময় এসেছে “Dead Letter Office” এর কাছে ফিরে যাওয়ার।”
তারপর যখন তাঁর চোখের দৃষ্টি গেল কমে, তাঁর নয়নের মণি এই আমি হয়ে উঠলাম তাঁর পত্রলেখক। ঝর্ণা কলমের সরু নিবের ব্যবহারে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে ঐ একখানা পোস্টকার্ড বা ইনল্যান্ড লেটারের পাতায় আমায় লিখতে হত কৃত্তিবাসী রামায়ণ। যতই আর্তনাদ করি, “আর না, অনেক হল” , মাতামহ ততই বলেন “আঃ, ল্যাখ ভাই, ল্যাখ– আর এট্টুখানি ল্যাখ”! টেবিলের পাশে রাখা কাঁচের বয়ামে কাজু কিসমিস।

এগুলোর ব্যাপারে খানিক কৃতজ্ঞতা ছিল আমার তাঁর প্রতি– সেজন্য ‘না’ বলা না গেলেও সে যে কী যাতনা!, বলে বোঝাবার নয়। “গাছে বারোটি চালকুমড়া হইয়াছে” আর “আসিবার সময় সম্ভব হইলে একখান কাঁসার মালসা আনিবেন” কিছুই বাদ যেত না সেই চিঠিতে। অতঃপর , চিঠির ইতি টানা হত “আঃ বিঃ কিঃ”– তিন অক্ষরের এই সাঙ্কেতিক বাক্যবন্ধে যার সম্প্রসারিত রূপ “আর বিশেষ কি”!
আজ সেই সব স্মৃতি…।
চিঠির জন্য এই অপেক্ষা থাকে প্রবাসেও। স্বদেশের আঙিনা পেরিয়েছে যে মানুষ, তার কাছে একসময়ে চিঠিই ছিল একমাত্র যোগসূত্র। সমরাঙ্গন যার নিরুদ্দেশের ঠিকানা, তার কাছে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের সূত্র, হাতে লেখা চিঠি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা বহু চিঠি এভাবেই সেই দিনগুলোর দলিল হয়ে রয়ে গেছে ইতিহাসের পাতায়। চিঠিরা বুকে বয়ে এনেছে জীবনযাপন আর দৈনন্দিনতার খবর, অসহয়তার, অমানবিকতার, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুমুখে- দুঃসাহসিকতার, কখনও বারুদের গন্ধভরা সামরিক ক্যাম্প, কখনও বা কারাগারের অতল অন্ধকার থেকে। (Post Box)
কিন্তু যে চিঠিরা এল না কোনওদিন– তাদের জন্য প্রতীক্ষা তো রয়েই গেল। ইংরেজি ছবি “Finding Fanny”-এর ফারদিন্যান্দ কে মনে পড়ে। গোয়ার এক অজ পাড়াগাঁয়ে পোস্টমাস্টার সে। সুন্দরী ফ্যানিকে চিঠিতে একদিন সে জানিয়েছিল যে সে তার পাণিপ্রার্থী। দীর্ঘ ৪৬ বছর বাদে, চিঠিটি একদিন ফেরত আসে তার কাছে। ফারদিন্যান্দ বুঝতে পারে ফ্যানির কাছে পৌঁছতে পারেনি সেই চিঠি। তার ভালবাসার কথা, ফ্যানি কোনওদিন জানতেই পারেনি। এবার ফারদিন্যান্দ মরিয়া, খুঁজে বার করতেই হবে ফ্যানিকে, জানান দিতে হবে সে এখনও তার জবাবের প্রতীক্ষায়! (Post Box)
কয়েকদিন আগে রাতের কলকাতায় চোখে পড়ল ১৮৭৬ সালে তৈরি “Dead Letter Office”। আলোয় উদ্ভাসিত তার লাল ইমারত। আসলে এটা হল পথহারা চিঠিপত্রের অন্তর্জলি যাত্রার শেষ পৈঠা। অন্তর্জাল আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কাছে পরাজিত ডাক ব্যবস্থার বুঝি এবার সময় এসেছে “Dead Letter Office” এর কাছে ফিরে যাওয়ার। ডাকবাক্স যা একসময় যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম ছিল, তার দিন ফুরিয়েছে, ফসিল হতে চলেছে একটা ইতিহাস। তবুও আমরা স্মৃতির বুকে আঁকিবুঁকি কাটি, হয়ত বা গেয়ে উঠি “just like before, it’s yesterday once more”! (Post Box)
(শুরুতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা “হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান” থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হয়েছে)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।