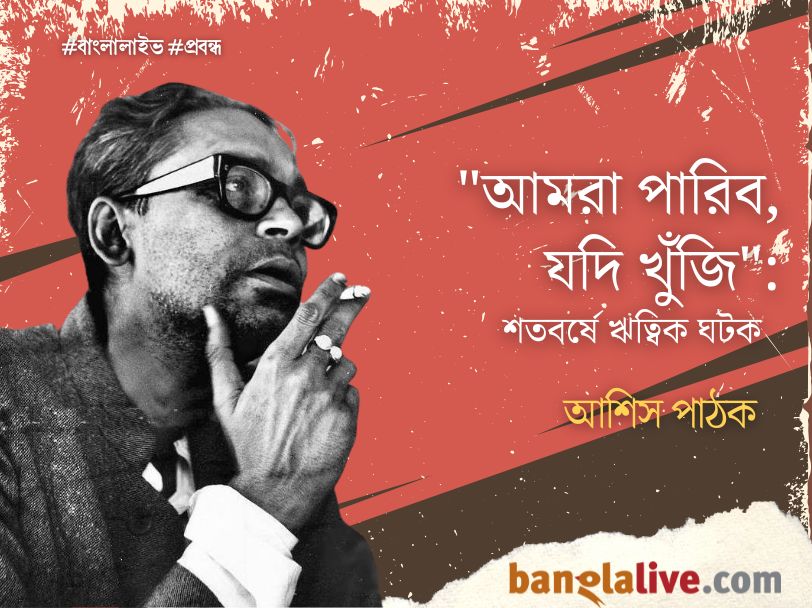(Ritwick Ghatak)
শতবর্ষ পার করলেন যে ঋত্বিককুমার ঘটক, তিনি কোন ভাষায় সিনেমা তৈরি করতেন?
উদযাপনের এই আবহে এমন একটা বোকা বোকা প্রশ্ন করলে মনেপ্রাণে ঋত্বিকময় বাঙালি নিশ্চয় তেড়ে উঠবেন, সে আবার কী? দু-একটা ডকুমেন্টারি বাদ দিলে ঋত্বিকের সব সিনেমা তো বাংলা ভাষায়! (Ritwick Ghatak)
সে কথা ঠিক। বাংলাই তাঁর প্রায় সব সিনেমার টাইটেল কার্ডের ভাষা, তাঁর চরিত্রেরা কথাও বলে বাংলা ভাষায়। কিন্তু সিনেমার ভাষা তো কেবল সংলাপের ভাষা নয়। কেবল ছবি, মানে দৃশ্যের ভাষাও নয়। আবহসঙ্গীত বা সঙ্গীতের ভাষা? না, তা-ও তো নয়। (Ritwick Ghatak)
আরও পড়ুন: অবাক আলোর লিপি: শতবর্ষে তৃপ্তি মিত্র
এ সব কথা অবশ্য শুনেছি আমরা কতবার। এ বাংলায় ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সেই গোড়া থেকেই। সেও তো হল প্রায় আশি বছর। সত্যজিত রায় আমাদের বোঝালেন যে, কথাটা হল সিনেমার সবচেয়ে দুর্বল অস্ত্র। গল্প বলাটাই সিনেমার প্রধান কাজ। কিন্তু সে-গল্প সাহিত্যের মতো কথার মালা গেঁথে বললে চলবে না। না-কথার শব্দ, সুর, দৃশ্য এমনকী স্তব্ধতার গান— সবে মিলে তৈরি হয় ছবির ভাষা। (Ritwick Ghatak)
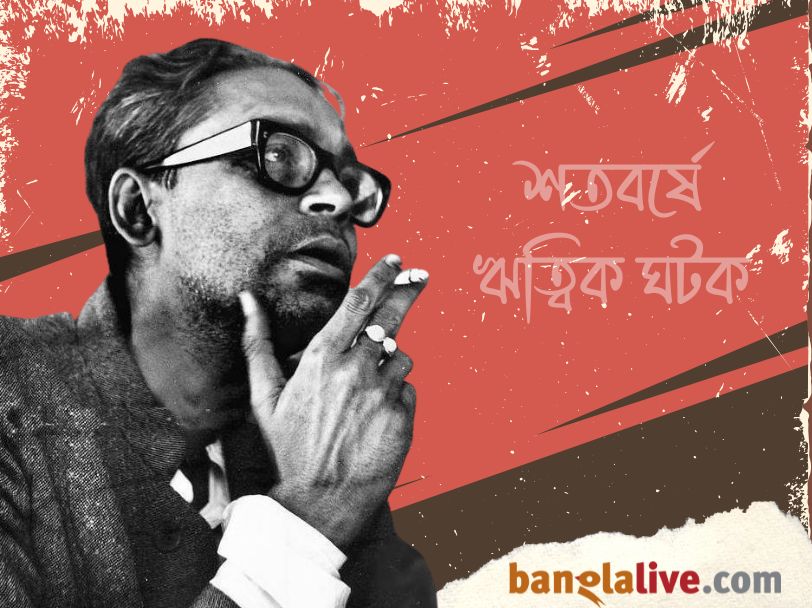
সেই ভাষার সন্ধানেই ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। সারা জীবন। মানসিক হাসপাতালে যখন, তখন অমৃত পত্রিকার ক্রীড়া বিনোদন সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর, ছবি করা। সাধু গদ্যে লেখা প্রবন্ধ। সেখানে সেই ভাষার সন্ধান, বেশী ছবি আমি দেখি নাই। এ দেশে বসিয়া তেমন বায়োস্কোপ দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। বেশী যে পড়িয়াছি, তাহাও নহে। তবু এই একটা আদর্শ কেমন করিয়া জানি না আমার সম্মুখে ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ যেমন। (Ritwick Ghatak)
“আমরা খুঁজি কি? জন্মের শতবর্ষ পেরোল ঋত্বিকের। এখন এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। নিজস্ব চিত্রভাষার সন্ধান বাংলা সিনেমায় কতটুকু?”
একটি ভাষা, যাহা কম বলিবে। যাহা স্বয়ং দ্যোতনাময়। যাহার allusion এর ভার নাই, পরিপূর্ণ ধার আছে। যাহা Reference ভারাক্রান্ত করে না, অথচ মনে পড়াইয়া দেয়, কারণ ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় যে অনুভূতি আর যে চিত্রকল্প, তাহারা Archetypal যে ভাষা সমস্ত mood-কে একটি Patriarchal ভঙ্গীতে ধরাইয়া দিবে। আপাত শুষ্ক, ভিতরে মালদহের কালাচাঁদ ভোগ আমটি একেবারে টইটুম্বুর। (Ritwick Ghatak)

তেমন ভাষাটি কিন্তু আছে। খুঁজিয়া পাইতেছি না, কি সব আজে-বাজে করিতেছি।…বায়োস্কোপে ঐ ভাষায় কথা বলা প্রয়োজন। য়ুরোপ পারিবে না, এ যুগে। আমরা পারিব, যদি খুঁজি। (Ritwick Ghatak)
আমরা খুঁজি কি? জন্মের শতবর্ষ পেরোল ঋত্বিকের। এখন এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে। নিজস্ব চিত্রভাষার সন্ধান বাংলা সিনেমায় কতটুকু? ঋত্বিক ঘটকের প্রথম নির্মিত, শেষ রিলিজ করা ছবি নাগরিক-কে যদি বাদও দিই, সত্যজিতের পথের পাঁচালী থেকে ধরলেও বাংলা আধুনিক সিনেমার বয়স এখন সত্তরের ঘরে। এই সত্তর বছরের বাংলা সিনেমার কতটুকু নিছক গল্প বলার ভাষার বাইরে কতখানি গিয়েছে? (Ritwick Ghatak)
আরও পড়ুন: রক্তকরবী: বইয়ের শতবর্ষ, নাটকের নয়
বরং বলা ভাল, যেতে পেরেছে। সাহিত্য, চিত্রকলা, এমনকী সঙ্গীতেও নতুন ভাষার সন্ধানটা জনগণেশের দাক্ষিণ্য-সাপেক্ষ নয়। খুব কম খরচেই সে-নিরীক্ষা করা যায়। কিন্তু নাট্য, যাত্রা বা সিনেমা বিপুল খরচ দাবি করে। সেই বিপুল খরচটা প্রোডিউসার করবেন কেন, যদি দর্শক না-নেয়? দর্শকই নেবে কেন যদি ওই ভাষা সে বুঝতে না-পারে? ডিম-আগে-না-মুরগি-আগের মতো এই প্রশ্নটা গত সত্তর বছরের বাংলা সিনেমার ইতিহাসে পাক খেয়েই চলেছে। (Ritwick Ghatak)
তবু ঋত্বিক ঘটকের ‘মেঘে ঢাকা তারা’ জনপ্রিয় হয়েছিল। টিকিট বিক্রি হয়েছিল বেশ ভাল। কারণ সে-ছবি গল্পই বলেছে প্রধানত। বহু মানুষের আইডেন্টিটির সঙ্গে জড়িয়ে এক করুণ গল্প। কিন্তু সেই ছবির লাভ থেকে পয়সা ঢেলে যখন পরের ছবি ‘কোমল গান্ধার’ করলেন, ডুবে গেল সব। কারণ সে ছবি তো নতুন এক ভাষার খোঁজ করেছিল। আলোয়, ছয়, গানে আর গানের মতো গঠনে তৈরি এক ভাষা— এমনকী খুব প্রখর অনুভূতি থাকলে খোয়াইয়ের ধারে যার জ্যোৎস্নাদৃশ্যে বসন্তের বাতাসটুকুও চলে যায় প্রাণের পরে। (Ritwick Ghatak)
“শতবর্ষী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যারা কথা দিয়েই তাঁর কথা বলি, তারা কি কখনও ছুঁয়ে দেখতে চাইব, না-বলার ওই থেমে যাওয়াকে?”
সেই ভাষার খোঁজ গত সাত দশকে আর করেনি বাংলা সিনেমা। ঋত্বিকও করেননি। করতে পারেননি। তিনি ততদিনে ফ্লপ ডিরেক্টর। তাই প্রযোজকেরা তাঁকে পয়সা দেন না ছবি করার। সরকারি পয়সাও পান না। সেই বিষ্ণুপ্রিয়া নামে একটা ছবির প্রস্তাব পাঠান সরকারি ফিল্ম ফিনান্স কর্পোরেশনে, উত্তর মেলে না। অথচ, সে ছবি, যা তিনি করতে চেয়েছিলেন, নতুন চিত্রভাষার দাবি করেছিল। নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া নামে কোনও একটি মেয়ের ধর্ষিতা হয়ে খুন হওয়ার ঘটনাকে তিনি দেখবেন শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপের সঙ্গে মিলিয়ে। প্রবীর সেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলছেন:
“চৈতন্যদেবের প্রথমা স্ত্রী ছিলেন লক্ষ্মীপ্রিয়া। তিনি সর্পদ্রংষ্টা হয়ে মারা যান। তারপর তার ছোট বোনকে বিয়ে করেন ঐখানেই চৈতন্যদেব। আর চৈতন্যদেব, অ্যাজ ইউ নো, যে, সারা বাংলায় তাঁর ইনফ্লুয়েন্স ফিফটিন্থ সেঞ্চুরীতে… তাঁর পাশে তো দাঁড়াবার কেউ ছিল না। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। এবং অ্যাজ লাক উড হ্যাভ ইট, ঠিক সেই গ্রামেই আরেকটা বিষ্ণুপ্রিয়া আজকে মারা গেল। যে গ্রাম, আপনারা যে কোনো গ্রামে যান শুনতে পাবেন যে, ‘শচীমাতা গো আমি যুগে-যুগে হই জনম দুখিনী।’ এটা আমার বাংলার যে কোনো গ্রামে আপনি ঢুকলে পাবেন। (Ritwick Ghatak)
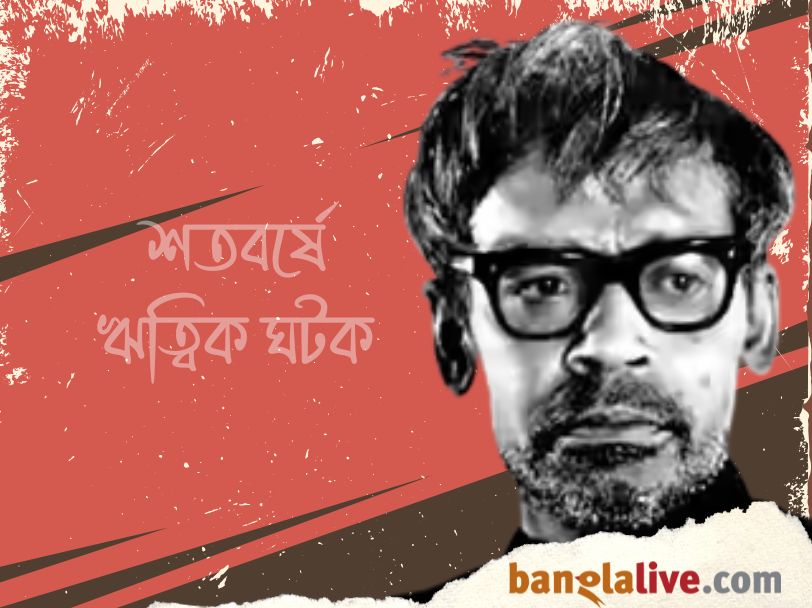
ওটার সঙ্গে ক্রস রেফারেন্স আমি যেগুলো করবো (লোকেশ ঘটককে নির্দেশ ক’রে) ও জানে না হয়তো। ওকে এমনি জাস্ট একটা রাফ স্কেচ করতে দিয়েছি। দেখুন, নব্যন্যায় তখন বাংলায় সবে জন্মগ্রহণ করছে। ঐ নবদ্বীপের ঘাটে। সেই সময়ে নবদ্বীপে ছিল একেবারে ব্রিলিয়ান্ট ইনটেলেকচ্যুয়াল্স। একটা নয়, একশোটা। মহাপণ্ডিত, মহাশিক্ষিত। এ’রা ছিল তখন, ঐ নবদ্বীপের ঘাটে বসত। আলোচনাগুলো সব, ঘাটে বসে হত। তার মধ্যে নিমাই সন্ন্যাসী একজন ছিল। (Ritwick Ghatak)
হ্যাঁ, সে, জীবন…কানা রঘুমনি, তিনি স্মার্ত পণ্ডিতের শেষ… স্মৃতির শেষ কথা সে বলে গেছে। এই সমস্ত পার্টি…তো ঐগুলোকে ইন্টারকাট করবো—আজকের এই জীবন আর তার সঙ্গে ঐ জীবন, দুটোকে আমি পাশাপাশি রাখবো। এই মোটা-মুটি আমার মাথার মধ্যে আছে। লিখতে হবে ভাল করে। ন্যায়, নব্যন্যায়। যেটা একমাত্র বাংলার কন্ট্রিবিউশন। (কিন্তু) এবার সারা ভারতবর্ষে এখন চলছে এসবগুলো…এইসব আর কী। আর বেশি বলে লাভ কী?” (Ritwick Ghatak)
আরও পড়ুন: শেষ ভাইফোঁটার বর্ণ-ছবি
নতুন ছবি সম্পর্কে কথা থামিয়ে দেন ঋত্বিক।
শতবর্ষী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যারা কথা দিয়েই তাঁর কথা বলি, তারা কি কখনও ছুঁয়ে দেখতে চাইব, না-বলার ওই থেমে যাওয়াকে? (Ritwick Ghatak)
ডিজিটাল ও মুদ্রিত মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
আশিস পাঠক বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের প্রকাশনা ও বিপণন আধিকারিক।
আনন্দবাজার পত্রিকায় সাংবাদিকতার পাশাপাশি নানা সময়ে যুক্ত থেকেছেন সাহিত্য অকাদেমি, বাংলা আকাদেমি, কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিভাগের নানা প্রকল্পে, নানা পুরস্কারের বিচারক হিসেবে। সংস্কৃতির নানা মহলে তাঁর আগ্রহ, বিশেষ আগ্রহ রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থবিদ্যায়।