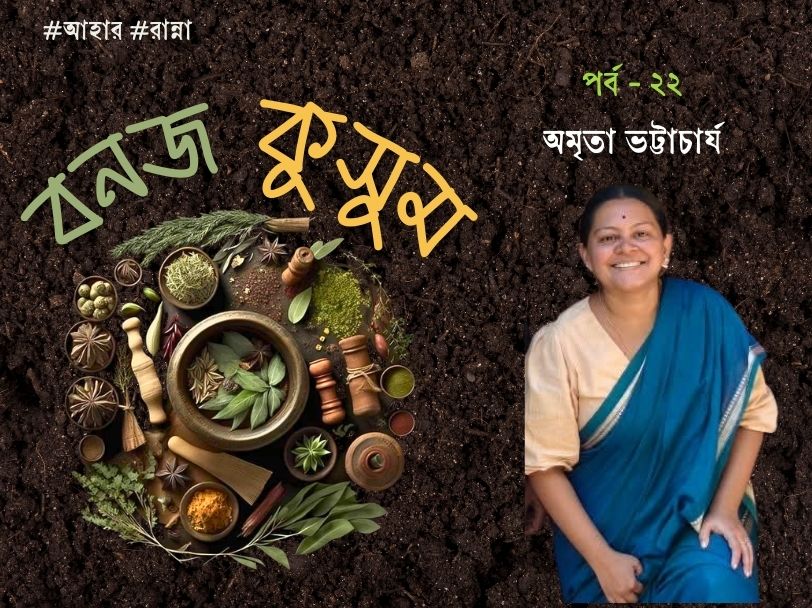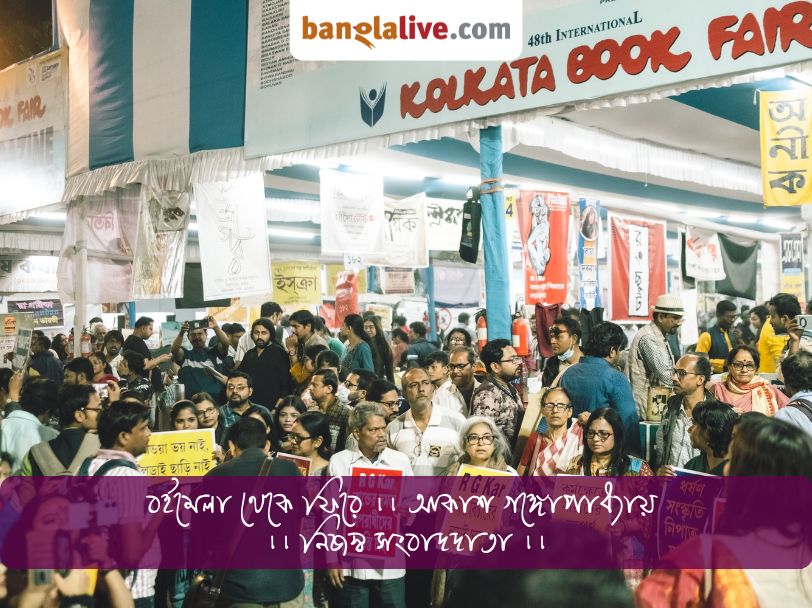“রেনম্যান” সিনেমায় ডাস্টিন হফম্যানের চরিত্রটি কি মনে আছে? সে ছিল অঙ্কে পারদর্শী। এতটাই যে তাকে জিনিয়াস বলা চলে। সে একটা টেলিফোন ডিরেক্টরি এক লহমায় মুখস্থ করে ফেলতে পারত। কিন্তু সেই চরিত্রটি ছিল অটিজম-আক্রান্ত। অটিজম মানেই কিন্তু জড়-বুদ্ধি নয়। অটিজম-আক্রান্ত কিন্তু ভয়ঙ্কর রকম বুদ্ধিমান হতে পারে, দারুণ ট্যালেন্টেড, মেধাবী—সব রকম গুণ তার থাকতে পারে। সুতরাং অটিজম নিয়ে আলোচনা করার আগে, এটা বুঝে নেওয়া ভাল যে অটিজম-আক্রান্ত মানেই জীবন শেষ নয়, সমাজ বহির্ভূত নয়। সে স্বাভাবিক জীবনের অধিকারী। তাকে আলাদা করে রাখার কোনও প্রয়োজন নেই।
ইদানীং কালে “অটিজম” কথাটি বা অসুখটি শিশুদের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খুব শোনা যায়। অটিজম মস্তিষ্কের স্নায়ুজনিত একটি অসুখ। কিন্তু প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে অটিজম শুনলেই ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। অটিজম-এর পরিধি যেহেতু অনেকটা বিস্তৃত, তাই যে কোনও শিশুর অটিজম আছে মানেই সে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে না, এমনটা মোটেও নয়। যেহেতু অটিজম-এর পরিধি অনেকটা বিস্তৃত তাই এখন কেবল অসুখটিকে অটিজম না বলে বলা হয় “অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার”। কোনও শিশুর মধ্যে খুব অল্প লক্ষণ দেখা দিতে পারে, কোনও শিশুর মধ্যে মাঝারি তীব্রতার লক্ষণ দেখা দিতে পারে আবার কোনও কোনও শিশুর মধ্যে তীব্র লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সেই অনুযায়ী এখন শিশুদের চিকিৎসা পদ্ধতিও তৈরি হয়েছে। আসলে, মস্তিষ্কের যে অংশ মানুষের মধ্যে সামাজিকতা বোধ, অন্যের সঙ্গে মেলামেশা করার বোধকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই অংশের ঠিক মতো বিকাশ না ঘটলে যে সব সমস্যা দেখা যায়, সেই সবই অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার-এর মধ্যে পড়ে।
কিন্তু অটিজম ব্যাপারে সবচেয়ে বড় শিক্ষা নিতে হবে এবং আত্মস্থ করতে হবে অটিস্টিক শিশুর মা-বাবাকে। তাঁরা যদি মেনে নিতে না পারেন যে তাঁর বাচ্চা “অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার”-এর মধ্যে কোথাও পড়ছে, তা হলে সেই শিশুর বেড়ে ওঠায় সমস্যা হতে পারে। প্রথমেই অভিভাবককে এ কথা বুঝতে হবে যে অন্য যে কোনও শিশুর মতোই সে জীবনযাপন করতে পারে। বরং অল্প লক্ষণ থাকতে থাকতে যদি থেরাপি আরম্ভ করা যায়, তা হলে সেই শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবন আর পাঁচটা সাধারণ বাচ্চার মতোই হতে পারে। আজকালকার মা-বাবারা শিশুর যে কোনও বিষয়ে এত সচেতন অথচ দেখা যায় যদি এই ধরনের সমস্যা শিশুর মধ্যে দেখা যায়, তখন তাঁদের চিন্তাভাবনা পুরনো যুগের চেয়ে কিছু এগোয়নি। যদি কোনও বাচ্চা কথা বলতে বেশ দেরি করে, তখন তার ঠাকুমা-দিদিমা বলতে থাকেন, শিশুটির মা বা বাবাও দেরি করে কথা বলেছিল, কী দেরি করে হাঁটতে শুরু করেছিল। আমি তখন ভাবতে চেষ্টা করি আমার বাচ্চারা কোন সময় কথা বলেছিল বা ঠিক কোন বয়সে হাঁটতে শুরু করেছিল, আমার ঠিক মনে নেই। এর দুটি উত্তর হয়। এক, হয় আমি একেবারেই বুদ্ধিমান নই বা আমার স্মৃতিশক্তি খুব নিম্নমানের এবং অন্যদের স্মৃতিশক্তি খুবই প্রখর। আর দুই, আসলে কেউই ত্রিশ-বত্রিশ বছর বাদে ঠিক মনে রাখতে পারেন না, সন্তান কোন বয়সে কথা বলেছিল বা হেঁটেছিল। যেটা বলেন সেটা অনুমান মাত্র। এতে আর কিছুই নয়, শিশুটির ক্ষতি হয়। একটি ফোসকা পড়লে মা-বাবা বাড়ি মাথায় করেন, ডাক্তারের চেম্বারে এসে দু-দণ্ড অপেক্ষা করতে পারেন না। আর অটিজম সংক্রান্ত লক্ষণ দেখা দিলে এমন ব্যবহার করেন, যেন এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক। তাঁদের সন্তানের কিছুই হয়নি, ডাক্তারবাবু বাড়াবাড়ি করছেন।
যাঁরা বুঝতে চান বা শিশুদের সাহায্য করতে চান, তাঁরা সবাই জানতে চান যে কী দেখে বুঝব বাচ্চাটি অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডারের আওতায় পড়ছে। প্রথমেই বলি, অটিজম কিন্তু আঠারো মাস বয়স থেকেই বোঝা যায় কয়েকটি লক্ষণ দেখে। আবার সব সময় সেই লক্ষণ মানেই যে বাচ্চাটি তীব্র ভাবে অটিজম-এর শিকার হবে, তা না-ও হতে পারে। বিদেশে কিন্তু এখন সব বাচ্চাকেই প্রায় এই পরীক্ষা করা হয়। আমাদের এখানে যেহেতু সেই চল নেই, এবং অভিভাবকরাও উৎসুক নন, তাই আমরা এড়িয়ে যাই। কিন্তু কয়েকটি লক্ষণ যদি অভিভাবকরা নিজেরাই লক্ষ করে ডাক্তারকে জানান, তা হলে পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে যেতে পারবেন শিশুটি অটিজম আক্রান্ত কি না। যদি হয়ও, তা হলেও এত রকম থেরাপি এখন রয়েছে যে তার দ্বারা শিশুরা সাধারণ জীবনযাপন করতে সক্ষম।
যে লক্ষণগুলি দেখলে বুঝবেন যে শিশু অটিজম আক্রান্ত হতে পারে:
- চোখে চোখ রেখে কথা বলতে অস্বস্তি
- দেরিতে কথা বলতে শুরু করা বা একেবারেই কথা না বলা
- সামাজিক মেলামেশায় অনীহা
- সামান্য চেনা পরিস্থিতি বদলেও মানসিক চাপ
- অচেনা পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে অস্বস্তি, বিরক্তি, রাগ প্রকাশ
- শরীরী ভাষা প্রকাশে অনিচ্ছা বা তার অর্থ না বোঝা
এই লক্ষণগুলি কিন্তু মা-বাবাকে এখন অনেক আগে থেকে সচেতন করতে সমর্থ সন্তানের অটিজম আছে কি না। পরিসংখ্যান বলছে এখন ৫৪ জনে এক জন শিশু অটিজম আক্রান্ত হচ্ছে। ফলে এটা নেহাতই একটা সাধারণ ঘটনায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আগেও কি অটিজম ছিল না? নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তখন এত আমল দেওয়া হত না বা এত বেশি রিপোর্ট হত না। আরও একটি প্রশ্ন জাগে যে, এখন কি বেশি রিপোর্ট হচ্ছে না অসুখটি বেড়েছে? এই প্রশ্নের দুটো উত্তরই, হ্যাঁ। আগের চেয়ে মানুষ সচেতন হয়েছেন বলে রোগটি রিপোর্ট হচ্ছে অনেক বেশি। এবং, আমার মতে, এখন শিশুরা মোবাইল ও টিভি অনেক বেশি দেখে বলে আগের চেয়ে অটিজম রোগে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে। শিশুদের মনোযোগ কমে গিয়েছে, সামাজিক মেলামেশা করতে বাধ্য হয় না তারা, বাইরের পৃথিবীতে কী ঘটে চলেছে তা এক বার মুখ তুলে চেয়ে দেখেও না। ফলে প্রকৃতির নিয়মে যে সব বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি ঘটে, তার কিছুই হয় না এখন। আর তা-ই মোবাইল জগতে ঢুকে গিয়ে শিশুদের প্রকৃত জগত সম্পর্কে বিশেষ ধারণাই জন্মাচ্ছে না। এটা কিন্তু বিশেষ চিন্তার কারণ।
ড. অপূর্ব ঘোষ প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। ইনস্টিটিউট অব চাইল হেলথ-এর অধিকর্তা। সম্প্রতি মৃণালিনী ক্য়ান্সার সেন্টার তৈরি করেছেন শিশুদের ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য। বহু সামাজিক কর্মে নিযুক্ত রাখেন নিজেকে। সাহিত্য ভালবাসেন, তবে মনীষীদের জীবন তাঁকে বিশেষ উদ্বুদ্ধ করে।