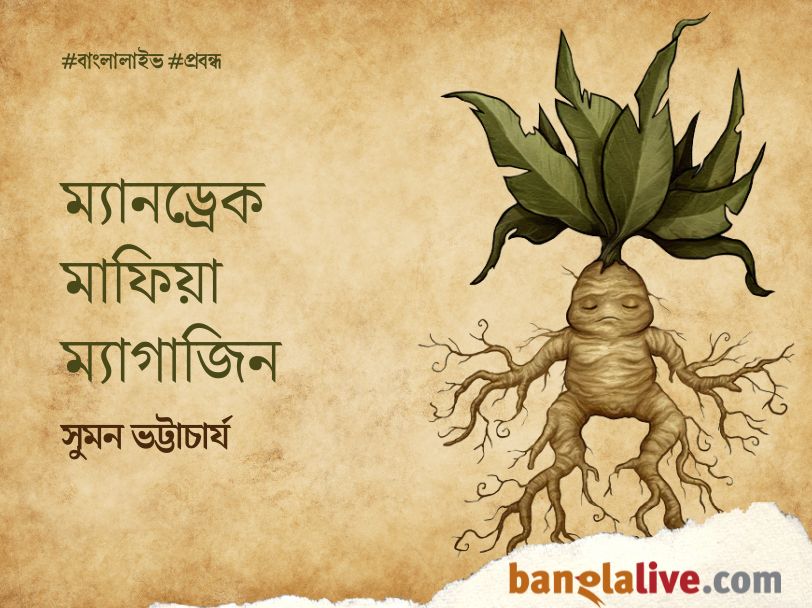(Mandrake)
এ-যেন কেমন, বেড়ালের তালব্য শ দিয়ে চশমা।
নাকি গ্যালিভার-দন কিহোতে-ঘনাদার আড্ডা। বরং এরকমটা বলা যায়। ডুবে ডুবে খায় জল/একাদশীর গ্যাঁড়াকল সে বলা যায় যা খুশিই। এমনকি গ্যালিভারের সঙ্গে ঘনাদার আড্ডাওতো জমেই। ম্যানড্রেককে তো জানেন সকলেই অন্তত আজ যাঁদের বয়স পঞ্চাশের ওপর, তাঁরা সকলেই। জাদুকর ম্যানড্রেক তাঁর স্ত্রী সুন্দরী নার্সা এবং বলবান সহযোগী লোথার। (Mandrake)
আরও পড়ুন: রূপলাল হাউস: ভাঙা কার্নিশে হলুদ শাড়ি আর অন্দরে জৌলুশের মরিচা
যুযুৎসী কৌশলী পাচক হোজো আর স্ফটিক গোলোক নিয়ে কালদ্রষ্টা হেরন এঁদের কেরামতিতে গাঁথা লী ফক্-এর চিত্রকথামালা তো এক সময়কার নিত্য পাঠ্যই। আবার এখন যাঁরা পনেরো-কুড়ি-বা তিরিশ, তাঁরা রাউলিং-এর হ্যারি পটারের খেই ধরে চেনেন আরেক ম্যানড্রেক। কিন্তু জাদু আর ম্যানড্রেক কেন একযোগে আসে বারবার। এর গোড়ায় আছে ম্যানড্রাগোরা বা মাল্লাগোরা নামে এক ধরণের গুল্ম তার আরেক নাম ম্যানড্রেক। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের গাছ। তবে কথাটা আক্ষরিক অর্থেই গোড়ার। মানে শিকড়ের। এই গাছের শিকড়কে দেখলে হঠাৎ করে মানুষের মতোই লাগে। যেন এক দু-পেয়ে জীব। কে জানে, ওই আড়াই ফুটিয়া গাছের ছবি-ছাবা দেখবার পরেই রবীন্দ্রনাথ, তালগাছ-এর কথায় অমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে শব্দটি লিখেছিলেন কী না! (Mandrake)

এই ম্যানড্রেক চলে এসেছিল কৌতূহল আর রহস্যের খাসতালুকে। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা নেড়ে-ঘেঁটে দেখেছেন, এর প্রথম বিশেষত্ব একটা মিষ্টি গন্ধ, যা টেনে রাখে মানুষকে। তারপর দেখা গেল ভেতরকার ‘দ্রব্যগুণ’-এ আছে হ্যালুসিনেশন লা দৃষ্টিবিভ্রমের কারিগরি। সুতরাং এরপর জাদুকরের নাম তো ম্যানড্রেক হতে বাধ্য। ম্যানড্রেকও তো সম্মোহিত করতেন বদের হদ্দ লোকজন, থুড়ি, প্রতিপক্ষকে। (Mandrake)
ম্যানড্রেকের কেরামতির যেন শেষ নেই। বোধহয় একমাত্র চিৎকার করা গাছ, বলা হয় ম্যানড্রেকের কলা। ভেষজবিদ্যার ওস্তাদরা এই গাছপালা থেকে ওষুধবিষুধ বানাবার সময় কানে সেঁটে নিতেন ঠুলি যাতে ওই শব্দ মাথা না ঘুলিয়ে দেয়। এরকম গাছকে ঘিরে গল্প তো গড়ে উঠবেই। বলা হ’ল ডাইনিরা যে উড়ন্ত মলম ব্যবহার করে, তা এই ম্যানড্রেক দিয়েই আর তাদের জাদু পানীয়ের মূল উপাদানও ম্যানড্রেক। ম্যানড্রেকের ছেলে-গাছ, মেয়ে-গাছ চেনা খুব সহজ। পুরুষ ম্যানড্রেক দেখে মনে হয় লম্বা দাড়িওয়ালা কেউ দাঁড়িয়ে। আর মেয়ে-ম্যানড্রেকের মাথায় যেন ঘন চুলের ঝোপ-ঝল্পর গোছা। (Mandrake)
“এই গাছ রক্ষা করে দানবদের কবল থেকে। ম্যানড্রেক শিকড়ের পাশে টাকা রাখলে তা দ্বিগুণ-তিনগুণ হয় আর উর্বরতা, গর্ভধারণ তার সুস্থিতির সঙ্গেও মিলেমিশে আছে, ম্যানড্রেক।”
গাঁজা গাছের জন্মকথায় শয়তানের সঙ্গে যোগাযোগ নিয়ে আছে হরেক কিস্সা। ম্যানড্রেক নিয়েও গল্প এরকম, যে ফাঁসিতে ঝোলা পুরুষের পায়ের তলায় জন্মায় এই গাছ। মৃত পুরুষের স্থলিত শুক্রপাত থেকে মাটিতে নেমে আসে বৃক্ষসীজ “project human seed into animal earth” মোটের ওপর ব্যাপার খুবই গোলমেলে। (Mandrake)
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের গুল্ম। সুতরাং ফ্রিক সাহিত্যেও এর অবস্থান অনিবার্য। এই গাছের ফলকেই বলা হয়েছে। ‘লাভ-অ্যাপল’ আর আফ্রোদিতি-র সঙ্গেও যোগাযোগ অতি ঘনিষ্ঠ। হোমারের ওডিসিতে সেই কনটিনেনট অফ সার্সির কুহকিনীরা তো ম্যানড্রেকের ব্যবহারেই, শুয়োর করে রাখতেন পুরুষদের। (Mandrake)
তবে বেশ জবরদস্ত উপাখ্যান, ম্যানড্রেক সংগ্রহ নিয়েই: চাঁদনি রাতে ম্যানড্রেক গাছের সঙ্গে একটা কুকুরকে বেঁকে রেখে তাড়া করতে হয়। কুকুরের দৌড়ে উপড়ে আসে ম্যানড্রেক আর মারা যায় বেচারা কুকুরটি। (Mandrake)
“মারিও পুজোর অনবদ্য উপন্যাস Godfather বলা উচিত, গডফাদার ট্রিলজিও দুনিয়া কাঁপানো। তার দুসরা উপন্যাসের নামই দ্যা সিসিলিয়ান (১৯৮৪)-এর নায়ক সালভাতোর গিউলিয়ানো।”
শুধুই কি এমন সব ভয়ংকরের ডাকহাক! না। কিছু ভাল কথাও আছে। এই গাছ রক্ষা করে দানবদের কবল থেকে। ম্যানড্রেক শিকড়ের পাশে টাকা রাখলে তা দ্বিগুণ-তিনগুণ হয় আর উর্বরতা, গর্ভধারণ তার সুস্থিতির সঙ্গেও মিলেমিশে আছে, ম্যানড্রেক। মনে করুন এ হল চন্দ্রবিন্দুর চ। (Mandrake)
মাফিয়া তো সকলে জানেন, এখন আর মগের মুলুক তেমন বলে না কেউ। তা এখন মাফিয়া মুলুক। মাফিয়ার মুঠি বা তালুও বলা যায়। সিসিলির একটি অপরাধী দল বা অপরাধীদের জমায়েত একদা চিহ্নিত হয়েছিল মাফিয়া নামে। (Mandrake)

অধুনা সর্বদেশেই যে বা যারা বাঁকা পথে, ট্যারা মতে বেশ কিছুটা দাবিয়ে রাখে সিধেপথের লোকজন বা সংস্থা-প্রতিষ্ঠানকেও তারাই মাফিয়া। সাধারণ পাড়ার রক বা এলাকার মোড় থেকে মদ-মজলিশ যেকোনও চত্বরে, দাপুটে লোকজন নরনারীই মাফিয়া। পাড়ার বাজার, খেলার মাঠ থেকে বৃহত্তর অঙ্গন শিক্ষা-সাহিত্য-কালচারেও মাফিয়া বিস্তর। (Mandrake)
আরও পড়ুন: ব্রহ্মা জানেন গোপন কম্মোটি
মাফিয়া কিন্তু গোড়া থেকেই এমন নয়। মানে শব্দটার গোড়ায় অত ময়লা ছিল না। বরং ছিল অসহায়তা। ম্যানড্রেকের তুলনায় মাফিয়া কালের বিচারে বিরিঞ্চিবাবার চোখে যিশুখ্রিস্ট এক্কেবারে সেদিনের ছেলে। সিসিলিতে আরব্যদুনিয়ার অধিকার গেড়ে বসলে, সেই নবম শতক, সিসিলির যেসব পরিবার ওখানকার পাহাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করেছিল, আশ্রয় নিয়েছিল আরবরা তাদের বলত মাফিয়া। মাফিয়া-মূলত আরবি শব্দ যার মানে, একটা আশ্রয়। যেমন তেমন করে লুকিয়ে থাকাও বলা যায়। এবং অতঃপর আরেক প্রস্থ “বেহড় বাগী বন্দুক” এর বিলিতি সংস্করণ। সেই লুকিয়ে থাকা লোকজন কোনও রকমে চাষবাস করে খায়, আর আরবদের হটিয়ে তাদের নিজভূমে ফেরবার চেষ্টা করে। সুতরাং তখন তারা চিহ্নিত হতে থাকে ডাকাতের তকমায়। এগারো শতকে নর্মান কস্কোয়েস্ট পর্বেও ইতালির সঙ্গে সংযুক্তির পর, যাঁরা একদা ছিলেন আশ্রয়ার্থী দেশোদ্ধার ব্রতী তাঁরা নানাধরণের অপরাধকেই করে নেন তাঁদের নিত্যবৃত্ত। (Mandrake)
একটা বড় অংশ চলে গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮৯০-এর দশক থেকেই সেখানেও নানান উপদ্রবের ধারাবাহিকতায় তাদের ক্ষমতা যেন অবিসংবাদী। ১৮৯৯-এ জন্মেছিলেন “বিখ্যাত” গ্যাংস্টার আলফাঁসো আল কাপোন। ইতালিতে বেনিতো মুসোলিনির আমলে তাঁর কঠোর নিয়ন্ত্রণে, দমনবিধিতে তিষ্ঠোতে না পেরে সিসিলির মাফিয়াদের আর একটা বড় অংশ চলে আসে যুক্তরাষ্ট্রে। বিশেষত শিকাগোতে। এরপর একটা সময় যাবতীয় চোরাকারবার, জুয়ার আসর-গণিকা সদন, এবং আরও আরও কাণ্ডকারখানায়, যাকে বলে “বিকশিত” হয়েছিল অতি কুখ্যাত মাফিয়াযুগ, আল কাপোন যুগ। (Mandrake)

মারিও পুজোর অনবদ্য উপন্যাস Godfather বলা উচিত, গডফাদার ট্রিলজিও দুনিয়া কাঁপানো। তার দুসরা উপন্যাসের নামই দ্যা সিসিলিয়ান (১৯৮৪)-এর নায়ক সালভাতোর গিউলিয়ানো। তবে এখন এদের কথায় ঢুকলে বেরোনো মুশকিল। (Mandrake)
“ইস্কুলে ইনস্পক্টরের “প্রাদুর্ভাব” জীবনে কী হতে চাও এই কঠিন প্রশ্নে, শিবরামের ইচ্ছে ছিল ফিলানথ্রপিস্ট বলবার। কিন্তু মোক্ষম মুহূর্তে তা গুলিয়ে ওঠায়, বলে ফেললেন প্যাট্রিয়ট।”
তাই এর লাগোয়া কথায় আসা ভাল, উনিশ শতকেই নেপল্স-এ আরও এক গোষ্ঠী ঘনিয়েছিল তাদের নাম ক্যামোরা। দলবদ্ধ গুণ্ডাবাজি, যাবতীয় বেআইনি কাজে অতি করিৎকর্মা এই ক্যামোরার উদ্ভব জেলখানায়। ছক একই -জেলখানাগুলো হয়ে যায় বদমাশদের বীজতলা। মোটামুটি ১৮২০ থেকে এই কারবারের বাড়বাড়ন্ত হতে হতে ১৮৪৮-এ এঁরা সেঁধিয়ে যান প্রশাসনের অন্দরে। রাজনীতিতে। দৌরাত্ম্য চলছিল, ১৯১১-এ যতদিন না সমূহ কঠোরতায় দুরমুশ করা হয় এই ক্যামোরা-কুলকে। স্প্যানিশ ভাষায় ক্যামোরা শব্দের মানে, অত্যন্ত সরল আর পরিষ্কার ঝগড়া। (Mandrake)
এখন আর সেরকম গোষ্ঠীনামে চেনা দুর্বৃত্ত সংঘ তেমন নেই, তবে ডন-বেশ চলছে। ডনদের বৈঠক বা জমায়েতকে যদিও ডনবৈঠক বলে না, তবে বললে আপত্তি করবেন কেউ? মারিও পুজো-ই লিখেছিলেন, দ্য লাস্ট ডন, দোমেনিকো ক্লেরিকুজিও, তো ঠিক করেইছিলেন, ছেড়ে দেবেন, সপরিবারেই, মাফিয়াজীবন। অবশ্য এখানে রবীন্দ্রনাথের ‘মদনভস্মের পর’ কবিতার সূত্র মেনে বলা যায়: (Mandrake)
মাফিয়াদেরকে নামেই হঠিয়ে
করেছ এ কি সন্ন্যাসী?
বিশ্বময় দিয়েছ তারে গড়ায়ে
কঠোরতর দাপট তার বাতাসে ওঠে নিঃশ্বাসি
অস্ত্র তার দুনিয়াজোড়া ছড়ায়ে।।
“ম্যাগজিন বা সাময়িকীও লেখকদের, শিল্পীদের আশ্রয়। কতজনই তো আছেন, ছিলেন পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, আজীবন। বেশ ভাল লেখা লিখেও, হারিয়ে গিয়েছেন মানুষের স্মৃতি থেকে।”
তাহলে একে কী বলবেন? বেড়ালের তালব্য শ? অবশ্য বেড়ালের তালব্য শ-ও আছে। যদি অনুমতি করেন পরে বলা যাবে। ছিল বাস্তুচ্যুত নিরীহ মানুষ হয়ে উঠল…? (Mandrake)
রহস্য-টহস্য থামানো যাক। আসুন ম্যাগাজিন প্রসঙ্গে। খুবই ভাল কথা। ম্যাগাজিন তো বঙ্গজনের প্রাণের আরাম-আত্মার শান্তি! শিবরাম তো লিখেইছিলেন, প্যাট্রিয়ট আর ফিলানথ্রপিস্ট এই দুটো শব্দ নতুন শিখে তাকে জুৎসই দেগে দিতে ছটফট করছেন তিনি। ইস্কুলে ইনস্পক্টরের “প্রাদুর্ভাব” জীবনে কী হতে চাও এই কঠিন প্রশ্নে, শিবরামের ইচ্ছে ছিল ফিলানথ্রপিস্ট বলবার। কিন্তু মোক্ষম মুহূর্তে তা গুলিয়ে ওঠায়, বলে ফেললেন প্যাট্রিয়ট। ইনস্পেক্টর রুষ্ট। কতিপয় ছাত্র হৃষ্ট। একজন তো নিয়েই গেলেন গুপ্ত সমিতিতে। শিখতে হবে অস্ত্র প্রয়োগ। চালাতে হবে রিভলভার। তারপর শ্বেতাঙ্গ শাসকদের হত্যা করতে হবে প্রকাশ্য সমাবেশে। উৎসাহিত করলেন স্বাধীনতাব্রতী অগ্রজ। ধরা তিনি পড়বেন না ধরা পড়তে দেওয়া হবে না।

শিবরাম সাহেবকে গুলি করা মাত্র গুলি করা হবে তাঁকেও। শিবরামের প্রশ্ন: মরেই তো গেলাম! তো আর দেশসেবা কেমন করে হবে? উত্তর প্রস্তুত: শহীদ হলে বিভিন্ন কাগজে জীবনী বেড়োবে ফলাও করে। কিন্তু লিখবে কে? যিনি বা যাঁরা জীবিত থাকবেন লিখবেন তাঁরাই। ভেবেচিন্তে শিবরাম প্রস্তাব দিলেন। ব্যাপারটা যদি জীবনী লেখাই হয়, তবে আর গুলিগোলায় কাজ কী। একটা ম্যাগাজিন বের করা যাক, সেখানে একে অপরের জীবনী লিখবে। পড়তে পারবে নিজেরাও। যুক্তি নিখুঁত। আর বঙ্গজনের ম্যাগাজিন- প্রাণ তারও বিপুল হাওয়া বাতাস! (Mandrake)
তবে কিনা, ম্যাগাজিন কিন্তু গুলি গোলার বাইরে নয় মোটে। এ আর তেমন বিশদ করে বলবার নয়। বন্দুকেই থাকে। মাফিয়ার মতো সরাসরি আরবি শব্দ নয়। কিন্তু এরও মূলে আছে আরবি শব্দ মাখজান makhzan মানে ভাঁড়ার ঘর। যেখানে জমা করে রাখা হয় হরেক জিনিস। এই সংগ্রহকথা কেমন করে সাময়িকপত্র অর্থে এল? ১৭৩১-এ এডোয়ার্ড কেভ-এর সম্পাদনায়, বেরোয় The Gentlemen’s Magazine, এর ভূমিকায় যা লেখা হয়েছিল, তা এরকম: বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনদের বিবেচনায় আসা বিশেষ প্রসঙ্গ বা বিষয় নিয়ে, লেখালিখির একটি সংকলন যা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বেরোবে। গেজেত্তা (Gezetta) থেকে সাময়িকীর ম্যাগজিন হয়ে ওঠার সেই শুরু। লেখালিখির সংগ্রহপত্র-ভাঁড়ার ঘর হল ম্যাগাজিন। এরপর দিন গেছে, মাস গেছে ও বছর আর শতাব্দীও গেছে, ম্যাগাজিন চলছেই। (Mandrake)
ম্যাগজিন বা সাময়িকীও লেখকদের, শিল্পীদের আশ্রয়। কতজনই তো আছেন, ছিলেন পত্রপত্রিকায় লিখেছেন, আজীবন। বেশ ভাল লেখা লিখেও, হারিয়ে গিয়েছেন মানুষের স্মৃতি থেকে। তবু আশ্রয়। রুমালের মা-এর মতোই। (Mandrake)
কথা উঠবে একাদশীর কী হল? হ্যাঁ ওই ডুবে ডুবে জল খাওয়ার তরিকা আরবি দুনিয়া। ভূমধ্যসাগরের গাছ-মানড্রেক, কেমন করে আরবিতে আবুল-রুহ হয়ে গেল। সে রহস্য আরেক প্রস্থ। তাহলে? গালিভারের ভ্রমণ, কিহোতের বিভোর-বিহ্বল বীরত্ব আর ঘনাদার দুর্মর সব ‘অভিজ্ঞতা’ যেন ম্যানড্রেকের কুহকে মাফিয়ার উত্তেজনায় ঘাঁটি গাড়ে ম্যাগাজিনের আসরে। দুনিয়াজোড়া মাদক ব্যবসার নিষিদ্ধ বুহকে লেপটে থাকা লোকজন, মাফিয়াকুল বা একটু অন্যমাত্রায় ম্যাগাজিন সূত্রেও মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করা মাতব্বর ব্যক্তিকুল এসে মিলছেন, এক সমতলে। ম্যানড্রেক নিয়ে, মাফিয়া নিয়ে গল্পকথা অল্প নয় আদৌ। তার আক্রমণও মাফিয়ার মতো মারাত্মক, ম্যানড্রেকের মতো সম্মোহক আর তার বাহন এখনও অনবদ্য ম্যাগজিন, তা কাগজের হোক বা ই-চিহ্নিত পর্দাক্ষরে। (Mandrake)
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
সুমন ভট্টাচার্য
জন্ম, ১৯৬৯ সালে। পেশায় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। মূলত কবি। জাতিবর্ণ-আন্দোলন ও বাংলা সাময়িকী বিষয়ে গবেষণা-উপাধি। এছাড়া গবেষণা করেছেন এবং করছেন দেশভাগ ও তার জাতিবর্ণ প্রেক্ষিত বিষয়ে।
কার্টুন, সচিত্রণ, গ্রন্থচিত্রণ প্রভৃতি বিষয়েও বহু প্রবন্ধ আছে।
প্রকাশিত বই:
লে লে বাবু ছ'আনা (কবিতা),
দশকুমারচরিত, গাথাসপ্তসতী (উপন্যাস),
বই-শাখ হে (রম্যরচনা)