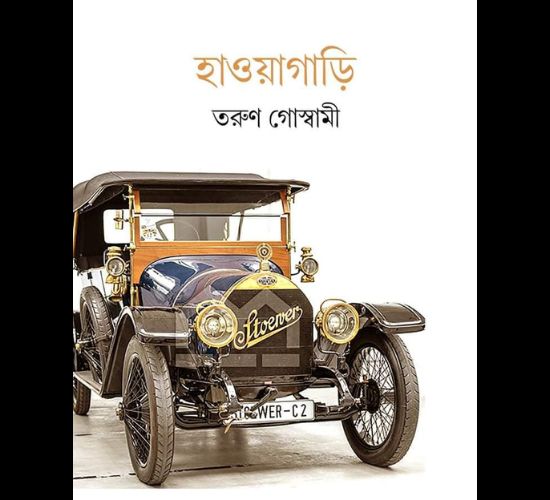হাওয়াগাড়ি
লেখক: তরুণ গোস্বামী
প্রকাশক: তবুও প্রয়াস
মূল্য: ৫০০ টাকা
কখনও শুনেছেন কোনও গাড়িকে সমাধিস্থ করা হয়েছে? শহর কলকাতায় এমনটাই ঘটিয়েছিলেন মানিকলাল দে নামে এক জমিদার। সময়টা তিনের দশকের শেষাশেষি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। একদিন বাংলার ছোটলাট মানিকলালবাবুকে বললেন, ব্রিটিশ সেনার ব্যবহারের জন্য তাঁর অ্যাডলার গাড়িটি সরকারের চাই। কিন্তু জমিদারবাবুর সাফ কথা, তিনি জীবিত থাকতে বাইরের কাউকে ওই গাড়ি কিছুতেই চড়তে দেবেন না। তাঁর নির্দেশে সেই গাড়িকে কবর দেওয়া হল বরানগরের বাগানবাড়িতে। আবার তাঁরই কথামতো, মাটির উপরে পোঁতা হল একটি চাঁপাগাছ যাতে জায়গাটি পরে চেনা যায়। প্রায় তিন দশক পর, ১৯৬৫ সালে মানিকলালবাবুর নাতি গদাইচন্দ্র হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর, তাঁর বাবা হরিমোহন, পুরস্কার হিসাবে সেই গাড়ির চাবি দিয়ে বললেন বাগানবাড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করতে। মাটি খুঁড়ে, ক্রেন দিয়ে সেই ধূলিমলিন জার্মান গাড়ি তোলা দেখতে তখন উৎসাহী জনতার ভিড়। এক বছরের চেষ্টায় সে গাড়ির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। ইঞ্জিন পরিষ্কারের পর ঢালা হল পেট্রল। এল নতুন টায়ার আর হুড। এর পর গদাইচন্দ্র স্টিয়ারিংয়ে বসতেই গর্জন করে উঠল অ্যাডলার। এ যেন সত্যিই ‘পাষাণের ভাঙালে ঘুম।’

এমন বহু হিরে-জহরত লুকিয়ে আছে বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণ গোস্বামীর ‘হাওয়াগাড়ি’ বইটিতে। এর বেশিরভাগ লেখা ইনস্ক্রিপ্ট ডট এম ই নামে এক ডিজিটাল পোর্টালে গত বছর প্রকাশিত হয়। লেখকের বৈঠকী মেজাজ গাড়ির কথা ও কাহিনিকে আরও মনোগ্রাহী করে তুলেছে। এ যেন টাইম মেশিনে চড়ে এক আশ্চর্য ভ্রমণ প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতে এবং অবশ্যই কলকাতায়। তার পাশাপাশি অনুভব করা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, গাড়ি প্রস্তুতকারক চারটি প্রধান দেশ – আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি এবং ইতালির মধ্যে তুমুল রেষারেষি। আমেরিকার বুইক, শেভ্রোলে, ক্রাইসলার, ক্যাডিল্যাক, জিপ, ফোর্ডের সঙ্গে তখন পাঞ্জা লড়ছে ব্রিটেনের রোলস-রয়েস, ল্যান্ড রোভার, মরিস, উলসলি, অস্টিন। অন্য দিকে, জার্মানির মার্সিডিজ, ফোক্সওয়াগেনের মুখোমুখি হয়ে তাল ঠুকছে ইতালির ফিয়াট। এর মধ্যে কয়েকটি গাড়ি আজও কলকাতায় একইসঙ্গে বিরাজমান ও চলমান। কেউ শতবর্ষ পার করেছে আবার কেউ তার দোরগোড়ায় । ফলে সবাই ভিন্টেজ কারের তকমাধারী। বইয়ের মুখবন্ধে তরুণ আক্ষেপ করেছেন, পুরনো বাড়ি হেরিটেজ তকমা পেলে, পুরনো গাড়িও কেন সেই মর্যাদা পাবে না? কয়েকটি রাজ্যে এই প্রক্রিয়া আরম্ভ হলেও, পশ্চিমবঙ্গে এখনও হয়নি। তরুণের আশা, এই সব গাড়ির ঠিকুজি-কুলুজি একদিন আমাদের সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি চমৎকার বলেছেন, ‘পুরোনো গাড়ির মালিকেরা অযান্ত্রিকের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন পান।’ তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই সব গাড়ি পরিবারের সদস্য হয়ে গিয়েছে। সামাজিক মর্যাদা আর বৈভবের সঙ্গে মিশেছে আবেগ।
লেখক যথার্থই বলেছেন, ন’য়ের দশক থেকে পুরনো বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরি করার প্রবণতা বাড়ে। এর ফলে বহু পুরনো গাড়ির মালিক তাঁদের সাবেক বাড়ি ভেঙে তৈরি ফ্ল্যাটে থাকা শুরু করেন। স্বাভাবিক ভাবেই, গ্যারেজে বড় গাড়ির থাকা আর হল না। তারা চলে গেল ভিন্ রাজ্যে আর অন্যান্য মেট্রো শহরে। কিন্তু যারা রয়ে গেল, তারাই বা কম কিসে? বিশ্বের একমাত্র স্টোয়ার গাড়ি রয়েছে এই শহরেই– এখন বয়স ১০৯। অন্য দিকে, ১০৮ বছর পার করা যে ১৩টি উলসলি গাড়ি এখনও রয়ে গিয়েছে, তার একটির বাস কলকাতায়। আবার এই গ্রহের একমাত্র স্টুডিবেকার প্রেসিডেন্ট এইট মডেলটি একশো ছুঁই-ছুঁই বয়সেও এই শহরে চলেফিরে বেড়ায়। বিশ্বে যে ছ’টি মাত্র অস্টিন টেন টুরার আছে, তার একটির ঠিকানা কলকাতায়, অমিতাভ সাহার বাড়ি। এর পাশাপাশি, এশিয়ার একমাত্র মার্সিডিজ স্পোর্টস কার ১৩০ এইচটি রয়েছে সুব্রত সেনের জিম্মায়। ভারতের একমাত্র হিলম্যান সুপার ইম্প-এর মালিক কলকাতার প্রসূন হাজরা।

বলে রাখা ভাল, জাপান-কোরিয়ায় গাড়ির জগতে আলোড়ন ওঠে সাতের দশকের গোড়ায় যখন হন্ডা, সুজুকি, হুন্ডাই, কিয়া, ডেয়ু, কিয়া তাদের প্রথম মডেল বার করে। তার আগে পর্যন্ত সবেধন নীলমণি ছিল টয়োটা, যাদের প্রথম গাড়ি এএ মার্ক ওয়ান আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৫-এ। ফলে, কলকাতার পুরনো এবং চালু গাড়ির হল অফ ফেম-এ ইউরোপ আর আমেরিকারই রমরমা।
বইয়ে যে ২৭টি ভিন্টেজ কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে দুটির বিরাট ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। প্রথমেই আসবে জার্মান গাড়ি ওয়ান্ডারার। এতে চেপেই ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারির রাতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মহানিষ্ক্রমণ করেন। প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দূরের গোমো স্টেশনে নেতাজিকে পৌঁছে দেন তাঁর ভাইপো শিশির বসু। এই কাজের মহড়া হিসাবে শিশির বসুকে এক বার বর্ধমান পর্যন্ত ট্রায়াল রান দিতে হয়। টায়ার বদলানোর পদ্ধতি রপ্ত করতে আগে থেকে কিছুটা অনুশীলনও করতে হয়। আজ এই গাড়ি এলগিন রোডের নেতাজি ভবনের অন্যতম আকর্ষণ।

ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ যে রোলস-রয়েসে চড়ে শপথ নিতে যান সেটির বর্তমান মালিক কলকাতা নিবাসী বসন্ত কারনানি। গাড়ির বয়স ৮৫ হলেও, তার যৌবন অটুট। এক সময় যে সব বিশিষ্ট বাঙালি রোলস-রয়েস চড়তেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, স্যার রাজেন মুখার্জি এবং সন্তোষের মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী। আর রোলস-রয়েসই যে সেরার সেরা, তা নিয়ে গাড়ি প্রেমিকদের মধ্যেও কোনও দ্বিমত নেই।
এমন সব দুষ্প্রাপ্য গাড়ি স্মৃতির অতলে বিলীন হয়ে যেত, যদি তাদের মালিকের রোখ ও রেস্ত-র পাশাপাশি, এক ঝাঁক দক্ষ মোটর মেকানিক শহরে না থাকতেন। তরুণের কথায়, ‘কলকাতার গাড়ি সারাইয়ের মিস্ত্রিরা শাপভ্রষ্ট দেবতা।’ তাঁরা ‘বিশ্বকর্মার বরপুত্র’ও বটে। এমনই কয়েকটি নাম গুনোবাবু, নদিয়াবাবু এবং ধনঞ্জয় দাস। এর সঙ্গে অবশ্যই বলতে হবে অসাধারণ কয়েকজন কার রেস্টোরারের কথা, যাঁরা একেবারে ঝুরঝুরে হয়ে যাওয়া গাড়িকে পুনর্জন্ম দিয়ে জোশ মেশিন করে তুলেছেন। এমন কয়েকটি নাম প্রতাপ চৌধুরী, সঞ্জয় ঘোষ, শশী কুমার কানোরিয়া। তরুণ সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁদের স্মরণ করেছেন। তাঁদের সৌজন্যেই আজ কলকাতার ভিন্টেজ কার র্যালিতে দেখা যায় উলসলি, স্টোয়ার, ফক্সওয়াগেন বিটল, ট্রায়াম্ফ, হিলম্যান সুপার ইম্প-এর মতো বিখ্যাত গাড়িগুলি।

‘হাওয়াগাড়ি’র অন্যতম আকর্ষণ, গাড়িগুলি খুঁজে পাওয়ার গল্প। যেমন সঙ্গীতরসিক অমৃতেন্দু রায় যে ফোর্ড অ্যাংলিয়াটি চালান, এক সময় তার মালিক ছিলেন বিখ্যাত ফুটবলার সুভাষ ভৌমিক। মেরিন ড্রাইভে বলিউড হিরো জ্যাকি শ্রফ যে টু-সিটার ট্রায়াম্ফ চালাতেন, তার বর্তমান মালিক কলকাতার সৈকত দত্ত। আইনজীবী রূপক ঘোষ রাজস্থানের চুরুর একটি হাভেলি থেকে ১৯৪৮ সালের একটি এমজিটিসি উদ্ধার করে, কলকাতার পথে নামিয়ে প্রমাণ করেন এই গাড়ি জগদ্দলও নয়, এঁড়ে গরুও নয়। আটের দশকে ডিব্রুগড়ের এক আশ্রম থেকে উলসলির খোঁজ পান শশী কুমার কানোরিয়া। বহু সাধ্য-সাধনার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত একটি ফোর্ড জিপ পুরুলিয়ার এক গির্জা থেকে সংগ্রহ করেন কলকাতার রবি খেদওয়াল। ২০০৮ সালে এক বিয়েবাড়ি গিয়ে অমিতাভ সাহা আবিষ্কার করেন ১৯৩৯ সালের অস্টিন টেন টু্র্যার গাড়ি। এই প্রসঙ্গে ব্রিটেন, আমেরিকার বিভিন্ন কার মিউজিয়ামের ভূমিকা এবং সংশ্লিষ্ট গাড়ি কোম্পানিগুলির স্পেয়ার পার্টস দিয়ে অসাধ্য সাধন করাও ভোলার নয়।
বাংলা সিনেমায় ‘অযান্ত্রিক’এ বিমলের জগদ্দল ফোর্ড এবং ‘অভিযান’এ নরসিংয়ের ক্রাইসলার বহুদিন আগেই অমরত্ব লাভ করেছে। পিছিয়ে নেই ‘দেয়া নেয়া’র ডজ আর ‘ছদ্মবেশী’র অ্যাম্বাসাডরও। এর পাশাপাশি তরুণ আলোকপাত করেছেন বাংলার সংস্কৃতি জগতের তারকাদের গাড়িবিলাসের উপরও। প্রথমেই বলতে হয় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ‘নীলু’ প্লাইমাউথের কথা। ১৯৫০ সালে কেনা গাড়ি হাতবদল হয়ে আজও কলকাতার রাস্তায় সচল। বর্তমান মালিক স্বপন লাহিড়ি। উত্তমকুমারের প্রিয় গাড়ি ছিল র্যাম্বলার। পাহাড়ী সান্যালের দুটি মার্কিন গাড়ি ছিল– ফোর্ড অ্যাংলিয়া আর ভক্সহল। তা সত্ত্বেও তিনি রোল্যান্ড রোডের মোবিলিটি গ্যারেজ থেকে মার্সিডিজ ১৩০ এইচ (বেবি মার্ক) নিয়ে শুটিং করতে যেতেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর বসন্ত চৌধুরীর পছন্দ ছিল অ্যাম্বাসাডর। শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় চড়তেন ফিয়াট ১১০০।

শেষে কয়েকটি খটকার কথা না বললেই নয়। লেখকের কথায় তরুণ জানিয়েছেন ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ বেবি অস্টিন চালাতে চালাতেই দিবানিদ্রা দিতেন। সঙ্গে কোনও না কোনও ছাত্র থাকায় গাড়িটি দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেত। অথচ ৬৭ পৃষ্ঠায় মরিস মাইনর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তরুণ একই ঘটনার অবতারণা করেছেন। এখন প্রশ্ন, ব্যায়ামাচার্য কোন গাড়ি চালাতেন, বেবি অস্টিন না মরিস মাইনর? নব্বই পৃষ্ঠায় তরুণ লিখেছেন মার্সিডিজ ডবলু ১১৫-এর বর্তমান মালিক সৌরজিৎ পালচৌধুরীর আদি বাড়ি নদিয়ার মহেনগঞ্জে। এটি আসলে হবে মহেশগঞ্জ। সেখানে একটি চমৎকার ভ্রমণস্থল গড়ে তুলেছেন এই পরিবার। এই সামান্য হোঁচটটুকু বাদ দিলে বইটি আগাগোড়াই সুখপাঠ্য। চমৎকার ছাপা এবং ২৭টি গাড়ির রঙিন ছবি বইটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলেছে।
তবুও প্রয়াস প্রকাশিত একশো কুড়ি পাতার এই হার্ডবাউন্ড বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন সন্তু দাস। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডে শতবর্ষ-প্রাচীন স্টোয়ার গাড়িটি ফুটেও উঠেছে চমৎকার। তবে বইয়ে আলোচিত গাড়ির সঙ্গে এর নম্বর, রঙ, কোনওটাই মিলছে না। এই বিষয়ে শিল্পীর আরও সজাগ হওয়া উচিত ছিল। অক্ষরবিন্যাসের জন্য আক্ষরিককে ধন্যবাদ। অক্ষরগুলির ফন্ট এবং লাইন স্পেসিং যথাযথ। ফলে প্রবীণ পাঠকদেরও পড়তে কোনও অসুবিধা হবে না। বইয়ের বাঁধাইও ঠিকঠাক, ইংরেজি কফিটেবিল বইগুলির সঙ্গে স্বচ্ছন্দে তুলনীয়। ধন্যবাদ প্রাপ্য ইনস্ক্রিপ্ট ডট এম ই-র সম্পাদক অর্ক দেবেরও। তাঁর উৎসাহেই, গাড়ি নিয়ে তরুণের সাপ্তাহিক লেখাগুলি পোর্টালের কানাগলি থেকে বেরিয়ে জায়গা করে নিয়েছে দুই মলাটের ভিতরে।
*ছবি সৌজন্য: তবুও প্রয়াস
দু’দশক ইংরেজি সংবাদপত্রের কর্তার টেবিলে কাটিয়ে কলমচির শখ হল বাংলায় লেখালেখি করার। তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কয়েকজন ডাকসাইটে সাংবাদিক। লেখার বাইরে সময় কাটে বই পড়ে, গান শুনে, সিনেমা দেখে। রবীন্দ্রসঙ্গীতটাও নেহাত মন্দ গান না।