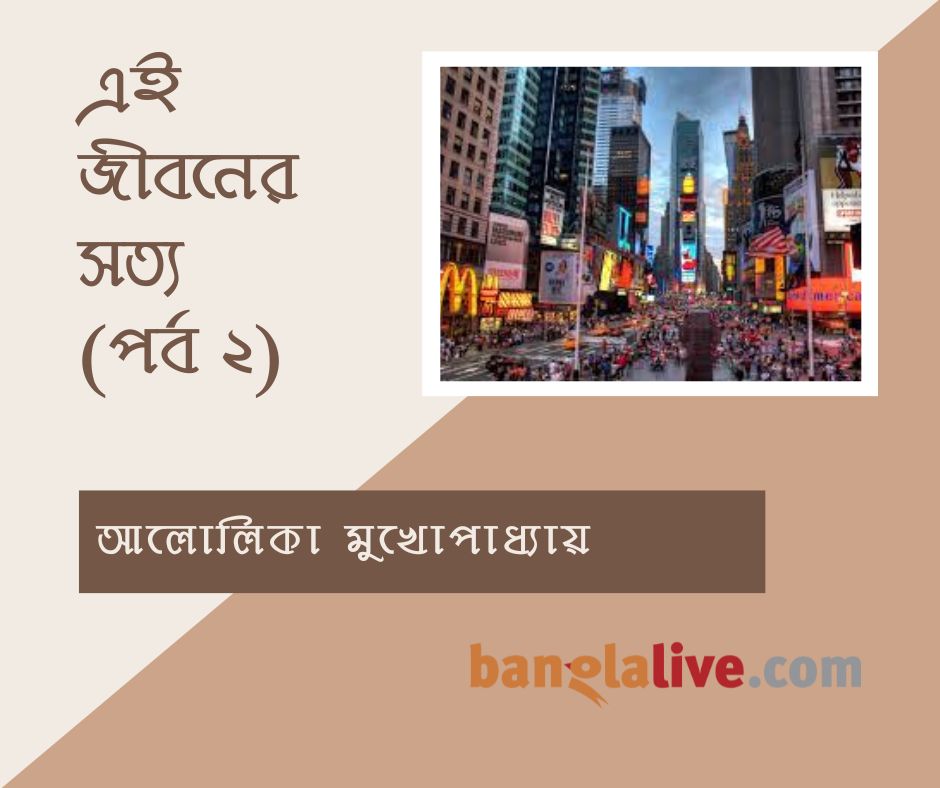ক্রিসমাসের আগে হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়ে গেল। দুদিন ধরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি। ভেজা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া। শমীক প্রায় চোদ্দটা ব্লক হেঁটে অফিস যায়। হাঁটতে ভালোই লাগে ওর। আজ এমনিতেই বেরোতে দেরি হয়ে গেছে। রাস্তায় নেমে খেয়াল হল ছাতা আনেনি। বৃষ্টির সঙ্গে ঝিরিঝিরি বরফ শুরু হয়েছে। দুটো ব্লক হেঁটে শমীক সাবওয়ে নিল। অফিসের কাছে স্টেশনে ওঠার মুখে সিঁড়িতে ক্যারেনের সঙ্গে দেখা। সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ক্যারেন বলল, ‘আজ তাহলে হাঁটা হল না?’
‘ওয়েদারটা আইডিয়াল বলছ? একে দেরি হয়ে গেছে, তার ওপর ছাতা ফেলে এসেছি।’
দুজনে কথা বলতে বলতে অফিসে পৌঁছে গেল। ক্যারেন বলছিল, ‘এ-বছর তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা পড়ে যাচ্ছে। ক্রিসমাসের আগেই স্নো শুরু হল।’
শমীক এলিভেটরের বোতাম টিপে বলল, ‘পড়ুক। আমাকে তো আর রোজ রোজ কমিউট করতে হচ্ছে না। দ্যাট ওয়াজ রিয়্যাল পেইন।’
এলিভেটরে দাঁড়িয়ে ক্যারেন হাসল, ‘শীতের মধ্যে হেঁটে হেঁটে কমিউট করাও সোজা নয়। কতগুলো ব্লক। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে সন্ধেবেলায় বুঝবে।’
ফিফথ্ ফ্লোরে পৌঁছে ওরা নিজেদের ডিপার্টমেন্টের দিকে যাচ্ছিল। ক্যারেন জিজ্ঞেস করল, ‘উইক এন্ডে ফ্রি আছ? শনিবার সন্ধেবেলা?’
‘এখনও পর্যন্ত কিছু নেই। কেন? কোথাও যাচ্ছ?’
ক্যারেন হলওয়ের ডানদিকে ঘুরল, ‘ভিলেজে যাব। ডেভিডের ছাত্ররা একটা নাটক করছে। লাঞ্চে কথা হবে।’
শনিবার ক্যারেন আর ওর বর ডেভিডের সঙ্গে শমীক গ্রিনিচ ভিলেজে গেল। ডেভিড নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির ড্রামা ডিপার্টমেন্টে পড়ায়। অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। ওর ছাত্রছাত্রীরা আজ একটা নতুন নাটক করছে।
ছোট অডিটোরিয়াম। নিচু স্টেজ। পর্দা খোলা আছে। অন্ধকারে সেট দেখা যাচ্ছে। শমীকরা সিটে বসার পর একটি ভারতীয় মেয়ে এসে বসল। ক্যারেন আলাপ করিয়ে দিল, ‘আমার বন্ধু অ্যানা। এ হচ্ছে শমীক। আমার কোলিগ।’
মেয়েটি শুধু বলল, ‘হাই।’ চেয়ার ছেড়ে উঠে তার কালো ওভারকোট খুলে দাঁড়াতেই শমীকের সঙ্গে চোখাচোখি হল। দীর্ঘ সুঠাম শরীর। জিন্স্-এর ওপর স্লেট রঙের হাই-নেক সোয়েটার। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। আই মেক-আপ আর কালচে লিপস্টিকে মুখখানা আকর্ষণীয় দেখাচ্ছে। শমীক চোখ সরিয়ে নেওয়ার মুহূর্তে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, ‘আপনার পাশে কেউ আসবে?’
‘জানি না তো। আপনি বসবেন? তাহলে একটা সিট সরে বসতে পারি।’
‘সে জন্যে নয়। আমাদের কোটগুলো রাখা যেত। কেউ এলে সরিয়ে নেব। খুব বেশি লোক হবে বলে মনে হচ্ছে না।’
শমীক গম্ভীরভাবে বলল, ‘আপনার কোটটা রেখে দিন। নয়তো সিটের পেছনে ঝুলিয়ে দিন। লোক আসছে মনে হচ্ছে।’
মেয়েটি সিটের পেছনে কোট ঝুলিয়ে রেখে শমীকের পাশেই বসল। ডেভিডের জায়গায়। ডেভিড দূরে কার সঙ্গে কথা বলছিল। ফিরে এসে ক্যারেনের ওপাশে বসল। ঝুঁকে পড়ে শমীককে বলল, ‘শমীক, অ্যানা ভালো কবিতা লেখে। ওর কবিতার থিম নিয়েই আজকের নাটক।’
শমীক এ-দেশে অ্যানা বলে কোনও ভারতীয় কবির নাম শোনেনি। ঝুম্পা লাহিড়ী, চিত্রা ব্যানার্জি, দিবা কারুনির বুক-সাইনিং-এ গেছে। এ-মেয়েটির পুরো নাম কী? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাঙালি হতেও পারে। ও আগ্রহ দেখাল, ‘ইনটারেসটিং! কবিতা নিয়ে নাটক? পোয়েট্রি ইন মোশন?’
ডেভিড নাটকীয় ভঙ্গীতে হাত ঘুরিয়ে দেখাল, ‘পোয়েট্রি ইন অ্যাকশন!’
অ্যানা এত গম্ভীর কেন কে জানে! শমীকের কথার উত্তরে শুধু বলল, ‘দেখি এরা কীভাবে করে।’
‘কেন, স্ক্রিপ্ট দেখে নেননি?’
‘ডেভিড দেখেছে।’
শমীক প্লে-বিল-এ নাটকের নাম দেখেছে—‘প্রমিসেস্, প্রমিসেস্’। আর একবার খুলে দেখার আগে হলের আলো নিভে গেল।
আবহ সঙ্গীত শুরু হয়েছে। অন্ধকারে দুটি মানুষ এসে দাঁড়াল। ক্রমশ আলোর বৃত্তে তাদের মুখ দেখা গেল। বিয়ের পোশাকে একজন নারী, একজন পুরুষ। স্বগতোক্তির মতো শপথ উচ্চারণ করছে— ‘আই ডু প্রমিস অ্যান্ড কোভেল্যান্ট বিফোর গড অ্যান্ড দিজ উইটনেসেস টু বি ইওর লাভিং হাজবেন্ড অর ওয়াইফ ইন সিক্নেস অ্যান্ড ইন হেলথ্, ইন প্লেনটি অ্যান্ড ইন ওয়ান্ট, ইন জয় অ্যান্ড সরো, অ্যাজ লং অ্যাজ উই বোথ শ্যাল লিভ…’
মাত্র দশ মিনিট বিরতি ছিল। নাটকটা নিয়ে প্রথম শমীক কথা তুলল, ‘আপনার কবিতার থিম আর নাটকটা কাছাকাছি গেছে?’
অ্যানা বলল, ‘থিম ঠিকই রেখেছে। নাটকের জন্যে কয়েকটা বাড়তি চরিত্র আর ঘটনা এনেছে।’
‘প্লে-বিল-এ দেখছিলাম ঘটনা মেক্সিকোয় নিয়ে গেছে। আপনার কবিতায় নেই বোধহয়?’
‘মেক্সিকোর বদলে ইন্ডিয়াতেও নিয়ে যেতে পারত। আমার কবিতায় তাই আছে।’
ডেভিড ওপাশ থেকে বলল, ‘ম্যারেজ ভাও-এর সিন-টিন-এর জন্যে ক্রিশ্চান ব্যাকগ্রাউন্ড এনেছে। এথ্নিসিটি বোঝাতে মেক্সিক্যান-আমেরিকান।’
শমীক হাসল, ‘তোমাদের কি ধারণা আমাদের হিন্দু ওয়েডিং-এ ম্যারেজ ভাও নেই?’
ডেভিড বলল, ‘থাকবেই তো! কিন্তু এরা থিমটা অ্যাড্যাপ্ট করেছে। সেভাবেই স্ক্রিপ্ট লিখেছে।’

ক্যারেন আজ একদম চুপচাপ। নাটক দেখে বেশ অভিভূত মনে হচ্ছে। ডেভিড হলের বাইরে গেল। অ্যানা নিজে থেকে কথা বলছে না। কোলের ওপর দু-হাত রেখে কিছু ভাবছে। শমীক প্লে-বিল খুলে দেখেছে আর চারটে সিন বাকি। তখনই কবিতার বই আর কবির নাম দেখে নিয়েছে। ‘স্টেয়ার্স অফ থর্ন্স্’ বাই অনন্যা দাশগুপ্ত।
অ্যানা হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি বাঙালি?’
শমীক হাসল, ‘আপনার পদবিও তাই বলছে!’
‘কেন, চেহারা দেখে মনে হয় না?’
‘আন্দাজ করা যায়!’
ক্যারেন একেবারেই কথা বলছে না। শমীকের আজ ওকে অ্যানার মতোই গম্ভীর মনে হয়েছে। মেয়েরা নাটক দেখে একটু বেশি অভিভূত হয়! হলের আলো নিভে আসছে। ডেভিড সিট-এ ফিরে এল। বিরতি শেষ হবার মুহূর্তে শমীক জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি বাংলা জানেন?’
‘জানি। বলার সুযোগ হয় না।’
নাটকের দ্বিতীয় পর্বে দৃশ্যপট বদলে গেছে। কাহিনি শুরু হয়েছিল শিকাগোয়। এবার মেক্সিকোর একটি ছোটো শহরে হাসপাতালের দৃশ্য। নাটকের শুরুতে যে মেয়েটির বিয়ের দৃশ্য ছিল, তার এখন মধ্য বয়স। পারকিন্সনস্ সিনড্রোমে অসুস্থ। বিছানায় বসে আছেন। বুকের কাছে ধরা একটি ছবি। হাত কাঁপছে। মাথা কাঁপছে। অবসন্ন শরীর।
তাঁর বৃদ্ধা মা ঘরে ঢুকলেন। হাতে খাবারের বাক্স। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রেখে বললেন, ‘দেরি হয়ে গেল। সময়মতো বাস আসে না।’
অসুস্থ মহিলার ক্ষীণ স্বর শোনা গেল, ‘রোজ রোজ কেন এত কষ্ট করে আসো?’
মা বললেন, ‘এই কষ্ট করেও তোকে যদি ভালো করতে পারতাম! বাড়ি নিয়ে যেতে পারতাম!’ বৃদ্ধা তাঁর মেয়ের গালে, কপালে চুম্বন করলেন। টেবিলে থালার ওপর খাবার সাজাতে গিয়ে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। মেয়ের কোলের কাছে ছবিটা পড়েছিল। মা খাবার খাওয়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন। এক হাতে তুলে নিয়ে বললেন, ‘মেয়েকে দেখতে ইচ্ছে করছে? ফোন এলে বলব। একবার চলে আসতে বলব।’
মহিলার দু-চোখে জলের ধারা। কথা বলতে চেষ্টা করছিলেন। অস্ফুট গোঙানির শব্দ উঠে এল। অসহায় রোগজীর্ণ দেহে প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসছে। মা তাঁর শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন।
অন্ধকারে দৃশ্যান্তর হয়ে যাচ্ছে। শমীক ভাবছিল এরকম প্লট কি অ্যানার কবিতায় ছিল? গল্প-উপন্যাস তো নয়। যদিও গল্প বলার জন্যেও একদিন শুধু কবিতাই ছিল।
শেষ দৃশ্যে আবার আমেরিকা। শিকাগো নয়। সমুদ্রের ধারে অচেনা শহর। একটি ঘরের জানলা দিয়ে ভোরের আলো এসে পড়েছে। বিছানায় তন্দ্রাচ্ছন্ন যুবক-যুবতী। দুটি শিশু রাতের পোশাক পরে ছুটে এল। হাতে মার জন্যে আঁকা ছবি, চকলেট, মাটির ফুলদানিতে লুকিয়ে রাখা ফুলগাছ। তারা খাটে উঠে মায়ের বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে ডাকছে, ‘হ্যাপি মাদার্স ডে! আই লাভ ইউ মমি! ওয়েক আপ! ওয়েক আপ…’
যুবতী ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। বিছানা জুড়ে শোরগোল। মায়ের বুকের কাছে দুটি শিশু। ছোট ছোট হাতে মায়ের জন্য উপহার। ছবি, ফুল, চকলেট! যুবতীর সদ্য ঘুমভাঙা উজ্জ্বল প্রসন্ন মুখে হঠাৎই বিষণ্ণতার ছায়া। যুবক লক্ষ করে। হাতে হাত রাখে।
নাটক শেষ হয়ে আসছে। মঞ্চে একটিমাত্র চরিত্র। তার মুখে কয়েকটি সংলাপ। গভীর রাতে সেই যুবতী তার মায়ের ছবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মেক্সিকোর হাসপাতালে তার মা কবেই মারা গেছেন। তবু এই বিশেষ রাতে মায়ের কাছে ক্ষমাভিক্ষা করে। অশ্রুভারে অবরুদ্ধ, অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর—
‘মা, আজ তোমার জীবনের বিনিময়ে বেঁচে আছি। শৈশব, কৈশোর সবই যেন সমুদ্র তীরে বালির ওপর আঁকা ছবি। কখনো ঢেউ এসে, কখনো ঝড় এসে মুছে দিয়ে গেছে।
‘তবু স্বপ্নে দেখি জ্যোৎস্নার রুপালি নীল ছায়া। সেই ছায়ায়-ছায়ায় তোমার হাত ধরে পথ চলা। বুকের ভেতরে বড়ো সঙ্গোপনে সেইসব রাত আসে, যায়।
‘মাগো, তোমার জন্যে বেঁচে আছি
শুধু তোমার জীবনের বিনিময়ে
আ অ্যাম হিয়ার বিকজ অফ ইউ
আই সারভাইভ্ড বিকজ অফ ইউ
স্টিল, দিস ইজ নো ওয়ে টু লিভ
নো ওয়ে টু সারভাইভ…’
শমীকের মনে হল এই কথাগুলো কোথায় যেন পড়েছে। বিশেষ করে শেষের কয়েকটা লাইন। চেনা-চেনা লাগছে। কোথায় পড়েছে?
নাটক শেষ হবার পর শমীক অ্যানাকে কিছু বলার আগেই ডেভিড ওকে স্টেজে নিয়ে গেল। দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। অ্যানার হাতে ফুলের তোড়া। সকলের অভিনন্দনের উত্তরে সে সৌজন্যের হাসি হাসল। কয়েকবার বলল, ‘ধন্যবাদ! ধন্যবাদ!’
হল থেকে বেরিয়ে ডেভিড জিজ্ঞেস করল, ‘এখন কোথায় খেতে যাচ্ছি আমরা?’
ক্যারেন বলল, ‘পেনাং-এ রিজার্ভেশন করেছি। শমীক, তুমি মালয়েশিয়ান ফুড পছন্দ করো?’
‘গেলেই হয়। এনি এশিয়ান ফুড ইজ ওকে উইথ মি।’
অ্যানাও রাজি হয়ে গেল। শমীকের পাশাপাশি অ্যানা চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল। কালো লং কোটের ওপর দিয়ে গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে নিয়েছে। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের চেনে হাত রেখে জুতোর খুটখাট শব্দ তুলে হাঁটছে। খোলা চুল শীতের হাওয়ায় এলোমেলো। এই মেয়েটির সঙ্গ শমীকের ভালো লাগছিল। নাটক নিয়ে দু-চার কথার পর শমীক বলল, ‘আপনার কবিতা পড়িনি। কাদের পাবলিকেশন?’
কানের ওপর থেকে চুল সরিয়ে নিয়ে অ্যানা উত্তর দিল, ‘ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে পাবলিশ করেছে।’
‘একটা কপি পেলে নাটকের জন্যে রিভিউ লিখতে পারি।’
অ্যানা ক্ষুণ্ণ হল, ‘নাটকের রিভিউ লেখার জন্যে কবিতা পড়বেন! জাস্ট নিজের প্রফেশনের জন্যে?’
শমীক হেসে ফেলল, ‘না, না, ঠিক তা নয়। কবিতার জন্যেই চাইছি। আসলে আমার প্রফেশনটা এমন, দু-কলম লেখার ব্যাপারটা এসে যায়।’
অ্যানা বলল, ‘ঠিকানা পেলে বই পাঠিয়ে দেব।’

পেনাং-এ ডিনার শেষ হওয়ার আগে শমীক ওর বিজনেস কার্ড দিল। রেস্তরাঁটা ডাউন টাউনে। সোহো অঞ্চলে। অ্যানা ওদিকেই থাকে। ক্যারেনরা যাবে অন্যদিকে। শমীক বাড়ি ফেরার জন্যে ট্যাক্সি নিয়ে পথে অ্যানাকে নামিয়ে দিয়ে গেল। মনে-মনে ওই চারটে লাইনের রহস্য উদ্ধার করে ফেলেছে। ক্যারেনের কবি-বন্ধুর সঙ্গে শমীকের বোধহয় আবার দেখা হবে।
ক্রিসমাসের দিন অফিস ছুটি। আগের দিন পার্টি ছিল। শমীক অনেক রাতে ফিরেছে। সকালে ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙল। বহুদিন পরে সুদেষ্ণার গলা, ‘কী খবর? ভালো আছ? নিজে থেকেই কল করলাম।’
‘কেন? মেসেজ পাওনি? নীল একদিন আসবে বলেছিল, কী হল?’
সুদেষ্ণা সে কথার উত্তর দিল না। জিজ্ঞেস করল, ‘ক্রিসমাসের ছুটির মধ্যে একদিন আসতে পারবে?’
‘আমার শুধু আজকেই ছুটি আছে। কেন বলো তো? কিছু হেলপ্ দরকার?’
‘বাড়িটা সেল্-এ দিয়েছিলাম। বিক্রি হয়ে গেছে। তোমার জিনিসপত্র এখনও পড়ে আছে। এসে নিয়ে যাও।’
শমীক অবাক হল, ‘বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছ! নীল কলেজে যাওয়ার আগেই? কোথায় মুভ করছ?’
‘কাছেই। টাউন হাউসে চলে যাচ্ছি। এত বড় বাড়ি, বাগান আর মেনটেন করতে পারছি না।’
শমীক বুঝতে পারছিল সুদেষ্ণা তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে। ক্রিসমাসের সময় পুরনো বছরগুলোর কথা মনে পড়ছে। শমীক বলল, ‘আজ একবার যাওয়ার চেষ্টা করতে পারি। তবে ক্রিসমাসের দিন বাস-টাস কখন কী পাব, জানি না। তোমাদের ওখানে স্নো পড়ছে না?’
‘সেরকম নয়। সন্ধেবেলায় আসবে? এখানে ডিনার কোরও।’
‘না, অতক্ষণ থাকা যাবে না। সন্ধেবেলা অন্য প্রোগ্রাম আছে।’
সুদেষ্ণা চুপ করে থাকল। শমীক ভাবছিল আজ যাওয়াই মুশকিল। কতক্ষণে বাস পাবে। কতক্ষণে ফিরতে পারবে। তা-ও জিজ্ঞেস করল, ‘কী করব? আজ সকালে যাব? না পরে একদিন গিয়ে তোমাকে হেল্প করে আসব?’
‘ছেড়ে দাও। যদি পারি তোমার জিনিসপত্র ডরোথির গ্যারাজে রেখে যাব। পুরনো সুটকেসভর্তি হাবিজাবি জিনিস। ফেলে দিলেই হয়। দোতলা থেকে টেনে নামাব কী করে জানি না…’
শমীকের খারাপ লাগছিল। অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ‘কাজটা আমারই করে আসা উচিত ছিল। তাড়াহুড়োয় খেয়াল করিনি সুদেষ্ণা।‘’
সুদেষ্ণা বলল, ‘তা নয়। আসলে মায়া। মনে হয় একদিন কাজে লাগবে। শেষপর্যন্ত সেই ফেলে দিতেই হয়। তোমার তো শুধু একটা সুটকেস। আমি কত কী ফেলে যাচ্ছি ভাবো?’
‘মুভিং-এর সময় দরকার হলে ডেকো। চলে আসব।’
ফোন রাখার আগে সুদেষ্ণা জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার গার্লফ্রেন্ড কি আমেরিকান?’
শমীক অবাক, ‘এ-খবরটা কে দিল?’
‘কেউ নয়। আমি জিজ্ঞেস করছি।’
অন্য লাইনে শমীকের একটা ফোন এল। সুদেষ্ণা অপেক্ষা না করে ফোন রেখে দিল।
শমীক বুঝতে পারছিল সুদেষ্ণা তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছে। ক্রিসমাসের সময় পুরনো বছরগুলোর কথা মনে পড়ছে। শমীক বলল, ‘আজ একবার যাওয়ার চেষ্টা করতে পারি। তবে ক্রিসমাসের দিন বাস-টাস পাব কখন কী পাব, জানি না। তোমাদের ওখানে স্নো পড়ছে না?’
সন্ধের সময় সাব-ওয়ে নিয়ে শমীক ডাউন টাউনে গেল। নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি অ্যানার অ্যাপার্টমেন্ট। ক্রিসমাসে কলেজ বন্ধ। ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি গেছে। অন্যদিনের মতো এ-পাড়ায় রাস্তাঘাটে তেমন ভিড় নেই। ক্রিসমাসের রাতে সাবার্ব-এর রেস্তরাঁগুলো বেশিরভাগ বন্ধ থাকে। এদিকে ‘সোহো’-র কাছাকাছি কয়েকটা খোলা আছে। আজ অ্যানার বাড়িতে পার্টি না থাকলে শমীক ওকে নিয়ে এখানে ডিনারে আসতে পারত।
টোয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটে অ্যানার অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে শমীক দেখল অনেকেই এসে গেছে। অ্যানা কিচেনে ছিল। শমীককে দেখে লিভিং রুমে এল। আলগাভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, ‘মেরি ক্রিসমাস।’ ডোর বেল বাজল। অ্যানা শমীকের হাত ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে গেল। তারপর থেকে সারাক্ষণ ব্যস্ত।
রাতে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে শমীক অ্যানার দেওয়া ক্রিসমাসের গিফ্টের মোড়ক খুলল। একটা কোলনের বাক্স। ‘র্যালফ্ লরেন’-এর সাফারি। অন্য মোড়কে বই। ‘স্টেয়ার্স অফ থর্নস্’। কেন মেল করেনি বোঝা গেল। ভেতরে লিখেছে—‘টু আ ফ্রেন্ড অ্যান্ড ক্রিটিক’। নীচে ছোটোদের বাংলা হাতের লেখার মতো নাম সই করা—অনন্যা দাশগুপ্ত। শমীক কবিতাটি খুঁজে পেল।
এপ্রিলের শেষে বসন্ত এল। অ্যানা ঘরের জানলা খুলে দিয়েছে। ছোট্ট বারান্দায় সারি সারি টব। পাম, রাবার প্ল্যান্ট, আফ্রিকান ভায়োলেট, পিটুনিয়া, জিরেনিয়াম। রোজ ফুল ফুটছে। সারা শীত ঘরবন্দি থেকে এতদিন পরে আবার আকাশ, রোদ, বৃষ্টি, বসন্তের হাওয়া। শমীক এ-শহরে নতুন ঘাসের গন্ধ পায় না। পেভমেন্টের বুকে একা দাঁড়িয়ে থাকা গাছ। কবে তাদের পাতা ঝরল, কবেই বা নতুন পাতা এল, তেমন করে চোখে পড়ে না। শুধু যখন অ্যানার কাছে আসে, এই ছোট্ট বারান্দার সারি-সারি গাছ হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে বসন্তের খবর দেয়।

এই পরিপার্শ্ব কেমন এক প্রভাব সৃষ্টি করে। শমীক অ্যানার কাছে জীবনের গল্প শোনে। গল্প বলে। পরস্পরের কাছে স্বীকারোক্তির মতো এক দায়বদ্ধতা যেন। অ্যানা বলে নিজের মা’র কথা, ‘শমীক জানো, মার সবচেয়ে চিন্তা ছিল বইগুলো নিয়ে। স্টাডিভর্তি দেওয়ালের তাকে বাংলা বই। কবিতার সারিতে কবিতা সাজাতে সাজাতে মা বলতেন— এত সব বই কী হবে? আমাদের পরে কেউ তো পড়বে না। বাবার উত্তর ছিল— এত পুরনো বইপত্র জমিয়ে রাখো কেন? লোকজনদের দিয়ে দাও। আমি চুপ। কোনওরকমে বাংলা লিখতে-পড়তে পারি। তা বলে মোটা মোটা বই পড়ার ক্ষমতা নেই।
‘শুধু বই নয়, বাড়ির অনেক জিনিস নিয়েই মার চিন্তা শুরু হল। অথচ তখন মার অসুখের কথা জানিও না। মা যে ভেতরে-ভেতরে এতরকম অসুখ বাধিয়েছেন, বুঝতেই পারিনি। মাঝে মাঝে হাত কাঁপত। বাবা বলতেন, নার্ভাসনেস। সব ব্যাপারে তোমার থতমত খাওয়া স্বভাব। আসলে পারকিনসন্স্ বোঝার আগেই মার ওভ্যারিয়ান ক্যানসার ধরা পড়ল।’
শমীক জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার মার তখন কীরকম বয়স?’
‘ফর্টি ওয়ান।’
‘চেক আপ করাতেন না?’
‘ওভ্যারিয়ান ক্যানসার প্যাপ টেস্টে ধরা পড়ে না। তখন অত স্পেসিফিক টেস্টও করা হত না। যখন ধরা পড়ল, লাংস-এ স্প্রেড করেছে। নিঃশ্বাসের কষ্ট থেকে সিম্পটম শুরু হয়েছিল…’ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অ্যানা বলল, ‘এত পার্সোনাল কথা শোনার ধৈর্য্য আছে তোমার?’
‘আমি তো শুনতে চেয়েছি। তোমার কবিতা, সেদিনের নাটক, কোথাও কোনও যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছি। ক্যারেন বলেছিল, তুমি নিজেই হয়তো একদিন আমাকে বলবে।’
অ্যানা জানলার বাইরে চেয়ে ছিল। এক সময় শমীকের দিকে মুখ ফেরাল, ‘মার কথা ভাবলে আমার শুধু দুঃখ হয় না শমীক। বুকের ভেতর থেকে নিজের সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা আর লজ্জা উঠে আসে। নিজের কাছে এত ছোট হয়ে বেঁচে থাকা, এ যে কী কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না।’
এপ্রিলের শেষে বসন্ত এল। অ্যানা ঘরের জানলা খুলে দিয়েছে। ছোট্ট বারান্দায় সারি সারি টব। পাম, রাবার প্ল্যান্ট, আফ্রিকান ভায়োলেট, পিটুনিয়া, জিরেনিয়াম। রোজ ফুল ফুটছে। সারা শীত ঘরবন্দি থেকে এতদিন পরে আবার আকাশ, রোদ, বৃষ্টি, বসন্তের হাওয়া। শমীক এ-শহরে নতুন ঘাসের গন্ধ পায় না। পেভমেন্টের বুকে একা দাঁড়িয়ে থাকা গাছ। কবে তাদের পাতা ঝরল, কবেই বা নতুন পাতা এল, তেমন করে চোখে পড়ে না। শুধু যখন অ্যানার কাছে আসে, এই ছোট্ট বারান্দার সারি-সারি গাছ হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে বসন্তের খবর দেয়।
অ্যানার গলার স্বর কান্নায় বুজে আসছিল। শমীক ওকে স্থির হতে সময় দিল। এ অবস্থায় কীই-বা বলা যায়? অ্যানার মার পরিণতি যদি সত্যিই ওই নাটকের মতো হয়ে থাকে, শমীক কি ঘটনাটা অনুমান করতে পারছে না? অ্যানার কথায় সেই যুবতী মেয়েটির অনুশোচনার সংলাপ শুনছে না? কিন্তু শমীক তো এখন নাটক দেখছে না। ওর পক্ষে নীরব দর্শক হয়ে থাকা সহজ হল না। শমীক অ্যানার পাশে এসে বসল। ওর হাত নিজের হাতে ধরে রেখে বলল, ‘আজ তোমার এসব কথা মনে হচ্ছে কেন জানো? বোঝার বয়স হয়েছে বলে। হয়তো একটা বয়সে আমরা নিজের ইচ্ছে-অনিচ্ছের কথাই শুধু ভাবি। অপরিণত বয়সের অবুঝ আবেগ। তখন নিজেকে ছাড়া কারোর কথা ভাবতে চাই না। তাছাড়া, তোমার তো তখন ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতাও ছিল না।’
অ্যানা ধীরে-ধীরে মাথা নাড়ল, ‘না শমীক, সেটা কোনও যুক্তি ছিল না। আমার তখন ষোলো বছর বয়স। দু-বছর পরে কলেজে যাব। মার জন্যে আমি কতটুকু ভেবেছি? কী ত্যাগ স্বীকার করেছি? সার্জারির পর কেমো শুরু হল। মার কষ্ট দেখা যায় না। বমি, জ্বর, সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা। ছ-মাস চিকিৎসার পর যখন একটু স্বস্তি পেলেন, পারকিন্সন্স ধরা পড়ল। বাবা সব দিক সামলাতে পারছিলেন না। বাড়িতে সারাদিন কারওর থাকা দরকার। মেডিকেল ইনসিওরেন্স থেকে সব খরচ দিত না। কিন্তু বাড়িতে সারাক্ষণ কে থাকবে? আমি ইলেভেনথ্ গ্রেডে। বাবার পক্ষেও ছুটি নিয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। মা ভীষণ ভেঙে পড়লেন। বুঝতে পারছিলেন ক্রমশই সংসারে বোঝা হয়ে উঠেছেন। ‘লং টার্ম কেয়ার’-এর মতো প্রাইভেট ইনসিওরেন্সও করা ছিল না। যখন টুয়েলভথ্ গ্রেডে উঠলাম, বাবা একটা ডিসিশনে এলেন। মাকে আর এ-দেশে রাখবেন না। ইন্ডিয়ায় পাঠিয়ে দেবেন। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। যতই অসুস্থ হন, এটাই মায়ের নিজের জায়গা। নিজের বাড়ি। মা কোথায় যাবেন? কেন যাবেন?

‘বাবা আমাকে বোঝালেন— তুমি ক-মাস বাদে কলেজে চলে যাবে। চার বছর বাড়িতে থাকবে না। আমাকে তো চাকরিটা রাখতে হবে অ্যানা। কার ভরসায় ওকে বাড়িতে রাখব। আমি বলেছিলাম, ইন্ডিয়া থেকে কাউকে স্পনসর করে আনা যায় না? লোকে বেবি সিটার, ন্যানি, হাউসকিপার আনায় তো।
‘বাবা রেগে উঠলেন—তোমার মাকে হ্যান্ডল্ করা আমাদের পক্ষেই শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। দেশ থেকে কাউকে আনালেও থাকবে ভেবেছ? আজকাল ওসব ভিসা নিয়েও প্রবলেম হচ্ছে।
‘আমি বাবার কথা মানতে পারছিলাম না। রেগে গিয়ে তর্ক শুরু করলাম— নিশ্চয়ই আরও উপায় আছে। মাকে তো এখানেই নার্সিংহোমে রাখা যায়। আমার ছুটির সময় বাড়িতে নিয়ে আসব।
‘বাবা বোঝালেন— মেডিকেল ইনসিওরেন্স থেকে সব খরচ পাব না। আমি সবদিক ভেবে ডিসিশন নিয়েছি।
‘আমি গুম হয়ে আছি দেখে বাবা বলতে লাগলেন— চার বছর তোমাকে কলেজে পড়তে হবে। প্রায় হান্ড্রেড থাউজেন্ড ডলার্স। দিন-দিন টিউশন ফি আরও বেড়ে যাচ্ছে। আমাকে তার প্রভিশন রাখতে হচ্ছে। আমাদের কোম্পানিতে লে-অফ হচ্ছে। যদি চাকরিটাই চলে যায়, কী ডিফিক্যালটিতে পড়ব, ক্যান ইউ ইম্যাজিন? হঠাৎ কেমন ভয় হল। এত আন্সার্টেন অবস্থা আমাদের।
‘বাবা বোঝালেন—তোমার মার লং টার্ম কেয়ারের জন্যে ইন্ডিয়াতে ভালো ব্যবস্থা করেছি।
‘মা কোথায় থাকবে বাবা?
‘কলকাতার কাছেই। একটা প্রাইভেট নার্সিংহোমে। তোমার দিদিমা, মামা-টামারা দেখাশোনা করবে। খোঁজখবর নেবে। আমরাও যাব মাঝে মাঝে।
‘বুঝলাম বাবা তার মানে ভেতরে-ভেতরে ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। মামার বাড়িতেও জানে। কিন্তু মা? মা কী করে থাকবেন? আমাকে ছেড়ে, বাবাকে ছেড়ে বাকি জীবনটা দেশের নার্সিংহোমে থাকবেন? এ-কথা মাকে আমরা বলব কী করে?
‘মাকে বাবা-ই বললেন। সেই দিনটা ভুলতে পারব না শমীক। মার চোখে অবিশ্বাস, ভয়! সেই অসহায় ভয়ার্ত দৃষ্টির নিঃশব্দ দহনে আমরা যেন পুড়ে যাচ্ছিলাম। যে মা এক সময় বলতেন চিরদিন বিদেশে থাকব না, সেই মা দেশে যাওয়ার কথায় অসহায়ভাবে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন। দিনের পর দিন বাবা বুঝিয়েছেন। বাধ্য হয়ে আমিও চেষ্টা করেছি। মা মানতে চাননি। কত বছর মা চাকরি করেছেন। বাবাকে সাহায্য করেছেন। এই বাড়িঘর, সংসারে তাঁর তো একই অধিকার। আজ অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে আমরা দূরে ঠেলে দিচ্ছি। নিষ্ঠুরতার সেই অভিযোগ অভিমান নিয়েই মা চলে যেতে বাধ্য হলেন।’
শমীক জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি সঙ্গে গিয়েছিলে?’
‘না, বাবা গিয়ে রেখে এলেন। যাবার আগের দিন বাবা জিনিসপত্র গোছাচ্ছিলেন। মা আমাকে ডাকলেন। দেওয়ালে ঝোলানো ফ্যামিলি পিকচার থেকে একটা ছবি চেয়ে নিলেন। মার সঙ্গে আমার ছোটবেলার ছবি। বললেন— এটা নিয়ে যাই? তোদের তো অনেক ছবি আছে। কথাটা বুকে বাজল। এ-বাড়ির জিনিসপত্র এবার থেকে শুধু আমাদের। মার নয়। আমার ছবিও শুধু আমাদের। মার নয়। তাই একটা মাত্র চেয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলাম না। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছি। মা আদর করে বললেন— আরও কটা বছর বাঁচব তো? তুই আবার নিয়ে আসবি। এখানেই কোথাও রেখে দিবি। তবু তো দেখতে পাব।
‘সেদিন মনে হয়েছিল, মা আমাকে ক্ষমা করেছেন। ভেবেছেন আমার তো কোনও ক্ষমতা নেই। বাবার ওপর কথা বলতে পারছি না। জানো শমীক, মা বোঝেননি আমি সেদিন নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবছি। কর্নেল-এ অ্যাডমিশন পেয়েছি। ইউ.পেন-এ পেয়েছি। কলাম্বিয়ার চিঠির অপেক্ষা করছি। আইভি-লিগ কলেজে পড়ব। বাবাকেই চার বছর পড়াতে হবে। আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই বাবাকে এমন একটা ডিসিশন নিতে হয়েছে। বাবার নিজের জীবনেই বা কী থাকল? সেদিন এইভাবেই আমি মনকে বুঝিয়েছিলাম শমীক।’
‘মার সঙ্গে তোমার আর দেখা হয়নি?’
‘হয়েছিল। পরের বছর সামারে গিয়েছিলাম। মার অবস্থা দেখলাম আরও খারাপ। এ অসুখের শেষের দিকে যা হয়। কয়েক বছর ধরেই তো শুরু হয়েছিল। রেস্টিং মাস্লস্-এ ট্রেমর। ভীষণ উইকনেস। নার্ভ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেবার গিয়ে দেখলাম আরও ডিজেনারেট করেছে। মা কথা বলতে পারছে না। জড়ানো কিছু স্বর, দু-চোখ দিয়ে জল পড়ছে।
‘সবচেয়ে কষ্ট হচ্ছিল থাকার জায়গাটা দেখে। নার্সিংহোম বলতে যা ভেবেছিলাম, তা নয়। ঘিঞ্জি এলাকায় একটা পুরনো বাড়ি। ঘরে-ঘরে কজন ডিস্এবল্ড্ রুগী। অ্যাটেনডেন্টরা দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে ডাক্তার আসেন। ট্রেইন্ড নার্সও বোধহয় নেই। যাঁর বিজনেস, সেই মহিলাই বললেন— অল্প খরচে এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা করা যায় না। ওষুধপত্র, তিনবেলার খাবার, সবই আমরা দিই।
‘ভাবছিলাম বাবা কী করে এ জায়গাটা খুঁজে পেলেন? কেউ নিশ্চয়ই খবর দিয়েছিল। বাবা পরে বলেছিলেন মামার বাড়ির কাছাকাছি বলে ওখানে রেখেছিলেন।’
‘ওঁরাই দেখাশোনা করতেন বোধহয়?’
‘মামার বাড়ি বলতে দিদিমা আর দুই মামার ফ্যামিলি। কলকাতায় এক মাসি। হ্যাঁ, ওঁরাই খোঁজখবর করতেন। মাঝে মাঝে দেখতে যেতেন। সেদিক থেকে জায়গাটা খুব দূর ছিল না। কিন্তু কী নোংরা রাস্তাঘাট ভাবতে পারবে না। বাজারের গোলমাল। বাসের আওয়াজ। এক তলায় মার ঘরটায় ঢুকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। দিনের বেলাতেও মাকে মশারির মধ্যে শুইয়ে রেখেছে। শমীক, আমার মনে হয়েছিল এটা পাপ। তিল-তিল করে আমরা একটা মানুষকে মেরে ফেলছি। দিদিমা যখন বললেন—তোদের বড়লোকদের দেশে মানুষ এত নিষ্ঠুর হয়? মা, বউয়ের অসুখ হলে বাড়ি থেকে বার করে দেয়? চিকিৎসা করায় না? সেবাযত্ন করে না?
‘তখন বাবার পক্ষ নিয়ে একটা কথাও বলিনি। মাথার মধ্যে কেবলই ওই পাপ কথাটা ঘুরে-ফিরে আসছিল। মাকে আমরা কত কষ্ট দিলাম।’
শমীক জিজ্ঞেস করল, ‘মা কতদিন বেঁচে ছিলেন?’
‘তারপর বছরখানেক।’
‘তোমার বাবার দিকের আত্মীয়স্বজন?’
‘বাবার বাড়ি নর্থ বিহারে, পূর্ণিয়ায়। কলকাতায় বিশেষ কেউ নেই। যাঁরা ছিলেন, তাঁরা মাঝে মাঝে মাকে দেখতে যেতেন।’
‘তোমার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে কনট্যাক্ট নেই?’
‘খুব কম। ইন্ডিয়ায় আর যাওয়াই হয় না।’
‘এ-দেশে কেউ নেই?’
‘মার এক কাজিন আছেন। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন না। ওই সময় বাবার সঙ্গে একটা রিফ্ট হয়ে গেছে। হয়তো ওঁর নাম শুনেছ। সাউথ এশিয়ান উইমেনদের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স নিয়ে কাজ করেন। বৃন্দা সেন।
‘আসলে বাঙালি কমিউনিটিতে মার ব্যাপারটা নিয়ে অনেক কথা উঠেছিল। দু-চারজন বাবার অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু বেশিরভাগই বাবার বিরুদ্ধে। সমালোচনার কথা আমাদের কানে আসত। বাবা কনফ্রন্ট করতে চাইতেন না। বৃন্দামাসি বাবাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। আমাকেও মেয়ে হিসেবে একটা স্ট্যান্ড নিতে বলতেন। শেষপর্যন্ত ওঁদের উইমেন্স্ গ্রুপ ‘সহেলী’ মার কাছে এল। ওঁরা মাকে বোঝালেন মা যদি ডিভোর্স ফাইল করতে চান, ওঁরা লিগ্যাল অ্যাসিস্টেন্স দেবেন। সবরকম সাপোর্ট দেবেন।’
‘ডিভোর্স পেলেও বা কী সলিউশন হত?’
‘বাবা তাহলে মাকে নিজের বাড়ি থেকে সরাতে পারতেন না। লিগ্যালি তো তা পারেন না, না? তখন কোর্ট অর্ডারে বাবাকেই বাড়ি ছেড়ে আলাদা থাকতে হত। আমি তখনও ডিপেনডেন্ট, মা অসুস্থ, অলমোস্ট ডিস্এবল্ড্। বাবাকে মাসে মাসে অ্যালিমনি দিতে হত। মাকে দেখাশোনার জন্য অবশ্য কী ব্যবস্থা করা যেত, তখনও জানতাম না।’
শমীক জিজ্ঞেস করল, ‘তোমার মা ডিভোর্স ফাইল করতে রাজি হলেন না?’
‘না, অত স্ট্রেস নেওয়ার মতো ক্ষমতা ছিল না। আমার কথাও ভেবেছিলেন। আমার কেরিয়ারের জন্যে মাকেই সবচেয়ে বেশি দাম দিতে হল। বাবাও সেটাকেই প্রায়োরিটি দিয়েছিলেন।’
‘এ-দেশে কত ছেলে-মেয়ে স্টুডেন্ট লোন নিয়ে পড়ে। তোমার বাবা কেন কলেজ লোন নিয়ে পড়ালেন না? পে-ব্যাক করার জন্যে তুমি কত বছর সময় পেয়ে যেতে।’
‘প্রত্যেক ব্যাপারে বাবার ডিসিশনই শেষ কথা ছিল। মেল ডমিনেটেড ফ্যামিলির যেমন হয়। তখন বন্ধুবান্ধব কারওর অ্যাডভাইস নেননি। আঠারো বছর বয়সে আমারও কোনও ভয়েস ছিল না। আজ যে এত কষ্ট পাচ্ছি, সে তো এই জন্যেই। যত দিন যাচ্ছে বুঝতে পারছি, সলিউশন নিশ্চয়ই ছিল। বাবা খুঁজে পাননি। নয়তো, খুঁজতে চাননি।’
‘তোমার বাবা এখন কোথায়?’
অ্যানা ম্লান হাসল, ‘আছেন। ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন। কমিউনিটির লোকজনদের সঙ্গে ব্রিজ খেলেন। এধার ওধার বেড়াতে যান। বিবেকও পরিষ্কার। এখনও মনে করেন, যা করেছেন, ওই অবস্থায় তার বেশি কিছু সম্ভব ছিল না।’
(চলবে)
ছবি সৌজন্য: Wikimedia Commons, Rawpixel
দীর্ঘকাল আমেরিকা-প্রবাসী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখালিখির সূচনা কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে। আমেরিকার নিউ জার্সির প্রথম বাংলা পত্রিকা "কল্লোল" সম্পাদনা করেছেন দশ বছর। গত আঠাশ বছর (১৯৯১ - ২০১৮) ধরে সাপ্তাহিক বর্তমান-এ "প্রবাসের চিঠি" কলাম লিখেছেন। প্রকাশিত গল্পসংকলনগুলির নাম 'পরবাস' এই জীবনের সত্য' ও 'মেঘবালিকার জন্য'। অন্য়ান্য় প্রকাশিত বই 'আরোহন', 'পরবাস', 'দেশান্তরের স্বজন'। বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য নিউইয়র্কের বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ থেকে ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।