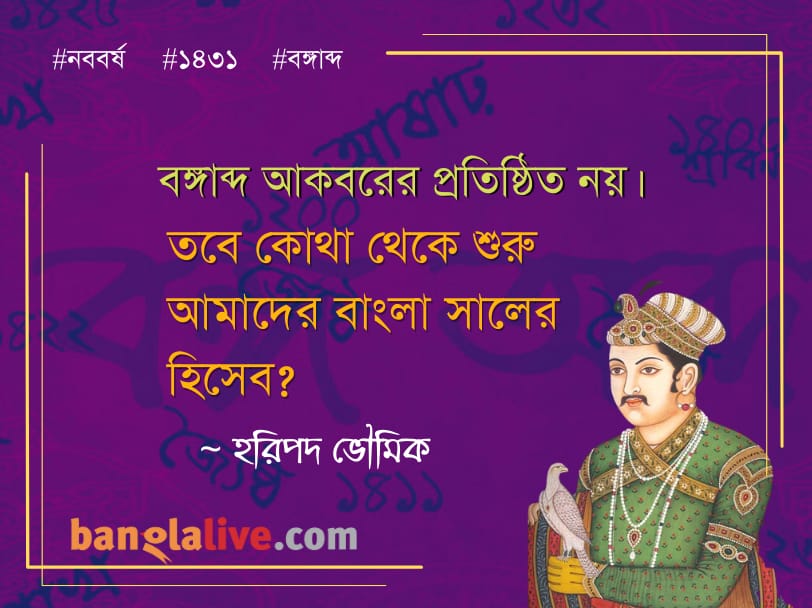রমাতোষ সরকার তাঁর লেখা ‘প্রসঙ্গ বঙ্গাব্দ’-তে জানিয়েছেন —‘বঙ্গাব্দ চান্দ্র আর সৌর গণনা-পদ্ধতির এক অভিনব সংমিশ্রণ। মুসলিম দুনিয়ায় প্রচলিত চান্দ্র পদ্ধতির হিসাবপত্র একটা সময় পর্যন্ত মেনে নিয়ে, বঙ্গাব্দ তার পরবর্তী হিসাবরক্ষায় প্রয়োগ করা শুরু করল সৌরপদ্ধতি—যা প্রকৃতির ঋতুচক্রের সঙ্গে সমতাল, অতএব কৃষি এবং অন্যান্য নানা কাজকর্মের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। প্রাচীন ভারতবর্ষে যাকে অনেক সময়ে বলা হয় হিন্দু যুগ, সেই যুগে ‘সূর্যসিদ্ধান্ত’ ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ পঞ্জিকা-প্রণয়ন তথা জ্যোতির্বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গ্রন্থ। সূর্যসিদ্ধান্তে সূর্যভিত্তিক বর্ষগণনার নির্দেশ ছিল। মধ্যযুগের বাঙালিরা সেই গণনা পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন।
বঙ্গাব্দ হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির দুই ধারার এক বিচিত্র সুন্দর সমন্বয়। বাংলা ভাষার মতো বঙ্গাব্দও আজ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালির এক গৌরবজনক সাধারণ উত্তরাধিকার। বঙ্গাব্দ বাঙালির নিজস্ব অব্দ—এ অব্দে তার অপ্রতক্য স্বত্ব।
‘হিজরি প্রথমত এবং প্রধানত ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের ব্যবহৃত অব্দ’। আজকাল অবশ্য মুখ্যত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রেই ওঁরা এই অব্দ ব্যবহার করে থাকেন—জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বড় একটা নয়। এই অব্দের রীতি অনুসারে হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা প্রস্থানের বছর থেকে কালগণনার শুরু। সেটা ছিল খ্রিস্টাব্দের হিসাবে ৬২২ সাল। অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দের হিসাবে যা ৬২২ বছর বলে চিহ্নিত, হিজরির হিসাবে তা ১ম বছর। বঙ্গদেশে যখন (এই সন) এল তখন খ্রিস্টাব্দের হিসাবে ১৫৫৬ সাল—দিল্লির সিংহাসনে সেই বছরেই বাদশা হয়ে বসেছেন তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবর। (প্রসঙ্গ বঙ্গাব্দ পৃ. ৪)। তিনি হিজরি ও বাংলা সন নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছিলেন।

ঢাকা বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত (১৯৭৭) ‘বাংলা সনের জন্মকথা’ গ্রন্থে মুহম্মদ আবুতালিব ‘সনের রূপান্তর প্রসঙ্গ’ (পৃ. ৫৯) ‘হিজরী, বাংলা ও ইংরেজী সন (খ্রিঃ)’-এর একটি তালিকা দিয়েছেন নিম্নরূপে :
হিজরি/বাংলা ১লা মুহররম/১লা বৈশাখ খ্রিস্টাব্দের কত তারিখ
১ হিজরি জুলাই ১৬, ৬২২ খ্রিঃ
২ হিজরি জুলাই ৫, ৬২৩ খ্রিঃ
৩ হিজরি জুন ২৪, ৬২৪ খ্রিঃ
৯৬৩ সন পর্যন্ত হিজরি ও বাংলা সন একই
৯৬৩ হি নভেম্বর ১৬, ১৫৫৫ খ্রিঃ
৯৬৩ হি বাংলা সন (নবজন্ম) ১০/১১ এপ্রিল, ১৫৫৬ খ্রিঃ
১৩৭৩ (বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত) – ১৫ এপ্রিল, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ।
এই তালিকায় একটা বড় রকমের গোলমাল রয়েছে, যা সাদা চোখে বোঝা যাবে না। আমরা ঠিক ওই একই তালিকা ধরে আর একটি তালিকা তৈরি করে দিচ্ছি—
খ্রিস্টাব্দ তারিখ হিজরি সন
৬২২ খ্রিঃ ১৬ জুলাই – ১ হিজরি সন শুরু।
৬২৩ খ্রিঃ ৫ জুলাই ২ হিজরি সন।
৬২৪ খ্রিঃ ২৪ জুন ৩ হিজরি সন।
[৬২৪ খ্রিস্টাব্দের ৯৩১ পর ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে]
১৫৫৫ খ্রিঃ ১৬ নভেম্বর ৯৩৩ হিজরি হওয়া উচিত।
[কিন্তু তা লেখা হয়নি।]
১৫৫৬ খ্রিঃ ১৬ নভেম্বর ৯৩৪ হিজরি হওয়া উচিত।
১৫৫৬ খ্রিঃ ১০/১১ এপ্রিল ৯৬৩ হিজরি বাংলা সালের ‘নবজন্ম’ বলা হলো।
[৯৬৩ -৯৩৩ হিজরি = ৩০ বছর নিয়েই গোঁজামিল দেখা যাচ্ছে! ৯৩৩ হিজরি-কে ৯৬৩ বলে চালিয়ে দেওয়া হল।]
বঙ্গাব্দ হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির দুই ধারার এক বিচিত্র সুন্দর সমন্বয়। বাংলা ভাষার মতো বঙ্গাব্দও আজ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সব বাঙালির এক গৌরবজনক সাধারণ উত্তরাধিকার। বঙ্গাব্দ বাঙালির নিজস্ব অব্দ—এ অব্দে তার অপ্রতক্য স্বত্ব। 'হিজরি প্রথমত এবং প্রধানত ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের ব্যবহৃত অব্দ'। আজকাল অবশ্য মুখ্যত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রেই ওঁরা এই অব্দ ব্যবহার করে থাকেন—জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বড় একটা নয়। এই অব্দের রীতি অনুসারে হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনা প্রস্থানের বছর থেকে কালগণনার শুরু। সেটা ছিল খ্রিস্টাব্দের হিসাবে ৬২২ সাল। অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দের হিসাবে যা ৬২২ বছর বলে চিহ্নিত, হিজরির হিসাবে তা ১ম বছর। বঙ্গদেশে যখন (এই সন) এল তখন খ্রিস্টাব্দের হিসাবে ১৫৫৬ সাল—দিল্লির সিংহাসনে সেই বছরেই বাদশা হয়ে বসেছেন তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবর।
এখানে অনেকগুলি প্রশ্ন উঠে এসেছে, তাই বিষয়টিকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি—
এক. হিজরি সনের শুরু ৬২২ খ্রিস্টাব্দে, তখন বঙ্গাব্দ ছিল, কিন্তু কত সন তা জানা গেল না। তখন হিজরি সন শুরু হয়েছিল জুন-জুলাই মাসে।
দুই. ঢাকা বাংলা একাডেমির বই থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিজরি ৯৩৩ সন হওয়ার কথা, কিন্তু কেন ৯৩৩-কে ৯৬৩ করা হল? তার কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি!
তিন. ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ সময়কালে হিজরি সন এবং বাংলা সন একই ছিল, অর্থাৎ ৯৬৩ সন।
এই সনে ‘বাংলা সন (নবজন্ম)’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঢাকা বাংলা একাডেমির গ্রন্থে (পৃ. ৫৯)।
১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৬ নভেম্বর তারিখে হিজরির নববর্ষ হয়। ৫ মাস পরে ১০/১১ এপ্রিলে আবার হিজরি সনের নববর্ষ বলে ঘোষণা হয়েছে দেখা যাচ্ছে! এটাকেই কি বাংলা সনের নবজন্ম বলা হলো? কিন্তু কেন!! বাংলা নববর্ষ ১লা বৈশাখ তো ১০ থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই পড়ে। সুতরাং বলা যায় হিজরি সনের নববর্ষ যা আদিতে ছিল জুন- জুলাইতে, পরে করা হয় নভেম্বরে—শেষে নভেম্বর থেকে এপ্রিলে নিয়ে আসা হয়—এর অর্থ হিজরি সনের নবজন্ম দিয়ে আকবর বাংলা এবং হিজরিকে ১লা বৈশাখকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন—তাঁর বঙ্গে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য ‘ফসলি সন’ হিসাবে।
বঙ্গবাসী হিন্দুগণ তখন বাংলা সন ও হিজরি সনের এই মিলনকে মেনে নিতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পক্ষে রমাতোষ সরকার ‘প্রসঙ্গ বঙ্গাব্দ’ (পৃ. ৪) জানিয়েছেন—‘সে-যুগের বাঙ্গালিরা হিজরিকে নির্বিচারে হুবহু মেনে নেননি। বাদশার কাছে আর্জি জানিয়ে, (আকবরের) মঞ্জুরি নিয়ে হিজরিকে তাঁরা প্রয়োজনমতো কিছুটা সংস্কার করে নিয়েছিলেন’।
হিজরি সনকে কিভাবে সংস্কার করে নেওয়া হয়েছিল? রমাতোষ সরকার সেই সংস্কার প্রসঙ্গটি লিখেছেন এভাবে :
‘হিজরি শুরুতে খ্রিস্টাব্দের চেয়ে ৬২১ বছর পিছিয়ে ছিল, তাই সাধারণভাবে সেই ব্যবধানটাই বরাবর থেকে যাওয়ার কথা। কিন্তু হিজরির চলার ধরনটা কিছুটা অসাধারণ; চলার পথে হিজরি কিছুটা লাফিয়ে লাফিয়ে অন্যান্য অব্দগুলোর তুলনায় নিজেকে এগিয়ে নেয়—প্রতি বছর প্রায় ১১ দিন করে অর্থাৎ প্রতি ৩২.৫ বছরে এক বছর করে বা ৬৫ বছরে দু’বার করে। তাই, ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভূমিতে যখন হিজরি প্রবর্তিত হল, হিজরির হিসাবে সে-সালটি ১৫৫৬-৬২১ = ৯৩৫ না হয়ে হল (৯৩৫/৩২.৫) = ৯৩৫ + ২৮.৭৭ (প্রায়) = ৯৬৩ (প্রায়)। সহজ করে বলা যায়, ১৫৫৬ সালে আকবর সিংহাসনে আরোহন করে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। এই বছর ৯৩৪ হিজরি সন হয়, আকবর ফসলী বাংলা সনের সঙ্গে এক করতে মোটামুটি ২৯ দিন হিজরি সনের সঙ্গে যোগ করে বাংলা সন ও হিজরি সন সমান করেছিলেন। ৯৬৩ – ৯৩৪ = ২৯ দিন, সঠিক হিসেবে হয় ২৮.৭৭ দিন বা ২৯ দিন প্রায়।
বাংলা সনের সমসময়ে সম্রাট আকবরের নির্দেশে প্রথম ‘ইলাহিসন’ (Devina Era) নামে একটি সনের প্রবর্তন হয়। যতদূর জানা যায়, এটি ছিল তাঁর রাজ্য সন (Reignal Era)। তাঁর রাজত্বকালের পরে এটি আর চলেনি।
‘আইন-ই-আকবরী’ থেকে জানা যায়, সম্রাট এমন একটি ত্রুটিমুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত সৌরসনের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, যা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যই আদর্শ হবে। বাংলা সনের মাধ্যমে তাঁর সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়েছিল মনে করা যেতে পারে। কেননা, বাংলা যেমন ‘হিজরি সন’ নয়—তেমনি এটি ‘ইলাহী সন’ থেকেও ভিন্ন। হিজরি সনের উপর ভিত্তি করা হলেও এর গঠন পদ্ধতি ভারতীয় শকাব্দের মতো, অথচ এটি শকাব্দেরও সমগোত্রীয় নয়। শকাব্দের সঙ্গে এর সম্পর্ক এইটুকু যে, এর মাস ও দিনের নাম শকাব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে।
বলা যায়, বাংলা সন পুরাণ কাহিনীর Mar Maid নামক সেই জন্তুটির মতো, যার দেহের নিম্নাংশ মাছের মতো এবং উর্ধাংশ ঠিক যেন স্ত্রীলোকের মতো। বাংলা সনও তাই। তার ভিত্তি হিজরির (চান্দ্রসন) উপর, অথচ আকৃতি ‘শকাব্দ’ শ্রেণীর সৌর সনেরই মতো ( পৃ. ৭)।
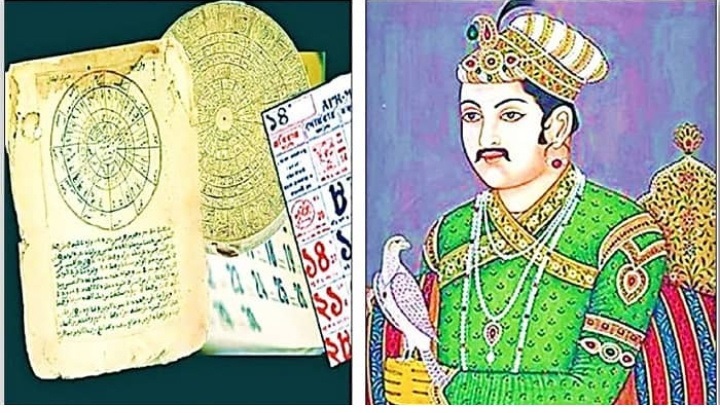
উপরের অংশটিরও লেখক মুহম্মদ আবুতালিব, তাঁর লেখা থেকে যে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হল—
এক, সম্রাট আকবর বাংলা সনকে ত্রুটিমুক্ত, বিজ্ঞানসম্মত সন বলে স্বীকার করেছেন।
দুই, চান্দ্রমাস ধরে বাংলা সনের গণনা শুরু হলেও পরবর্তীকালে সৌরমাসকে যুক্ত করায় নির্ভুল একটি গণনা-পদ্ধতির নাম বাংলা সন।
তিন, সম্রাট আকবর চেয়েছিলেন বাংলা সনের সঙ্গে হিজরি সনকে এক করে দিলে ভাল হবে।
চার, একদিকে হিন্দুরা এই মিলন চাইল না, তাই এক করা গেল না।
পাঁচ, সম্রাটের মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ার কারণে তিনি নতুন একটি ইলাহি সন প্রচলন করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই সনটি গ্রহণযোগ্যতা হারায়। এর একটি কারণ হতে পারে, সম্রাটের ধর্মীয় মানুষও চাননি হিন্দুসনের সঙ্গে তাঁদের পবিত্র সন হিজরিকে যুক্ত করার বিষয়টি। তাই তাঁরা সবটাই বর্জন করেছেন।
বর্তমান যুগে পুরনো ভাবধারাকে নতুন মোড়কে পরিবেশন করার চেষ্টায় বাংলা সনটি হিজরি সনের উপরেই ভিত্তি করে যেন বঙ্গাব্দের জন্ম হয়েছে!! মুহম্মদ তালিব ভূমিকায় (পৃ. ৭) জোর গলায় বলেছেন—‘এটি সর্বসম্মত মত যে, বাংলা সনের জন্ম হয় সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে, বিশেষ করে তাঁরই নির্দেশে (৯৯২ হি ১৫৮৪ খ্রি) বাংলা সনের উদ্ভাবন হয়। প্রচলিত হিজরীর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে রাজ-জ্যোতিষী মহাপণ্ডিত আমীর ফতেহ্ উল্লাহ্ সিরাজী এই বাংলা সনের উদ্ভাবন করেন।’ উল্লেখ্য যে, বাংলা সনের অনুষঙ্গী হয়ে আরও একাধিক সৌরসনের প্রচলন হয়, তন্মধ্যে ‘ইলাহি সন’ অন্যতম। ইলাহি সনও বাংলা সনের প্রায় সম-সময়েই প্রবর্তিত হয় এবং উভয় সনই সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহণের স্মারক হিসেবে চালু হয়। তাই তাদের প্রারম্ভিক বৎসর হিসাবে সম্রাটের সিংহাসনে আরোহনের বৎসর ধরা হয় (৯৬৩ হিঃ = ১৫৫৬ খ্রিঃ)।
আবার বলতে হচ্ছে, সম্রাট আকবর চেয়েছিলেন বাংলা সনের সঙ্গে হিজরি সনকে মিলিয়ে দিতে, কিন্তু এই দুই পক্ষই এই মিলনে রাজি না হওয়ায় সম্রাট নতুন অব্দের প্রচলন করেন—বাংলা সন বাংলা সনের জায়গাতেই থেকে যায়। সম্রাট সেখানে নিজে তাঁর সভা-পণ্ডিত দিয়ে একটি নতুন ‘ইলাহি সন’ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

একই তথ্য নানাভাবে পরিবেশনের মধ্য দিয়ে একটি অসত্য তথ্যকে সত্য প্রমাণের চেষ্টা যিনি করেন তিনিই জানেন সত্যটা ঠিক কি? নিজের জান্তে-অজান্তে সেই কথাটি কিন্তু প্রকাশ হয়েই পড়ে, তাই মুহম্মদ আবু তালিব মহোদয় ঠিকই বলেছেন ‘কৈফিয়ত’-এ (পৃ. ১০)—“ইতিহাস বড় কঠিন স্থান। সে সকলকেই গ্রহণ করে। কাউকেই বর্জন করে না বা অবহেলা করে না। তার মনের আয়নায় সকলের ছবিই ঠিক ধরা পড়ে। সে কাউকেই অতিরিক্ত খাতিরও করে না, বা কাউকে মাফও করে না। বাংলা সনের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়।”
সঠিক কথা! ইতিহাস কিন্তু আকবর বঙ্গাব্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেই তথ্য রয়েছে আইন-ই-আকবরীতে বলে দাবি করেছেন—তা সম্পূর্ণ ভুল—একথা জোর দিয়ে বলা যায়।
আবুল ফজল ‘আইন-ই-আকবরী’-তে ঠিক তথ্য দিয়েছেন এবং সেই সময়ে প্রচলিত অব্দগুলি সম্বন্ধে তিনি এমনটি লিখেছেন—
‘সম্রাট (আকবর) বিভিন্ন তারিখের গণ্ডগোলের জন্য হিন্দুস্থানে একটি নূতন অব্দ প্রচলিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি ‘হিজিরা’ অর্থাৎ ‘পলায়ন’ এই কথাটি পছন্দ করেন না অথচ অজ্ঞলোকে মনে করে এই অব্দ ও ইসলাম ধর্ম অবিচ্ছেদ্য, যদিও বুদ্ধিমান লোক সহজেই বুঝিতে পারে যে অব্দের প্রয়োজন সাংসারিক কার্য পরিচালনার জন্য, তাহার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই। জগতে অজ্ঞলোকের সংখ্যাই অধিক, জ্ঞানী বুদ্ধিমান ব্যক্তি অল্পই আছেন, সেই জন্যই নিজের ইচ্ছা কার্যে পরিণত করিতে তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করিলেন এবং ৯৯২ হিজরীতে যখন তাঁহার আলোক মানবজাতির উপর পতিত হওয়ায় তাহাদের বুদ্ধির প্রসারতা হইল তখন তিনি তাঁহার এই অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিতে সেই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করিলেন। বিচক্ষণ আমীর ফতা-উল্লাহ্ সিরাজী উলুগ বেগের জ্যোতিষিক পঞ্জী হইতে বর্ষ-পঞ্জিকা সংশোধন করিয়া সম্রাটের রাজ্যারোহণের কাল হইতে এই অব্দের গণনা আরম্ভ করিলেন এবং সম্রাটের চরিত্রের অনুসারে ইহার নাম রাখা হইল ‘তারিখ ইলাহী’। ইহার মাস ও বৎসর উভয়ই সহজ সৌরগণনা অনুযায়ী হইবে, কোনোরূপ অতিরিক্ত দিন থাকিবে না। মাসের প্রত্যেক দিনটি প্রাচীন পারসিক নাম অনুযায়ী রাখা হইবে। পারসিক মাসে কোনো সপ্তাহ নাই, ত্রিশটি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, যে মাসে ৩২ দিন হয় তাহার শেষ দুই দিনের নাম রাখা হয় ‘রোজাশব’ বা ‘অহোরাত্র’ এবং একটিকে অপরটি হইতে পৃথক বুঝাইবার জন্য ‘প্রথম’ ও ‘দ্বিতীয়’ এই বিশেষণে বিশেষিত করা হয়” (অনুবাদ ত্রিদিবনাথ রায়)।

দীর্ঘকাল ধরে আইন-ই-আকবরী-তে বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠা সম্রাট আকবর করেছেন বলে যা প্রচার করা হয়েছে বা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে যা অসত্য এবং ভুল।
মাসের নাম
প্রাচীন রোমান খ্রিস্টাব্দ বঙ্গাব্দ
১। মাসিয়াস জানুয়ারি বৈশাখ
২। এপ্রিলিস ফেব্রুয়ারি জ্যৈষ্ঠ
৩। মেয়াস্ মার্চ আষাঢ়
৪। জুনিয়াস এপ্রিল শ্রাবণ
৫। কুইনটিলিস মে ভাদ্র
৬। সেক্সটিলিস জুন আশ্বিন
৭। সেপ্টেসি জুলাই কার্তিক
৮। অবেটাব্রিস আগস্ট অগ্রহায়ণ
৯। নভেমব্রিস সেপ্টেম্বর পৌষ
১০। ডিসেমব্রিস অক্টোবর মাঘ
১১। জানুয়ারিস নভেম্বর ফাল্গুন
১২। ফেব্রুয়ারিয়াস ডিসেম্বর চৈত্র
কলকাতার সংস্কৃতি ও তার ইতিহাস চর্চা লেখকের অতি প্রিয় বিষয়। পুরোনো কলকাতাসহ নানা বিষয়ে অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে তিনি বিদ্বৎসমাজে স্বপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত অনেক বইয়ের মধ্যে ‘সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতা’ গ্রন্থ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ নিশীথরঞ্জন রায় লিখেছিলে – ‘হরিপদ ভৌমিক গবেষণামূলক তথ্যভিত্তিক বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। গভীর নিষ্ঠা নিয়ে উপাদান সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে বিপুল শ্রম ও অধ্যাবসায়সাধ্য কর্মসূচি গ্রহণ করলেন তার ফলে গবেষণার মান উন্নীত হবে। গবেষণার দিগন্ত উজ্জ্বলতর হবে’।
রসগোল্লা বিতর্ক নিয়ে তাঁর ‘রসগোল্লা-বাংলার জগৎ মাতানো আবিষ্কার’ গ্রন্থটি তাঁকে সর্বভারতীয় পরিচিতি এনে দিয়েছে। তাঁর রচিত ও সম্পাদিত অনেক বইয়ের মধ্যে ‘নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা’, কালীক্ষেত্র কালীঘাটের ‘বিন্দু মা’, ‘বিয়ের শব্দকোষ’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।