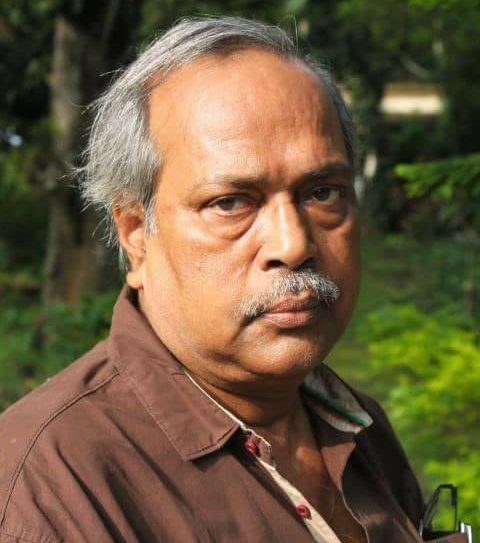আগের পর্বের লিংক: [১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১] [১২] [১৩] [১৪] [১৫]
হরিপদদার চায়ের দোকান খোলা হত ভোর হবার বেশ আগে৷ বলা যায়, শেষরাতের শেষভাগে৷ ভোরের পার্ক-সার্কাস মাঠে খেলব বলে বল নিয়ে বেরোনোর সময় আমরা দেখেছি হরিপদদা কয়লা ভাঙছেন৷ অহনই চললি বল লইয়া? রাইত অহনও বাকি আছে৷ সাবধানে যাইস৷ কুত্তাগুলারে ঢিলাইস না৷ চাক কয়লা হাতুড়ি দিয়ে ভাঙার খাট খাট শব্দ হত৷ দু-একটা পাখি তখন ডাকা শুরু করেছে৷ সূর্য উঠতে না উঠতেই পথ ধোওয়ানোর করপোরেশন হাজির৷ চার্চের কাছে গাড়ি রেখে হইহই করে নেমে পড়তেন কর্মীরা৷ গঙ্গার কলের মুখ খুলে বিশাল হোসপাইপ লাগিয়ে দূরে দূরে জল ছিটিয়ে দিতেন প্রবল বেগে৷ অর্ধবৃত্তাকার সেই জল-উৎক্ষেপে আমরা রামধনু দেখেছি কতদিন৷ জলস্রোতে ভেসে যেত হরিপদদার ভাঙা কয়লার পরিত্যক্ত গুঁড়ো৷ ফুটপাত সাফসুতরো৷ কিছুক্ষণ পরই সাইকেল টিঙটিঙিয়ে আসত খবরের কাগজ৷ ‘যুগান্তর’ খুলে হরিপদদা চোখ বুলিয়ে নিতেন প্রথম পৃষ্ঠায়৷ খাদ্যের দাবিতে বিক্ষোভ জেলায় জেলায়, বা, পূর্ববঙ্গ হইতে হাজার হাজার মানুষের বাংলায় আশ্রয়৷ বা, মুখ্যমন্ত্রীর কাঁচকলা খাওয়ার পরামর্শে বিরোধীদের রসিকতা৷ হরিপদদা হয়তো মনে মনে বলতেন, দ্যাশটা ছারখার হইয়া যাইব৷ যত শয়তান আর আকাইম্মার হাতে পড়ছে দ্যাশটা৷ ‘হয়তো’ বলা এইজন্যে যে প্রকাশ্যে তাঁকে বলতে শুনেছি, একটা ভালো খবর নাই চাইরপাশে৷ খালি মানুষের কষ্ট আর কষ্ট।
সাতটা বাজতে না বাজতেই হরিপদদার ইস্ট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট জমজমাট৷ হরিপদ, তোমার কাগজে কী লিখছে? জেলা থেইকা চাউল নাকি শহরে ঢুকতে দিব না! নাম দিছে ‘কর্ডনিং সিস্টেম’৷ আরে, ভাদাইম্মা পাহারা দিব কি হরিশচন্দ্রে না যুধিষ্ঠিরে? শালা, কালাবাজারের দরজা হাট কইরা দিল পুরা বাংলায়৷… হরিপদ, একখান মুখ্যমন্ত্রী পাইছি বটে আমরা৷ পানুবাবু, কাগজটা এবার দিন৷ হেডলাইন দেখে দিয়ে দেব৷ মাসকাবারি বাজার আছে৷ সান্যালবাবু, সারা পৃথিবী তো জ্বলছে৷ আপনাদের পার্টি কী বলে? আপনাদের পার্টির কাগজ, কী যেন নাম, হ্যাঁ ‘কালান্তর’ কী বলে? হাসপাতালের দেওয়ালে পত্রিকাটা মাঝে মাঝে দেখি৷ এখানে ওইরকম একটা ব্যবস্থা করতে পারেন৷

বেলা ন-টা থেকে এগারোটা— কেটলি যত গরম, জল যত ফোটে, ইস্ট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টও ততটাই গরম, ততটাই টগবগ৷ বাংলা পেরিয়ে ইন্ডিয়া ধরে ফেলে কথাবার্তা, বিধান রায়-প্রফুল্ল সেন পেরিয়ে জওহরলাল-লালবাহাদুর, ঢুকে পড়ে ইতিহাসে— চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-ভগৎ সিং-তেভাগা৷ ভোটের সময় তুলকালাম৷ দলে ভারী সিপিআই, সিপিএম৷ রাঙাদা, বিমলদা কংগ্রেসের সমর্থক হলেও তাঁদের স্টক কম৷ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার মতো অস্ত্র বেশি নেই৷ রাঙাদা পট করে বিবেকানন্দে চলে যান৷ বিমলদা ‘সব পার্টি সমান’ বলে পলায়ন করেন৷ একা শিবেনদা কংগ্রেসের লড়াকু সৈনিক— বিয়াল্লিশের মার-খাওয়া বিপ্লবী যেন৷ আরে, চুপ কর, নাইনটিন ফরটিটু-তে তরা বিশ্বাসঘাতকতা করসিলি, মনে আছে? ফরটিথ্রি-তে কী করলি? জনযুদ্ধের লাইন৷ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এখন কোনও লড়াই না৷ কেন? ব্রিটিশ কি সোহাগের জামাই হইল? রাশিয়া বিবাহের কার্ড ছাপাইয়া দিল৷ আর, তরা সানাই বাজাইলি৷ চুপ যা, চুপ যা৷ এখন তো তরা মস্কো আর পিকিং লাইনে জরাসন্ধ৷ সিপিআই-সিপিএম একযোগে চিৎকার করে ওঠে— হোওওওওওও৷ টেবিল বাজায়৷ শিবেনদার গলা চাপা পড়ে৷ কিন্তু শিবেনদাকে থামানো কঠিন৷ তিনি বলেই যান৷ হরিপদদা কখনও কখনও বেজায় চটে বলে ওঠেন, এত চিল্লান কেন? এইটা বয়রাগো দ্যাশ নাকি? উনানে কাঁচা কয়লা ফেইলা তাড়ামু, কইয়া রাখলাম৷
শিবেনদাকে হইহই করে কোণঠাসা করতে পারলেও সিপিআই-সিপিএমরা সেসময় ভোটে জিততে পারত না৷ হাসতে হাসতে জিততো কংগ্রেস৷ আমাদের ওয়ার্ডে পুলিনবিহারী খটিক, পাশের ওয়ার্ডে সুশীল মোতায়েদ ছোটোবেলা-থেকে-দেখা কাউন্সিলর৷ সিপিএম-সমর্থিত অমলেন্দু চক্রবর্তী, নির্দল ডা. অনুতোষ মজুমদার, নির্দল গৌরাঙ্গ রায় ধারাবাহিক পরাভূত৷ শুধু রিফিউজি-প্রধান আমাদের পাড়ার ভোট দিয়ে যে জেতা যায় না, সে-অঙ্ক বোঝার বয়স তখনও হয়নি৷

রিফিউজি বলেই হয়তো আমাদের পাড়া বামপন্থী৷ শিবেনদার মতো কংগ্রেস-সমর্থক ছিলেন, তবে সংখ্যায় খুব কম৷ ১৯৬৫-৬৬র একটা সময় পাড়া আলোড়িত হল ‘কল্লোল’-এ, পাড়া দাঁড়াল ‘কল্লোল’-এর পাশে৷
উৎপল দত্তর লিটল থিয়েটার গ্রুপের নাটক ‘কল্লোল’-এর কথা বলছি৷ নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ২৮ মার্চ ১৯৬৫৷ থার্টিনাইন বাই ওয়ান-এর বস্তিবাড়ি এই নাটক সম্পর্কে কিছুটা জেনেছে আগেই৷ হেমাঙ্গ বিশ্বাসের সৌজন্যে৷ এখানে রত্না সরকার ও শৈলেন সরকারের ঘরে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং তাঁর দলের গানের রিহার্সাল হত৷ নৌবিদ্রোহ নিয়ে একটা অসাধারণ নাটক করতে চলেছেন উৎপল দত্ত, এ-সংবাদ তিনি জানিয়েছিলেন সহশিল্পীদের৷ ‘কল্লোল’-এর গান ও সুর হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রচনা৷ শেখর চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, অনন্যসাধারণ গান হেমাঙ্গ বিশ্বাসের— ‘বাজে ক্ষুব্ধ ঈশান কোণে বজ্র বিষাণ’৷ মহারাষ্ট্রের পোয়াজ আর লাউনি সুরে গান তৈরি করলেন তিনি৷ অসাধারণ সুরপ্রয়োগ৷ যেন মেহনতি মানুষের প্রাণের কথাকে সুরে তুলে ধরা৷ ব্যবহৃত হয়েছিল জার্মান, রুশ ও চিনা নৌবিদ্রোহের গান৷ সঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্গীত৷ প্রসঙ্গত, শেখর চট্টোপাধ্যায় এই নাটকের বিদ্রোহী নেতা শার্দূল সিং৷ প্রজন্মের ব্যবধানে যাঁদের এ তথ্য অজানা থেকে গেছে, তাঁদের জন্য বলা৷
বস্তি-অধ্যুষিত আমাদের রিফিউজি পাড়া কীভাবে এই নাটকের পাশে দাঁড়িয়েছিল, সে-খবর হয়তো কারও জানা নেই৷ না-থাকার একটা কারণ, সেদিন এই নাটকের পাশে শহর মফসসলের হাজার হাজার পাড়া দাঁড়িয়েছিল৷ ‘কল্লোল’ বন্ধ করে দেবার সরকারি চেষ্টা রুখে দিয়েছিল৷ ‘বসুমতী’ পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন, প্রাইভেট আর্মি গড়ে উঠেছে ‘কল্লোল’-কে কেন্দ্র করে৷ আমাদের পাড়া সেইসব পাড়ার একটি৷ ব্যতিক্রমী কিছু নয়৷ আর-একটা কারণ, এমন কোনও নামী মানুষ ছিলেন না আমাদের পাড়ার ‘কল্লোল’-অভিযানে, যাঁর সূত্রে এই এলাকা বিশেষ উল্লেখ পেতে পারে৷ হারিয়ে-যাওয়া একটা নাম মনে পড়ছে, অসীম… পদবি মনে নেই। আমাদের বস্তির ঘুপচিঘরে একা থাকা যুবক ‘অসীমদা’ একদিন ডেকে বললেন, একটা কাজের দায়িত্ব নিতে হবে৷ পোস্টার লাগাতে হবে৷ বড় রাস্তায়, গলিতে, বাসের গায়ে৷ ছড়িয়ে দিতে হবে৷ কাজটা করতে হবে গোপনে৷ কারণ কোনও পার্টি বা পুলিশ বাগড়া দিতে পারে৷ কাজে বাধা আসতে পারে শুনলে ওই বয়সে শরীর-মন চাঙ্গা হয়ে উঠত৷ অসীমদা কাজ করতেন সিপিএম-এর প্রকাশনা সংস্থা ন্যাশনাল বুক এজেন্সি-তে৷ তিনি হয়তো দলীয় কর্মী ছিলেন৷ তবে পাড়ায় তাঁকে দলের কাজ করতে দেখিনি৷ পুলিনদাদের সঙ্গে মিছিলে হাঁটতে দেখিনি৷ কোনও পক্ষের ভোটের প্রচারেও দেখিনি৷ তিনি আমাদের অন্যরকম বইয়ের কথা বলতেন, গল্প করতেন৷ এক সন্ধ্যায় পোস্টারের বান্ডিল নিয়ে এলেন৷ তিন লাইনের পোস্টার: ‘মিনার্ভায়/ কল্লোল/ চলছে চলবে’৷ আটা জ্বাল দিয়ে আঠা বা লেই তৈরি হল৷ পোস্টার সাঁটানোর অভিজ্ঞতা হয়েছিল করপোরেশনের ভোটে৷ সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগল৷ সব গলি জেনে গেল ‘মিনার্ভায় কল্লোল চলছে চলবে’৷ দুপুরে বাস দাঁড় করিয়ে তার গায়ে পোস্টার মারার ব্যাপারটা রীতিমত অ্যাডভেঞ্চারাস৷ একটা নাটকের জন্য লড়াই৷ নাটকের বিষয়টা তখনও এক-দু লাইনের বেশি জানি না।

কেন এভাবে পোস্টার মারতে হল? অসীমদা বলেছিলেন, খবরের কাগজগুলো এই নাটকের বিজ্ঞাপন ছাপছে না৷ নাটক নিয়ে আজেবাজে কথা তো লিখেছেই৷ বিজ্ঞাপন না ছেপে ওরা নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিতে চায়৷ এটা সরকারের চক্রান্ত৷ নৌবিদ্রোহে কংগ্রেস যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেই সত্য মানুষকে জানতে না দেওয়ার চক্রান্ত৷ সরকারের চাপে খবরের কাগজগুলো এই ব্যবস্থা নিয়েছে৷ আমাদের লড়াই সত্যের পক্ষে, চক্রান্তের বিরুদ্ধে৷ সত্যি বলতে কী, ইতিহাসের অত জটিল ব্যাপারস্যাপার আমরা তখন জানতাম না, বুঝতাম না৷ একটা বিশ্বাসের জায়গা থেকে সরকারের বিরুদ্ধে, নাটকের পক্ষে কয়েকদিন ধরে অলিগলি ঘুরে পাঁচিলে পাঁচিলে সংবাদ সেঁটেছি, বাসের পেছনে লেইয়ের টিন হাতে দৌড়েছি৷ মধ্য-ষাটের বাংলার বিক্ষোভ বিদ্রোহে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ ছিল বস্তির রিফিউজি ছেলেপুলেদের৷ ‘কল্লোল’ হয়ে উঠেছিল বিক্ষোভের একটা ইস্যু৷
অনেক পরে জেনেছি কী হয়েছিল সেদিন ‘কল্লোল’ নিয়ে৷ আনন্দবাজার, যুগান্তর ‘ইতিহাস বিকৃতি’র অভিযোগ আনে নাটকটির বিরুদ্ধে৷ এমনকি ‘বামপন্থী’ পরিচয় পত্রিকাও৷ প্রশাসনের তরফে নাটক বন্ধ করার জন্য ভূতুড়ে ফোন করা হয় অভিনেতাদের ভয় দেখিয়ে৷ পুলিশের ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্মীরা উঠেপড়ে লাগে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে৷ কংগ্রেসকর্মীরা হামলা করবার চেষ্টা করে৷ প্রধান অভিনেতাদের নামে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট জারি হয়৷ সেদিনের শাসকদলের ডাকাবুকো নেতা পুলিশকে হুকুম করেছিলেন৷ গ্রেফতার হন উৎপল দত্ত৷ তাঁর মুক্তির দাবিতে সভা হয় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সত্যজিৎ রায়, সবিতাব্রত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণাল সেন প্রমুখ৷
থার্টিনাইন বাই ওয়ান বস্তির সব বড়রা দল বেঁধে ‘কল্লোল’ দেখতে গিয়েছিল। সেটা অভিনয় শুরুর মাস চার-পাঁচেক পর, টিকিট এনে দিয়েছিলেন অসীমদা৷ দলে জুটে গিয়েছিলাম স্কুলবালক আমিও৷ এই ইস্যুতে যথারীতি গরম হয়েছে ইস্ট ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট৷ ইতিহাসের পরিকল্পিত বিকৃতির বিরুদ্ধে হয়তো গলা ফাটিয়েছেন শিবেনদা৷ উনুনে কাঁচা কয়লা ফেলার হুমকি দিয়েছেন হরিপদদা৷ ওঁরা টের পাননি বস্তির বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা সামিল হয়েছে নৌবিদ্রোহে৷
*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ১১ জানুয়ারি ২০২৩
ছবি সৌজন্য: PIXAHIVE, Unsplash.com, Twitter, লেখক
মধুময়ের জন্ম ১৯৫২ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহে, কিশোরগঞ্জে। লেখাপড়া কলকাতায়। শৈশব-যৌবন কেটেছে স্টেশনে, ক্যাম্পে, বস্তিতে। গল্প লিখে লেখালেখি শুরু। পরে উপন্যাস। বই আখ্যান পঞ্চাশ, আলিঙ্গন দাও রানি, রূপকাঠের নৌকা। অনুসন্ধানমূলক কাজে আগ্রহী। পঞ্চাশের মন্বন্তর, দাঙ্গা-দেশভাগ, নকশালবাড়ি আন্দোলন নিয়ে কাজ করেছেন। কেয়া চক্রবর্তী, গণেশ পাইন তাঁর প্রিয় সম্পাদনা। প্রতিমা বড়ুয়াকে নিয়ে গ্রন্থের কাজ করছেন চার বছর। মূলত পাঠক ও শ্রোতা।