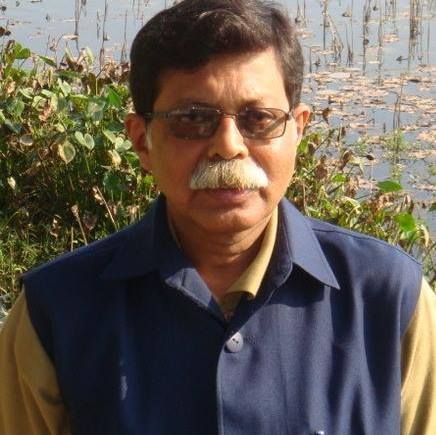ইস্ট জয়ন্তিয়া হিলস্ এবং ওয়েস্ট জয়ন্তিয়া হিলস্ মিলিয়ে দুই জেলার অন্তত শ’ পাঁচেক গ্রামে র্যাটহোল মাইনিং-এর কাজ চালু রাখার জন্য প্রয়োজন যে বিপুল শ্রমিকবাহিনী তা কোত্থেকে আসে? মেঘালয়ের যা জনসংখ্যা তাতে করে এত শিশু-কিশোর নিয়মিত নিয়োগ করা সম্ভব নয়। স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাগুলির সমীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রতিবেশী রাজ্য অর্থাৎ অসম, বিহার, মণিপুর এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই শিশু-কিশোর শ্রমিকদের আগমন।
প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপাল এবং বাংলাদেশও র্যাটহোল মাইন-এর শিশু শ্রমের যোগানদাতা। একবিংশ শতাব্দীতে অবিশ্যি বাংলাদেশ থেকে আসা শিশুদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে এসেছে। শোনা যায় গোড়ার দিকে মানে উনিশশো আশির দশকের সূচনা লগ্নে, যখন র্যাটহোল মাইনিং-এর প্রসার-বিস্তার শুরু হয় তখন নাকি কয়লা ভর্তি ট্রাক জোয়াই থেকে রওনা দিয়ে কখনও খালি অবস্থায় ফিরে আসত না। জোয়াই-এ এসে প্রতিটি ট্রাক উগরে দিত এক ঝাঁক নতুন শিশু অথবা কিশোর, যাদের উচ্চতা কম এবং চেহারায় রোগা-পাতলা। তাদের পরিচয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। খর্বাকৃতি এই শিশুদের কীভাবে সংগ্ৰহ করা হয়েছে তা কেউ জানতে চায়নি। সকলেই জানে যে আড়কাঠি সর্বত্র বিরাজমান। তাদের মাতৃভাষা নিয়ে কারও মাথা ব্যথা নেই। কোনও কোনও শিশুর গরিব মা-বাবাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে, প্রয়োজনে তাদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কখনও আবার অনাথ আশ্রম বা এতিমখানার সঙ্গে শলা করে এক লপ্তে তুলে আনা হয়েছে একঝাঁক শিশু। অনেকেই আবার পারিবারিক দারিদ্র নিরসনে বাড়ির বাচ্চাদের মেঘালয়ে পাঠিয়েছে।

এখনকার দিনে সকলের জ্ঞাতসারে এত বড় মাপের মানব পাচারের চক্রের খবর অন্য কোথাও পাওয়া গেছে কি? পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের সংসদে যখন শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করার আইন, মানব পাচার বন্ধ করার আইন, অবৈধ খননের বিরুদ্ধে আইন অথবা পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয় তখনই প্রতিবেশী রাজ্য ও রাষ্ট্র থেকে পাচার হয়ে চলে আসে হাজারে হাজারে শিশু যাদের শ্রমের বিনিময়ে জয়ন্তিয়া পাহাড়ের র্যাটহোল মাইন থেকে বেরিয়ে আসে কালো সোনা। দিনের আলোয় হারিয়ে যায় তাদের ঠিকানা-পরিচয় এবং মাতৃভাষা। সর্বোপরি লোপ পায় তাদের শৈশব-কৈশোর। তাদের তখন একটাই পরিচয় র্যাটহোল মাইন-এর শ্রমিক।
বাপুং, লাকাডং, লুম্পশং, মালওয়ার, মুসিয়াং, লামারে, মুতাং, শুতঙ্গা, জারাইন, ইত্যাদি এলাকার গ্রামগুলিতে র্যাটহোল মাইনিং-এর কাজ শুরুর আগেই ট্রাকে করে অথবা টাটা সুমো গাড়িতে চেপে কোত্থেকে যেন হাজির হয়ে যায় এক ঝাঁক শিশু-কিশোর শ্রমিক। জমির মালিক তাদের নাম ঠিকানা জানতে উৎসাহ প্রকাশ করেন কি? র্যাটহোল মাইনিং-এর জন্য যিনি অর্থ বিনিয়োগ করেছেন তাঁরও শ্রমিকদের নাম, মা-বাবার নাম, ঠিকানা প্রভৃতি জানার দরকার নেই। তিনি শুধু সর্দারকে চেনেন। সর্দার সাধারণত স্থানীয় জনজাতির মানুষ নয়। অধিকাংশই বহিরাগত। নেপাল অথবা অসম বা অন্য কোথাও থেকে কাজের খোঁজে আসা মানুষ।
কোনও কোনও শিশুর গরিব মা-বাবাকে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে, প্রয়োজনে তাদের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কখনও আবার অনাথ আশ্রম বা এতিমখানার সঙ্গে শলা করে এক লপ্তে তুলে আনা হয়েছে একঝাঁক শিশু।
সর্দারকে পুরুষ হতেই হবে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবে অবশ্যই স্থানীয় নয়। নবাগতদের দিকে তাকিয়েই সর্দার বুঝে নিতে চান কাকে কোন কাজে লাগাতে হবে। এক নজরে সর্দার বুঝে নিতে পারেন কে কুয়োর ভিতরে ঢুকে কয়লার সীম কাটতে কাটতে এগিয়ে যাবে, কাটা কয়লা ঝুড়িতে ভরে কে কুয়োর ভূগর্ভস্থ মুখে এনে জমা করবে অথবা মাটির ভেতর থেকে সেই কয়লা কে উপরে তুলে আনবে তারপর সেই কয়লা ভেঙে কে ছোট ছোট টুকরো করবে। এমনকি ভাঙা কয়লা ঝুড়িতে করে ট্রাকে তোলার কাজে কাকে লাগাতে হবে তা-ও সর্দার স্থির করেন। এছাড়াও মেকানিক, ছুতোর ইত্যাদি হিসেবে কাকে নিযুক্ত করা হবে সেসব সর্দারই ঠিক করে দেন। এ যেন আফ্রিকা থেকে আমেরিকা বা ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে নিয়ে আসা দাস ব্যবস্থার আধুনিক সংস্করণ।
সম্পূর্ণ অপরিচিত নতুন জায়গায় হঠাৎ করে পৌঁছে যাওয়ার পর প্রাথমিক পর্যায়ে হয়তো বিস্মিত হয়ে যায় নবাগত শিশু বা কিশোর। মা-বাবা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুদের থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন পরিবেশে থিতু হতে হয়তো তার কয়েকদিন সময় লাগে। ব্যস, ওই পর্যন্তই। কয়েকদিনের মধ্যেই সে পুরোদস্তুর কয়লা খনির শ্রমিক হয়ে যায়। তখন নাম, ঠিকানা, পরিচয় হারিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী নাটকের চরিত্রের মতো ৪৭ফ বা ৬৯ঙ গোছের কোনও এক নম্বরের শ্রমিকে সেই শিশু বা কিশোর রূপান্তরিত হয়ে যায়। অথবা এখনকার আধার কার্ডের নম্বরের মাধ্যমে সমস্ত ভারতীয় যেমন নতুন পরিচিতি পেয়েছে সেইরকমই নবাগত শ্রমিক পেয়ে যায় তার নতুন পরিচিতি।
খনি মুখের আশপাশে গজিয়ে ওঠা প্লাস্টিক-ত্রিপলের ছাউনিতে জোটে মাথা গোঁজার ঠাঁই। খড়ের বিছানা হলেও আপত্তি নেই। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, ওই ছাউনিই ভরসা। তীব্র ঠান্ডায় কীভাবে যে তাদের রাত কাটাতে হয় তার খবর কেউ রাখে না। কিন্তু অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে অনেকেই বাড়ির পথে রওনা দেয়। যাদের বাড়ি ফেরার সুযোগ আছে, তারা। অন্যথায় জল-ঝড়ে কোনওমতে রাত কাটানোই জীবন। প্রচণ্ড বর্ষায় অবিশ্যি উৎপাদন খানিকটা থমকে যায়। সর্দার থেকে শুরু করে তার ওপরওয়ালারা সেটুকু ক্ষয়ক্ষতি বাধ্য হয়েই মেনে নেন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে মার্চ-এপ্রিল অর্থাৎ প্রচণ্ড ঠান্ডার মরশুমে সেই ঘাটতি কড়ায় গন্ডায় পুষিয়ে নেওয়া হয়। শীতের সূর্য ভাল করে আকাশে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার আগেই শুরু হয়ে যায় র্যাটহোল মাইনিং-এর নিত্যকার ক্রিয়াকর্মাদি। পাহাড়-জঙ্গলের ফাঁকে পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরেও করে আঁধার ঘনিয়ে আসা পর্যন্ত চলতে থাকে রোজকার উৎপাদন প্রক্রিয়া। অবসরের এতটুকু অবকাশ নেই। নেই ফাঁকি মারার সুযোগ। চতুর্দিকে সর্দারের কড়া নজর।
শৌচাগার বলতে নীল আকাশের নীচে চরাচর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাহাড়ের মাঝে এক টুকরো জমি যার আশপাশে রয়েছে ঝরনা অথবা কোনও শীর্ণ নদী। তবে সে জল ভুলেও কেউ মুখে দেয় না। এমনকি সেই জলে স্নান করা তো দূরের কথা হাত-পা ধোয়াও নিষিদ্ধ। এমনিতেই র্যাটহোল খনির শিশু-কিশোর শ্রমিকরা কিছুদিন কাজ করার পরই নানানরকমের অসুখে ভুগতে শুরু করে। বাতাসে উড়তে থাকা কয়লার গুঁড়োয় শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। নেহাত বয়স কম বলে সহনশীলতা অথবা প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় মুখ বুঁজে কাজ করে যায়। তবে এই শ্বাসকষ্টের যন্ত্রণায় ভুগতে হয় সারা জীবন। অনেকেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত। বর্ষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই চলে আসে ম্যালেরিয়া। তার উপরে এইসব ঝরনা বা নদীর জল যা দূষিত হয়ে গেছে তা পেটে পড়লে ডায়রিয়া অবধারিত। হাত-পা ধুলে আঁকড়ে ধরবে ত্বকের নানাবিধ অসুখ।
ছবি সৌজন্য: minesandcommunities
প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ ও পরিচিত পরিকল্পনাবিশারদ। পড়াশোনা ও পেশাগত কারণে দেশে-বিদেশে বিস্তর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। তার ফসল বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বই। জোয়াই, আহোম রাজের খোঁজে, প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণে, কাবুলনামা, বিলিতি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।