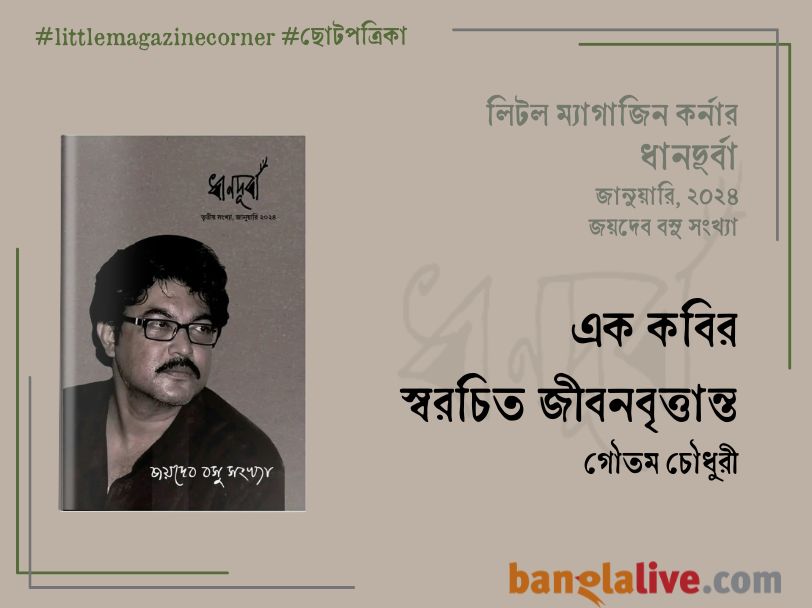১.
লেখকের যাপনের সহিত পাঠকের দেদার সমীপতা কিংবা বেহুদা ফারাক, এই দুই অবস্থানই নৈর্ব্যক্তিক রসাস্বাদনের কাজটি বন্ধুর করিয়া তুলে। ঘটনাচক্রে কবি জয়দেব বসুর সহিত যৌথস্মৃতিগুলি অনুরূপ টানা ও পোড়েনে বোনা বলিয়া, তাঁহার কাব্যকৃতি বিষয়ে কোনও নিরাবেগ মন্তব্য করিবার হক আমার আদপে আছে কি না, সেই দ্বিধা পহেলাই কবুল করিতে হয়। একদিকে ১৮ বছর বয়সী এক প্রখর, শানিত ও মায়াময় সদ্যতরুণ জয়দেব, যাঁহার গোপন কবিতাগুলির ক্রম-উদ্ভাসনের নিবিড়তায় আমাদের জড়াইয়া থাকা। অন্যদিকে, যুগ না ঘুরিতেই, পশ্চিমবাংলার তৎকালীন কাব্যরাজনীতির জটিল রন্ধ্রপথে, বহু মানুষ যেখানে সূচ হইয়া সিঁধাইয়া ফাল হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইবার এবাদতে রত, আপন যোগ্যতাবশে সেই আলিশান অদৃশ্য কারখানায় বড়দরের কর্মকর্তা হইয়া উঠা জয়দেব। যে-অবস্থানের পূর্বশর্তই ছিল, আমাদের মতো প্রান্তিক কয়েকজনের বেহেড বিরোধিতা। ফলত সেই প্রেমিক মানুষটির সহিত পয়দা হইল এক দুষ্পাচ্য দূরত্ব। এবং সেই বার্লিন-প্রাচীর ভাঙিতে ভাঙিতে এই শতকের প্রথম দশকটিও প্রায় কাবার। যে-পুনর্মিলনের জন্য কবি সৌম্য দাশগুপ্তর কাছে আমার অকুণ্ঠ ঋণ। (Little Magazine)
ইতোমধ্যে দুনিয়ায় অনেক সরকার আসিয়াছে গিয়াছে। মানুষের হাতে মানুষের রক্ত ঝরিয়াছে হিমবাহে, মরু-প্রান্তরে, রাজপথে, পাড়াগাঁয়। মেরুচূড়ার বরফ গলিতেছে গলগল করিয়া। দেখিলাম, জয়দেবও পাল্টাইয়া গিয়াছেন এন্তার। তাঁহার তর্ক ও অনুসন্ধান নানান অজানা দিকে বিস্তারিত হইয়াছে। এক ভিন প্রেক্ষিতে তাঁহার সহিত এক ভিন্ন ধরনের যৌথতা গড়িয়া উঠিল আবার। খ্রিস্টীয় আধুনিকতা ও ব্রাহ্মণ্য বর্ণহিন্দুবাদ শাসিত পশ্চিমবঙ্গীয় মননে যেসব প্রসঙ্গ কোনও রূপ ঢেউ তুলে না, বুঝিবা তেমন কিছু তুচ্ছ বিষয় লইয়া এই শহরে আলাপের প্রায় একমাত্র মানুষ হইয়া উঠিলেন জয়দেব। এমন কি, যে-ভঙ্গীতে তাঁহাকে লইয়া এই সামান্য বয়ানটি রচনার মকশ করিতেছি, তাহার পিছনেও তাঁহার তেরছা প্রবর্তনা কিছুটা কাজ করিতেছে। কিন্তু হায়! আমা হইতে ঠিক এক দশক পরে দুনিয়াতে আসা আমার এই বন্ধুটি, সহসা চলিয়া গেলেন। দুই-তিন ঘণ্টার বেদনা-প্রকাশের সামান্য সুযোগ পাইলেন মাত্র। প্রিয় পাঠিকা প্রিয় পাঠক, অবিশ্বাস করিলে করুন, মাতৃবিয়োগের পর এতবড় শোক ইতিমধ্যে অনুভব করি নাই। (Little Magazine)
তাঁহার জীবনের কথা আর যে বড় একটা জানি, তাহা নয়। বা, যাহা জানি, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। কাজেই সেইসব কথা থাক। বরং তাঁহার যে-জীবন পরিকীর্ণ হইয়া আছে তাঁহার নানান রচনার হরফে হরফে, আসেন আমরা সেইদিকে চোখ ফিরাইতে কোশেশ করি। তাঁহার তরুণ হাসির আড়ালে আসলেই আগুন ঢাকা ছিল। ব্যক্তিগত এক মেঘদূতের বিস্তীর্ণ মন্দাক্রান্তায় যখন সে-পাবক উদগত হইল, বালকবীরের বিশ্বজয় করিতে খুব একটা দেরি লাগিল না-
ঘটুক নিষ্ক্রমণ, যে পথ দিয়ে তুমি এসেছ সেই পথে ফেরো আবার দুপাশে দেখবে মিতা, নিসাড় শুয়ে আছে কুকুরকুণ্ডলী বহু মানুষ তাদের শিয়রে এসে আসনপিঁড়ি বোসো, প্রলম্বিত লয়ে গহন শ্বাস পড়ছে, এরাই হল আমার স্তোত্রের প্রজ্ঞাপারমিতা, জনার্দন
শ্লোক ১২৩, মেঘদূত
পথের দুইপাশে কুকুরকুণ্ডলী হইয়া নিঃসাড়ে শুইয়া থাকা মানুষজনকে ধ্রুপদী আঙ্গিকের ভিতর এইভাবে জায়েজ করিয়া তুলিবার প্রকৌশলটি লোকে খাইতেছে দেখিয়া ২৩ বছরের তরুণ এক করুণ দোটানায় পড়িলেন। প্রায় একই সময় একটি স্বতন্ত্র কবিতায় তিনি লিখিলেন- ‘তোমাদের হাত থেকে টাকা নিই, বোধ নিই, বিবেকখচিত এক পিকদানি নিই। গলা শিরদাঁড়া তাতে ধরে রাখি’। কবিতাটি শেষ হইল এই নির্মম উপলব্ধিতে ‘বোঝা যায়, আরো বহুদিন তোমাদের উপদংশে চুমু খেতে হবে’। কবিতাটির নাম ‘বুদ্ধিজীবী’, রচনা ১ এপ্রিল ১৯৮৫। প্রসঙ্গত, জয়দেবের মেঘদূত রচনা শেষ হয় ২৪ মে ১৯৮৫। বহি হইয়া প্রকাশিত হয়, ১৯৯০ সালের বইমেলায়। (Little Magazine)
ওই একই বইমেলায় প্রকাশিত হয় তাঁহার আরও একটি কবিতাবই, ‘ভ্রমণকাহিনি’। বস্তুত ১৯৮৫ হইতে ১৯৯০, এই সময়কালে রচিত কবিতাগুলি জয়দেবের একাধিক কেতাবে ছড়াইয়া আছে- ‘ভ্রমণকাহিনি,’ ‘ভবিষ্যৎ’ (প্রকাশ ১৯৯২), ‘জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার ও অন্যান্য’ (প্রকাশ ১৯৯৪)। এমন কি তাঁহার সর্বশেষ প্রকাশিত কবিতাবই ‘সাইকোপ্যাথ’- এও এই পর্যায়ের কবিতা কিছু রহিয়া গিয়াছে। বোধ করি, পরিমাণের দিক দিয়া এই সময়টিই তাঁহার কবিতাজীবনের সর্বাধিক ফলপ্রসূ সময়।
‘ভ্রমণকাহিনি’ বিখ্যাত হইয়া উঠে তাহার উৎসর্গপত্র হইতেই, যাহা একটি রাজনৈতিক দলের প্রতি এহেন এক গভীর আবেগ লইয়া উচ্চারিত- ‘তুমিই চিনিয়েছিলে সন্ধ্যার ধ্রুবপথ, নিখিল জলের নীচে ভোমরার ভীত আর্তনাদ। নামহীন, গোত্রহীন আমি তাই বেঁচে আছি রাক্ষসনগরে’। কিন্তু বহিটির পাতা উল্টাইয়া আমরা টের পাই, একজন তরুণ কবি কীভাবে দেখিতেছেন তাঁহার সমসাময়িক বাংলা কবিতাকে- ‘…যেমন নির্জীব হয়ে পড়ে আছে বাংলার লিরিক কবিতা’। কীভাবে দেখিতেছেন তাঁহার অব্যবহিত কাব্য-পরিমণ্ডলকে- ‘তাহলে কীভাবে বলো খাপে-খাপে ঢুকে পড়ব আমলাবাগানে? অথবা কবির দলে- ভঙ্গবঙ্গজোড়া খেউড়ের সুনিশ্চিত অন্ধকার নীড়ে?’ তিনি সেই নির্জীব লিরিককে ভাঙিবার জন্য গদ্যস্তবকের এন্তেজাম করিলেন। প্রশ্ন তুলিলেন- ‘যে জন ডিভোর্স দেয় শবদে শবদে সেও কেন কবি নয়? যদি সেই দম্পতি হয়ে থাকে পুরাতন- সরস্বতীহীন?’ বেঞ্জামিন মোলাইজের মৃত্যুর পটভূমিতে বাংলা বাইবেলি ঢঙে লিখা কবিতাখানি এবিষয়ে তাঁহার সাফল্যের এক আশ্চর্য নমুনা। সেই দীর্ঘ কবিতাটি হইতে সামান্য একটু অংশ তুলিবার লোভ সামলাইতে পারিতেছি না-
… আমি এক নূতন আকাশমণ্ডল আর এক নূতন পৃথিবী দেখিলাম। কারণ প্রথম আকাশমণ্ডল আর প্রথম পৃথিবী অন্তর্হিত হইল। এবং, সমুদ্রের আর অস্তিত্ব রহিল না। আমি দেখিলাম পবিত্র নগরী, নূতন বান্টুস্তান-সে স্বামীর নিকটে বিভূষিতা বধূর ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল।
পরে আমি শুনিলাম, মৃত্যু আর থাকিবে না। শোক, আর্তনাদ বা বেদনাও আর থাকিবে না। কারণ সমস্ত প্রথম বিষয় অতীত হইল।
পুনরুত্থান / ভ্রমণকাহিনি
কিন্তু এতকিছুর পরেও কবি যে সেই লিরিকের হাতেও কিছু ধরা খাইবেন, তাহারও নমুনা রাখিলেন-
শহর থেকে এনেছি কবিওলা
বেজায় বোলবোলাও
নাম- জয়দেব, বেসুরো গান করেন:
“কী ভালো যে বাসি তোমায় জানেন শুধু লরেন্স…”
প্রণয়মঙ্গলা / ভ্রমণকাহিনি
‘ভ্রমণকাহিনি’-র প্রায় পাশাপাশিই রচিত হইতেছিল ‘ভবিষ্যৎ’ নামক যে- গ্রন্থের কবিতাগুলি, তাৎপর্যপূর্ণভাবে বহিনির্মাণের পর দেখা গেল, তাহার প্রথম কবিতার শিরোনাম ‘বিপ্লব’ (১১ মার্চ ১৯৮৫), আর শেষ কবিতা হইল ‘নিজেকে দেখুন’ (২৫ মে ১৯৯০)। নিজেকে দেখার সহিত বিপ্লবের কোনও বিরোধিতা আছে, এমন নহে। দেখি, নিজের ২৩তম জন্মদিনে জয়দেব
লিখিতেছেন (৯।৫।৮৫)-
তোর থেকে কিছু চাই না। শুধু তুই আয়। আমি আরও একবার তোর মুখোমুখি বসি। এই ধুলো আমার দেশের। এই ঝরাপাতা, এই সন্ধ্যা, দিগন্ত অবধি এই শাঁখের আওয়াজ- এই সবই আমার জীবন। তুই আয়, আমি তোর হাতে তুলে দিই দারিদ্র্যরেখার এই দেশ।
তেইশতম জন্মদিন / ভবিষ্যৎ
সরল ও সুনির্মল আন্তরিকতায় তিনি এইভাবে এক ও বহুকে মিলাইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু এই মিলন ঘটাইবার জন্য যে-জমিনটি তাঁহার বরাদ্দ, তাহা যে স্রেফ কবিতা, অন্য কিছু নহে, এই সত্যটি যেন, বিগত শতকের সেই ৮০র দশকের উপান্ত অবধি, তিনি বহুদূর মানিতে চাহেন নাই। বা, অন্তত, তিনি যে কবিসমাজের কাছে ‘অপর’ প্রাণপণে এমন এক অহঙ্কার বজায় রাখিতে চাহিয়াছেন। যেমন-
১. এরকমই এক যুবক সে, তার কোনো নাম নেই/ প্রাতিষ্ঠানিক ছন্দ ভেঙেছে নিজের সমাজে/ এই অপরাধ স্থান খুঁজে তার দিয়েছে দারুণ/ ঊষর চূড়ায় (ভূমিকা / মেঘদূত)
২. কবিতাটবিতা নয়, সেসবের চেষ্টাও নয়, সোজা-সাপ্টা কথা আছে কিছু। (রাধাকথন / ভ্রমণকাহিনি)
৩. আমি কি তরুণ কবি?… তরুণ কবিরা শুনি অনেকেই অতিবিপ্লবী। কেউ কেউ দাড়ি রাখে, কেউ যায় খালাসিটোলায়। বাকি সব করে রব এখানে সেখানে। (দুশ্চিন্তা / ভ্রমণকাহিনি)
৪. এত কিছু লিখে সেই তরুণটি দেখতে পেল তার লেখা কংক্রিট না অ্যান্টিও না এমনকি পোইট্রিও হয়নি এখনও (মানসযাত্রা / নীলোৎপল তরুণের কথা / ভবিষ্যৎ)
৫. … আমার কবিতাও হায়- কিস্যু হয় না, কফির টেবিল থেকে নিঘিন্নে বৃহন্নলা হেঁকে বলে, ‘অপাঠ্য এসব’, চনমনে তরুণরা ভদ্রতা করে বলে- আরো লেখো, মন দিয়ে লেখো। বলে… লেখো। বলে- হচ্ছে না হচ্ছে না হচ্ছে না… (কলম্বাসের ডিম / ভবিষ্যৎ)
৬. কবিতা লেখার আগে দু’বছর পোস্টার সেঁটে নেওয়া ভালো (জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইস্তাহার: এক)
কিন্তু কবিতা ও কবিসমাজ লইয়া এতসব ঘোষিত বিরক্তি সত্ত্বেও, ১৯৯০ সাল বরাবর পঁহুছিয়া দেখা গেল, কখন যেন তিনি প.বঙ্গীয় কাব্যরাজনীতির দ্বারা আত্তীকৃত হইয়া পড়িয়াছেন। ‘ভবিষ্যৎ’-এর আখেরি কবিতা নিজেকে দেখুন-এ সেই ঘটনারই নির্মল আত্মস্বীকৃতি ফুটিয়া উঠিল এইভাবে- ‘আমাকে ঘিরে গজিয়ে উঠেছে অসাধারণ সব সমস্যা,/ অর্থাৎ, দেশ পত্রিকায় লিখব কি না, পার্টিতে আর কদ্দিন আছি,/ কে আমার প্রোমোটার শঙ্খবাবু না সুনীল গাঙ্গুলি’। এইভাবে কবিসমাজের একজন বলিয়া নিজেকে মানিয়া লওয়ার ভিতর দিয়াও জয়দেব একভাবে এক ও বহুকে মিলাইলেন। এইবার তিনি সেলিব্রিটি কবি হইলেন।
২
জয়দেব আন্তরিকভাবেই লিরিকের বিরুদ্ধে ছিলেন। ফলত, নানাসময় নানা-বিধ গদ্যভঙ্গিই তাঁহার অবলম্বন হইয়াছে। এমন কি প্রগতিবাদীর কাছে অস্পৃশ্য ক্ষুধার্তদের বান্ধারাও ক্বচিৎ তাঁহার জবানে আসিয়া ভর করিয়াছে-
আমার কাটা আঙুল, ভাঙা পাঁজর, থ্যাঁৎলানো বিচি- তা তোমাকে সপ্তাহান্তে অপরাধী করে। অর্থাৎ বিবেক ও বাতকর্মের মধ্যে কোনো সীমাই তুমি অবশিষ্ট রাখনি।
বাগি / ভবিষ্যৎ
অন্যদিকে, অধিক অধিকতর পাঠকের কাছে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষাটিও আদর্শের কারণে তাঁহার ফরজ ছিল। ফলত, না-কবিতার ছদ্মবেশে একপ্রকার বুঝাইয়া বলা গদ্যের অতিকথনের দিকে তাঁহার কাব্যভাষা টাল খাইতেছিল। অথচ, তাঁহার কবি-আত্মার গহনে শুরু হইতেই ছিল এক ধ্রুপদীয়ানার আঁশ। ‘মেঘদূত’-এরও আগে ১৯৮৩ সালে তিনি ‘রাধেয়-অধিরথসূত’ নামে একটি কবিতার মুসাবিদা করেন। পরে, ১৯৮৬-তে ঘষামাজা করিয়া তাহার চূড়ান্ত রূপ দেন ও ‘ভ্রমণকাহিনি’-তে সংকলিত করেন। প্রকাশিত কবিতাসমূহের ভিতর সম্ভবত এটিই তাঁহার প্রাচীনতম রচনা। অন্তর্নিহিত এই শক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার ঘটিল ‘জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়’ (প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ১৯৯৩) পুস্তকে।
তিনটি সুদীর্ঘ কবিতায় জয়দেব এইখানে নিজেকে যথাসাধ্য উজাড় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং তাঁহার দূরস্পর্শী সাফল্য আমাদের ব্যথিতই করে এই জন্য যে, তিনি তাঁহার এই আপন ক্ষেত্রটি যথাযথ চিনিতে পারিলেন না। বা, চিনিতে পারিলেও, ততদূর মনস্থাপন করিতে পারিলেন না, যাহাতে বাংলা ভাষায় মধুসূদনের পর আমরা আরও একজন প্রকৃত মহাকবিকে পাইতে পারিতাম। তাঁহার পরবর্তী কবিতাবই ‘জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার ও অন্যান্য’ (প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪)-এর বেশ কিছু রচনাতেও এই মহাকবিতার আভা ইতস্তত ছড়াইয়া আছে। এই পুস্তকের একটি উপপর্ব হে প্রাণ, সমষ্টিপ্রাণ…-এর অন্তর্গত একটি কবিতা হইতে সামান্য একটু অংশ উদ্ধার করা যাক-
আমাকে উদ্ধার কর- হে প্রাণ, সমষ্টিপ্রাণ, তুচ্ছতম জীবকোষে- ব্যাপ্ততম নীহারিকা দেশে শূন্যতার ওপার যে শূন্যতর অর্থবহ অতীব শূন্যতা যে শূন্য চিরগতি বৈজয়ন্ত, আনন্দস্বরূপ সে তুমি প্রকাশ হও আমাকে আঘাত করো ছিন্ন করো বন্ধ প্রতিবেশ- আমাকে রক্ষা করো, শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি প্রতিদিন…
আমাকে উদ্ধার করো… হে অদিতি… হিরণ্যগর্ভ কাল
কালের অতীত…
জাতক / জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার ও অন্যান্য
প্রিয় পাঠিকা প্রিয় পাঠক, এহেন কবিতার রচয়িতাকে স্রেফ ‘রাজনৈতিক কবি’ বা ‘দলীয় কবি’ তকমা লাগাইয়া দেওয়া যে তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচার, আপনারাও আশা করি এই অনুভবের শরিক হইবেন।
তবে রাজনীতিহীন কোনও বিশ্বে আমরা কেহই যেরূপ বসত করি না, জয়দেবও তাহার ব্যতিক্রম নহেন। ব্যক্তি হইতে ব্যক্তিতে যেমন নানা বিষয়ে আসক্তির তারতম্য ঘটে, নানান রাষ্ট্রনৈতিক কর্মকাণ্ডে তিনিও সেইভাবে আগ্রহ অনুভব করিতেন। হয়তো অনেকের চেয়ে ঢের বেশি করিতেন। ফিলহাল বাংলা ভাষার অপর একজন প্রধান কবি প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ পশ্চিম-বাংলার একজন অন্যতম সেরা ফুটবল বিশেষজ্ঞও বটেন। বিশ্বফুটবল লইয়া বছর ২৫ পূর্বে রচিত তাঁহার কেতাবটি তো ইতিমধ্যেই খেলাপ্রেমীদের কাছে প্রায় একটি ধ্রুপদী আকরবহি হইয়া উঠিয়াছে। তাই বলিয়া তাঁহার উত্তর কলকাতার কবিতা কি স্রেফ ফুটবলের আলোকে ব্যাখ্যা করিবার কথা কেহ ভাবিতে পারেন!
৩.
‘ভবিষ্যৎ’ কবিতাবইটির সূচনাপত্রে মিখাইল বাখতিন-এর শিল্পপ্রতিভা ও দায়বদ্ধতা হইতে যে খানিক উদ্ধৃতি জয়দেব দিয়াছিলেন, তাহার একটি পঙ্ক্তি এইরূপ- ‘জীবন ও শিল্প শুধুমাত্র পারস্পরিক দায়িত্বই বহন করে না,-(পারস্পরিক) ভ্রান্তিও বহন করে।’ ১৯৯০ সালে যখন তাঁহার বয়স মাত্র ২৮, মায়াকোস্কির বয়ানে জয়দেব আমাদের মৃত্যুর কথা শুনাইলেন-
কে আমাকে প্রতিদিন বলত- বেঁচে থাকো।
কেউ তোমাকে চায় বা না চায়- বেঁচে থাকো দুঃখে থাকো, আনন্দে থাকো- বেঁচে থাকো। আর, লেখো আর বেঁচে থাকো আর লেখো আর বেঁচে থাকো…
মনে পড়েনা, আমার কোন স্বর মনে নেই।
আ, কেন আপনি এত নাছোড়বান্দা সিস্টার, কী করবে সে বেঁচে থেকে, সে অন্যের কোন কাজেই আসে না?
মায়াকোভস্কির শেষ সাতদিন / জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার ও অন্যান্য
তাহা হইলে, কবিতা লইয়া, কবিসমাজ লইয়া, কবিজীবনের শুরুয়াত হইতেই জয়দেবের যে-অস্বস্তি, বাংলা কবিতার দিগন্তে উজ্জ্বল এক তারাকবি হইয়াও, সেই অস্বস্তিবোধ কি তাঁহাকে নিস্তার দিল না! কবিতা লিখা কি ততদিনেও তাঁহার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ এক কাজ বলিয়া প্রতিভাত হইল না, যাহাতে লিপ্ত থাকিলে অন্যের কাজেই আসা হইল বলিয়া প্রত্যয় হয়? এইভাবেই কি অন্যের কাজে আসিবার ভূত তাঁহার উপর চাপিয়া বসিল? এইসব সওয়ালের জবাব আমরা জানি না।
আমরা শুধু দেখি, এক রাক্ষসের শক্তি লইয়া অজস্র সহস্রবিধ ‘কাজের’ ঘূর্ণিপাকে তিনি কেবলই জড়াইয়া পড়িলেন। উপন্যাস রচনা, অধ্যাপনা, বক্তৃতা, সেমিনার, উৎসব সংগঠন, টিভির মেগা ধারাবাহিকের চিত্রনাট্য, মায় সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে খবর কাগজের উত্তরসম্পাদকীয়। শুধু বোধ হয় ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীই তাঁহার এই কর্মকাণ্ডের বাহিরে পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই ঠাট্টার আড়ালে যে-ভয়ঙ্কর প্রশ্নটি চাপা পড়িয়া গিয়াও পুনর্বার মুখ বাড়ায়, এই সবই কি তিনি করিয়া চলিতেছিলেন বাঁচিয়া থাকাকে নিজের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য করিয়া তুলিবার জন্য! নহিলে, এ-কথা তাঁহাকে দিয়া কে লিখাইল-‘কী করবে সে বেঁচে থেকে, যে অন্যের কোন কাজেই আসে না?’
এই সমূহ তৎপরতার জন্য তাঁহার অমানুষী প্রতিভাকে হয়তো সালাম জানাইতেই হয়। কিন্তু ‘আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ’ (প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯) বহির সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৯৯৪ সালের পর তাঁহার কবিতারচনা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। সমসাময়িক যে-দুএকটি অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতে আর যাহাই হউক, কোনও মহাকবিতায় উড়াল দিবার স্বপ্ন পাঠক বরাবর সঞ্চারিত হয় না-
১. এতদিন যারা ছিল ইমানের রক্ষী/ মোটামুটি আজ ফিরিঅলা সব্বাই।
২. নিরীহ লোকের গায়ে কালশিটে, চাঁদার জুলুম,/ শনি-মন্দিরের পাশে চোলাই আর সাট্টার ধূম।
৩. কিছু কি ঘটবে এরপরও,/ সাইনবোর্ড পালটে ফেলা ছাড়া?
৪. মাঝে-মধ্যে মনে হয় উঠে দাঁড়াই। বেরিয়ে পড়ি। কিন্তু, কী লাভ?
সন্ধ্যা নামলেই মাথার ভিতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। শরীর কোনো সান্ত্বনা দেয়না। নিবিড়তা মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন বঞ্চনাগুলির কথা। আর, ও নিশান, তোমার এই কীটদষ্ট রূপ আমার ভালো লাগেনা ভালো লাগে না
তবু তোমাকেই প্রণাম। তোমার এই জীর্ণতার বিনিময়েই আমি পেয়েছি অপেক্ষা ও উপবাসের দীক্ষা- এককথায়, পরিণতি।
কিন্তু এই ‘অপেক্ষা ও উপবাসের দীক্ষা’ যে-পরিণতিতে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিল তাহা এক হিমশীতল স্তব্ধতার অন্ধকার উপত্যকা মাত্র। যেখানে হয়তো জীবনের আর সব আয়োজনই রহিয়াছে, শুধু কবিতা নাই। ২০০০-০২ সালের পর কবিতা জয়দেবকে ছাড়িয়া গেল। ওই সময়ের একটি কবিতায় তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন- ‘বো-শিল্প-কমুনিস্ট এ সব জড়িয়ে, আমি জানি,/ নষ্ট করেছে এই কলমের অবিরত অপূর্ব বাখানি’ (০১-০৩- ২০০০)।
ইহার পর প্রায় ভস্ম হইতে উঠিয়া আসা পৌরাণিক পাখির মতো ২০০৭ নাগাদ আবার কবিতায় ফিরিলেন জয়দেব। পুরানো-নতুন কবিতা লইয়া আরও দুইখানি কেতাব, ‘আর-এস চতুর্দশপদী’ ও ‘সাইকোপ্যাথ’, সংযোজিত হইল তাঁহার রচনাপঞ্জীতে। কিন্তু কোনও কাব্যিক পুনরুথানের পক্ষে সময়টি তাঁহার দিক দিয়া অনুকূল ছিল না। আত্মনির্মাণের যে-সঞ্চারপথ তিনি আকৈশোর কবুল করিয়াছিলেন, পাল্টাইয়া যাওয়া বাস্তবতা যেন সেই পবিত্র কল্পলোকের সম্মুখে প্রতিস্পর্ধায় মুখোমুখি দাঁড়াইয়া-
-দেখতে পাচ্ছি… অশ্রুতে সব আবছা… কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সব…
-কথা বোলো না, দেখতে থাকো, সময় বেশি নেই….
-কিন্তু ওরা কারা! ওরা যে আমার হাতেই খুন, অবাস্তব!
-অবিশ্বাসী! বাস্তবতা এই মুহূর্তে তোমার সামনেই….
কবিতা ৩২, আর-এস চতুর্দশপদী
প্রসঙ্গত, কবিতাটির রচনা-তারিখ ৮ মার্চ ২০০৭, পশ্চিমবাংলার চলতি ইতিহাসের একটি সন্ধিলগ্ন! ফলত, নানান আত্মকৌতুক যেন তাঁহার গূঢ় অন্তর্লীন বিষণ্ণতাকে চাপা দিবার জন্য কেবলই মুখর হইয়া উঠিয়াছে এই সময়ের কবিতায়। সেইসব লঘু পরিহাসের ভিতর ঘাপটি মারিয়া থাকা দুইটি লাইনে সহসা আমাদের চোখ আটকায়-
মদেই শেষ আশ্রয়? নয়। আমিও জানি সেইটাই ভয়, ওগো পাঠক,
কক্ষনো না, না।
তার চে’ বরং টিকিট কেটে পাতাল রেলের স্টেশন থেকে…তবুও জেনো ওটাই মোক্ষ না।
কবিতা ৩৭, আর-এস চতুর্দশপদী
আমরা শিহরিত হই, আমরা বুঝিতে পারি না, ‘পাতাল রেলের স্টেশন থেকে…’-র ভয়ঙ্কর প্রস্তাব কবির মনে আদৌ উত্থাপিত হয় কেন? ইহা কীসের আলামত? তখন মনে হয়, মৃত্যুর ভয়াল মুখের গড়াইয়া পড়া ছায়া হইতে আত্মচিকিৎসার মতো এই কবিতাগুলি ডানা মেলিতে চাহিয়াছিল। তখন লক্ষ করি, ‘সাইকোপ্যাথ’ গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করিয়াছেন এক চিকিৎসককে।
জয়দেবকে লইয়া এই আলাপের যেখানে নূতন করিয়া মোহরত হইতে পারিত, সেইখানে আসিয়া তাহা সহসা হোঁচট খাইয়া পড়িল। মদে নয়, কবিতাতেই যে তাঁহার শেষ আশ্রয়, তাহা জানাইতেও তিনি কসুর করেন নাই। কিন্তু আমি সে-কবিতা পড়িলাম তাঁহার মৃত্যুর পর।
লেখা আমার মা, আমায় ছেড়ে যেন তুমি কোথাও যেও না
এই যে এত আলস্য আর নিজেকে এত ঘৃণা ঘোষিত নির্বিবেক থেকে অমানদক্ষিণা, এ-সব থেকে নিষ্ক্রমণের তেমন কোনো ভূমি থাকলে পরে সেই মাটিতে পৌঁছে দিও তুমি।
লেখা আমার মা, আঁচল দিয়ে আগলে রেখো, কোথাও যেও না।
বাতাস যদি নিজেকে দেয় বীজন গন্ধ যদি নিজের ঘ্রাণে আকুল, পানীয় যদি নিজেকে পান করে জীবন তবে নিজের সমতুল। লেখা কি তবে নিজেকে লিখে যায়, মা কি আমি….আমিই তবে মা? আমায় ছেড়ে যেন আমি কোথাও যাই না।
লেখা আমার মা / অগ্রন্থিত
এমন একটি কবিতা লিখিবার পরও কেন যে তিনি সহসা এইভাবে নিজেকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, সেকথা ভাবিয়া ভিতরে ভিতরে এক গুনাহগারি বোধ করি। মনে হয়, তাঁহার তরুণ হাসির আড়ালে যে কোন্ রহস্যময় আগুন ঢাকা ছিল, আমরা কেহই তাহা ঠিকঠাক টের পাই নাই।
(‘লেখকের বহুবচন, একবচন’ গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত)
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।