আমরা সবাই বই ভালবাসি, বই নিয়ে আমাদের আবেগের শেষ নেই, বইকে নিয়ে মেলা, খেলা, ব্যবসা, অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি-চর্চা সবই গড়ে উঠেছে। বই সবসময় মানবিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে । এমনকি বই দেশের অগ্রগতির জন্য অনুঘটক হিসাবে কাজ করে বলেও মনে করা হয়।
বর্তমানে বই প্রকাশনা সেক্টরটি ৩০% এর একটি চক্রবৃদ্ধি বার্ষিক হারে (CAGR) বর্ধিত হচ্ছে। ভারতের বই বাজারের গুরুত্ব সারা বিশ্বে স্বীকৃত হয়েছে, ২০০৯ সালের লন্ডন বইমেলায় বই বাজারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতবর্ষ। ভারতের বই বাজারে বর্তমানে ইংরেজি সহ ২৪টি ভাষায় প্রতি বছরে এক লাখের উপর নতুন বই প্রকাশিত হয়। ভারতীয় প্রকাশনা বাজার অ-সমজাতীয় এবং তা অঞ্চল অনুযায়ী ও ভাষা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। ভারতে প্রকাশিত মোট বই-এর অর্ধেকেরও বেশি হিন্দি এবং ইংরেজিতে, হিন্দি প্রায় ২৬%, এরপর ইংরেজি ২৪%।
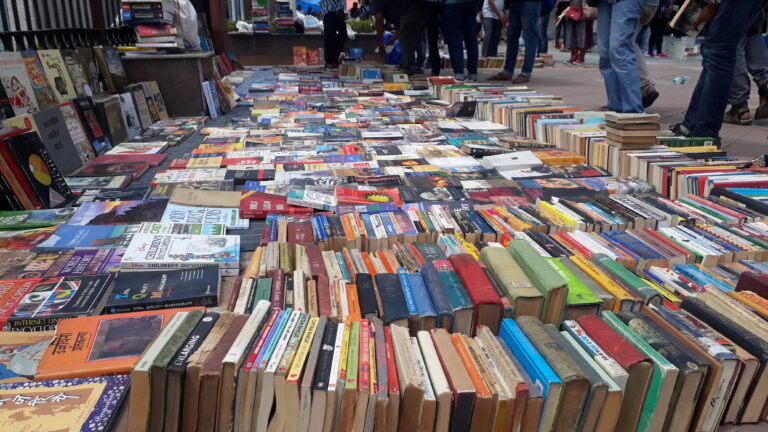
ভারতের পাঠ্যপুস্তকের বাজারে সরকারি প্রকাশনা সংস্থাগুলির আধিপত্য বেশি। ১৯৬১ সালে এনসিইআরটি (NCERT) স্থাপনের পূর্বে পাঠ্যপুস্তকের বাজারে মুষ্টিমেয় বিদেশি প্রকাশকের আধিপত্য ছিল। বর্তমানে সরকারি সংস্থা এনসিইআরটি, প্রতিটি রাজ্যের পুস্তক পর্ষদ, এনবিটি (ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট) এবং প্রকাশনা বিভাগ (পাব্লিকেশনস ডিভিসন) পাঠ্যপুস্তকের ক্ষেত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
ভারত সরকার প্রকাশনা সংস্থাগুলিকে ১০০ শতাংশ এফডিআই করার অনুমতি দেয়। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, লন্ডনের অনেক বিদেশি প্রকাশনা সংস্থা ভারতে তাদের নিজস্ব ইউনিট খুলেছে। ভারতকে প্রকাশনা শিল্পের শীর্ষ পাঁচটি দেশের মধ্যে গণনা করা হয়। ইংরেজি ভাষার বই-এর ক্ষেত্রে ভারত পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম প্রকাশক, আমেরিকা আর লন্ডনের পরেই। ভারতের প্রকাশনা শিল্পের বর্তমান বাজার মূল্য আনুমানিক ১২,০০০ কোটি টাকার ।
এ হেন প্রকাশনা শিল্পের মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর সংখ্যা ভারতে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অপ্রশিক্ষিত কর্মীর সংখ্যা অত্যধিক। অথচ বই যে ধরনের বস্তু, এর নির্মাণে অপ্রশিক্ষিত কর্মীর থেকে প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন বেশি। অথচ আমাদের অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই বই কীভাবে তৈরি হয়। স্বল্প পরিসরে আমরা বইপাড়ার পর্দার আড়ালের কাজকর্ম একবার দেখে নিতে পারি। গ্রন্থ-নির্মাণ শিল্পের নেপথ্যে আছে দুটি বিভাগ ।
গ্রন্থ নির্মাণ শিল্প
নির্মাণ বিপণন
১। সম্পাদনা বিভাগ ৩। প্রচার
২। উৎপাদন বিভাগ ৪। বিক্রয়
পাণ্ডুলিপি (Manuscript)– হাতে লেখা বই-এর সম্পূর্ণ খসড়াকে পাণ্ডুলিপি বলে। লেখক তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রকাশনা সংস্থায় জমা দিতে পারেন। কোনও প্রকাশনা সংস্থাতে পাণ্ডুলিপি অযাচিতভাবেও (নিজের থেকে) কেউ জমা দিতে পারেন, সেক্ষেত্রে সেই পাণ্ডুলিপিকে অযাচিত পাণ্ডুলিপি বা আনসলিসিটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট (Unsolicited Manuscript) বলা হয়। প্রকাশনা সংস্থার তরফেও নিজে কোনও বিশেষ বিষয়ে বই তৈরি করতে বা লিখতে কোনও লেখককে অনুরোধ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রকাশনা সংস্থার পক্ষে সম্পাদক যে বিষয়গুলি ভেবে লিখতে অনুরোধ করেন তা হল:
- বিষয়টির উপর বই-এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
- বাজারে বিষয়টির উপর বই-এর অলভ্যতা বা না থাকা
- বিষয়টির সঠিক বিশেষজ্ঞের দ্বারা বইটি লেখানো
- বইটির টার্গেট রিডার বা উদ্দীষ্ট পাঠক কারা, তার পরিমাণ
- বইটির বিপণন কৌশল বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভাবনা
- বইটির সঠিক মূল্য নির্ধারণ, যাতে বেশি লোক বইটি কিনতে পারে।
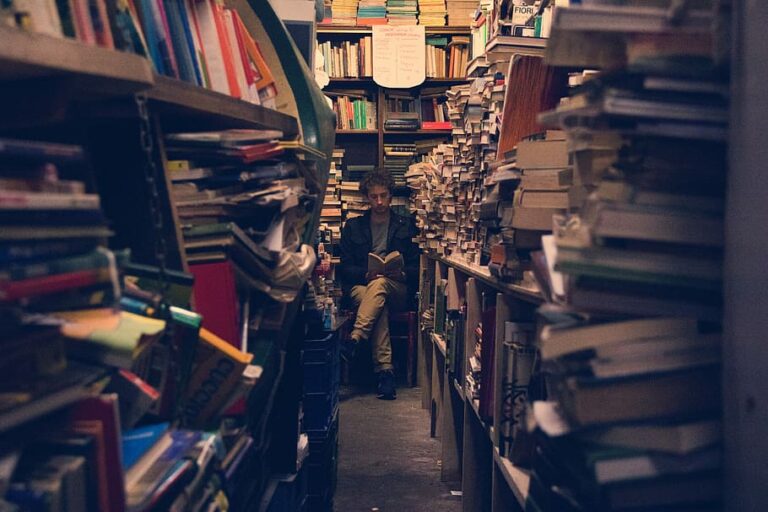
স্বল্পকালীন প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিষয় নির্বাচন ও বই প্রকাশ করা ক্ষতিকর হতে পারে। সাধারণভাবে কোনও বিশেষজ্ঞকে অনুরোধ করেন সংস্থার সম্পাদক বা কমিশনিং এডিটর (Commissioning Editor)। সম্পাদক সময় বেঁধে দেন যে, নির্দিষ্ট দিন বা মাসের মধ্যে বই-এর খসড়া লিখে জমা দিতে হবে। বড় প্রকাশনা সংস্থা এই মর্মে বিশেষজ্ঞ বা লেখকের সঙ্গে চুক্তিও করে থাকেন। এরপরে সেই বিশেষজ্ঞ বা লেখক যখন ঐ বিষয়ের উপর লিখে পাণ্ডুলিপি জমা দেন তাকে বলে ‘ম্যানুস্ক্রিপ্ট’ বা ‘স্ক্রিপ্ট’ বা ‘টাইপস্ক্রিপ্ট’। লেখকের সঙ্গে চুক্তি এভাবে ছাড়াও আরেক ভাবে হয়। সেখানে পাণ্ডুলিপি বা বই গৃহীত হবার পরে নির্দিষ্ট চুক্তি পত্রে প্রকাশক এবং লেখক সাক্ষী রেখে সই সাবুদ করে চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট সম্পাদন করেন। স্বাভাবিকভাবে চুক্তিতে লেখক প্রকাশককে প্রকাশনার বা বই ছাপার অধিকারটুকু দেন, যাকে বলে পাব্লিশিং রাইট (Publishing Right)। যিনি লিখেছেন অর্থাৎ যিনি লেখক তার অধিকার বা লেখকের স্বত্ব সর্বদা সুরক্ষিত থাকে—যাকে বলে কপিরাইট (Copyright)। অনেক সময় অসাধু প্রকাশক লেখকের কাছ থেকে চুক্তিপত্রে কপিরাইট নিয়ে নেন, লেখকরা কপিরাইট ও পাব্লিশিং রাইট বোঝেন না, ফলে পরবর্তীকালে, লেখক- প্রকাশকের সম্পর্ক মধুর থাকে না। লেখকের কাছে তাঁর লেখা বই স্বাভাবিকভাবেই খুব ভালো এবং প্রিয়, প্রকাশকের কাছে তা ব্যবসার বস্তু মাত্র। যতদিন সেই জিনিস থেকে টাকা বা লাভ আসবে ততদিন তার কদর করবেন প্রকাশক, যে মুহূর্তে সেই বই-এর আর কোনও বাজারমূল্য নেই, সেই মুহূর্ত থেকে প্রকাশক সেই বইকে নিয়ে আর কোনও আগ্রহ দেখাবেন না। এতে লেখককুল দুঃখ পান বটে, কিন্তু এতে কিছু করার নেই। প্রতিটি বই-এর একটা নিজস্ব আয়ু বা সেলফলাইফ (selflife) থাকে। চিরকালীন বিষয় হলে তার আবেদন থাকে দীর্ঘকাল। আর সস্তা চটুল সাম্প্রতিক বিষয় হলে তার আয়ু হয় সীমিত।
যাই হোক, অযাচিতভাবে (নিজের থেকে) জমা দেওয়া কোনও পাণ্ডুলিপি বা আনসলিসিটেড ম্যানুস্ক্রিপ্ট যদি প্রকাশনা সংস্থার পছন্দ হয় এবং সম্পাদক যদি মনে করেন যে এই পাণ্ডুলিপিটি তাদের প্রকাশনা নীতির (Publishing Policy)* সঙ্গে খাপ খায়, অর্থাৎ যদি পাণ্ডুলিপি গৃহীত বা অ্যাকসেপ্টেড হয় তাহলে ছাপার আগে সংস্থার নিয়ম-নীতি অনুসারে লেখকের সঙ্গে চুক্তি করেন।
পাণ্ডুলিপি জমা পড়ার পরে, সেটির নিরীক্ষার কাজটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিই রেডি টু প্রিন্ট বা সরাসরি ছাপার জন্য তৈরি থাকে না। পাণ্ডুলিপিকে ছাপার যোগ্য করে তোলার যে প্রক্রিয়া, তাকেই বলে সম্পাদনা বা এডিটিং।
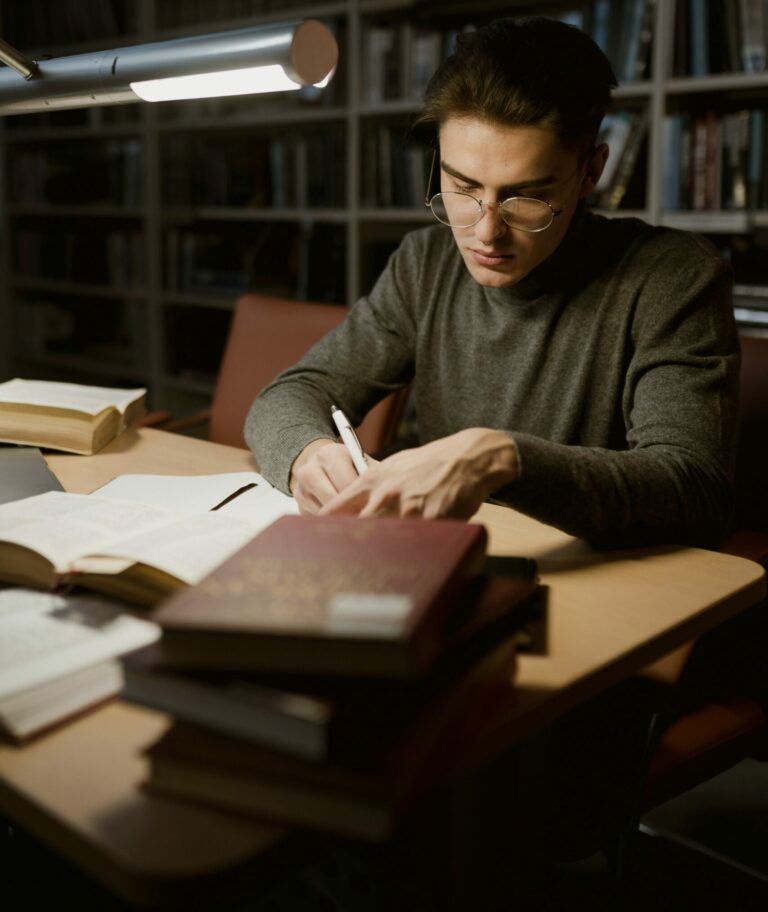
পাণ্ডুলিপি হল, বেশ কিছু বা বড় সংখ্যক লিখিত পাতা বা পৃষ্ঠার সমাহার। এর প্রতিটি পাতার দুটি অংশ, একটি রেক্টো (Recto) অন্যটি ভার্সো (Verso)। একটি বইয়ের ডানদিকের পাতাকে রেক্টো বলে আর তার পিছনের দিকটিকে বা বাঁদিকের পাতাটিকে বলে ভার্সো।**
সাধারণভাবে কপি এডিটিং (Copy editing) বলতে বোঝায়, পাণ্ডুলিপির বা বই আকারে লিখিত কোনও খসড়ার সম্পাদনা। সম্পাদনার কাজটি কয়েকটি স্তরে সম্পন্ন করতে হয়।
১। যে বিষয়ে পাণ্ডুলিপিটি লেখা, সম্পাদক যদি মনে করেন যে সেটি সেই বিষয়ের অপর কোনও বিশেষজ্ঞের দ্বারা সম্পাদনা করাতে চান তা তিনি করতে পারেন, বইটির যথার্থতার স্বার্থে।
২। যদি মনে করেন যে তিনি নিজে সম্পাদনা করবেন তাহলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় তা করতে হবে।
সম্পাদনা বা কপি এডিটিং-এর প্রধান কার্য হল— নিজেদের প্রকাশনা সংস্থার নীতি বা পলিসি মনে রেখে প্রথমত সম্পূর্ণ বইটি খুঁটিয়ে পড়ে দেখা। ভাষা, বানান, বাক্যগঠন, ব্যাকরণ এবং বিষয় আলোচনায় পরিমিতি সবই দেখতে হয়। ভাষাগত ত্রুটি থাকলে সেটি চিহ্নিত করা ও ঠিক করা। বানান ও ব্যাকরণগত ত্রুটি থাকলে সেটি ঠিক করে দেওয়া। প্রকাশনা সংস্থার নিজস্ব বানানবিধি থাকলে সেটি যাতে সঠিকভাবে অনুসৃত হয় সেটি দেখা। বিষয়বস্তু ব্যাখ্যায় ও আলোচনায়, পরিমিতি আছে না অতিরঞ্জিত করা হয়েছে তা দেখা। বানানের ক্ষেত্রে দেখা যে সম্পূর্ণ বইয়ে একই বানান ব্যবহার করা হয়েছে কিনা। কোনও বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়েছে কিনা, হলে একটি বাদ দেওয়া।
ন্যারেশন বা বলার ধরণ/শৈলীতে কোনও আড়ষ্টতা আছে কি না? যদি থাকে তাহলে সেটা ঠিক করা। সোজা কথায়, বর্ণনাটি সরলভাবে এগোচ্ছে না হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে সেটি দেখা। পাঠকের যাতে পড়তে অসুবিধা না হয়। ‘ফ্রি ফ্লো রিডিং’ বা সাবলীলভাবে যেন পড়া যায়। বিষয়টির গুরুত্ব ও আলোচনা যথাযথ হয়েছে কিনা সেটা দেখা। যদি দেখা যায় যে লেখক কোনও একটি নির্দিষ্ট দিক নিয়ে আলোচনা করেননি তাহলে সেটা লেখককে জানানো ও নতুন করে সেটা সংযোজন করা।
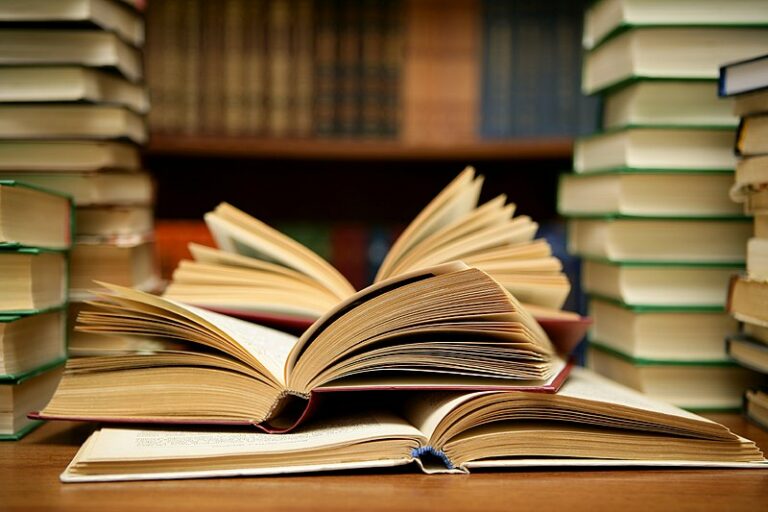
এরপর আসছে কপি এডিটিং-এর পরের ধাপ, যাকে বলে মূল সম্পাদনা বা সাবস্ট্যান্টিভ এডিটিং (Substantive Editing) বা কনটেন্ট এডিটিং। এর অর্থ হল মূল বিষয়বস্তুর সম্পাদনা।
কনটেন্ট এডিটিং-এ মূল বিষয়ের প্রয়োজন অনুসারে সম্পাদনা করা হয়। দেখতে হবে বিষয়টির অবতারণা কীভাবে করা হয়েছে? বিষয়টির সবগুলি দিক ঠিক ঠিক ভাবে আলোচনায় এসেছে কিনা। লেখক যে তথ্যগুলি পরিবেশন করেছেন সেগুলি ঠিকঠাক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা। বিষয়বস্তুর পর্যায়ক্রম আলোচনায় সঠিক অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছে কিনা, অধ্যায়গুলির সঠিক নামকরণ হয়েছে কিনা দেখা। কোনও কিছু বাদ পড়ছে কিনা দেখা। সাল, তারিখ, দিন, সময় সবকিছুর সঠিক ব্যবহার হয়েছে কিনা দেখা।
দেখে নেওয়া যে বইটির ভূমিকা যথাযথভাবে আছে কিনা, তাছাড়া খালি পৃষ্ঠা বা ব্ল্যাঙ্ক পেইজ কোথায় কোথায় যাবে, ফন্ট সাইজ বা ছাপার অক্ষরের মাপ কত বড় হবে, শিরোনামে অক্ষরের মাপ কত হবে, বই-এর প্রতি পাতার উপরে ফোলিও হেডিং (Folio Heading) যায়, তার ফন্ট সাইজ কত হবে সেসব নির্দেশ পাণ্ডুলিপির পাশের খালি অংশে দিতে হবে টাইপসেটার বা কম্পোজারের জন্য।
আরও পড়ুন: ছাপা বই ও এক অর্বাচীন পাঠকের ভাবনা
প্রতি অনুচ্ছেদ বা প্যারাগ্রাফের শুরুতে ইনডেন্ট (Indent) বা ছাড় দিতে হয় সেসবের নির্দেশ পাণ্ডুলিপির পাশের খালি অংশে দিতে হবে টাইপসেটার বা কম্পোজার-এর জন্য। নতুন অধ্যয় শুরু হলে সিঙ্ক (Sink) দেওয়াতেও একধরনের ছাড় দেওয়া যেটা উপর থেকে নীচে নামানোকে বলে। কোনও বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে কিনা যা থেকে কোনও বড় বিতর্ক বা সমস্যা তৈরি হতে পারে কিনা দেখা। সেসব কীভাবে এড়ানো যায় সেটা দেখে নেওয়া। বই এর শেষে ঋণস্বীকার (Acknowledgements) দেওয়া হয়েছে কিনা, ইনডেক্স বা নির্ঘণ্ট দেওয়া হয়েছে কিনা, নির্ঘণ্টে সঠিক পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া হয়েছে কিনা খতিয়ে দেখা (সব বই-এ অবশ্য থাকে না)। বই এর প্রিলিমস্ (Prelims) বা প্রারম্ভিক পর্বে উৎসর্গ পত্র থাকবে কি থাকবে না সব দেখে নেওয়া (সব বইয়ে থাকে না)।
মূল সম্পাদনা করতে করতে দেখা, কোথাও কোনো চিত্র বা ছবির বা ইলাস্ট্রেশনের প্রয়োজন আছে কিনা, থাকলে ছবির ‘বিষয়’ বা মোটিফ লিখে রাখা যাতে প্রকাশনা সংস্থার শিল্প বিভাগ বা আর্ট ডিপার্টমেন্ট সেই ছবিটি তৈরি করতে সক্ষম হয়। তাছাড়া বইটির প্রচ্ছদ বা কভার ডিজাইনের ওপর বইটির বিপণন নির্ভর করে, সেজন্য প্রচ্ছদ বা কভার ডিজাইনের বিষয় বা মোটিফও শিল্প বিভাগকে লিখিতভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। শিল্প বিভাগ বা আর্ট ডিপার্টমেন্ট-এর শিল্পীরা বইটি পড়েও সেটি করতে পারেন, তবে সময় কম থাকে বলে এবং প্রকাশনা সংস্থায় যেহেতু অনেক বই নিয়ে এই প্রক্রিয়া চলে সেহেতু ‘বিষয়’ বা ‘মোটিফ’ শিল্প বিভাগকে লিখিত ভাবে বুঝিয়ে দেওয়াটাই শ্রেয়। আরো একটা বিষয় হল যে, শিল্প বিভাগের শিল্পীরা বই-এর ভাষা নাও জানতে পারেন, সেক্ষেত্রে বিষয় বা মোটিফ দিয়ে দেওয়া-ই বিধেয়। সাধারণত শিল্প বিভাগ দুটি থেকে তিনটি সম্ভাব্য প্রচ্ছদ তৈরি করেন। সম্পাদক কখনও নিজে কখনও বা লেখকের সঙ্গে আলোচনাক্রমে একটি প্রচ্ছদ-চিত্র নির্বাচন করেন।
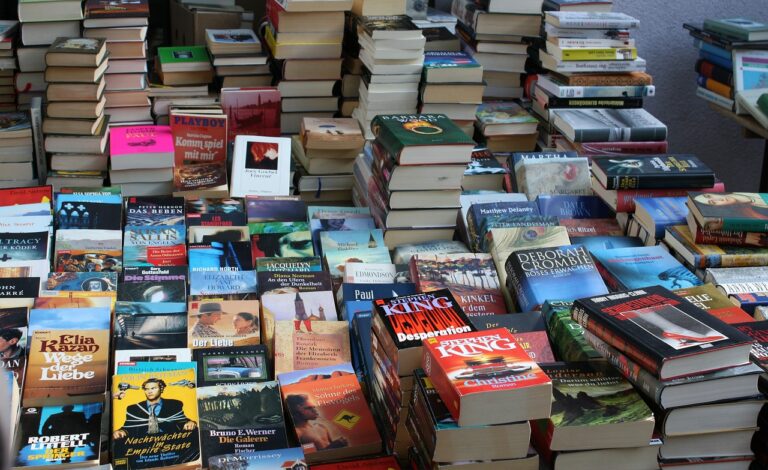
সম্পাদনা কর্মের শেষে সম্পাদিত পাণ্ডুলিপিটিকে বলে প্রেস কপি (Press Copy) । প্রেস কপি পাঠানো হয় কম্পোজার বা টাইপসেটারের কাছে। কম্পোজ হয়ে যাবার পর কাজ শুরু হয় প্রুফ রিডার (Proof Reader) -এর। তাহলে এতক্ষণ যা বললাম, তার সার কথা হল, এডিটিং কী? এডিটিং এর বাংলা অর্থ সম্পাদনা। কোন কিছুকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করাই এডিটিং। এডিটিং এর প্রয়োজনীয়তা কী? এডিটিং এর প্রয়োজনীয়তাসমূহ হল:
- অসুন্দরকে বাদ দেয়া বা আড়াল করা।
- বিষয়বস্তুকে শিল্পগুণসম্পন্ন করে উপস্থাপন করা।
- দর্শকদের বিরক্তির হাত থেকে বাঁচানো।
- বক্তব্য বা মতামতকে সূচারু ও সুন্দরভাবে নান্দনিক উপস্থাপন।
সম্পাদককে দেখতে হবে, বই পড়ার ক্ষেত্রে পাঠকের কোনো অসুবিধা হবে কিনা, বা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা। প্রুফ রিডারের প্রথম কাজ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি শব্দ বা লাইন বা লিখিত বস্তু যথাযথ উঠেছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা। এটাকে ইংরেজিতে বলে ‘comparing the manuscript with the First proof’. First Proof এ সম্পাদকের করে দেওয়া কারেকশন বা পাণ্ডুলিপির পাশের খালি অংশে চিহ্নাঙ্কিত ভুল বা মার্কিং গুলি টাইপসেটার বা কম্পোজার ঠিকঠাক তুলেছে কিনা। কোনো বিষয়ে সংশয় বা সন্দেহ তৈরি হলে সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। সাধারণত তিন বার প্রুফ দেখে বই ছাপতে পাঠানো হয়। থার্ড প্রুফ বা CRC কে ‘Camera Ready Copy’ বলা হয়।
বই কম্পোজিং-এ পাঠানোর আগে এবং সম্পাদনার শেষে সম্পাদক এই কাজগুলি করবেন ধাপে ধাপে —
- বইটির কভার ডিজাইন বা প্রচ্ছদ চিত্র সম্পর্কে শিল্প বিভাগকে নির্দেশ দেবেন।
- বইটির ফোর্থ কভারে বইটি সম্পর্কে এবং লেখক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হয়, একে ব্লার্ব (Blurb) বা ‘Back Cover matter’ বলে। সেটি তৈরি করা।
- বইটি কোন সাইজ এ ছাপা হবে সেটা ঠিক করে টাইপসেটারকে বলে দেওয়া।
- বইটির নাম ও লেখকের নাম ও প্রকাশনা সংস্থার লোগো কি সাইজ এ যাবে তার নির্দেশ দেওয়া।
- কোন কাগজে ছাপা হবে সেটা বলে দেওয়া।
এর পরে উৎপাদন বিভাগ বইটির এই বিষয়গুলি দেখে— কতগুলি কপি ছাপা হবে? এর উপর নির্ভর করছে, বই-এর দাম বা প্রাইস। সম্ভাব্য বিক্রি (Expected Sale) এবং বইটির বিষয়ের উপরে। বইএর মূল্য কী হবে? বইটির দাম নির্ভর করছে কত কপি ছাপা হচ্ছে তার উপর, কত পৃষ্ঠার বই, কত পরিমাণ কাগজ লাগছে, এবং কত ঘনত্বের কাগজ বা কাগজের কত ‘Grammage’ যাকে সংক্ষেপে এবং অশুদ্ধ ইংরেজিতে GSM বলে। GSM যত বেশি হয় কাগজের দাম ততই বেড়ে যায়। সাধারণভাবে বই ছাপার জন্য ৭০-৮০-৯০ GSM এর কাগজ ব্যবহার করে হয়, বই-এর বিষয়, গুরুত্ব ও বইটির চরিত্র দেখে। আনুষঙ্গিক সকল খরচ ধরা, প্রচ্ছদ চিত্র ও অন্য কোনো রঙিন চিত্র বই–এর ভিতরে আছে কিনা। এসব কিছু জেনে তারপর বই-এর মূল্য নির্ধারণ হয়। এত কাণ্ডের পরে একটা বই প্রকাশের মুখ দেখে।
প্রুফ রিডারের প্রথম কাজ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি শব্দ বা লাইন বা লিখিত বস্তু যথাযথ উঠেছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখা। এটাকে ইংরেজিতে বলে ‘comparing the manuscript with the First proof’. First Proof এ সম্পাদকের করে দেওয়া কারেকশন বা পাণ্ডুলিপির পাশের খালি অংশে চিহ্নাঙ্কিত ভুল বা মার্কিং গুলি টাইপসেটার বা কম্পোজার ঠিকঠাক তুলেছে কিনা। কোনো বিষয়ে সংশয় বা সন্দেহ তৈরি হলে সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। সাধারণত তিন বার প্রুফ দেখে বই ছাপতে পাঠানো হয়। থার্ড প্রুফ বা CRC কে ‘Camera Ready Copy’ বলা হয়।
সব শেষে আসি, বাস্তবের ভূমিতে। উপরে যা বললাম, তা হল থিওরি। প্রাক্টিক্যালে এই পদ্ধতি সর্বদা অনুসৃত হয় না। প্রকাশকরা, লেখকের সঙ্গে চুক্তি করেও র্যয়াল্টি দিতে আগ্রহী হয় না, দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। অধিকাংশ প্রকাশকের কাছেই কোনও সম্পাদক বা এডিটর থাকে না, প্রুফ রিডার দিয়ে সম্পাদনার কাজ করানো হয়। কখনো কখনো লেখক নিজে টাকা দিয়ে বই ছাপান, প্রকাশকরা বই ছাপার পর বইটির উপযুক্ত প্রচার প্রসার করেন না। প্রকাশকদের মধ্যে একধরনের পরিবারতন্ত্রের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। বই প্রকাশনা নিয়েও চলে দলাদলি, রাজনীতি আর ভালো বই খারাপ বই এর তকমা। শহরের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে গড়ে উঠেছে বই পাড়া, ছোট ছোট মফস্বল শহরে দুটি তিনটি বই-এর দোকান। গ্রামে তাও নেই, অথচ গ্রামেই মানুষের সংখ্যা বেশি। কিন্তু গ্রাম অবধি বই পৌঁছায় না। বছরে দুটি চারটি এখানে সেখানে বইমেলা। বই-এর থেকে অন্যান্য জাঁকজমক বেশি হয়ে যায়। বইমেলার দেশীয়, আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, নানান পার্থক্য আছে। বিশ্বের বড় বড় বইমেলায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড় হয়, বই যেহেতু মানুষের মনের খুব কাছাকাছি বাস করে, রাজনীতির মানুষজনও তাই আজকাল বই নিয়ে নানান আগ্রহ ও আতিশয্যে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তবু মানুষের সঙ্গে বই এর সম্পর্ক সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। প্রকাশনা জগতে আরও প্রশিক্ষিত, শিক্ষিত উঁচু মনের মানুষের প্রয়োজন, না হলে মানুষের মনে রেখাপাত করার এই বস্তুটি আপন গরিমা হারিয়ে ফেলবে অচিরেই। একটা বই লিখতে সময় লাগে এক থেকে দু বছর, কখনও আরও বেশি। এই দু বছরে লেখক কত কত বই পড়েন, গবেষণা করেন, তারপর যত্ন করে লেখেন। আর সেই বই মানুষ পড়ে ফেলে দুই থেকে পাঁচ দিনে। আর তাতেই ঘটে বিন্দু থেকে সিন্ধুর দর্শন। লেখক দু বছরে যা সংগ্রহ করে লিখলেন তা পাঠক পাঁচদিনে পেয়ে গেলেন। তাই বই পড়াতেই লাভ, না পড়লেই ক্ষতি।
* প্রকাশকের নীতি থাকে কোন বিষয়ে বই ছাপবে আর কোন বিষয়ে ছাপবে না।
** ল্যাটিন শব্দ
তথ্যসূত্র: অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ফিকি। নয়াদিল্লি।
লেখক ব্রতীন দে পড়াশোনা করেছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির, পাঠভবন, শান্তিনিকেতন, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতীতে। অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন শুরু। কাজ করেছেন বেঙ্গল ইন্সটিটিউট অফ টেলনোলজি ও ম্যানেজমেন্ট, শ্রীনিকেতন, ইন্সটিটিউট অফ এডভান্স ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা, ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা, পূর্ণিদেবী চৌধুরী মহিলা মহাবিদ্যালয়। ২০০৬ থেকে শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্ত ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়ার বাংলা সম্পাদক। প্রকাশিত বই ও অনুদিত বই-এর সংখ্যা অর্ধশতাধিক।




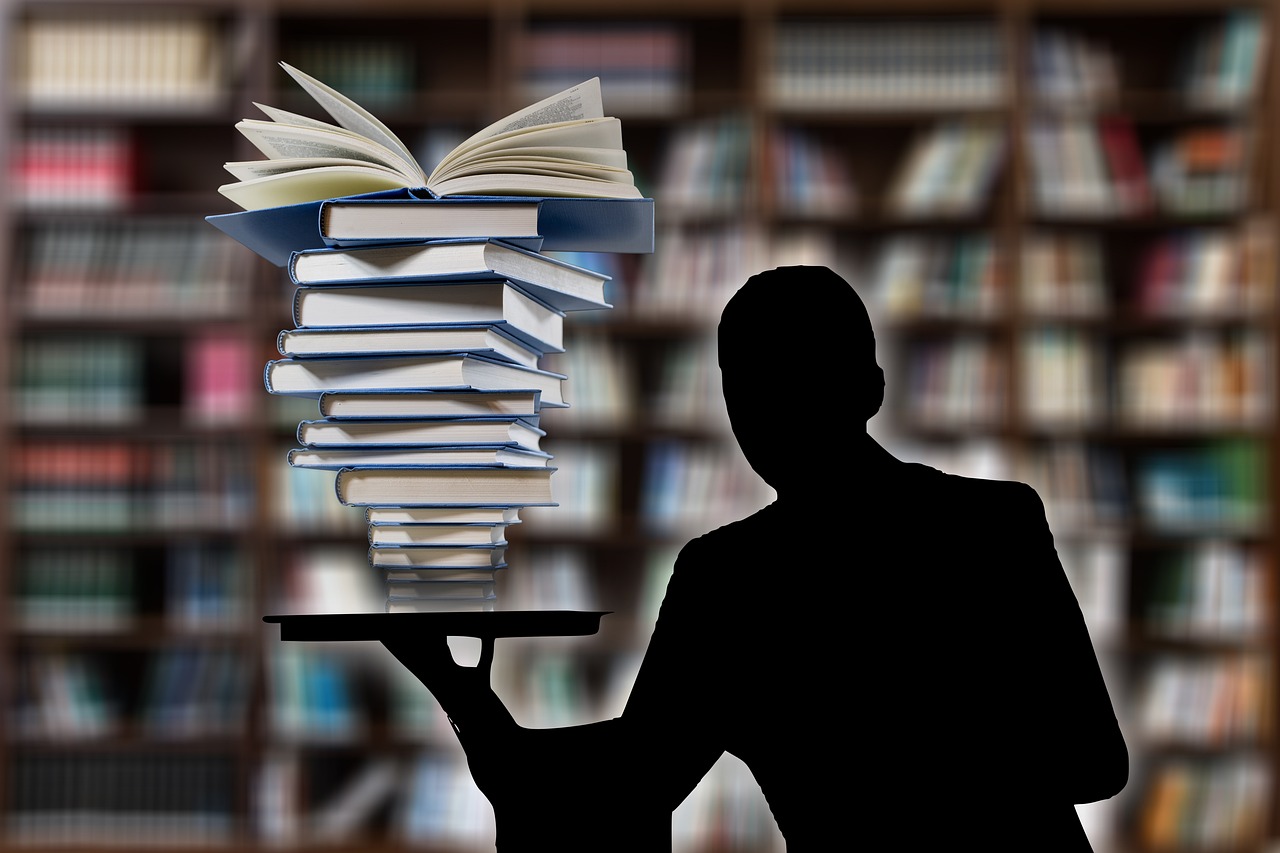





















4 Responses
অত্যন্ত সহজ ভাষায় রচিত তথ্যপূর্ণ লেখা।
সরল গদ্যে লেখা প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন
অনেক ভালো এবং বিস্তৃত ভাবে আলোচিত। বই এর উৎস ও উৎপাদন কাহিনী মা নবীন পাঠক ও লেখক উভয়কেই রূপরেখা দেবে।
Very usefull articale. Found a lot of unknown information.