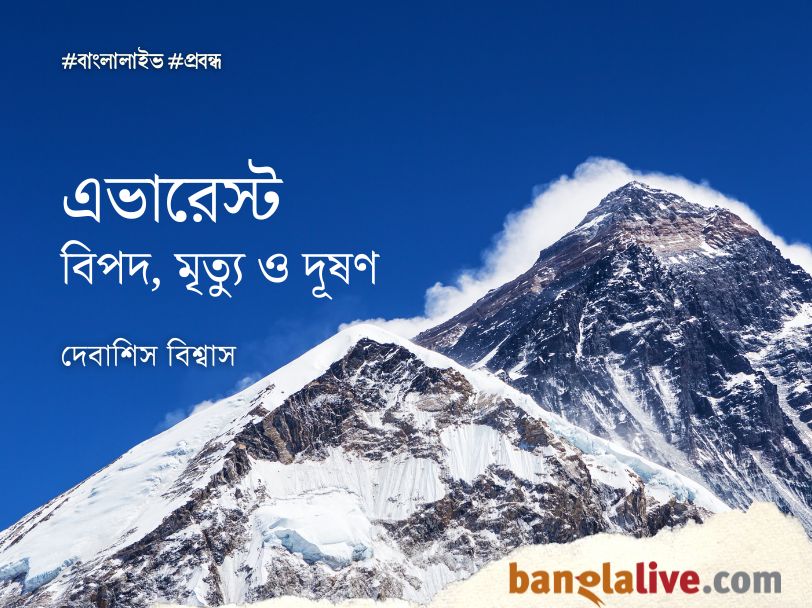পর্বতারোহণ (everest expedition) আমার ভালোলাগা, ভালোবাসা। পাহাড়-বরফের রাজত্বে কিছুদিন কাটাতে পারলে যেন আর কোন জাগতিক পাওয়া না-পাওয়ার প্রতি আমার চাহিদা থাকে না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের চাপে সারা বছর পাহাড়ে থাকা তো সম্ভব নয়।
১৯৯৪-৯৫ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে পাহাড়ে গেলেও, ২০১০ সালকে আমি মনে করি আমার পর্বতারোহী জীবনের এক টার্নিং পয়েন্ট। তার আগে পর্যন্ত ভারতীয় হিমালয়ের বিভিন্ন নামী দামী শৃঙ্গে আরোহণ করলেও, ২০১০ সালে পা বাড়াই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট – চোমোলুংমা (The Goddess of Earth) এর উদ্দেশ্যে। সে বছরের ১৭ মে সকাল সাড়ে সাতটায় আমরা পৌঁছে যাই পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দু, মাউন্ট এভারেস্ট শীর্ষে।
এভারেস্ট নেপাল এবং তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত বলে, দুদিক দিয়েই এভারেস্ট আরোহণ হয়। আমাদের প্রাথমিক ভাবনা তিব্বতের দিক থেকে আরোহণের থাকলেও, কাঠমাণ্ডু গিয়ে জানতে পারি, সে বছর কোনও ভারতীয়কে তিব্বতের দিকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে না। অতএব আমরা বাধ্য হই নেপালের দিক থেকে এভারেস্ট আরোহণে যেতে।
আরও পড়ুন: অক্সিজেন ছাড়া এক সঙ্গে দুই শৃঙ্গ- বিপদ আমার হাতের মুঠোয়
নেপালের দিক থেকে এভারেস্ট অভিযানে বেস ক্যাম্পের পরের পথ খুম্বু গ্লেসিয়ার বরাবর। সেখানে তো প্রত্যেক পায়ে যেন মৃত্যুর ভ্রুকুটি। সে পথের পুরোটাই সমান বিপদজনক। এই পথে চলার সময় সঙ্গে থাকা শেরপারা ক্রমাগতই তাড়া দিয়ে চলে- জলদি চলো, জলদি চলো। ইয়ে ইলাকা বহত খতারনাক হ্যায়।
কোথাও অল্প সময় বসতে দেয় না। কিন্তু এটা কি নির্দিষ্ট করে বলা যাবে যে, জলদি গেলেই সে পথের সম্ভাব্য বিপদ এড়ানো যাবে? যে জায়গা মনে হচ্ছে বিপদজনক, দৌড়ে সেখান থেকে যেখানে পৌছাব, সেটাও তো সমান বিপদজনক। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ জায়গা বলতে তো সেই ক্যাম্প ওয়ান। আর বেস ক্যাম্প থেকে এক দৌড়ে একদম ক্যাম্প ওয়ানে পোঁছানর ক্ষমতা কার রয়েছে? এক দৌড়ে তো সেখানে পৌঁছান যাবে না।
আর তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নিই যে, কোনও পর্বতারোহণকারী এক দৌড়ে সোজা ক্যাম্প ওয়ান পর্যন্ত পুরো রাস্তা পার হয়ে যেতে পারে, সে ক্ষেত্রেও, তার দৌড়ানোর সময়ও যে জায়গা দৌড়ে পার হচ্ছে, সেই মুহূর্তে সেই জায়গায়ও তো বিপদ নেমে আসতে পারে। তখন?
নেপালের দিক থেকে এভারেস্ট অভিযানে বেস ক্যাম্পের পরের পথ খুম্বু গ্লেসিয়ার বরাবর। সেখানে তো প্রত্যেক পায়ে যেন মৃত্যুর ভ্রুকুটি। সে পথের পুরোটাই সমান বিপদজনক। এই পথে চলার সময় সঙ্গে থাকা শেরপারা ক্রমাগতই তাড়া দিয়ে চলে- জলদি চলো, জলদি চলো। ইয়ে ইলাকা বহত খতারনাক হ্যায়।
দেবাশিস বিশ্বাস
বারবার সেই বিপদজনক খুম্বু গ্লেসিয়ার এলাকা পার হতে হয়। প্রতিবারই দেখেছি, যে পথ দিয়ে গেছি, আসবার সময় সেই পথের মাঝে দুই চার জায়গায় রাস্তা ভেঙে গেছে। শেরপারা নতুন করে ফের সেই জায়গার রাস্তা বানিয়েছে। খুম্বু গ্লেসিয়ারের পুরোটাই ভাঙাচোরা বরফের রাজত্ব। পুরো পথ জুড়েই ছোট বড় আইস টাওয়ার আর লক্ষ লক্ষ বরফের ফাটল বা ক্রিভাস। প্রায় প্রতি মিনিটেই কোথাও না কোথাও তার কোনও একটা ভেঙে পড়ছে। সেই ভঙ্গুর বিপদজনক এলাকা দিয়েই পথ বানিয়ে নিতে হয়। প্রচণ্ড দক্ষ একদল শেরপা থাকে এই রাস্তা বানাবার দায়িত্বে। তারা এতটাই দক্ষ যে তাদের বলা হয় – আইস ফল ডক্টর। রাস্তা বানানো মানে, যে জায়গা দিয়ে আরোহীদের যেতে সুবিধা হবে, সহজতম সেই পথ খুঁজে বের করে সেই পথ বরাবর দড়ি লাগানো, যেখানে পথ রোধ করে আছে কোন ফাটল বা ক্রিভাস, সেখানে সেই ফাটলের উপর মই পাতার কাজ ইত্যাদি।
খুব ছোট ফাটল হলে লাফিয়ে পার হওয়া যায়। ফাটল বড় হলে অ্যালুমিনিয়ামের একটা মই, আর ফাটল বেশ বড় হলে, সেই ফাটলের চেহারা অনুযায়ী এক সাথে দুই-তিন বা আরও বেশি মই বেঁধে ফাটলের উপর পাতার কাজ করতে হয়। এভাবে শুধু একবার রাস্তা তৈরি করে দিলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যায় না। প্রায় প্রতিদিনই তাদের ওই রাস্তা মেরামত করতে হয়। কারণ হিমবাহ খুবই ভঙ্গুর। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও রাস্তা ভেঙে যায়। এই কাজে অনেক দুর্ঘটনার মুখোমুখিও হয় তারা। ২০১৪ সালের ঘটনা সবচেয়ে বেশি মর্মান্তিক। সে বছর ১৮ই এপ্রিল সকাল সাড়ে ছটায়, এরকমই খুম্বু আইস ফলে রাস্তা তৈরির সময় এভারেস্টের ওয়েস্ট সোল্ডার থেকে নেমে আসা এক বিশাল অ্যাভালাঞ্চে ১৬ জন শেরপার মৃত্যু হয়।

পুরো গ্লেসিয়ার জুড়ে হাজার হাজার ক্রিভাস – তার কোনওটা উন্মুক্ত বা ওপেন ক্রিভাস, আবার অনেকগুলো হালকা বরফের আস্তরণে ঢাকা বা হিডেন ক্রিভাস। যেগুলো উন্মুক্ত, তার গভীরতা ভয়াবহতা তো চোখের সামনে থাকে, তাই সেগুলো ততটা বিপজ্জনক নয়। ছোট ফাটল হলে লাফিয়ে পার হয়ে যাওয়া যায়, বড় হলে তা পার হওয়ার জন্য তার উপর পাতা হয় মই। কিন্তু যেগুলো বরফের আস্তরণে ঢাকা, সেগুলো এক একটা গোপন মৃত্যুফাঁদ।
পর্বতারোহণ করতে গিয়ে বহু আরোহী, এমনকী নামিদামি শেরপাদেরও মৃত্যু হয়েছে ক্রিভাসের অতলে তলিয়ে গিয়ে। সেরকমই একজন বাবু ছিরি শেরপা। যিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করে প্রচারের আলোয় চলে আসেন। পরপর আরোহণ করেন ধৌলাগিরি, শিশাপাংমা, চোয়ু। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বাবু মোট দশবার আরোহণ করেন এভারেস্টে, তার মধ্যে ১৯৯৫ সালে একই সিজনে দু’বার আরোহণ – সে সময় সেটা ছিল এক রেকর্ড। ২০০০ সালের ২০ মে, বেস ক্যাম্প থেকে বিকাল ৫ টায় রওনা দিয়ে মাত্র ১৬ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে এভারেস্ট শীর্ষে পৌছে যান বাবু। যেখানে এভারেস্টের মাথায় সবাই মাত্র কয়েক মিনিটই কাটান, সেখানে ১৯৯৯ সালে, তাঁবু খাটিয়ে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ বিন্দুতে অতিরিক্ত অক্সিজেন ছাড়াই ২১ ঘণ্টা কাটান বাবু। কিন্তু এই মাপের একজন শেরপা ২০০১ সালের এভারেস্ট অভিযানে, ক্যাম্প -২ এলাকায় ফটো তোলার জন্য পিছোতে গিয়ে এক বড় ক্রিভাসে পড়ে মারা যান।
ক্রিভাসের উপর যে মই পাতা হয়, তার উপর দিয়ে যাওয়ার এক সুন্দর টেকনিক আছে। মই এর দু’পাশে দুটো দড়ি ফেলে রাখা থাকে। অভিযানে চলার জন্য যখন আমরা তাঁবু থেকে বের হই, তখন কিছু সরঞ্জামে ঠিকঠাক সুসজ্জিত হয়ে আমাদের বের হতে হয়। সেই সাজের এক জরুরী জিনিস হার্নেস। দুই পা ও কোমর জড়িয়ে থাকে এই হার্নেস। হার্নেসে আমরা স্লিং এর সাহায্যে আরোহণের বিভিন্ন সরঞ্জাম, যেমন জুমার, ডিসেন্ডার, আইস অ্যাক্স, ক্যারাবিনার লাগিয়ে নিই। আর হাত দুয়েক লম্বা এক দড়ির টুকরো, যাকে বলে ‘স্লিং’, তার সাহায্যে আলাদা একটা ক্যারাবিনারও হার্নেসের সাথে বেঁধে নেওয়া হয়। একে বলে সেফটি। অনেক সময় আমরা কোমরে দুটো সেফটিও ব্যবহার করি।

ক্রিভাস পার হওয়ার সময়, পাশে ফেলে রাখা দড়িতে একটা সেফটি পরিয়ে দিতে হয়। কারণ, মই দিয়ে ফাটল পার হওয়ার সময় কোনও কারণে মই থেকে পড়ে গেলেও নিচের ফাটলে আছড়ে পড়ব না। ওই সেফটির জন্য সেই দড়িতে ঝুলতে থাকবো। জীবনকে নিরাপদ রাখে, এইজন্য ওই ক্যারাবিনার সহ স্লিংকে বলে ‘সেফটি’।
এরপর মইয়ের মাঝের বিটগুলোতে পা ফেলে ফেলে পার হতে হয় ক্রিভাস। দড়িতে সেফটি লাগিয়ে দুই হাতে দুটো দড়ি পেছনের দিক থেকে টেনে রাখতে হয়। ক্রিভাসের উপর সমতল ভাবে মই পাতা হলে তা পার হওয়া মোটামুটি সহজ। আর যেখানে খাড়াভাবে মই পাতা, সেখানে পাশের দড়িতে সেফটি লাগিয়ে মই হাত দিয়ে ধরে উঠতে হয়। সেভাবে ওঠাও বেশ সহজ।
কিন্তু যেখানে মই নিচের দিকে ঢালু করে পাতা, সেখানে পার হতে বেশ ব্যালেন্সের দরকার। সেজন্য নিচের দিকে ঢালু অবস্থায় মই পাতা হলে, মইয়ের দিকে উল্টো হয়ে ঘুরে, দুই হাতে মই ধরে নামটাই সুবিধাজনক। তবে, সবক্ষেত্রেই মই এর পাশে ফেলা দড়িতে সেফটি লাগানো বাধ্যতামূলক।

সেই সব ফাটল বা ক্রিভাসের কতই না বৈচিত্র! কিছু ক্রিভাসের মধ্যে তাকালে দেখা যাচ্ছে অন্তত দশ বারো ফুট গভীর গর্ত। আবার বহু ক্রিভাস অতলান্ত অন্ধকার বুকে নিয়ে শুয়ে আছে। তার গভীরতা বোঝে সাধ্য কার?
ব্যক্তিগত ভাবে আমার খুব প্রিয় এবং কাছের শেরপা – দার্জিলিং এর তিন ভাই- পাসাং, পেম্বা ও তাশি। পাসাং-পেম্বার সাহায্যে আরোহণ করতে পেরেছি ভারতীয় ও নেপাল হিমালয়ের অনেক বিখ্যাত শৃঙ্গ। ২০১৮ সালের ১৩ই জুলাই কাশ্মীর হিমালয়ের সাসের কাংরি ফোর অভিযানে গিয়ে, সফল আরোহণ করে ফেরার সময় এক ক্রিভাসে পড়ে নিখোঁজ হয়ে যায় পেম্বা। পুরো নাম পেম্বা ছুটি শেরপা, অনেক চেষ্টা করেও ওর দেহ উদ্ধার করা যায়নি।
সেই ২০১০ এর এভারেস্ট অভিযানেই প্রথম সামনাসামনি এক অভিযাত্রীর মৃত্যুর মুখোমুখি হলাম। ক্যাম্প থ্রি পৌঁছেছিলাম ১৪ মে। পরদিন ওঠার কথা ক্যাম্প ফোর বা সামিট ক্যাম্পে। সাউথ কলে লাগানো হয় এই ক্যাম্প ফোর। ক্যাম্প টু এর পরে পথ পৃথিবীর চতুর্থ উচ্চতম শৃঙ্গ লোৎসের গা বরাবর। লোৎসে এভারেস্টের দক্ষিণে একদম গা ঘেঁষে দাঁড়ানো শৃঙ্গ। লোৎসে ফেস বরাবর উঠেই পৌঁছতে হয় ক্যাম্প থ্রি হয়ে ক্যাম্প ফোর।
ক্যাম্প থ্রি থেকে বের হয়ে সেই একই লোৎসের খাড়া বরফের ঢাল। সেই ঢালের মাঝেই আড়াআড়ি পাথরের এক দেওয়াল। সাড়ে সাত হাজার মিটারের কাছাকাছি উচ্চতার হলুদ রঙের সেই পাথুরে বর্ডারকে বলে ‘ইয়োলো ব্যান্ড’।
পুরো পথটাতেই দড়ি লাগানো ছিল। সেই রোপে জুমার, সেফটি লাগিয়ে ওঠা। একই দড়িতে আগে পরে অনেক ক্লাইম্বার। মাঝেমধ্যেই বেশি কষ্টকর জায়গায় কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে, স্বভাবতই পিছনের লোকেরাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ফলে তৈরি হচ্ছে জ্যাম। এ রকম জ্যাম এ পথে খুব স্বাভাবিক। এরই নাম ‘হিউম্যান ট্রাফিক জ্যাম’। ইয়োলো ব্যান্ডের পর ফের বেশ খাড়া বরফের ঢাল। খাড়া ওঠার পর বাঁ-দিকে ট্রাভার্স, পথ বেঁকে গেছে বাঁদিকে। সে সময় সামনে দেখি এক মন খারাপ করা দৃশ্য।
পর্বতারোহণ করতে গিয়ে বহু আরোহী, এমনকী নামিদামি শেরপাদেরও মৃত্যু হয়েছে ক্রিভাসের অতলে তলিয়ে গিয়ে। সেরকমই একজন বাবু ছিরি শেরপা। যিনি মাত্র ২৩ বছর বয়সেই কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহণ করে প্রচারের আলোয় চলে আসেন। পরপর আরোহণ করেন ধৌলাগিরি, শিশাপাংমা, চোয়ু। ১৯৯০ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বাবু মোট দশবার আরোহণ করেন এভারেস্টে, তার মধ্যে ১৯৯৫ সালে একই সিজনে দু’বার আরোহণ – সে সময় সেটা ছিল এক রেকর্ড।
দেবাশিস বিশ্বাস
এক আরোহীর মৃতদেহ নামিয়ে আনছে শেরপারা। যে দড়ি ধরে আমরা উঠছি, তাতেই বেঁধে নামাচ্ছে সেই মৃতদেহ। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, একজন রাশিয়ান। এসেছিল লোৎসে ক্লাইম্ব করতে। কিন্তু অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে মারা যায়।
এই আট হাজারি শৃঙ্গগুলোতে কেউ মারা গেলে, পাহাড়ে তার মৃতদেহ আবর্জনা হিসেবে ধরা হয়, আর সেটা নামিয়ে আনতে হয়। এই আবর্জনা পরিষ্কার করার একটা চার্যও ধরা আছে।
মন খারাপ হয়ে গেল। আমাদেরই মতন এক অভিযাত্রী যে ভালোবেসে এসেছিল পাহাড়ে, কিন্তু আর বাড়ি ফিরতে পারলো না। এর বাড়িতে না জানি কত আপনজন, বন্ধুবান্ধব ওর খবর পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তারা হয়তো এখনও পর্যন্ত জানে না এর পরিণতি।
এই ধরনের ঘটনা যে কারও সাথেই হতে পারে। এই আরোহীর অক্সিজেন শেষ হয়ে গিয়েছিল। কোনও অভিযানের মাঝেই আমাদের অক্সিজেনও তো শেষ হয়ে যেতে পারে। পথে এক হিসাব করে বের হলাম, কিন্তু কোনও কারণে পথে ২-৪ ঘন্টা আটকে দেরি হয়ে গেল, কিন্তু অক্সিজেন তো তার নিজের নিয়মেই শেষ হতে থাকবে। সেটা তো আর আমার অসুবিধার জন্য বেশি সময় ধরে চলবে না। কিংবা আরও একটা জিনিস হতে পারে, সেটা আমরা কখনও হয়তো ভেবে দেখি না। সাধারণত যে অক্সিজেন সিলিন্ডার আমরা ব্যবহার করি তাতে চার লিটার অক্সিজেন থাকার কথা। কিন্তু যখন এজেন্সিরা আমাদের অক্সিজেন সিলিন্ডার দেয়, তখন তো আর আমরা ওজন করে সেটা বুঝে নিই না। যে সিলিন্ডার নিয়ে আমি চলছি, তার ভেতর যে চার লিটার অক্সিজেনই ছিল, তার গ্যারান্টি কোথায়? তাতেও তো আমার হিসাব গোলমাল হয়ে যেতে পারে।

কে জানে, এর মধ্যে ঠিক কোন কারণে রাশিয়ান ছেলেটি মারা গেল? ঠিক তেমনি জানা যাবে না এরকমই কোনও আপাত তুচ্ছ কারণেই কি আমরা হারিয়েছি গৌতম ঘোষ, সুভাষ পাল, পরেশ নাথ বা কুন্তল, বিপ্লবকে?
পাহাড়ে একটি খুব প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট বা সময়জ্ঞান। যেমন- বেস ক্যাম্প থেকে কারও ক্যাম্প ওয়ান পৌঁছানোর জন্য খুব বেশি হলে ছয় থেকে আট ঘন্টা সময় লাগা উচিত। কেউ যদি সেই পথ অতিক্রম করতে এর থেকে অনেকটাই বেশি সময় লাগিয়ে ফেলে, তাহলে পথ চলার পরিশ্রম অনেকটাই বেড়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই শরীরে আসে চরম ক্লান্তি। পাশাপাশি সাথে থাকা জল কিংবা খাবার শেষ হয়ে গেলে, ক্লান্তির সাথে সাথে তৃষ্ণা এবং ক্ষুধা এসে শরীরকে আরও কাহিল অবসন্ন করে দেয়। অভিযানের পুরো পথের ক্ষেত্রেই এই সময়জ্ঞান প্রযোজ্য।
আর এই রকম ভাবেই ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় না পৌঁছতে পারার খেসারত অনেক সময় আরোহীকে তার জীবন দিয়েও দিতে হতে পারে। এটা বেশি দেখা যায় শীর্ষ আরোহণের সময়। সাধারণত, যে নিয়ম সবাই মেনে চলে তা হচ্ছে, আগের সন্ধ্যায় রওনা দিয়ে সারা রাত চলে পরদিন সকালের মধ্যে এভারেস্টের শীর্ষে পৌঁছতে হবে এবং সেখান থেকে ফের নামতে শুরু করে, এগারোটা বারোটার মধ্যে ঢুকে যেতে হবে সামিট ক্যাম্প। এভারেস্ট আরোহণের বেসিক নিয়ম অনুযায়ী, শীর্ষে পৌঁছানোর শেষতম সময় হতে পারে মোটামুটি সকাল দশটা – সাড়ে দশটা। এটাই বলা হয় যে, সকাল দশটা অবধি তুমি যেখানে পৌঁছতে পেরেছো, সেখান থেকেই তোমাকে ফেরার পথ ধরতে হবে। তা না হলে সুস্থ ভাবে কিংবা জীবিত অবস্থায় ক্যাম্প ফোরে ফেরা সম্ভব নাও হতে পারে। অতিরিক্ত সময় ব্যয় হওয়াতে তখন শরীরে ক্লান্তির পাশাপাশি পিঠের সিলিন্ডারের যে মহার্ঘ অক্সিজেন – সময়ের সাথে সাথে তা শেষ। সেক্ষেত্রে জীবিত অবস্থায় নিচে নামা হয়ে যাবে আরও কঠিন কিংবা অসম্ভব এক ব্যাপার। এরকম পরিস্থিতির শিকার হয়ে বেশ কিছু মৃত্যু আমরা দেখেছি এভারেস্টে।

এরকম এক উদাহরণ পাসাং লামু শেরপা। ১৯৬১ সালের ১০ই ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করা পাসাং লামু এভারেস্ট আরোহণকারী প্রথম মহিলা শেরপা। পর্বতারোহী পরিবারের মধ্যে জন্ম হওয়ায় আরোহণ ছিল তার রক্তে। সে সফল ভাবে আরোহণ করেছিল আল্পস এর বিখ্যাত মঁ ব্লা, চোয়ু ও আরও অনেক শৃঙ্গ। তিনবার এভারেস্ট আরোহণ করার চেষ্টা করে বিফল হলেও হাল ছাড়েনি। অবশেষে ১৯৯৩ সালের ২২ এপ্রিল সাউথ কলের রাস্তা দিয়ে এভারেস্ট আরোহণ করতে সফল হলেও, নামার পথে সাউথ সামিটের কাছে মারা যায়।
ডিহাইড্রেশন আরেক সমস্যা। একটানা পরিশ্রমের ফলে শরীরে জলের চরম ঘাটতি থেকে আসতে পারে মাসেল ক্রাম্প। তখন এক একটা পা ফেলাই হয়ে যায় চরম কষ্টকর। বিশ্রামের জন্য কেউ একবার হাঁটু মুড়ে বসে পড়লে, সেই অবস্থা থেকে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ানোটাই প্রায় অসম্ভব হয়ে যেতে পারে।
আরও একটা সমস্যা স্নো ব্লাইন্ডনেস। স্নো ব্লাইন্ডনেস হয় বরফের এলাকায়। আমি তো বেশ কয়েকবার অন্ধত্বের মুখোমুখি হয়েছি। কখনও হালকা আবছা দেখেছি, কখনও বা পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছি। সেই অন্ধ অবস্থায় নামতে হয়েছে ওই দুর্গম রাস্তায়। সেরকমই কোনও নামার সময়ে তো যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতেই পারত আমার সাথে।
চারপাশে দুধ সাদা বরফ। তাতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়ে যে তীব্রতা বেড়ে যায় আলোর, তাতে মাত্র কয়েক মিনিট খালি চোখে থাকলেই সেই আলো চোখের করোনায় এত তীব্র ক্ষতি করতে পারে যে, চোখে সাময়িক অন্ধত্ব চলে আসে। একেই বলে স্নো ব্লাইন্ডনেস। অন্ধত্বের সাথে শুরু হয় চরম ব্যথা। চোখ থেকে ক্রমাগত একটানা জল পড়তে থাকে। এটা যে শুধুমাত্র কড়া রোদে হয় তা নয়, মেঘলা আবহাওয়াতেও অনেক সময় খালি চোখে বরফের রাজত্বে চলাফেরা করলে এই অন্ধত্ব আসতে পারে। আসলে মেঘলা পরিস্থিতিতেও আলোয় UV Ray থাকে। ওই উচ্চতায় UV Ray এর পরিমাণ অনেক বেশি। আর সেই UV Ray বরফে প্রতিফলিত হয়ে চোখের ক্ষতি করে। স্নো ব্লাইন্ডনেস চলে আসে। এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় সেই তীব্র আলো থেকে চোখকে আড়াল করা করে রাখা; বরফের এলাকায় কালো সানগ্লাসে চোখ ঢাকা।

এছাড়াও, পাহাড়ে আমার চোখে আরও এক সমস্যা দেখা দেয়। রাতের অন্ধকারে হাঁটার সময় তো আর চোখে কালো চশমা পড়ি না, খালি চোখেই চলতে হয় তখন। আর রাতে ঠান্ডাও থাকে খুব বেশি। সেই চরম ঠাণ্ডায় খালি চোখে চললে, সেই ঠান্ডা সরাসরি চোখে লাগলে কিছুক্ষণ পর থেকেই চোখ কটকট করতে থাকে। সেই অবস্থায় অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পর, ধীরে ধীরে চোখে ব্যথা শুরু হয়, আর সেই ব্যথা ক্রমশই বাড়ে। তারপর ভোরের দিকে যখন ধীরে ধীরে আলো ফোটে, আমার চোখের দৃষ্টিও ধীরে ধীরে ঝাপসা হতে থাকে। চোখে ছানি পড়লে যেমন হয়, যেন দৃষ্টিপথে কেউ কোনও ঘষা কাচ রেখে দিয়েছে – এমনটাই দেখি। পরে রোদ উঠলে সেই আলোর তীব্রতায় আস্তে আস্তে চোখে স্নো ব্লাইন্ডনেস চলে আসে।
এভারেস্ট নিয়ে আরেকটা কথা আমরা প্রায়ই শুনে থাকি, যে এভারেস্টের বুকে পাহাড় প্রমাণ জঞ্জাল। কদিন আগে একটা খবর এসেছে, অভিযাত্রীদের নিজেদের মল-মূত্র এভারেস্টের বুকে ছেড়ে আসা যাবে না, সঙ্গে করে বয়ে নিচে নিয়ে আসতে হবে। আসলে সারা পৃথিবী থেকে হাজার হাজার অভিযাত্রী ছুটে যায় এভারেস্ট শীর্ষ আরোহণের উদ্দেশ্যে। স্বভাবতই, অন্যান্য পর্বত শৃঙ্গ থেকে এভারেস্টের বুকে অভিযাত্রীদের ফেলে যাওয়া জঞ্জালের পরিমাণও বহুগুণ। অসংখ্য ভাঙাচোরা তাবু, ছেঁড়াফাটা জামাকাপড়, খাবারের উচ্ছিষ্ট, টিনের ক্যান, বোতল, প্লাস্টিকের প্যাকেট, ছেড়ে আসা অক্সিজেন সিলিন্ডার, পথের জন্য লাগানো দড়ি মই – এসব তো রয়েছেই, এছাড়াও অগুন্তি মৃতদেহকেও এভারেস্টের বুকে আবর্জনা হিসাবেই মানা হয়।
এভারেস্ট বেস ক্যাম্প ট্রেকিংয়ের পথে, প্রশাসন থেকে লুকলা, এবং লুকলা থেকে এভারেস্ট বেস ক্যাম্প পর্যন্ত পথটি নিয়মিত পরিছন্ন করার জন্য বেশ পরিষ্কার। কিন্তু সেই একই চিত্র এভারেস্টের বেস ক্যাম্প কিংবা উপরের এলাকার নয়। বেস ক্যাম্পেও সাগরমাথা পলিউশন কন্ট্রোল কমিটি তাদের নিয়মিত পরিচর্যায় বেশ পরিষ্কার করে রাখার চেষ্টা চালায়, যদিও প্রচুর মালপত্র বয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রচুর ইয়াক আসার ফলে তাদের মল-মূত্রে বরফ-পাথরের এলাকা বেশ কলুষিত হয়ে থাকে।

বেস ক্যাম্পে টয়লেট টেন্ট বানানো বাধ্যতামূলক হওয়ার ফলে সেখানকার অভিযাত্রীরা বেশ ক্যাম্পের যেখানে সেখানে মলত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু উপরের শিবিরগুলোতে সেরকম বাধ্যবাধকতা না থাকায়, সেই জায়গাগুলো অভিযাত্রীদের মল-মূত্রে যথেষ্ট নোংরা হয়ে থাকে। তার উপর বেস ক্যাম্পে প্রশাসনের যে পরিমাণ নজরদারি থাকে, উপরের এলাকায় তা না থাকার জন্য সেসব এলাকা যথেষ্ট নোংরা। অভিযাত্রীদের মল-মূত্র, ছেঁড়াফাটা তাবু, জামাকাপড়, খাবারের উচ্ছিষ্ট, বাতিল ক্যান বোতল প্লাস্টিকের প্যাকেট, ফেলে আসা অক্সিজেন সিলিন্ডার, বাতিল দড়ি মই ইত্যাদি সহ এভারেস্ট কিন্তু যথেষ্টই নোংরা বলা যেতে পারে।
মাঝে মাঝে এভারেস্ট পরিষ্কার করার জন্য ক্লিন এভারেস্ট অভিযান হলেও, শুধুমাত্র প্রশাসন কিংবা সেই অভিযান দলের মুষ্টিমেয় কয়েকজন সদস্যদের প্রচেষ্টাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে, যদি সমস্ত অভিযাত্রী, শেরপা, বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন হাতে হাতে লাগিয়ে এভারেস্টের বুক থেকে দীর্ঘ শতবর্ষ ধরে জমা হওয়া আবর্জনা সরাতে সচেষ্ট না হন, তাহলে চোমোলুংমা – পৃথিবীর মা-কে আমরা কখনওই পরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারব না।
ছবি সৌজন্য: পিয়ালি বসাক, দেবাশিস বিশ্বাস, Wikimedia
দেবাশিস বিশ্বাস আয়কর বিভাগের ডেপুটি কমিশনার পদে কর্মরত। তিনি ২৯টি পর্বতারোহণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, মাকালু, অন্নপূর্ণা সহ অনেকগুলি শৃঙ্গ জয় করেছেন। ২০১৬ সালে তিনি তেনজিং নোরগে ন্যাশনাল অ্যাডভেঞ্চার অ্যাওয়ার্ড পান। তিনি প্রথম বাঙালি অসামরিক এভারেস্ট আরোহী যুগলের একজন এবং প্রথম ভারতীয় অসামরিক কাঞ্চনজঙ্ঘা আরোহী যুগলের একজন।