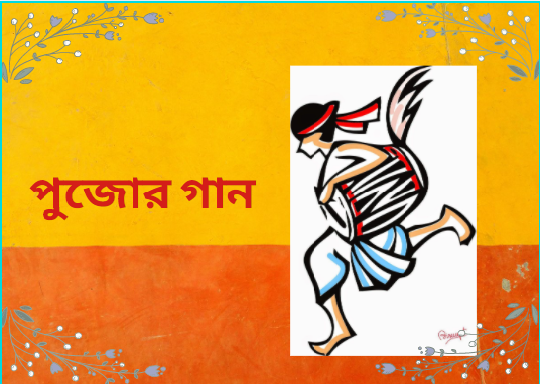সেই কোন ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি কোনও একটি বিজ্ঞাপনী প্রচারের ট্য়াগ লাইন – “বঙ্গজীবনের অঙ্গ”, তখন থেকেই মনে হয় বাঙালির জীবনে দুর্গাপুজোও সত্যিই তেমনিই এক অবিচ্ছেদ্য় অঙ্গ। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা বিভিন্নভাবে ছোটবেলার সেই ধারণাকেই প্রমাণসিদ্ধ করেছে। যুগের পরিবর্তনের ওঠা পড়ায় কত কিছু বদলেছে, প্রগতিশীলতা রক্ষণশীলতাকে কখনও পেছনে ফেলেছে, কত মূল্যবোধের পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমানের ইঁদুর-দৌড় প্রতিযোগিতায় হয়তো বা অনেক ঐতিহ্য হারিয়ে গেছে… কিন্তু দুর্গাপুজো, সে সাবেকি হোক বা থিমপুজো, আজও একমেবাদ্বিতীয়ম, স্বমহিমায় উজ্জ্বল। আর ঠিক সে রকমই এত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ঝড়ঝাপটা সামলেও দুর্গাপুজোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে চিরনতুন হয়ে রয়ে গিয়েছে পুজোর গান।
পুজোর গানের সেকাল-একাল, পুজোর গানের উন্মাদনার হ্রাস-বৃদ্ধি – এ এক বহু আলোচিত বিষয়। সে সব নিয়ে আমিও যে কখনও দু’চার কথা বলিনি তেমনটা নয়, তাই আজ আর বরং সে পথে না হেঁটে আমার কাছে পুজোর গান কখন কী ভাবে কোন তাৎপর্য নিয়ে এসেছে তাই নিয়ে কিছু কথা লিখি। পুজোর গানের প্রতি উৎসাহ বা বছরভর অপেক্ষা করে থাকা – এ সব কিছুই শুরু হয়েছিল স্কুলজীবন থেকে। আমাদের বাড়িতে রেকর্ড প্লেয়ার ছিল না। গান শোনার মাধ্যম বলতে রেডিও, ক্য়াসেট রেকর্ডার আর বিশেষ করে পুজোর গান শোনার অন্যতম প্রধান মাধ্যম ছিল পাড়ার পুজো প্যান্ডেল।
[the_ad id=”266918″]
সে সময় পুজোর জাঁক শুরু হত মহাসপ্তমী থেকে। কিন্তু মোটামুটি বাঁশ বাঁধার সময় থেকেই বিভিন্ন কোম্পানি থেকে প্রথিতযশা শিল্পীদের গান প্রকাশ পেয়েই যেত। তবে মাইকে না বাজা পর্যন্ত সে সব গান শোনার অবকাশ খুব একটা ছিল না। কারণ আমার প্রথম শিক্ষাগুরু, আমার বাবা, ছিলেন হিন্দুস্থানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে নিবেদিতপ্রাণ একজন রক্ষণশীল মানুষ। যেহেতু শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শিক্ষা ও নিয়মিত অনুশীলন দু’টোই অত্যন্ত ধৈর্য ও স্থৈর্যের বিষয়, তাই ওই অপরিণত বয়সে বেশি আধুনিক বাংলা গান শুনলে সেসব গানের আপাত সহজবোধ্যতায় রাগসঙ্গীতের প্রতি মানসিক স্থিরতায় ব্যাঘাত ঘটবে, এমন এক আশঙ্কা ছিল তাঁর। কিন্তু –
“আমার হাত বান্ধিবি, পা বান্ধিবি
মন বান্ধিবি কেমনে…”
বাবার চোখের আড়াল হলেই লুকিয়ে রেডিও বা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে, অথবা আশপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা গানে কান পেতে থেকে, পুজোর মাসখানেক আগে থেকেই প্রতিবছরই কোন কোন শিল্পীর কী কী গান প্রকাশিত হচ্ছে তার একটা সম্যক ধারণা তৈরি হয়েই যেত। এরপর শুধু পাড়ার প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে গানগুলো বাজার অপেক্ষা, আর শুনে শুনে মুখস্থ করে পছন্দের গানগুলো শিখে ফেলা – এই ছিল তখন আমার কাছে পুজোর গান।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব পুজোর গানই আমার কাছে তথাকথিত বাংলা আধুনিক গান শেখার মাধ্যম হয়ে উঠল। মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, বনশ্রী সেনগুপ্ত, হৈমন্তী শুক্লা, শ্যামল মিত্র– লিখে শেষ করা যাবে না। এমন সব যশস্বী শিল্পীদের অনবদ্য গায়নশৈলিই ছিল সে সময় পুজোর গানের সোনার ঝাঁপি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এঁরা কিন্তু সকলেই ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দীর্ঘ শিক্ষা ও চর্চার মধ্যে দিয়েই নিজেদের তৈরি করেছিলেন, অন্যথায় এমন মুন্সিয়ানা কখনওই সম্ভব নয়। একথা জেনেছিলাম এবং মর্মে মর্মে উপলব্ধিও করতাম। আর সে কারণেই এই ধারার গান শুনতে গিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা ও চর্চার প্রতি আমার আগ্রহ তো কমেইনি, বরং দ্বিগুণ হয়েছিল। গানের ছোট্ট ছোট্ট কাজ বা মুড়কির জায়গাগুলো, আর অবশ্যই ভাবের প্রাধান্য আয়ত্ত করা সম্ভবই নয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আশ্রয় ছাড়া। “তুঁহু মম মন প্রাণ হে” – এ গানে ‘প্রাণ’ শব্দটিতে যে সত্যিই প্রাণকাড়া একটা মড্য়ুলেশন, কী ভাবে সন্ধ্যাদি সেটা আনছেন, “এই চারুকেশে” -তে আরতিদি কী সব আয়াসসাধ্য তান ব্যবহার করছেন… আবার সেই আরতিদিই “বন্য বন্য এ অরণ্য” -র মত লাস্যময়ী গান গাইছেন – সেসব অপার বিস্ময়ে শুনতে থাকতাম। “এই তো সেদিন” গানটিতে “এ শুধু আমার তুমি কেঁদো না” — এই ‘কেঁদো না’ শব্দটিতেই নিজের সব কান্না বোধহয় উজাড় করে দিয়ে আজও হাজার বাঙালিকে কাঁদিয়ে দিতে পারেন মান্নাদা।
শুনলাম “ময়না বলো তুমি কৃষ্ণ রাধে” – ‘বলো’ শব্দের ওই সূক্ষ্ম কাজটা (র্রের্সানির্সার্রে) অত সূক্ষ্মতার সঙ্গে কী করে গলায় আনা যায়, সারাদিন ধরে চলল তার নিষ্ফল প্রয়াস। ঠিক সেইরকম “দূরে আকাশ শামিয়ানা”-র দ্বিতীয় লাইন “প্রদীপ জ্বালায় তারায়” – এখানে ‘তারায় শব্দটিতে যে ছোট্ট তান (মাধাপামাগারেসানিধা) অমন মোলায়েম ভাবে গাওয়া, অথচ প্রতিটি দানা স্পষ্ট। এসব কাজকম্মের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে যখন মশগুল হয়ে আছি, তখনই আবার পাহাড়ের গাম্ভীর্যের মত একটা গলা কানে এল -“আমার মনের এই ময়ূর মহলে” – শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আয়াসসাধ্য চেষ্টায় ফুরফুর করে গলায় কাজ যদিও বা কিছুটা আয়ত্ত করা গেল, কিন্তু সোজা সোজা সুর লাগানো যে এত শক্ত বিষয় তা তো আগে বুঝিনি!! তাঁর গাওয়া এমন অনেক গানের ছত্রে ছত্রে কিশোরকুমার সেটা টের পাইয়ে দিয়েছিলেন রীতিমত। এর পাশাপাশি কিন্তু পুজোর গানের তালিকায় সম্পূর্ণ কালোয়াতি বাংলা গানও (যাকে আমরা সাধারণত রাগপ্রধান বলি) সমানভাবে স্থান পেয়েছে। পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী, শিপ্রা বসু বা হৈমন্তীদির মতো শিল্পীদের রাগাশ্রয়ী বাংলা গানও কালজয়ী পুজোর গান হিসাবে আজও ভীষণভাবে সমাদৃত।
[the_ad id=”266919″]
স্কুল শেষ হয়ে যখন কলেজ জীবন শুরু হল তখন আবার পুজোর গানের তথা বাংলা আধুনিক গানের অন্য একটা দিক দেখতে পেলাম। তখন পুজোর ধরনও আস্তে আস্তে বদলে যেতে শুরু করেছে। কোথাও কোথাও সাবেকি থেকে একটু একটু করে থিমপুজো শুরু হচ্ছে। ঠিক সেরকম ভাবেই পুজোর গানও তার সাবেকিয়ানা থেকে কিছু ক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে শুরু করল। বিশেষ করে বাংলা গানের ভাষা তার বয়ঃসন্ধির সব রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে ভীষণভাবে উদ্ধত সাবালক হয়ে উঠতে চাইল এবং হলও তাই। সমস্ত লজ্জা সঙ্কট কাটিয়ে বাংলা গান সরাসরি দাবি করলো “এক কাপ চায়ে” আর “ঠান্ডা শীতের রাতে লেপের আদরে” – “আমি তোমাকে চাই”। উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আগেই প্রশ্ন করতে শিখল “এই তুমি কি আমায় ভালোবাসো??” কখনও বা প্রতিবাদের ভাষায় নিছক সারকাজ়ম শোনা গেল পুজোর গানে –
“ভিড় করে ইমারত আকাশটা ঢেকে ফেলে
চুরি করে নিয়ে যায় বিকেলের সোনা রোদ।
ছোট ছোট শিশুদের শৈশব চুরি করে-
গ্রন্থকীটের দল বানায় নির্বোধ।
এরপর চুরি গেলে বাবুদের ব্রিফকেস,
অথবা গৃহিনীদের সোনার নেকলেস,
সকলে সমস্বরে একরাশ ঘৃণা ভরে
চিৎকার করে বলে চোর চোর চোর চোর!!!!”
পুজোর গানে ধ্বজা উড়িয়ে এলেন সুমন-নচিকেতা। হই হই কলেজের দিনগুলো, প্রতিটি গানের কথা-সুর মুখস্থ, সব কলেজ ফেস্টের মঞ্চ সুমন-নচিকেতার গানে উত্তাল। সেই প্রতিবাদের সুরে সুর মেলালেন এক মহিলা কন্ঠ। বেশ চমকে উঠেছিলাম আমি ও আমার মত আরও বহু বহু বাঙালী শ্রোতা – লোপাদি (লোপামুদ্রা মিত্র)। “বেণীমাধব বেণীমাধব তোমার বাড়ি যাব” -র আর্তি যখন এক প্যান্ডেল থেকে আর এক প্যান্ডেলে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তখনই আবার অতি বাস্তবের কঠোরতা আড়াল করে ছোটদের জন্য গাইছেন লোপাদি – “ডাকছে আকাশ, ডাকছে বাতাস”, “আয় আয় কে যাবি”। কিন্তু তাই বলে পুজোর গান যে একেবারেই তার চিরাচরিত প্রথা ভুলতে বসেছিল তা তো নয়, সে সম্পদেও তখন পুজোর গানকে ভরিয়ে রেখেছিলেন একাধারে ইন্দ্রাণী সেন, ইন্দ্রনীল সেন, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকান্ত আচার্যের মতো শিল্পীরা। “বৃষ্টি তোমাকে দিলাম” যখন প্রথম শুনলাম, এক অদ্ভুত নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়েছিলাম – বহুদিন পর বাঙালি শ্রীকান্তদার মতন এমন একটা কন্ঠ পুজোর গানের উপহার হিসেবে পেল।
বাবার চোখের আড়াল হলেই লুকিয়ে রেডিও বা টেপ রেকর্ডার চালিয়ে, অথবা আশপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা গানে কান পেতে থেকে, পুজোর মাসখানেক আগে থেকেই প্রতিবছরই কোন কোন শিল্পীর কী কী গান প্রকাশিত হচ্ছে তার একটা সম্যক ধারণা তৈরি হয়েই যেত।
২০০১ সাল থেকে আমার কাছে পুজোর গানের সংজ্ঞা খানিকটা বদলে গেল। তেমন ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে পুজোর গান শোনার মজাটা কতকটা নষ্ট হয়ে গেল, কারণ ওই বছর থেকে পুজোর গানের তালিকায় আমার গান যোগ হল। আনন্দ যে খুবই পেয়েছিলাম একথা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। কিন্তু কী সব্বোনাশ!! এতদিন ধরে বাঙালি শ্রোতা পুজোর গান হিসেবে যাঁদের শুনে এসেছেন তাঁদের পরে আমার গানের গ্রহণযোগ্যতা কোথায় এসে ঠেকবে? আমি কি যথেষ্ট যোগ্য বা তৈরি? কোথাও যেন দায়িত্বরক্ষার দায় ও ভয় দু’টোই তলে তলে আঁকড়ে ধরত। তার ওপর আমি যেহেতু লেখা তো দূর অস্ত, দু’কলি সুরও করতে পারি না, তাই যাঁরা পরম যত্নে আমার জন্য গান তৈরি করেন, তাঁদের সৃষ্টির প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করতে পারছি কিনা, সেই চিন্তাও ছিল।
এসব ভাবতে ভাবতেই ২০২০-র পুজোও এসে গেল, কিন্তু আজও সে সংশয় একটুও কাটেনি। তবে আমার পুজোর গানের অস্তিত্ব যাঁদের জন্য, সেই অগ্রজ, অনুজ ও সতীর্থদের প্রতি আমার আকন্ঠ ঋণ। সে ঋণ স্বীকার না করলে এ লেখাও অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। এখনও তাদের কাছে নির্ভয়ে দাবি করতে পারি পুজোর গান – নচিদা, শ্রীকান্তদা, অর্ণাদি, জয়, সৈকত, সঞ্জয়, গৌতমদা, বিশ্বরূপদা, রূপঙ্কর, উদয়, প্রত্যূষ, চৈতালি, আজ আমরা সবাই এক বৃহত্তর পরিবার। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আজ আমার সঙ্গীতচর্চা, সঙ্গীতজীবন, বিশেষ করে পুজোর গান, অনেক যশস্বী শিল্পীদের অনেক কাছে এনে দিয়েছে। অগ্রজ শিল্পীরা তাঁদের প্রশ্রয়ে, স্নেহে প্রতিদিন আমাকে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করেন। কিন্তু মনের কোথাও কোনও গভীরতম গভীরে নিজের হাতে একটু দূরত্ব গড়ে রেখেছি – প্রিয় কাঙ্খিত যা কিছু, বড় বেশি পাওয়া হয়ে গেলে যদি তা মর্যাদাহীন হয়ে পড়ে. সেই ভয়ে। এই দূরত্বটাই তাঁদের মহত্ব আর আমার ক্ষুদ্রতার মধ্যে, আমাদের দুই প্রজন্মের পুজোর গানের মধ্যে একটা সাঁকো – সাঁকোটা থাক।
সঙ্গীতপ্রেমী বাঙালির কাছে শুভমিতা এক পরিচিত নাম। শুভমিতার জন্ম মালদায়।
শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে হাতেখড়ি বাবা যশোদা দুলাল দাসের কাছে। পরবর্তীকালে পণ্ডিত উলহাস কসলকর, বিদূষী পূর্ণিমা চৌধুরীর মতো দিকপাল গুরুদের কাছে তালিম নিয়েছেন। মঞ্চশিল্পী এবং প্লেব্য়াক শিল্পী হিসেবে সমান খ্য়াতি অর্জন করেছেন।