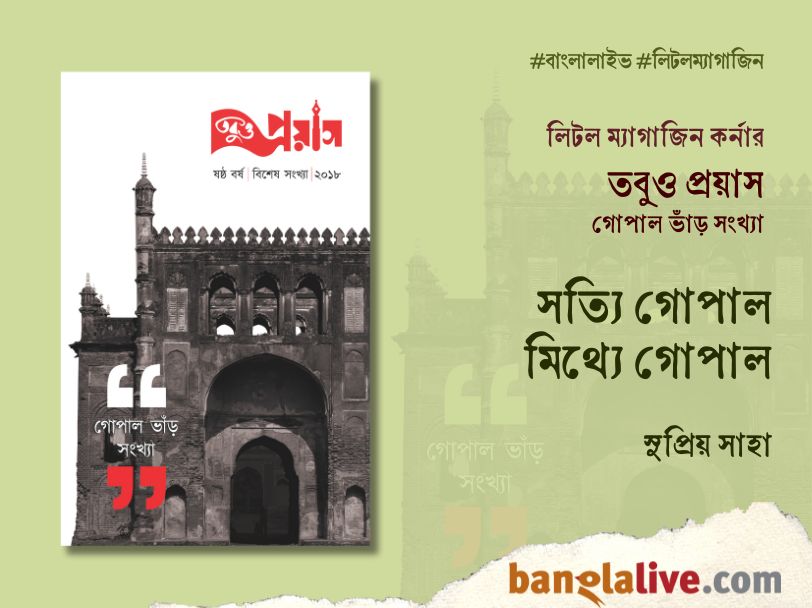(Gopal Bhar)
নদিয়ার মানুষের কাছে তথা সমগ্র বাঙালির কাছে যেমন শ্রীচৈতন্য-এর ‘হত্যা’ আজও এক রহস্য তেমনই গোপাল ভাঁড়ও এক অমীমাংসিত রহস্যচরিত্র। গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে তথ্যানুসন্ধানীরা মূলত তিন ভাগে বিভক্ত। কেউ কেউ বিশ্বাসে ভর করে ও “নবদ্বীপ কাহিনী” আঁকড়ে ধরে বলেন গোপাল সত্যি, আবার কেউ কেউ বিপরীত যুক্তিতে দেখিয়ে যেতে চান গোপাল মিথ্যে আর অল্প কিছু জনই আছেন যাঁরা এখনও কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছেন না সঠিক প্রমাণের অভাবে। এখনও পর্যন্ত, তিনি ছিলেন বা ছিলেন না, এরকম জোর গলায় বলার মতো কিছু হাতে পাওয়া যায়নি, বরং যুক্তির টানাপোড়েনে কোনো একটা দিক ভারী হলেও হতে পারে। (Gopal Bhar)
আরও পড়ুন: ‘সূত্রপাত’ পত্রিকা নবপর্যায়: নাসের রাবাহ-র কবিতা: ভাষান্তর: অরিত্র সান্যাল
২০১৪ সালে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত সুজিত রায় ও শুভাশিস চৌধুরীর লেখা বই “গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে” বর্তমানে শুধুমাত্র গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্ব নিয়ে আলোচিত একমাত্র বই। যদিও আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে বইটি পক্ষপাতদুষ্টতার উপরে উঠতে পারেনি। লেখকদ্বয় মূলত গোপাল ভাঁড়ের বংশধর বলে দাবি করা নগেন্দ্রনাথ দাসের লেখা ১৯২৭ (১৩৩৩ বঙ্গাব্দ) খ্রিস্টাব্দে কুন্তলীন প্রেস থেকে প্রকাশিত গোপাল ভাঁড়ের সম্পর্কে একমাত্র আকর গ্রন্থ বলে পরিচিত “নবদ্বীপ কাহিনী বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়” গ্রন্থটিকেই মান্যতা দিয়েছেন। (Gopal Bhar)
গোপাল ভাঁড়কে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক নানান গ্রন্থে, প্রবন্ধ-নিবন্ধে টুকরো কিছু মন্তব্য করেছেন বা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এরকমই গুরুত্বপূর্ণ মতামতগুলি একে একে তথ্যাদি এবং যুক্তির আলোয় নেড়েচেড়ে দেখতে থাকব এবং সেখান থেকে পাঠক যদি গোপাল ভাঁড় বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তের ধারে কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়, তবে সেটাই হবে এই লেখার সার্থকতা। (Gopal Bhar)
১৭২৮ সালে রঘুরাম মারা গেলে ১৮ বছর বয়সে নদিয়ার সিংহাসনে বসেন কৃষ্ণচন্দ্র। নিজের কাকার সাথে ছল করে সিংহাসনে বসা নিয়ে একটি লোকগল্প প্রচলিত আছে, যদিও তার সেভাবে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কথিত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্যতম সভাসদ ছিলেন গোপাল। রাজা বিক্রমাদিত্যের মতো রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেইসময় তার সভাসদদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কালিদাস সিদ্ধান্ত, কন্দর্প সিদ্ধান্ত, গোবিন্দ রাম, মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল চক্রবর্তী, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমূখ এবং অবশ্যই গোপাল ভাঁড় (যদি ধরে নিই তিনি ছিলেন)। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় কোনো জীবনী লিখিয়ে যাননি। তার জীবদ্দশায় লেখা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের “অন্নদামঙ্গল” থেকে তাঁর সভাসদ ও তাঁর রাজ্য-রাজকার্য সম্পর্কে ভরসা করার মতো তথ্য পাওয়া যায়। ‘ভরসা করার মতো’ বললাম এই কারণে যে, “অন্নদামঙ্গল” লেখার কথা তিনিই ভারতচন্দ্রকে বলেছিলেন। (Gopal Bhar)
“যদি “নবদ্বীপ কাহিনী”-র বক্তব্যে আস্থা রাখি তবে এখান থেকে বোঝা যায় যে, গোপালের সাথে অন্যান্য সভাসদদের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না।”
“তুমি তারে রায় গুণাকর নাম দিও।
রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও।।”
(অন্নদামঙ্গল, গ্রন্থসূচনা)
কৃষ্ণচন্দ্র যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন, সংস্কৃতসহ অন্যান্য ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল, এবং যেহেতু কাব্যগ্রন্থটি তাঁর আদেশে লেখা এবং যেখানে তাঁর নিজের কাহিনিও কিছুটা থাকছে, আশা করা যায় সেই গ্রন্থটি নিশ্চই রাজার অনুমতি ছাড়া ছাড়পত্র পায়নি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বা তাঁর সভাসদদের যে বিস্তারিত উল্লেখ আমরা “অন্নদামঙ্গল” থেকে পাই, সেখানে সামান্য বাজনাদারদেরও নাম কবি উল্লেখ করেছেন ‘কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন’ অংশে। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে কোথাও উল্লেখ নাই গোপাল ভাঁড়ের। গবেষকদের একাংশ এখানেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন গোপাল ভাঁড়ের অস্তিত্ব নিয়ে। তাঁদের মতে গোপাল ভাঁড় যদি সত্যিই থাকত, তবে ভারতচন্দ্র তাঁর নাম উল্লেখ না করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারতেন না। (Gopal Bhar)
এর বিরুদ্ধ যুক্তিতে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চ্যাটার্জী বা মদনমোহন গোস্বামীর মতো কেউ কেউ সন্দেহ করে থাকেন যে, সেসময় ভারতচন্দ্রের সাথে গোপালের সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না, ফলে উভয় তরফেই কখনও কেউ কাউরির বিষয়ে কোথাও উল্লেখ করেননি (যদিও তথ্যটি সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। কারণ, গোপাল ভাঁড়ের বিভিন্ন গল্প সংকলনে ‘রস গড়াবে’ নামক একটি গল্প পাওয়া যাচ্ছে, সে গল্পটি মূলত ভারতচন্দ্রের সাথে সরাসরি গোপালের রসিকতা বিষয়ক)। তাঁদের যুক্তি— ভারতচন্দ্র যেখানে একের পর এক কবিতা শুনিয়ে মহারাজকে খুশি করতে পারতেন সেখানে গোপাল খুব সহজেই তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির কৃপায় রাজাকে খুশি করে ফেলতেন— যার ফলে ভারতচন্দ্রসহ বেশিরভাগ সভাসদগণ গোপালকে হিংসে করত। তবে যুক্তির সেরকম কোনো প্রমাণ কিছুই নেই। তবুও আমরা যদি একটু ঘেঁটে দেখি তবে দেখব যে “নবদ্বীপ কাহিনী”-তে লেখক নগেন্দ্রনাথ দাস জানাচ্ছেন, ‘…এতদ্দৃষ্টে এবং মহারাজের নিকট তাহার বয়স্যোচিত প্রতিপত্তি থাকা দর্শনে অন্যান্য পণ্ডিতগণ ঈর্ষান্বিত হইয়া মহারাজপ্রদত্ত উপাধি “হাস্যার্ণব” অথবা “ভাণ্ডারী” উপেক্ষা করিয়া ভাণ্ডারীর স্থলে ‘ভাঁড়’ শব্দ যোগ করিয়া তাঁহার “গোপাল ভাঁড়” এই নাম প্রচার করিয়াছিলেন…’—যদি “নবদ্বীপ কাহিনী”-র বক্তব্যে আস্থা রাখি তবে এখান থেকে বোঝা যায় যে, গোপালের সাথে অন্যান্য সভাসদদের সম্পর্ক খুব একটা ভালো ছিল না। (Gopal Bhar)
“কৃষ্ণচন্দ্রের সামনে তাঁরই প্রচ্ছন্ন সম্মতিক্রমে একজন সভাসদকে কটাক্ষ করে রাধাকৃষ্ণের এই নিকৃষ্ট রূপ উপস্থাপন করা হয়েছিল, একথা মনে রাখলে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রুচি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে।”
এছাড়াও রজতকান্ত রায়ের “পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ” বইতে তিনি জানাচ্ছেন, ‘…রাজার রাজসভায় শুদ্ধাচার সেভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল না… রাধাকৃষ্ণের প্রণয় ঘটিত ব্যঙ্গ ছলে কোনো এক সভাসদের উপর কটাক্ষ করে রায় গুণাকর লিখেছিলেন:
কৃষ্ণের উক্তি
বয়স আমার অল্প নাহি জানি রস কল্প,
তুমি দেখাইয়া অল্প জাগাইলা যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া,
অঙ্গ ভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী। (Gopal Bhar)
…………………………………………………………….
………………………………………………………’
কৃষ্ণচন্দ্রের সামনে তাঁরই প্রচ্ছন্ন সম্মতিক্রমে একজন সভাসদকে কটাক্ষ করে রাধাকৃষ্ণের এই নিকৃষ্ট রূপ উপস্থাপন করা হয়েছিল, একথা মনে রাখলে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রুচি সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যাবে। রাজা নিজে একটি ধেড়ে (উদবিড়াল) পুষেছিলেন, রায়গুণাকর সেটিকে ছেড়ে কথা কননি:
ধেড়ে কুলে জন্ম পেয়ে বিলে খালে ধেয়ে ধেয়ে
বেড়াইতে ঘুষ খেয়ে লোকে দিত তেড়ে।
তেড়ে না পাইতে মাচ বেড়াইতে পাছ পাছ
এখন বাছের বাছ দিতে লও কেড়ে।। (Gopal Bhar)
………………………………………………..”
“এখন যাঁরা দাবি করেন যে, কবির সাথে গোপালের মোটেও ভালো সম্পর্ক ছিল না, তাঁদেরকে মান্যতা দিয়ে যদি ধরে নিই উপরোক্ত কবিতাগুলিতে যে সভাসদকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তিনি গোপাল ভাঁড়, তবে “অন্নদামঙ্গল”-এ গোপালের নাম উল্লেখ না থাকার অতিদুর্বল হলেও একটা যুক্তি তৈরি হয়।”
উপরিউক্ত লাইনগুলি (রজতকান্ত রায় এগুলির কোনো তথ্যসূত্র দেননি) থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, রায়গুণাকরের সাথে কোনো এক সভাসদের সম্পর্ক মোটেও ভালো ছিল না। রাজা উদবিড়াল পুষেছেন আর সেটিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন কবি— এই ধারণার চেয়ে বরং গোটা কবিতাটা পড়লে এটা ভাবা সহজ যে, এই কবিতাটিতে ভারতচন্দ্র সেই সভাসদকেই ‘ধেড়ে’ উল্লেখ করে ব্যঙ্গ করে গেছেন। এখন যাঁরা দাবি করেন যে, কবির সাথে গোপালের মোটেও ভালো সম্পর্ক ছিল না, তাঁদেরকে মান্যতা দিয়ে যদি ধরে নিই উপরোক্ত কবিতাগুলিতে যে সভাসদকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে তিনি গোপাল ভাঁড়, তবে “অন্নদামঙ্গল”-এ গোপালের নাম উল্লেখ না থাকার অতিদুর্বল হলেও একটা যুক্তি তৈরি হয়। (Gopal Bhar)
যদিও গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে একমাত্র আকর গ্রন্থ বলে পরিচিত “নবদ্বীপ কাহিনী”-র লেখক নগেন্দ্রনাথ দাস বইয়ের শেষে বলছেন উলটো কথা— “রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত যে তাঁহার (গোপাল ভাঁড়ের) হৃদ্যতা অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, তাহা রায়গুণাকরের কথাতেই ব্যক্ত হয়েছে। একদিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর নাটক পাঠ করিয়া বঙ্গের শ্রেষ্ঠকবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কবিবর— তুমি এই আদিরস কোন মহাসাগর মন্থন করিয়া সঞ্চয় করিলে— (Gopal Bhar)
তখন ভারতচন্দ্র বলিলেন— মহারাজ!—
অঞ্জনার তীরে ধাম গোপাল চন্দ্র নাই নাম,
রস-রাজ রসের সাগর।
ভারতচন্দ্র গুণাকর, যার গুণে গুণাকর,
মথিলাম সে মহাসাগর।।”
“কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হিসেবে পরিচিত হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত বা রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কারের নামও ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল”-এ পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও তারা যে ছিলেন তা পরবর্তীতে প্রমাণিত।”
সুজিত দাস তাঁর “গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে”-তে নিজেই এই লাইনগুলি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর গ্রন্থেই রয়েছে, “রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র”— গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক মদনমোহন গোস্বামী অবশ্য লিখছেন, ‘কিন্তু এই উক্তি যথার্থ বলিয়া মনে হয় না’। কারণ হিসেবে মদনমোহন গোস্বামী বলেছেন যে, লন্ডন এবং প্যারিসে সংরক্ষিত ভারতচন্দ্রের প্রাচীনতম বিদ্যাসুন্দর পুঁথিতে তিনি এই লাইনগুলি পাননি। কিন্তু এখানে একটা সন্দেহ থেকেই যায়, নগেন্দ্রনাথ কিন্তু কোথাও বলেননি যে তিনি এই লাইন বিদ্যাসুন্দর কাব্যগ্রন্থেই পেয়েছেন আবার তিনি কোথাও উল্লেখও করেননি যে এই লাইনগুলো তিনি পেয়েছেন কোথা থেকে। (Gopal Bhar)
তাহলে কি আমরা ধরে নেব যে, নগেন্দ্রদাস মহাশয় এই লাইন দুখানি নিজেই লিখেছিলেন(?) কারণ কাব্য রচনায় তাঁর যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল সেটা “নবদ্বীপ কাহিনী”-র উৎসর্গ পত্র পড়লেই বোঝা যায়। (Gopal Bhar)
এই প্রসঙ্গে আরো একটি সম্ভবনা তৈরি হয় যে, হয়তো রায়গুণাকর যখন কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় এসেছিলেন তখন গোপাল ভাঁড় রাজার সভাসদ হননি। ১৭৫২ সালে কৃষ্ণনগরে আসেন ভারতচন্দ্র। বছর তিনেক তিনি রাজসভায় ছিলেন, পরবর্তীতে বসবাস করেছেন মূলাজোড় গ্রামে। এবং কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে “অন্নদামঙ্গল” লেখা হয়েছে সম্ভবত ১৭৫২-৫৩ সালের মধ্যেই। গোপাল ভাঁড় ঠিক কত সালে রাজসভায় এসেছেন সে বিষয়ে কোনো তথ্যই কোথাও নেই। অনেকেই তথ্য ছাড়াই ধরে নেন তিনি প্রথম থেকেই রাজসভায় আছেন। আবার “নবদ্বীপ কাহিনী”-র মতানুসারে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে হুগলী থেকে নিয়ে আসেন, কিন্তু কত সালে সেসব কিছুই না থাকলেও একটা ইঙ্গিত এই বই থেকে পাওয়া যায়। এই বইয়ের ২৫ নং পৃষ্ঠার শেষের দিকে লেখক বলেছেন, “…কেবল একমাত্র সদানন্দ পুরুষ গোপালচন্দ্র মহারাজের জীবনের যৌবনকাল হইতে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত বসন্তকালের মলয় পবনে পুলকিত কোকিলের ন্যায় রসালাপে মহারাজের মনঃ পুলকিত রাখিয়াছিলেন।”— এই লাইনটি ধরে যদি আমরা হিসেব করি তবে দেখব যে, ১৭৫২ সালে মহারাজের বয়স ৪২ বছর, যখন ভারতচন্দ্র রাজসভায় আসেন। হতেই পারে রাজার বয়স যখন ৪৫, অর্থাৎ ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনগর থেকে বিদায় নিয়েছেন তার পরেই গোপালের আবির্ভাব। কারণ, গোপালের জন্মসাল-মৃত্যুসাল নিয়ে কোনো তথ্যই পাওয়া যায় না। (Gopal Bhar)
“ভারতচন্দ্র যখন ‘গুণাকর’ উপাধি পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অবস্থিতি করছিলেন তখন প্রধান নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত বা প্রধান স্মার্ত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার এরকম কাউকে সেখানে উপস্থিত দেখেননি…”
আবার “ক্ষিতিশ বংশাবলি চরিত” অনুয়ায়ী গোপাল শান্তিপুরের বাসিন্দা, কিন্তু কত সালে তিনি রাজসভায় আসেন সে বিষয়েও কিছু নাই। এই ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ‘চির নতুন গোপাল ভাঁড় রহস্য (হাস্যরসের ভান্ডার)’। এর কটি লাইনের দিকে তাকাই, যেখানে গোপালের গল্প নিয়ে বলা হয়েছে— “…কয়েকটা গল্পের উৎপত্তি নবাবী আমলে হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। তবে বেশিরভাগ গল্প ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দর কাছাকাছি ইংরাজ আমলের গোড়ার দিকের গল্প বলেই মনে হয়— তখন কৃষ্ণচন্দ্রের শেষ বয়স”, তাহলে মনে হবে যেন গোপালের আবির্ভাব কৃষ্ণচন্দ্রের শেষের দিকে অর্থাৎ আমাদের আগের যুক্তির সাথে এটা অনেকটাই মিলে যায়। এই যুক্তি অনুসারে “অন্নদামঙ্গলে” গোপালের অনুপস্থিতির কারণ কিছুটা ব্যাখ্যা করা যায়। তবে এর জন্য সেরকম কোনো উপযুক্ত প্রমাণ আমার হাতে না থাকলেও একটা প্রমান দেওয়ার চেষ্টা করব (Gopal Bhar)—
রজতকান্ত রায়ের “পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ” বইটির ৭৯ পাতায় অদ্ভুত কিছু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হিসেবে পরিচিত হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত বা রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কারের নামও ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙ্গল”-এ পাওয়া যাচ্ছে না, যদিও তারা যে ছিলেন তা পরবর্তীতে প্রমাণিত। রজতকান্ত রায় বলছেন—
“ভারতচন্দ্র যখন ‘গুণাকর’ উপাধি পেয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অবস্থিতি করছিলেন তখন প্রধান নৈয়ায়িক হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত বা প্রধান স্মার্ত রামগোপাল ন্যায়ালঙ্কার এরকম কাউকে সেখানে উপস্থিত দেখেননি— এঁরা নিজ নিজ ভূমি ও ভদ্রাসনের উপর বাস করে বিদ্যাচর্চা করতেন বলে ধরে নেওয়াই সঙ্গত”। (Gopal Bhar)
“সুজিত রায় তাঁর “গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে”-তে জানাচ্ছেন উপরিউক্ত এই লাইন দুটিকে প্রমাণস্বরূপ দেখিয়ে গবেষক সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, রাজসভায় গোপাল ভাঁড়ের উল্লেখ না থাকলেও ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যগ্রন্থে শঙ্কর তরঙ্গ এবং বলরাম (পাঠান্তরে রাম বোস) নামক দু’জন কৌতুকী পারিষদের নামোল্লেখ করেছেন।”
এই বক্তব্য মেনে নিলে কিন্তু “অন্নদামঙ্গল”-এ গোপালের নাম উল্লেখ না থাকার কারণের কিছুটা ব্যাখ্যা মেলে। কিন্তু আর একটি প্রশ্ন মনে উঁকি দিচ্ছে তা হল, ভারতচন্দ্র সাধক রামপ্রসাদের নাম উল্লেখ করেছেন, যদিও রামপ্রসাদ রাজসভায় কোনোদিনই স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি। তবে এটার একটা ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, রামপ্রসাদের গানের জন্য সাধক পূর্বে উল্লেখিত ঐ দুই ব্যক্তির থেকে মানুষের কাছে বেশি পরিচিত ছিলেন, এবং সেখান থেকেই ভারতচন্দ্র তাঁর নাম শুনে কাব্যে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রমাণ কিছুই আপাতত নেই। (Gopal Bhar)
অথচ রজতকান্ত রায় কোনো তথ্য প্রমাণ ছাড়াই বলছেন যে, “পারিষদ দলের মধ্যে ভারতচন্দ্র নিজের এবং গোপাল ভাঁড়ের নাম করেননি, কিন্তু এই দুই জনের জন্যই কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা বাঙালির স্মৃতিপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে।” এবং ঐ বইয়ের ৮৪ নং পাতাতে বলছেন, “…কিন্তু গোপাল ভাঁড় সম্পূর্ণ কল্পিত চরিত্র না হওয়াই সম্ভব।” (Gopal Bhar)
“অতিপ্রিয় পারিষদ শঙ্কর তরঙ্গ।
হরহিত রামবোল সদা অঙ্গসঙ্গ।।”
(অন্নদামঙ্গল , কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণন)
আরও পড়ুন: ‘সর্বনাম’ পত্রিকা, অষ্টম সংখ্যা: বিপজ্জনক কবিতার পাশে- রণজিৎ অধিকারী
সুজিত রায় তাঁর “গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে”-তে জানাচ্ছেন উপরিউক্ত এই লাইন দুটিকে প্রমাণস্বরূপ দেখিয়ে গবেষক সুকুমার সেন জানিয়েছেন যে, রাজসভায় গোপাল ভাঁড়ের উল্লেখ না থাকলেও ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যগ্রন্থে শঙ্কর তরঙ্গ এবং বলরাম (পাঠান্তরে রাম বোস) নামক দু’জন কৌতুকী পারিষদের নামোল্লেখ করেছেন। অনেকেই শঙ্কর তরঙ্গকে গোপাল ভাঁড় হিসেবে ধরে নেন। অলোককুমার চক্রবর্তী “মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ”-এ শঙ্কর তরঙ্গকে শুধুমাত্র মহারাজের নিত্যসহচর বলে উল্লেখ করেছেন। আবার সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত “বাংলাপিডিয়া”-র ৩য় খণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে, ‘রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেহরক্ষক হিসেবে শঙ্কর তরঙ্গ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য রাজা তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিতেন। হয়ত তিনিই পরবর্তীকালে গোপাল ভাঁড় হিসেবে কল্পিত হয়েছেন।’ কিন্তু রাজসভার প্রথাগত দেওয়ান ‘চক্রবর্তী’-র বংশধর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বাবা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় যখন মাহারাজ শ্রীশচন্দ্রের দরবারে কর্মরত ছিলেন তখন তিনি ১৮৭৫ সালে “ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত” নামে একটি বই লেখেন। বইটির অনেক তথ্য ১৮৫২ সালে বার্লিন থেকে মুদ্রিত সংস্কৃতে লেখা “ক্ষিতিশবংশাবলিচরিত্রং” বইটি থেকে নেওয়া— এমনটাই প্রচারিত। যাইহোক কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর গ্রন্থে জানাচ্ছেন যে, ‘রাজসভায় মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড়, এবং হাস্যার্ণব নামে তিন ব্যক্তি অসাধারণ রসিক ও পরিহাসক ছিল।” এবং তিনি এই তিনজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণীও দিয়েছেন। যদি “ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত”-কে অনেক গবেষকের মতো আমরাও মান্যতা দিই তাহলে মেনে নিতেই হয় যে, গোপাল ভাঁড় শঙ্কর তরঙ্গ নন, বরং তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি চরিত্র। আবার সংস্কৃতে লেখা “ক্ষিতিশবংশাবলিচরিত্রং” সম্পর্কে ঐতিহাসিক রজতকান্তি রায় ‘নির্ভরযোগ্য ইতিহাস বলে ধরা যায় না’ বলে মন্তব্য করেছেন। এই “ক্ষিতিশবংশাবলিচরিত্রং”-এর লেখক হিসেবে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ হয়, যদিও মোহিত রায় সম্পাদিত কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের লেখা “ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত”-এ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পরিষ্কার বলা আছে জার্মানে সংরক্ষিত “ক্ষিতিশবংশাবলিচরিত্রং”-এ লেখকের নাম কোথাও উল্লেখ নেই। কান্তিচন্দ্র রাড়ী তাঁর “নবদ্বীপ মহিমা”-তে জানাচ্ছেন এই বই কোনো একজন পণ্ডিতের লেখা নয় বরং কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভার পণ্ডিতদের দিয়ে এই বই লিখিয়েছিলেন। এ ছাড়াও ১৮৮০ সালে প্রকাশিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ রচিত “কল্পদ্রুম তৃতিয় খণ্ড”-তে লেখক “ক্ষিতিশবংশাবলিচরিত্রং”-কে “রাজতরঙ্গীনি”-র থেকেও ত্রুটিহীন, গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়ে এর লেখক সম্পর্কে বলছেন, ‘…ইহার রচনাপ্রনালী মার্জিত নহে। লেখার ধরন দেখিয়া স্পষ্ট অনুমান হয়, গ্রন্থকার সংস্কৃত বিদ্যায় ভালরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। আমরা অনেক যত্ন করিলাম; কিন্তু রচয়িতার নাম পাইলাম না।…’ এছাড়াও তিনি আরো বলেছেন যে, ‘…এমন প্রসিদ্ধ রাজ-বংশের ইতিবৃতব লিখিত মাই ইহ দেখিয় লড়া হেস্টিংস কোন পণ্ডিত দ্বারা নবদ্বীপ রাজবংশের বিবরণ লেখাইবার জন্য কৃষ্ণচন্দ্র রাজাকে বিশেষ অনুরোধ করেন। লাট সাহেবের নিরব্বন্ধীতিশয় অতিক্রম করিতে না পারিয়া দুইখানি পুস্তক লিখিত হয়— একখানি সংস্কৃত ভাষায়, তাহার নাম ক্ষিতিশবংশাবলিচরিত্রং। আর একখানি বাঙ্গাল ভাষায়, তাহার নাম কৃষ্ণচন্দ্রচরিত।’ এই “কৃষ্ণচন্দ্রচরিত” বা “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং’-এর লেখক নদিয়া রাজপরিবারের আত্মীয় রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলার শিক্ষক, তিনি উইলিয়াম কেরীর নির্দেশেই এই বই লেখেন (তথ্যসূত্র: গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে)। এখন এই রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, “ক্ষিতিশবংশাবলিচরিত্রং”, যে বই মূলত কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে, তার লেখক হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন। কিন্তু যেটা বলার তা হল, এই বইটিতে গোপালের কোনো কথা কোথাও লেখা নেই। তার মানে কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের “ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত”- এ তিনি গোপালের যে বিবরণ দিয়েছেন সেটি তাঁর নিজস্ব অথবা সেই সময়ের রাজপরিবার বা অন্য কোথাও থেকে সংগৃহীত। যেখানে তিনি বলেছেন, ‘…তাহার (গোপাল ভাঁড়) বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার ভিটায় অন্য একজন ক্ষুরিজাতীয় বাস করে।’ (Gopal Bhar)
“রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে, সেটা হল পলাশীর যুদ্ধ তথা পলাশীর ষড়যন্ত্র।”
পত্রপত্রিকা, বিভিন্ন রিসার্চ আর্টিকেল এবং বইয়ে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণনগর রাজবংশের সমস্ত প্রজন্মই ছোটো থেকে শুনে আসছেন গোপাল ছিল। এবং কৃষ্ণচন্দ্রের সাথে তাঁর ভীষণই গভীর সম্পর্ক ছিল— প্রমাণস্বরূপ নগেন্দ্রনাথ দাসের “নবদ্বীপ কাহিনী”। যেখানে লেখক এমনও বলেছেন যে, কোনো উচ্চব্যক্তির বাড়িতে গোপালের নিমন্ত্রণ না থাকলে রাজা নিজেও সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন না। অনেকে বলেছেন রাজা যখন শিবনিবাসে বা অন্যত্র বসবাস করছেন গোপাল তখনও তাঁর সঙ্গী ছিল। রাজপরিবারের তথ্যভাণ্ডার বা সমসাময়িক লেখায় যদিও আমরা তার উল্লেখ সেভাবে পাচ্ছি না, তবুও যদি ধরে নিই তিনি রাজার সর্বক্ষণের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন, তাহলে একটি জটিল রহস্য তৈরি হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটে, সেটা হল পলাশীর যুদ্ধ তথা পলাশীর ষড়যন্ত্র। (Gopal Bhar)
রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং” প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রীরামপুর থেকে ১৮০৫ সালে, এরপর ১৮১১ সালে লন্ডন থেকে এবং তারপর ১৮৩৪ এবং ১৮৫৭ সালে শ্রীরামপুর থেকে এবং শেষে রেবরণ্ড জে লং সাহেবের আদেশে ১৮৫৮ (১৭৮০ শকাব্দ) সালে গোপীনাথ চক্রবর্তী এন্ড কোম্পানির উদ্যোগে শ্রীরামপুর থেকে, যদিও এখানে লেখক হিসেবে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের নাম নেই। এই সব তথ্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, এই বইটি তৎকালীন সমাজে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল এবং এই বইটিই প্রথম বই যেখানে দাবি করা হয় পলাশীর ষড়যন্ত্রের মূল মস্তিষ্ক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এখানে বিশদে সেই চক্রান্ত এবং তার সাথে কীভাবে মাহারাজ যুক্ত ছিলেন তার বিবরণ দেওয়া রয়েছে। যদিও বইটি সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিকদের কাছে মোটেও বিশ্বাসযোগ্য নয়, কিন্তু তাঁরা এই বইয়ের সম্পূর্ণ বক্তব্যকে উড়িয়েও দেননি। মানে কৃষ্ণচন্দ্র কোনো না কোনোভাবে এই চক্রান্তের সাথে জড়িয়ে ছিলেন। পরবর্তীতে ১৮৭৫-এ নবীনচন্দ্র সেনও এই একই কথা বলেছেন এবং ১৯২৭-এ নগেন্দ্রনাথ দাসও “নবদ্বীপ কাহিনী”-তে বলছেন, ‘ইহা বেদবাক্য যে, একমাত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে।’ এছাড়াও দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় তাঁর “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত”-এও কৃষ্ণচন্দ্রের এই ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার কথা বলেছেন। আমরা এই বিষয়ের খুব ভিতরে ঢুকব না কারণ, সে এক মহাভারত হয়ে যাবে। বরং আমরা যদি ধরেই নিই উপরোক্ত কথাগুলো সত্যি, তাহলে “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং” থেকে বলতে পারি যে, এই ষড়যন্ত্রের বিষয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সর্বদা তাঁর নিত্যসহচরদের সাথে আলোচনা করতেন এবং নবাবের ভয়ে কোনো এক জায়গায় নির্দিষ্টভাবে বসবাস করতেন না। যদি ধরে নিই গোপাল ভাঁড় তাঁর নিত্যসহচর ছিল, তাহলে গোপাল ভাঁড়ও এ বিষয়ে জানতেন ধরে নিতে হবে। কারণ “নবদ্বীপ কাহিনী” বলছে গোপাল রাজার জটিল থেকে জটিল সমস্যা তৎক্ষণাৎ সমাধান করে দিত এবং ‘গোপালচন্দ্রের মতো ভগবৎকৃপাভিষিক্ত উত্তরসাধক মহারাজের পার্শ্বে না থাকিলে মুসলমান নবাবদিগের হস্তে মহারাজের রক্ষা পাওয়া দুর্ঘট হইত’ (কৃষ্ণচন্দ্রকে আলিবর্দি বেশ কয়েকবার খাজনা না দেওয়ার জন্য ধরে নিয়ে গেছিলেন এবং তৎকালীন দেওয়ানের বুদ্ধিতে তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন)। “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং” থেকে আমরা জানতে পারি যে, রাজার পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি এই ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল সম্ভবত তিনি রাজার দেওয়ান কালীশঙ্কর সিংহ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ব্যক্তিই কি গোপাল? কোনো প্রমাণ নেই। সুজিত রায় তাঁর “গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে”-তে জানাচ্ছেন যে, গোপাল ভাঁড়ের বর্তমান প্রজন্ম বলে পরিচিতি যাঁরা দেন তাঁরা জানিয়েছেন যে, গোপালের সাথে ক্লাইভের করমর্দনের একটি ছবি এখনও তাদের কাছে আছে। যদি তাদের কথা সত্যি বলে ধরে নিই, তাহলে একটা সন্দেহ দেখা দেয় যে, হয়তো গোপাল ক্লাইভের পূর্বপরিচিত ছিলেন (কারণ, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারীদের সাথে ক্লাইভের এরকম ছবির উল্লেখ তো পাওয়া যায় না), এবং সেটা কি পলাশীর ষড়যন্ত্রের কারণেই? এ শুধুই সন্দেহ, উত্তর নাই। সুজিতবাবু আরও জানাচ্ছেন যে, ‘তবে জনশ্রুতি, এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে মাহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের যুক্ত হওয়াকে গোপাল নাকি ভাল চোখে দেখেননি।’—এখন জনশ্রুতিকেই যদি ইতিহাস ধরে নিই, তাহলে তো ‘খনার বচন’ এর খনাকেও বাস্তব চরিত্র বলে ধরে নিতে হয়! (Gopal Bhar)
“জ্ঞানেন্দ্র কুমার বলছেন, গোপালের পদবি ‘ভাণ্ডারী’। নগেন্দ্রনাথ দাসের “নবদ্বীপ কাহিনী” থেকে জানতে পারছি যে, রাজা তাকে ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিয়েছিল, এবং ‘ভাণ্ডারী’ উপাধী দান করেছিল।”
গোপাল বাস্তব নাকি কল্পিত চরিত্র সে নিয়ে এত দ্বন্দ্বের কারণ গোপাল সম্পর্কিত কোনো তথ্যই একমুখী নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রমাণ ছাড়া তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী মতামত উঠে এসেছে, যেমন—
নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ বলছে, গোপালের জন্ম গুপ্তিপাড়া বা শান্তিপুরে, জাতিতে কায়স্থ, উপাধি ছিল বিশ্বাস, এবং লেখাপড়া জানতেন। —লেখাপড়া জানলে গোপাল তাঁর গল্পগুলো লিপিবদ্ধ করার কোনো ব্যবস্থা সেসময় নিশ্চই করত? আবার “নবদ্বীপ কাহিনী” জানাচ্ছে যে, গোপাল সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত ছিলেন না। (Gopal Bhar)
জ্ঞানেন্দ্র কুমার বলছেন, গোপালের পদবি ‘ভাণ্ডারী’। নগেন্দ্রনাথ দাসের “নবদ্বীপ কাহিনী” থেকে জানতে পারছি যে, রাজা তাকে ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিয়েছিল, এবং ‘ভাণ্ডারী’ উপাধী দান করেছিল। তাহলে তাঁর মূল পদবি কী ছিল? বেশিরভাগ গবেষকই বলছেন তাঁর বংশগত উপাধি ছিল ‘নাই’। (Gopal Bhar)
“অনেকেই জানাচ্ছেন তিনি ছিলেন জাতিতে নাপিত। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটু বিস্তারিত তথ্য যা পাওয়া যাচ্ছে মাত্র দুটি বইয়ে…”
ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত ঈশ্বরগুপ্ত রচিত “কবিজীবনী”-এর ৩১৮ নং পাতায় রয়েছে, ‘গোপাল ভাণ্ড কেবল ভাণ্ডই ছিল, তাহার অপর কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না।’ (Gopal Bhar)
অনেকেই জানাচ্ছেন তিনি ছিলেন জাতিতে নাপিত। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে একটু বিস্তারিত তথ্য যা পাওয়া যাচ্ছে মাত্র দুটি বইয়ে— কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের “ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত”-এ তিনি জানাচ্ছেন “রাজসভায় মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড়, এবং হাস্যার্ণব নামে তিন ব্যক্তি অসাধারণ রসিক ও পরিহাসক ছিল।’ এবং গোপালের বিস্তারিত তথ্যে তিনি বলছেন, ‘গোপাল ভাঁড় নরসুন্দর জাতীয় এবং শান্তিপুর নিবাসী। তাহার বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার ভিটায় অন্য একজন ক্ষুরিজাতীয় বাস করেন।’ মুশকিল হল যে, শেষ লাইনে যে ভিটের কথা তিনি বলেছেন, সে ভিটে কি শান্তিপুরে নাকি অন্য কোথাও? তাছাড়া লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী বর্তমানে (তৎকালীন) বসবাসকারী ‘ক্ষুরিজাতীয়’ ব্যক্তির সাথে কি গোপালের কোনোরকম সম্পর্ক ছিল? জানার উপায় নেই। গোপাল যদি রাজসভার সভাসদ এবং রাজার অতি কাছের লোক হয়েই থাকেন তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে, শান্তিপুরে তাঁর আদি নিবাস হলেও কৃষ্ণনগরে তাঁর বসবাস ছিল। যেমন ঘূর্ণি অঞ্চলের মানুষ মনে করেন যে, গোপাল ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন, কিন্তু প্রমাণ কোনো নাই। কিন্তু যদি আমরা “নবদ্বীপ কাহিনী”-র শেষে ভারতচন্দ্রের কবিতা বলে উল্লেখিত লাইনগুলি আরো একবার দেখি, ‘অঞ্জনার তীরে ধাম/ গোপাল চন্দ্র নাই নাম/ রস-রাজ রসের সাগর’ তাহলে মনে হবে গোপালের বাস অঞ্জনার তীরে মানে কৃষ্ণনগর বা তার আশেপাশেই। (Gopal Bhar)
“পরবর্তীতে গোপালের বেশিরভাগ গল্প সংকলনগুলিতে সম্পাদকেরা বিনা তথ্যপ্রমাণে তাঁকে ঘূর্ণি নিবাসী এক দরিদ্র ক্ষৌরকারের পুত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে গেছেন।”
হাস্যরসিক শ্রীশ্যামসুন্দর ধর ও ঔপন্যাসিক শ্রী ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত কলকাতা টাউন লাইব্রেরি থেকে ১৯৫১ সালে প্রকাশিত (তৃতীয় সংস্করণ) গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সংকলন “গোপাল ভাঁড় রহস্য” বইয়ের শুরুতে ‘গোপাল ভাঁড়ের জীবনী’ অংশে জানাচ্ছেন যে, সে-সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড় ছাড়াও আজু গোঁসাই, হাস্যরাম, মুক্তিরাম প্রভৃতি সুরসিকদের উপস্থিতি ছিল। তবে গোপালের মতো দেশ-বিদেশে খ্যাতি অন্য কেউ পাননি। গোপালের বাসস্থান সম্পর্কে তাঁরাও কিছুটা অন্ধকারে, একবার বলছেন যে হতে পারে ‘…ঘূর্ণি নামে যে পল্লী আছে সেই পল্লীরই এক দরিদ্র ক্ষৌরকার গৃহে গোপালের জন্ম হয়।’ আবার বলছেন, কেউ কেউ বলে শান্তিপুরে আদি বাস, বাবা মারা যাওয়ার পর গোপাল অর্থ উপার্জনের জন্য কৃষ্ণনগর আসেন। এবং তাঁরা এটাও জানাচ্ছেন যে, ‘…এ সকলের আর সুমীমাংসা হইবার কোনই উপায় নেই। প্রাচীন কাগজপত্রে কোথাও এ সম্বন্ধে যখন কোথাও কিছুই উল্লেখ নাই…’ —এখান থেকে তাহলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে সরকারি/ রাজদরবারী কাগজে কোথাও গোপালের উল্লেখ নাই। লেখকদ্বয় আরো জানাচ্ছেন যে, শান্তিপুর বা ঘূর্ণি যেখানেই গোপালের বাসস্থান হোক না কেন তিনি নাপিতের ছেলে এবং খুব গরিব। ছোটো বয়সে বাবা মারা যাওয়ার পর তাঁকেই উপার্জনের বিভিন্ন উপায় খুঁজতে হয়। ফলে খুব ছোটো থেকেই তাঁকে মিশতে হয়েছে নানান ধরনের মানুষের সাথে এবং জীবনের নানান অভিজ্ঞতা তাঁকে পোক্ত করেছে। এরফলে তাঁর ভিতরের সহজাত রসবোধ আরো ফুটে উঠেছে, এবং সেই গুণের কথা শুনেই মহারাজ তাঁকে ‘পরামানিকপুত্র’ জেনেও রাজসভায় স্থান দিয়েছেন। —গোপালের অস্তিত্বে বিশ্বাসী লেখকদ্বয় তাদের সপক্ষে তথ্যপ্রমান বা তথ্যসূত্র না দিলেও অনেকটাই বাস্তবসম্মত রূপরেখা টানতে সক্ষম হয়েছেন। (Gopal Bhar)
পরবর্তীতে গোপালের বেশিরভাগ গল্প সংকলনগুলিতে সম্পাদকেরা বিনা তথ্যপ্রমাণে তাঁকে ঘূর্ণি নিবাসী এক দরিদ্র ক্ষৌরকারের পুত্র হিসেবে পরিচয় দিয়ে গেছেন। এবং গোপালের খুব অল্প বয়সেই তাঁর বাবা মারা যান, ফলে তাঁর পড়াশুনো বন্ধ হয়, এবং তাঁর গুণের খবর পেয়ে রাজা তাঁকে নিয়ে আসেন— এই তথ্যই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলে গেছেন। এবং হয়তো এখান থেকেই নদিয়াবাসীদের একটা ধারণা হয়েছে যে, গোপাল বুঝি ঘূর্ণি’রই বাসিন্দা! (Gopal Bhar)
গোপাল ভাঁড়কে যাঁরা বাস্তব চরিত্র বলে ধরে নেন, তাঁরা সবথেকে বড়ো প্রমাণ হিসেবে নগেন্দ্রনাথ দাসের “নবদ্বীপ কাহিনী” বা “মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়” বইটিকে দেখান। আমরা এখন সেই বইটির নানান বক্তব্য নিয়ে কিছুটা আলোচনা করব। (Gopal Bhar)
“কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সকলেই বিশ্বাস করেন যে, গোপাল ভাঁড় ছিলেন, এবং এর আগে মাত্র “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত” ছাড়া সেভাবে কোথাও গোপালের উল্লেখ নেই, তাই শুধুমাত্র গোপাল ভাঁড় ও কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে লেখা একটি বই থাকলে তা অবশ্যই একটি প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।”
এই বইটি বর্তমানে জোগাড় করা বেশ কঠিন। আমি ন্যাশানাল লাইব্রেরিতে বইটির যে কপিটি পড়তে পাই, সেটাতে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২। বইটি কোন সালে প্রকাশিত কোথাও উল্লেখ না থাকলেও শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকার শেষে ১৩৩৩ সাল উল্লেখ আছে, এবং যদি ১৩৩৩-কে বঙ্গাব্দ ধরে নিই তাহলে সেখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, ইংরেজি ১৯২৭ সালে এটি প্রকাশিত। বইটি কুন্তলীন প্রেস থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশক স্বয়ং লেখক। ভূমিকার পর রয়েছে তৎকালীন মহারাজ শ্রীক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের একটি ছবি এবং পরের পাতায় তাঁকে এই বইয়ের উৎসর্গপত্রস্বরূপ একটি কবিতা। সুজিত রায়ের বই থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯২৯-এর আগস্ট মাসে এই বইটিকে নদিয়া জেলার প্রাথমিক ও মেয়েদের স্কুলের পাঠ্য বই হিসেবে বিবেচনার জন্য মাহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় তৎকালীন শিক্ষা সচিবের কাছে অনুরোধ করেছিলেন। এই তথ্য থেকে এটা বোঝা যায় যে, লেখকের সাথে তৎকালীন মাহারাজের সুসম্পর্ক ছিল এবং স্বাভাবিক যে বইটি লেখার জন্য মহারাজ ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কিছু ইন্ধন থাকতে পারে, কারণ কৃষ্ণনগর রাজপরিবারের সকলেই বিশ্বাস করেন যে, গোপাল ভাঁড় ছিলেন, এবং এর আগে মাত্র “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত” ছাড়া সেভাবে কোথাও গোপালের উল্লেখ নেই, তাই শুধুমাত্র গোপাল ভাঁড় ও কৃষ্ণচন্দ্রকে নিয়ে লেখা একটি বই থাকলে তা অবশ্যই একটি প্রতিষ্ঠিত প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। এবং বর্তমানে এই বইটিকেই রাজবংশের মানুষজন এবং গোপালের অস্তিত্বে বিশ্বাসী বা যারা তাঁর বর্তমান বংশধর বলে পরিচিতি দেন সকলেই বিনাশর্তে প্রমাণ হিসেবে ধরে নেন। (Gopal Bhar)
বইটি মোট ছটি ভাগে বিভক্ত। যথা—
১) শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা
২) নবদ্বীপ কাহিনীর উৎসর্গপত্র
৩) নবদ্বীপ কাহিনী – রসতত্ত্ব
8) সাহিত্য জাতীয় সভ্যতার সোপান
৫) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভান্ডারী
৬) গোপাল ভান্ডারীর বংশ ইতিহাস
“সিরাজ নবাব ছিলেন দু’বছরেরও অনেক কম, ফলে প্রথম লাইনটিও ভুল। এই ভুল হয়তো তৎকালে চলতে থাকা সিরাজ বিরোধী ধারণাকে ও প্রচলিত গল্পগুলিকে কেন্দ্র করেই মানুষের মনে বাসা বেঁধেছিল।”
এই বইয়ের ভূমিকা লেখার কারণ হিসেবে শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী লিখছেন, ‘আমার এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিবার কারণ এই যে, গ্রন্থকার আমার পরম স্নেহ ও প্রীতির পাত্র, গুণের সমাদর করা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের কূলধর্ম এবং বিশেষতঃ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত আমাদের সম্বন্ধ আছে। কারণ তিনি আমাদের পূর্ব পুরুষকে পাণ্ডিত্যের ও সদাচারের পুরস্কারস্বরূপ সহস্র বিঘা লক্ষ্মীর ভূমি ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন…’ এবং আর একটি অদ্ভূত তথ্য তিনি এখানে দিয়েছেন, ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বসময়ে বঙ্গ, বিহার এবং উড়িষ্যা প্রদেশগুলি নবাব সিরাজোদ্দৌলার অধীন ছিল। কঠিন প্রাণ সিরাজোদ্দৌলার মন মোহিত করিতে তৎকালে কেবল দুই জন মাত্র সাধক ছিল— প্রথম হাস্যার্ণব গোপাল ভাঁড় এবং দ্বিতীয় স্বভাবকবি কালীভক্ত রামপ্রসাদ।’—শেষ লাইনটির মানে এবং তাৎপর্য কিছুই বোঝা যায় না। সিরাজ নবাব ছিলেন দু’বছরেরও অনেক কম, ফলে প্রথম লাইনটিও ভুল। এই ভুল হয়তো তৎকালে চলতে থাকা সিরাজ বিরোধী ধারণাকে ও প্রচলিত গল্পগুলিকে কেন্দ্র করেই মানুষের মনে বাসা বেঁধেছিল। আমার বক্তব্য হচ্ছে শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী যদি এই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিশ্বাসী হয়ে তা পরিবেশন করতে পারেন তাহলে এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি এই গ্রন্থ সম্পর্কে ভুমিকাতে যে-সব স্তুতি বাক্য লিখছেন তাও কিছু পূর্ব ধারণার ফসল। (Gopal Bhar)
নগেন্দ্রনাথ দাস “নবদ্বীপ কাহিনী”-তে গোপালের গুণ সম্পর্কে যে-সব কথা বলেছেন তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি—
‘নদীয়াধিপতি মাহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ও ভান্ডারী গোপালচন্দ্র প্রমূখ পাঁচটি দুর্লভ রত্নসদৃশ ব্যক্তি তাঁহার ‘পঞ্চরত্ন’ সভা সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন।’—তিনি রাজার প্রধান সভাসদদের কথা উল্লেখ করলেও কোথাও বাকি তিন ‘রত্নসদৃশ ব্যক্তি’-র কথা উল্লেখ করলেন না(?) (Gopal Bhar)
আরও পড়ুন: ‘সর্বনাম’ পত্রিকা, অষ্টম সংখ্যা: আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ- মণিশংকর বিশ্বাস
‘তিনি যেমন সচ্চরিত্র ছিলেন তেমনি রাজভক্ত, বিখ্যাত সুপুরুষ, স্ত্রী পুত্রাদিতে অনুরক্ত, সত্যবাদী, সরল, সুচতুর, স্বভাবতঃ সুরসিক, কৌতুকী, কর্মবীর, ও অসাধারণ বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন কম্মঠ ছিলেন।’—পড়লে মনে হয় যে, লেখক যদি মনুষ্য চরিত্রের আরো কিছু গুণ সম্পর্কে অবহিত হতেন, তাহলে সেগুলিও গোপালের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে দিতেন! (Gopal Bhar)
লেখক জানাচ্ছেন যে, রাজা গোপালকে ‘হাস্যার্ণব’ উপাধি প্রদান করেছিলেন। অথচ “নবদ্বীপ কাহিনী”-র প্রায় একান্ন বছর আগে রচিত রাজপরিবারের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্রবাবুর “ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিত” থেকে আমরা জানতে পারছি যে, ‘হাস্যার্ণব’ নামে এক আলাদা রসিক ও পরিহাসক সেসময় ছিল। এবং তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বিবরণীও দিয়েছেন, ‘হাস্যার্ণব বিল্বপুষ্করিণী নিবাসী ও বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ। তাঁহার অসাধারণ রহস্যকারিতা শক্তি প্রযুক্ত রাজা তাঁকে এই নামে বিখ্যাত করেন। তাঁহার নকল করিবার অদ্ভূত ক্ষমতা ছিল । তিনি যে ভাষা কিছুমাত্র জানিতেন না, সে ভাষায় এমন চমৎকার অনুরূপ করিয়া কবিতা আউড়াইতেন বা উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেন যে, অপরিচিত ব্যক্তির যদিও তাহার অর্থগ্রহ হইত না তথাপি তিনি যে নকল করিতেছেন সহসা ইহা কোন প্রকারেই তাঁহার বোধগম্য হইত না। তিনি এরূপ আশ্চর্য কৃত্রিম সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষায় অপরিচিত পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতেন যে, তৎশ্রবণে শ্রোতাদিগের আমোদের অবধি থাকিত না।’ —তাহলে কাকে আমরা সঠিক বলে ধরে নেব? ‘হাস্যার্ণব’ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া দেওয়ানবাবুকে নাকি গোপাল ভাঁড়কেই রাজা ‘হাস্যার্ণব’ উপাধি দিয়েছিলেন শুধু এইটুকু তথ্য পরিবেশন করা “নবদ্বীপ কাহিনী”-কে? পাঠকই বিচার করুন। (Gopal Bhar)
“রাজা মারা যাওয়ার পর হটাৎ তাঁর আর কোথাও কোনো উল্লেখ কেন থাকল না? তাহলে কি গোপাল শুধুই এক মিথ(?)”
‘যে দিন কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনরূপ সোনার জাহাজ ডুবিল সেই দিন হইতেই গোপালচন্দ্রের রসিকতার যবনিকা পতন হইল।’—লেখক গোপালের মৃত্যু নিয়ে কিছুই বলেননি। ফলে আমরা এই বাক্য থেকে ধরেই নেব যে, কৃষ্ণচন্দ্র মারা যাবার পরেও গোপাল বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তাঁর ‘রসিকতার যবনিকা পতন’ হওয়ার কোনো কারণ বোঝা যায় না। যদি তিনি সত্যিই ‘রাজভক্ত’ হয়ে থাকেন তবে তাঁর কাজ পরবর্তী রাজাকেও সমানভাবে সাহচর্য দেওয়া। যেখানে লেখক নিজেই বলছেন, ‘মহারাজ তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে ও রাণী ও রাজকন্যাদিগের সহিত এত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে দিতেন’, আবার বলছেন যে, রাজা এবং রানি উভয়েই তাঁকে পুত্রের মতো স্নেহ করতেন, তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে যে, সভাসদ পদ ছাড়াও রাজপরিবারের সাথে তাঁর একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। তাহলে রাজা মারা যাওয়ার পর হটাৎ তাঁর আর কোথাও কোনো উল্লেখ কেন থাকল না? তাহলে কি গোপাল শুধুই এক মিথ(?), কৃষ্ণচন্দ্রের চলে যাওয়ার সাথে সাথে যে ব্যক্তিরও কল্পিত রক্তমাংসের চরিত্রের মৃত্যু ঘটল, শুধু রয়ে গেল তাঁর নামে প্রচারিত গল্পগুলো? (Gopal Bhar)
নগেন্দ্রনাথ দাস বলছেন রাজা গোপাল ভাঁড়কে ভাণ্ডারের দায়িত্ব দিয়ে ভাণ্ডারী করেছিলেন। এটি একটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ পদ। যদি ধরেই নিই যে এটা সত্যি, তাহলে এই বিষয়ে অন্তত কোনো তথ্য রাজপরিবারে থাকা উচিত, কিন্তু কিছুই নেই। লেখক গোপালকে ‘গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি’ বলে উল্লেখ করেছেন। এবং লেখকের কথা অনুসারে যদি রাজা এবং রানি উভয়েই তাঁকে পুত্রের মতো স্নেহ করে থাকেন তাহলে স্বাভাবিক যে, রাজপরিবার থেকে গোপাল নানান দান পেয়েছে। তাছাড়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সভাসদদের জমি দান করেছিলেন তাঁর প্রমান রয়েছে (ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সকলেই জমি পেয়েছেন সেসব প্রমাণিত), কিন্তু গোপালের ক্ষেত্রে এরকম প্রমাণ কিছুই পাওয়া যায় না। এর বিরুদ্ধ যুক্তিতে বলাই যায় যে, যেহেতু রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বর্গী আক্রমণ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রায় লেগেই ছিল, এবং নবারের রোষানলেও তিনি প্রায়শই পড়ার কারণে কৃষ্ণচন্দ্র কখনই স্থায়ীভাবে এক জায়গায় বসবাস করেননি। কৃষ্ণনগর, শিবনিবাস সহ অনেক জায়গাতেই তিনি মাঝেমধ্যেই চেঞ্জ করে করে থাকতেন। এবং হতে পারে এসব কারণে নানান সরকারী কাগজপত্র বা গোপাল সম্পর্কিত নথিপত্র (যদি থেকে থাকে) নষ্ট হয়েছে বা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এটাও একটু অবিশ্বাসযোগ্য যে অনান্য সভাসদদের নথিপত্র থাকলেও শুধু গোপালেরগুলোই নষ্ট হয়ে গেল! (Gopal Bhar)
“গোপালকে লেখক এই বইয়ে একজন তন্ত্র সাধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা অন্য কোনো গবেষক বা লেখক কোথাও কোনোদিন উল্লেখ করেননি।”
লেখক ‘মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভান্ডারী’ অংশের শুরুতে একটি কবিতা দিয়েছেন—
“…………………………………
সদা পুণ্যব্রতে রত পূত কলেবর।
নদীয়ার অধিপতি গুনের আকর।।
বঙ্গের গৌরব রাজা, অক্ষয় অমর।
গোপাল ভান্ডারী যার রসের সাগর।।”
এই কবিতা তিনি কোথা থেকে পেলেন সে বিষয়েই কিছুই বলেননি, তাই ধরে নিই এটি তারই লেখা। সত্যি বলতে কি এই বইটিতে কোথাও কোনো তথ্যসূত্র নেই। এমনকী খুব বেশি সালতারিখও লেখক দেননি। (Gopal Bhar)
গোপালকে লেখক এই বইয়ে একজন তন্ত্র সাধক হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা অন্য কোনো গবেষক বা লেখক কোথাও কোনোদিন উল্লেখ করেননি। এর সপক্ষে তিনি দুখানি গল্প বলেছেন, সেসব পড়লে মনে হবে যে, গোপাল বুঝি তখনকার দিনের এক সিদ্ধ তান্ত্রিক, যার নানান অলৌকিক গুণাবলি রয়েছে। এবং বইটির মূল বক্তব্য যেন তৎকালীন কৃষ্ণনগরে মাত্র দুটিই ব্যক্তি ছিলেন এক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যিনি রাজকার্য চালিয়েছেন এবং দ্বিতীয় গোপালচন্দ্র যিনি রাজাকে সমস্ত বিপদ থেকে একাই পরামর্শ দিয়ে এবং অনান্য উপায়ে রক্ষা করে গেছেন। গোপাল ছাড়া রাজা যেন অন্ধ, অসহায়! (Gopal Bhar)
“রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাবের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন।”
এই বইয়ের সবথেকে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ‘গোপাল ভান্ডারীর বংশ ইতিহাস’ অধ্যায়টি। অন্যান্য সকলের থেকে তিনি এখানে নতুন তথ্য দিয়েছেন গোপাল সম্পর্কে। যদি তর্ক-বিতর্ক তুলে রেখে সেসব মেনে নিই, তাহলে কোনো অসুবিধে নেই। বরং চলুন আমরা সেইসকল তথ্য একটু যুক্তি দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখি, কারন প্রমাণ কিছুই নেই যা নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারব। (Gopal Bhar)
লেখক বলছেন, অনেক আগে মুর্শিদাবাদে আনন্দরাম নাই নামে একজন নাপিত জাতির পরমতান্ত্রিক বাস করতেন। তিনি আলীবর্দি খাঁ-কে ঘোর অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখিয়ে জায়গিরদার হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র দুলালচাঁদ নবাবের বৈদ্য ও শল্যচিকিৎসক ছিলেন এবং সিরাজকে খুব ছোটো বয়সে তান্ত্রিকমতে চিকিৎসা করে তাঁকে রোগের মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচিয়েছিলেন। নবাব তাঁকে নিজের ছেলের মতো ভালোবাসতেন এবং দুলালচাঁদের দুই পুত্র কল্যাণ ও গোপালকে নিজের ‘পৌত্রের ন্যায় দেখিতেন’। রাজা রামমোহন রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাবের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি কল্যাণকে খুব ভালোবাসতেন এবং তিনিই তাঁকে হুগলীর তহশিলদার পদে নিযুক্ত করেন। এরপর কৃষ্ণচন্দ্র রায় আবার কল্যাণকে নিয়ে চলে আসেন কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদিবাড়ি খানাকুলে এবং তাকে রাধানগরে জমি দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করান। (Gopal Bhar)
“এদিকে অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী বাহাদুর রাজ রাজ্যেশ্বর নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় গোপালের গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে লইয়া যান”।
“নগেন্দ্রনাথ দাসের দাবি অনুযায়ী তিনি নিজে গোপালের দাদার পরবর্তী বংশধর।”
এই ঘটনা থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি হয়। প্রথমত যদি আমরা ধরেই নিই যে, কল্যাণকে নবাবের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী কৃষ্ণচন্দ্র রায় হুগলীর তহশিলদার পদে নিযুক্ত করেন তাহলে তাকে আবার পরে রাধানগরে নিয়ে এসে জমি দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করানোর কারণ কী? এই সময়গুলোতে গোপাল কোথায় ছিল? মুর্শিদাবাদে তাঁর বাবার কাছে নাকি তাঁর দাদা কল্যাণের কাছে? মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় গোপালকে কোথা থেকে এনেছিলেন? এসব তথ্য কিছুই নাই। যদি গোপালকে আলীবর্দি খাঁ নিজের ‘পৌত্রের ন্যায় দেখিতেন’ এবং গোপালের গুণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তাহলে তো এটাই স্বাভাবিক যে, এরকম একজন বিদূষককে নবাব নিজেই তার কাছে রেখে দিতেন। আবার যখন লেখক নিজেই বলছেন যে, গোপাল নিজেও সাধক ছিলেন, মানে এটাই স্বাভাবিক যে, তিনি এই সাধনা তাঁর বাবা বা দাদুর কাছ থেকেই শিখেছেন, তার মানে তিনি মুর্শিদাবাদেই বেশিদিন কাটিয়েছেন এবং নিশ্চই তাঁর বাবার কাছ থেকে চিকিৎসা বিষয়েও জ্ঞান লাভ করেছিলেন। আর সেটা যদি হয়, তাহলে নিশ্চই নবাব তাকে মুর্শিদাবাদেই রেখে দিত। (Gopal Bhar)
কিন্তু লেখক বলছেন যে, তাঁকে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় নিয়ে আসেন। আচ্ছা, ধরে নিই যে, তাঁকে রাজামশাই কল্যাণের বাড়ি রাধানগর থেকে এনেছিলেন। তার মানে দাদার সাথে গোপালের পরবর্তীতেও নিত্য যোগাযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক। এবং যখন রাজসভায় গোপালের এতটাই প্রতিপত্তি ছিল, তাহলে তাঁর দাদার বংশের কাউকে তিনি অনায়াসেই এবং স্বাভাবিকভাবেই রাজবাড়ির কোনো কাজে নিযুক্ত করতেন, যেহেতু গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর আর রাধানগর এমন কিছু দূরত্বে ছিল না। কিন্তু এসব বিষয়েও কিছুই তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। গোপালের নিজস্ব বংশ লোপ পেয়েছিল এ মতামত যেমন নগেন্দ্রনাথ দাসের তেমনি কার্তিকেয়চন্দ্র রায়েরও। নগেন্দ্রনাথ দাসের দাবি অনুযায়ী তিনি নিজে গোপালের দাদার পরবর্তী বংশধর। (Gopal Bhar)
“মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন কৌতুকপ্রিয় মানুষ। আমুদে লোক ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে ঘোষণা দিতেন যে, রাজসভায় ভাঁড়ের প্রয়োজন। তখন নানান জায়গা থেকে ভাঁড় আসত।”
এখানে তৎকালীন নদিয়া রাজপরিবারের স্ববিরোধী কিছু তথ্য দেওয়ার প্রয়োজন। মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের সময়ে প্রকাশিত শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত মূলত গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সংকলন “গোপাল ভাঁড়” বইটির শুরতেই ‘গুণের আদর’ অংশে লেখা আছে, ‘…আমাদের প্রার্থনামতে কৃষ্ণনগরের মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের প্রাইভেট সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচাজ্য মহাশয় যে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন তদনুসারে অনেক বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হওয়ায় ইহা সাহিত্যজগতের একমাত্র হাস্যরসের অক্ষয়ভাণ্ড হইয়াছে…’।—এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, বইটি রাজপরিবারের অনুমতি ও অনুগ্রহ ছাড়া প্রকাশিত হয়নি, কারণ সেখানে তৎকালীন রাজদরবার থেকে কিছুটা পাণ্ডুলিপি বা কারেকশন নোট যাচ্ছে। মানে এই বইটিতে পরিবেশিত গোপাল সম্পর্কিত তথ্যের উপর তাদের প্রকট বা প্রছন্ন সায় আছে, যেভাবে মহারাজ শ্রীক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সায় ছিল “নবদ্বীপ কাহিনী”-র উপর। এবার আসুন দেখা যাক এই “গোপাল ভাঁড়” নামক সংকলনে সংকলক তাঁকে নিয়ে কী তথ্য দিচ্ছেন। এখানে গোপালকে জাতিতে নাপিত, শান্তিপুর নিবাসী বলে জানানো হয়েছে, যাঁর বংশ লোপ পেয়েছে, এবং তাঁর বর্তমান ভিটেয় ক্ষুরি জাতীয় এক পরিবারের বসবাস। এবং কীভাবে গোপাল রাজসভায় আসেন সে নিয়ে একেবারে ভিন্ন এক তথ্য রয়েছে। সংকলক ‘গোপাল ভাঁড়ের কিঞ্চিৎ পরিচয়’ অংশে জানাচ্ছেন যে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন কৌতুকপ্রিয় মানুষ। আমুদে লোক ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে ঘোষণা দিতেন যে, রাজসভায় ভাঁড়ের প্রয়োজন। তখন নানান জায়গা থেকে ভাঁড় আসত। আবার কিছুদিন পর নতুন কৌতুকের জন্য ঘোষণা হতো। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে রয়ে যেত। এভাবেই একবারের ঘোষণা শুনে গোপাল ভাঁড়ও সভায় আসেন, এবং তাঁর কথায় রাজাকে মশগুল করে ফেলেন। সেই থেকে তিনি ধীরে ধীরে রাজার প্রিয় হয়ে ওঠেন। (Gopal Bhar)
“হারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের সময়ে শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত মূলত গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সংকলন “গোপাল ভাঁড়”, যেখানে গোপালের সংক্ষিপ্ত জীবনীও রয়েছে।”
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাজপরিবারের সাথে উপরে উল্লেখিত অনেক বইয়ের মধ্যে (গোপাল ভাঁড় সম্পর্কিত) তিনটি বইয়ের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে (যদিও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় মানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে লিখিত “অন্নদামঙ্গল”-ই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দলিল, এবং তাতে গোপালের উল্লেখ নাই!):
প্রথমত, দেওয়ার কার্তিকেয়চন্দ্রবাবুর লেখা “ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত”। (দেওয়ার কার্তিকেয়চন্দ্র অবসর নেন রাজা ক্ষিতীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের সময়ে)।
দ্বিতীয়ত, মহারাজ শ্রীক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের সময়ে (এবং হয়তো তাঁর অনুমতিতেই) গোপালের বংশধর বলে দাবি করা নগেন্দ্রনাথ দাসের “নবদ্বীপ কাহিনী”।
তৃতীয়ত, মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র রায়বাহাদুরের সময়ে শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত মূলত গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সংকলন “গোপাল ভাঁড়”, যেখানে গোপালের সংক্ষিপ্ত জীবনীও রয়েছে। (Gopal Bhar)
“তিনি কথাপ্রসঙ্গে আরো লিখেছেন যে, ‘…কাল্পনিক গোপাল ভাঁড় যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, তার চেয়েও বেশি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন যারা গোপালের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।’”
এই তিনটি বইয়ের গোপাল সম্পর্কিত তথ্য একে-অপরের সঙ্গে আলাদা। তার মানে এটাই দাঁড়ায় যে, রাজপরিবারের কেউই গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছুই জানতেন না (বাস্তব অস্তিত্ব ছিল না বলেই কি কেউ সঠিক কোনো কিছু জানতেন না?)। কিন্তু এক রাজ-ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে গোপালকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সকলেই নিজের মতো করে এবং নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী চালিয়ে গেছেন। কারণ, এটা অস্বীকার করা যায় না যে ‘মিথিক কিং’ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র-নিজ গুণে বিখ্যাত হলেও, তাঁর নামের প্রচার ত্বরান্বিত করেছে গোপাল ভাঁড়ের গল্প বা এই রহস্য চরিত্র। কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়-এই দুটি নামের একে-অপরকে বাদ দিয়ে চিন্তা করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। (Gopal Bhar)
“নবদ্বীপ কাহিনী”-তে গোপালের জন্ম, মৃত্যু, কবে কোথা থেকে তাঁকে রাজা নিয়ে আসেন, গোপালের বাবার কবে মারা যান বা গোপালের ছেলে, মেয়ে বা নাতিরা কবে মারা যায় (এই বইতে গোপালের মেয়ের নাম রাধারানি এবং মেয়ের দুই পুত্রের নাম রমেশ ও উমেশ বলে উল্লেখ থাকলেও ছেলের নাম লেখক জানাতে পারেননি। বরং তিনি জানাচ্ছেন যে, পুত্রের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। এখন আমরা যদি গোপাল ও তাঁর গল্পগুলিকে সত্যি বলে ধরে নিই, তবে দেখব যে, অনেক গল্পেই গোপালের পুত্রবধূর উল্লেখ আছে। গোপালের ছেলের কি বিয়ে হয়েছিল? তার কি কোনো সন্তান ছিল? নাকি গোপালের ছেলে মারা যাওয়ার সাথে সাথে তার স্ত্রী’ও গত হলেন?—এসব কিছুই জানা যাচ্ছে না। লেখক শুধু একটু জানিয়েই হাত ঝেড়ে ফেলছেন যে, তাঁর বংশ বিলুপ্ত হয়েছে!), গোপাল পরবর্তীতে কোথায় থাকতেন, গোপালের নামে কোনো সরকারি নথি আছে কিনা, এই বইতে উল্লেখিত গোপাল সম্পর্কে নানান ঘটনা বা গল্পগুলো তিনি কোথা থেকে জানলেন, বা এই ধরনের প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য পাওয়া যায় না, যেগুলোকে ইতিহাসের নূন্যতম উপাদান হিসেবে ধরা যাবে। বরং গোটা বইয়ের অনেকখানি জুড়েই কেন রাজারা বিদূষক রাখতেন, তাদের কার্যকলাপ, সাহিত্যে তাদের স্থান এই সব নিয়ে আলোচনা রয়েছে (যদি তিনি সত্যিই গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে জানতেন তাহলে এইসব বিষয় দিয়ে পাতা না ভরিয়ে অবশ্যই আরো বেশি করে গোপাল সম্পর্কে লিখতেন?)। যেগুলো খেয়াল করে হয়তো অলোককুমার চক্রবর্তী তাঁর “প্রসঙ্গ: কৃষ্ণচন্দ্র”-এ বলেছিলেন যে, ‘কাল্পনিক গোপাল ভাঁড়ের সাথে তিনি (নগেন্দ্রনাথ দাস) তার পূর্বপুরুষের নামের মিল খুঁজে পেয়েছেন বলেই কি তিনি নিজেকে গোপালের বংশধর বলে পরিচয় দিতে চান?’ এবং তিনি কথাপ্রসঙ্গে আরো লিখেছেন যে, ‘…কাল্পনিক গোপাল ভাঁড় যে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন, তার চেয়েও বেশি হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন যারা গোপালের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।’ (Gopal Bhar)
“আমার নিজস্বমত হল, পাঠক একবার কষ্ট করে হলেও খুঁজে নিয়ে এই বইটা পড়ুন, তাহলেই ঠিক বুঝতে পারবেন যে এটি গোপালের ইতিহাস নাকি স্রেফ গোপাল ভজনা”
আমার নিজস্বমত হল, পাঠক একবার কষ্ট করে হলেও খুঁজে নিয়ে এই বইটা পড়ুন, তাহলেই ঠিক বুঝতে পারবেন যে এটি গোপালের ইতিহাস নাকি স্রেফ গোপাল ভজনা (এবং যা করতে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে লেখক গল্পের গরু গাছে তুলে দিয়েছেন!)?
এবার আসি ছবি বিতর্কে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কোনো প্রামাণ্য ছবি কোথাও সেরকম পাওয়া যায় না। কিন্তু কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে একটি মোঘল ঘরানায় আঁকা ছবি পাওয়া যায় যেখানে রাজাকে ঘিরে চারজন ব্যক্তি উপস্থিত। সেখানেই একটু স্থূল চেহারার এক ব্যক্তিকে গোপাল বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা হয়। অনেকেই ঐ ব্যক্তিকে মুক্তিরাম মুখোপাধ্যায় বলেও দাবি করেন কোনো প্রমাণ ছাড়া। লেখক সুজিত রায়সহ সকলেই প্রায় মেনে নিয়েছেন যে, ছবিটি পুরোটাই কাল্পনিক যদিও ঐ ছবিটিই নগেন্দ্রনাথ দাসবাবু তাঁর “নবদ্বীপ কাহিনী”-তে ছেপে দিয়েছিলেন। আবার কীরকম বৈপরীত্য দেখুন, নগেন্দ্রনাথ দাসবাবু নিজে তাঁর বইতে কোথাও জানাননি যে, গোপালের চেহাড়া স্ফীত বা বর্তমানে আমরা কার্টুনে যেরকম দেখি সেরকম ছিল, বরং তিনি উলটো কথাই বলেছেন যে, তিনি সুপুরুষ ছিলেন, অথচ ঐ ছবিটির মোটা চেহাড়ার লোকটিকেই গোপাল বলে দেগে দিতেও ছাড়ছেন না। আবার আর একটি বিষয়, বর্তমান গোপালের বংশধর বলে দাবি করা পরিবারের দাবি অনুয়ায়ী এখনও টিকে থাকা গোপাল ও ক্লাইভের করমর্দনের ছবিটি বা রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে অধুনা নষ্ট হয়ে যাওয়া তাদের দেখা গোপালের আরও কিছু তৈলচিত্রের কথা কিন্তু নগেন্দ্রনাথ দাস কিছুই জানাননি বা বইতেও দেননি। অথচ সেইসব ছবি থেকে থাকলে তিনি জানতেন না, এটা ভাবা যায় না! (বরং গোপাল ও ক্লাইভের করমর্দনের ছবি বা এই ধরনের ছবিগুলো যদি সত্যি হতো তাহলে তিনি নিশ্চই সেগুলোই বইতে আগে ছাপতেন)। তার মানে গোপালের ছবি সংক্রান্ত বিষয়ে যা কিছু দাবি তার কোনোটাকেই ঐতিহাসিক প্রমাণ বলে মেনে নেওয়া যায় না। (Gopal Bhar)
“বটতলা থেকেই প্রথম গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলির সমগ্র প্রকাশিত হয়। গ্রন্থিত গল্পগুলি সবই লোকমুখে প্রচারিত গল্প থেকে সংগৃহীত।”
আর একটি বিতর্কও বেশ জটিল। গোপালের অস্তিত্বে অবিশ্বাসীরা বলে থাকেন যে, গোপাল জাতে ছিল নাপিত, এবং তৎকালীন এই নীচু জাতের একটি মানুষকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এতটা কাছে হয়তো ঘেষতে দিতেন না, যেভাবে আমরা তাঁর সাথে রাজার হৃদ্যতার কথা শুনি। এটা ঠিক যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় এরকম কথা প্রচলিত ছিল যে, যে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুদান পায়নি সে ব্রাহ্মণই নয়। এবং তিনি ছিলেন কথিত চৈতন্য বিরোধী (একমাত্র অগ্রদ্বীপ ছাড়া তিনি সেভাবে চৈতন্য স্মৃতিবিজড়িত কোনো কিছুর আলাদা গুরুত্ব দেননি, এবং তিনি চৈতন্যকে অবতার হিসেবেও স্বীকার করতেন না।) তাঁর ঈশ্বরভক্তিও ছিল প্রবল, কারণ তিনি প্রায়শই কালীঘাট যেতেন পুজো দিতে, এবং জাতপাতের বিভাজন তো ছিলই সে যুগে। ফলে নাপিত জাতির এক ব্যক্তিকে তিনি এতটা প্রশ্রয় দিতেন কিনা সেটা একটা প্রশ্ন, যদি গোপালের অস্তিত্ব থেকে থাকে। “নবদ্বীপ কাহিনী” অনুয়ায়ী তো গোপালের চলাচল রানিমহল পর্যন্ত ছড়ানো। কিন্তু এই বিষয়টি গোপালের অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয় না। কারণ সমস্ত সফল রাজা-বাদশাই গুণ ও গুণীর কদর করতেন। আর রাজসভার ‘পঞ্চরত্ন’-এর মধ্যে যাকে অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করা হয়, সেই রামপ্রসাদও ছিলেন জাতিতে বৈদ্য (যদিও তিনি কখনও রাজসভায় স্থায়ীভাবে অবস্থান করেননি)। (Gopal Bhar)
নগেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় লিখেছেন যে, রাজসভায় নানান বিদূষকের আনাগোনা লেগেই থাকত, কিন্তু গোপালের মতো কেউই স্থায়ী হননি। “গোপাল ভাঁড় রহস্য” বই থেকে জানতে পারছি সেসময় রাজসভায় গোপাল ভাঁড় ছাড়াও আজু গোঁসাই, হাস্যরাম, মুক্তিরাম প্রভৃতি সুরসিকদের উপস্থিতি ছিল। আবার কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ও জানাচ্ছেন যে, রাজসভায় মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড়, এবং হাস্যার্ণব নামে তিন ব্যক্তি অসাধারণ রসিক ও পরিহাসক ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রবাবুর তথ্যানুয়ায়ী মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি বীরনগর, এবং ‘কেবল সুরসিক বলিয়া রাজা তাঁহাকে বৈবাহিক সম্বোধন পূর্বক তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেন’। এখান থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে, রাজসভায় একাধিক পরিহাসক ছিলেন, কিন্তু জনপ্রিয়তা পেয়েছে একমাত্র গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলিই। এই গল্পের কোনো লিখিত রূপ ছিল না। বটতলা থেকেই প্রথম গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলির সমগ্র প্রকাশিত হয়। গ্রন্থিত গল্পগুলি সবই লোকমুখে প্রচারিত গল্প থেকে সংগৃহীত। এবং খেয়াল করলে দেখা যাবে বিভিন্ন সময়ে প্রকশিত সংকলনে নতুন নতুন গল্প জুড়ে গেছে। নির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল যে, এগুলির উদ্ভাবক নির্দিষ্ট একজনই কিনা! একটি গল্পের উদাহরণ দিই— (Gopal Bhar)
“নানান সময়ে নানান কৌতুক এসে জুড়ে যাচ্ছে গোপালের নামে। তার মানে এটাই বোঝা যায় যে, গোপালের গল্পগুলি কোনো এক ব্যক্তির প্রচারিত নয়।”
“রাজা, একদিন প্রত্যূষে, তাঁহাকে দেখিয়া কহেন, ‘মুখুজ্যে, গতরাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন তুমি বিষ্ঠার হ্রদে ও আমি পায়েসের হ্রদে পড়িয়াছি।’ তিনি উত্তর করেন, ‘ধর্মাবতার, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। কেবল বিশেষ এই, যেন হ্রদদ্বয় হইতে উত্থান করিয়া, আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি।” (Gopal Bhar)
এই গল্পটি বিভিন্ন আকারে আমরা ছোটো থেকেই গোপাল ভাঁড়ের অন্যতম একটি গল্প নামে জেনে, শুনে ও পড়ে আসছি। কিন্তু কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের “ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত”-এ দেখছি যে, লেখক এই ঘটনার প্রবক্তা হিসেবে মুক্তিরাম মুখপাধ্যায়ায়ের নাম করছেন। এবং সেখানে মুক্তিরাম ও কৃষ্ণচন্দ্র সম্পর্কিত আরো কয়েকটি কৌতুকের উদাহরণ আছে। অথচ পরবর্তীতে এই কৌতুক গোপালের নামে প্রচলিত হয়েছে। শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত সংকলন “গোপাল ভাঁড়” থেকে জানতে পারছি, ‘…গোপাল ভাঁড়ের বিস্তর গল্প এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, তাহা উক্ত ভাঁড়ের গল্প বলিয়াই বোধ হইত না। আবার অনেক নীরস বাজে গল্পকে গোপাল ভাঁড়ের গল্প বলিয়াও লোক জানিত। এইরূপ অনেক গল্প আজু গোঁসাই, হাস্যরাম ভাঁড় প্রভৃতির বলিয়াই এতদিন প্রচলিত ছিল।’—ঠিক এর উলটোটাও সম্ভব, মানে আজু গোঁসাই, হাস্যরাম ভাঁড় প্রমূখের গল্পও গোপাল ভাঁড়ের গল্প হিসেবেও পরিচিত ছিল বা আছে এখনও। এটা অস্বাভাবিক কিছুই নয়, কারণ, যেভাবে গোপালের নামে প্রচারিত গল্প মানুষ গ্রহণ করেছেন সেভাবেই ভুলে গেছেন সেসময়ের অন্যান্য কৌতুককারদের। এবং নানান সময়ে নানান কৌতুক এসে জুড়ে যাচ্ছে গোপালের নামে। তার মানে এটাই বোঝা যায় যে, গোপালের গল্পগুলি কোনো এক ব্যক্তির প্রচারিত নয়। ঠিক একইভাবে মোল্লা নাসিরুদ্দীন বা এই ধরনের বিখ্যাত মিথিক পরিহাসকদের নামে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন গল্প প্রচারিত আছে। তাই সন্দেহ তৈরি হয় গোপালের বাস্তবিক অস্তিত্ব সম্পর্কে। (Gopal Bhar)
গোপাল ভাঁড়ের রক্তমাংসের অস্তিত্ব থেকে থাকুক বা নাই থাকুক তাতে কিন্তু তাঁর গল্পের বা সেই গল্প থেকে পাওয়া মানুষের আরামের কোনো খামতি কোনোদিন হবে না। এরকম কখনই হবে না যে, হটাৎ যদি প্রমাণিত হয় তিনি শুধুমাত্র একটি মিথিক ক্যারেকটার, তাহলে মানুষজন তাঁর গল্প পড়া ছেড়ে দেবে বা তাঁর কার্টুন বন্ধ হয়ে যাবে বা তাঁকে নিয়ে সমস্ত আলোচনা রাতারাতি থেমে যাবে। তাই আমার বক্তব্য পরিষ্কার, গোপাল ভাঁড়ের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে যাঁরা নাড়াঘাঁটা করবেন তাদের হতে হবে সৎ। ইতিহাসের কাছে মিথ্যের কোনো স্থান নেই। যাঁরা এতদূর পড়ে এলেন কষ্ট করে তাঁরা হয়তো খেয়াল করেছেন যে, আমি কোথাও জোর দিয়ে বলিনি যে, তিনি ছিলেন বা ছিলেন না। হ্যাঁ, কোথাও কোথাও অবশ্যই যুক্তি ভারী হয়েছে। কিন্তু যুক্তিই তো ইতিহাসের শেষ কথা নয়। দরকার প্রমাণ। সত্যি বলতে কি গোপাল সম্পর্কে এখনও সেভাবে কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু তার মানে এই নয় কোনো বিশ্বাসযোগ্য তথ্য কোনোদিন হাতে আসবে না! আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সময়ের জন্য, অপেক্ষা করতে হবে অরো গভীর গবেষণার জন্য। (Gopal Bhar)
যে-সব বইয়ের সাহায্য নেওয়া হল:
১) নবদ্বীপ কাহিনী বা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপাল ভাঁড়, শ্রী নগেন্দ্রনাথ দাস
২) গোপাল ভাঁড়ের সন্ধানে, সুজিত রায় ও শুভাশিস চৌধুরী
৩) নদীয়া কাহিনী, কুমুদনাথ মল্লিক (মোহিত রায় সম্পাদিত)
৪) পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, রজতকান্তি রায়
৫) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
৬) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম, কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (মোহিত রায় সম্পাদিত)
৭) রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত, ১৮৫৮ সালে গোপীনাথ চক্রবর্তী এন্ড কোং এর উদ্যোগে প্রকাশিত
৮) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, অলোককুমার চক্রবর্তী
৯) বাংলাপিডিয়া ৩য় খণ্ড, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদনা)
১০) গোপাল ভাঁড়, শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক সংগৃহীত গোপাল ভাঁড়ের গল্প সংকলন
১১) গোপাল ভাঁড় রহস্য (তৃতীয় সংস্করণ), হাস্যরসিক শ্রীশ্যামসুন্দর ধর ও ঔপন্যাসিক শ্রী ক্ষেত্রমোহন ঘোষ প্রণীত গোপাল ভাঁড়ের গল্পের সংকলন
১২) The Mythic King: Raja Krishnacandra and Early Modern Bengal, Joel Bordeaux
১৩) হাস্যকৌতুকে মোল্লা নাসিরুদ্দিন গোপাল ভাঁড় বীরবল, শংকর (সম্পাদনা)
১৪) রসিকরাজ গোপাল ভাঁড়, অর্জুন সাহা (সম্পাদনা)
এছাড়াও বিশেষ কৃতজ্ঞতা:
১) ন্যাশানাল লাইব্রেরি, আলিপুর
২) প্রজ্ঞাতীর্থ লাইব্রেরি, দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির
৩) রামমোহন লাইব্রেরি ও ফ্রি রিডিং রুম
৪) গৌতম চট্টোপাধ্যায়
৫) কৃষ্ণগোপাল রায়
৬) সেলিম মণ্ডল
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।