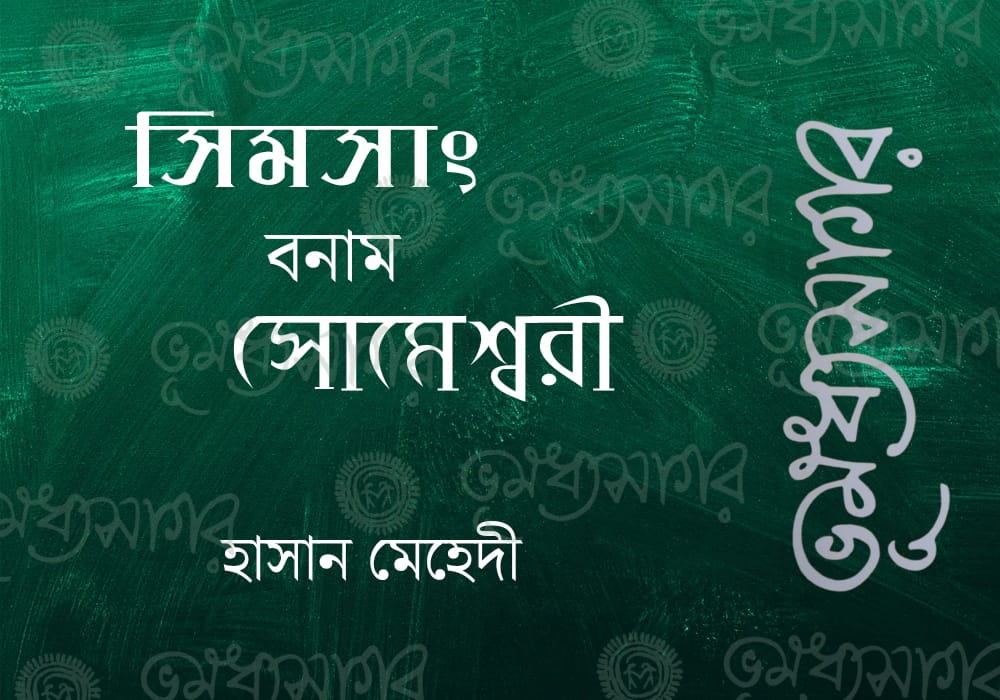হাসান মেহেদী
 সোমেশ্বরী নদী নিয়ে এক ধরনের আবেগ দেখি বাঙালি সংবেদী মানুষের মধ্যে। আমার জীবন শামুকের মতো। চারপাশের খবরে মন থাকে না। বাড়িতে শোনা রবীন্দ্র্রনাথের গান, কতকগুলো বঙ্কিমী উপন্যাসের মতো আঠারো শতকে আটকে থাকা সাহিত্যজ্ঞান নিয়ে বড় হওয়া আমার জানা ছিল না সোমেশ্বরীর খোঁজ। প্রথম যখন সোমেশ্বরীর ধারে দাঁড়িয়ে এর কাকস্বচ্ছ জল দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, তখনই পাড় ভেঙে পড়ে গেলাম নদীতে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাঁড়াতেই আবার গা থেকে ঝুরঝুরে বালিগুলো ঝরে পড়ল, যেন কিছুই লাগেনি গায়ে— একেবারে রাজহংস যথা। নদীর ওপারের মেঘালয় সীমান্ত পর্যন্ত না এগিয়ে অরসিকজনের মতো বিরিশিরি কালচারাল একাডেমিতে এসে বইপত্র খুঁজতে লাগলাম। কালচারাল একাডেমির পত্রিকা ‘জানিরা’র পুরোনো এক সংখ্যায় একটা গল্প পড়তে গিয়ে বোকা বনে গেলাম-‘সিমসাং রাজার রাজ্যহারার বেদনা’। ‘জানিরা’ অর্থ আয়না। সোমেশ্বরী নদীটির বাংলা নাম, এই নদীর আচিক বা মান্দি ভাষার নাম সিমসাং। হাজংরা নদীটিকে ডাকে ধাপাগাঙ্গ, যার বাংলা হয় বড় নদী। এ অঞ্চলে মান্দি, হাজং, কোচ, দালু জাতির বসবাস ছিল। গারো বা মান্দিদের রাজত্ব ছিল এই সুসং দুর্গাপুরে। আমাদের সবার প্রিয় রফিক আজাদ তখন সেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমির পরিচালক ছিলেন। বিরিশিরি, দুর্গাপুর, চুনিয়াকে পরিচয় করাতে তিনিই যথেষ্ট। সিমসাং রাজা কেমন করে রাজ্য হারালেন, সেই কাহিনি বলি বরং— রাজা-রানী সুখে শান্তিতেই বসবাস করেছিলেন। সোমেশ্বর পাঠক নামে এক লোক ভাগ্যান্বেষণে এসে এই রাজ্যে স্থান পায়। সে তন্ত্রমন্ত্র এবং ওষুধ নিয়ে কাজ করত। সোমেশ্বর পাঠক রাজাকে ওষুধের বদলে বিষ প্রয়োগ করে এবং রানীকে দখল করে নেয়। রাজ্য এবং রানী দখল তো হলোই, সেই কূট লোকটি সিমসাং নদীর নামটা বদলে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখল— সোমেশ্বরী। কবিস্বভাব লোকেরা নির্দোষ, তারা এক স্বচ্ছজল নদীর নামে মুগ্ধ হন, কিন্তু আমার মন গুমরে গুমরে বলে, ‘সিমসাং’, ‘সিমসাং’।
সোমেশ্বরী নদী নিয়ে এক ধরনের আবেগ দেখি বাঙালি সংবেদী মানুষের মধ্যে। আমার জীবন শামুকের মতো। চারপাশের খবরে মন থাকে না। বাড়িতে শোনা রবীন্দ্র্রনাথের গান, কতকগুলো বঙ্কিমী উপন্যাসের মতো আঠারো শতকে আটকে থাকা সাহিত্যজ্ঞান নিয়ে বড় হওয়া আমার জানা ছিল না সোমেশ্বরীর খোঁজ। প্রথম যখন সোমেশ্বরীর ধারে দাঁড়িয়ে এর কাকস্বচ্ছ জল দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, তখনই পাড় ভেঙে পড়ে গেলাম নদীতে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাঁড়াতেই আবার গা থেকে ঝুরঝুরে বালিগুলো ঝরে পড়ল, যেন কিছুই লাগেনি গায়ে— একেবারে রাজহংস যথা। নদীর ওপারের মেঘালয় সীমান্ত পর্যন্ত না এগিয়ে অরসিকজনের মতো বিরিশিরি কালচারাল একাডেমিতে এসে বইপত্র খুঁজতে লাগলাম। কালচারাল একাডেমির পত্রিকা ‘জানিরা’র পুরোনো এক সংখ্যায় একটা গল্প পড়তে গিয়ে বোকা বনে গেলাম-‘সিমসাং রাজার রাজ্যহারার বেদনা’। ‘জানিরা’ অর্থ আয়না। সোমেশ্বরী নদীটির বাংলা নাম, এই নদীর আচিক বা মান্দি ভাষার নাম সিমসাং। হাজংরা নদীটিকে ডাকে ধাপাগাঙ্গ, যার বাংলা হয় বড় নদী। এ অঞ্চলে মান্দি, হাজং, কোচ, দালু জাতির বসবাস ছিল। গারো বা মান্দিদের রাজত্ব ছিল এই সুসং দুর্গাপুরে। আমাদের সবার প্রিয় রফিক আজাদ তখন সেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমির পরিচালক ছিলেন। বিরিশিরি, দুর্গাপুর, চুনিয়াকে পরিচয় করাতে তিনিই যথেষ্ট। সিমসাং রাজা কেমন করে রাজ্য হারালেন, সেই কাহিনি বলি বরং— রাজা-রানী সুখে শান্তিতেই বসবাস করেছিলেন। সোমেশ্বর পাঠক নামে এক লোক ভাগ্যান্বেষণে এসে এই রাজ্যে স্থান পায়। সে তন্ত্রমন্ত্র এবং ওষুধ নিয়ে কাজ করত। সোমেশ্বর পাঠক রাজাকে ওষুধের বদলে বিষ প্রয়োগ করে এবং রানীকে দখল করে নেয়। রাজ্য এবং রানী দখল তো হলোই, সেই কূট লোকটি সিমসাং নদীর নামটা বদলে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রাখল— সোমেশ্বরী। কবিস্বভাব লোকেরা নির্দোষ, তারা এক স্বচ্ছজল নদীর নামে মুগ্ধ হন, কিন্তু আমার মন গুমরে গুমরে বলে, ‘সিমসাং’, ‘সিমসাং’।
নদীর ওপারের মেঘালয় সীমান্ত পর্যন্ত না এগিয়ে অরসিকজনের মতো বিরিশিরি কালচারাল একাডেমিতে এসে বইপত্র খুঁজতে লাগলাম। কালচারাল একাডেমির পত্রিকা ‘জানিরা’র পুরোনো এক সংখ্যায় একটা গল্প পড়তে গিয়ে বোকা বনে গেলাম-‘সিমসাং রাজার রাজ্যহারার বেদনা’। ‘জানিরা’ অর্থ আয়না। সোমেশ্বরী নদীটির বাংলা নাম, এই নদীর আচিক বা মান্দি ভাষার নাম সিমসাং। হাজংরা নদীটিকে ডাকে ধাপাগাঙ্গ, যার বাংলা হয় বড় নদী। এ অঞ্চলে মান্দি, হাজং, কোচ, দালু জাতির বসবাস ছিল।
সুন্দরের বিপদ বেশি। প্রকৃতি গোলাপে কাঁটা রেখেছে। কিন্তু আমরা মানুষেরা বন-বনানী, নদী-নালার জন্য নিরাপদবেষ্টনী দেবার ক্ষমতা রাখি না। অসহ্য হলে প্রকৃতি নিজেই ঘূর্ণিঝড়ে আমাদের আধুনিকতার ইমারত ভেঙে দিতে পারে। প্রকৃতি সম্পূর্ণ, সে নিজেই নিজের সেফগার্ড। কিন্তু মানুষের সমাজে কী ঘটে? বিরিশিরির পথে বালির ট্রাক চলে, চীনা মাটির পাহাড়ে, চীনা মাটিতে খাদ হয়। গারো পাহাড়ের ধার ঘেঁষে মান্দিরা যেমন করে টিকে আছে, হাজং, কোচ ও দালুরা তেমন করে টিকে থাকতে পারেনি। স্কুলশিক্ষক পল্টন হাজং বলছিলেন, সোমেশ্বর পাঠকের রাজত্ব ছিল উত্তরে মেঘালয় থেকে দক্ষিণে কংস পর্যন্ত। তবে তিনি নিজে বাস করতেন দুর্গাপুরের এই সমতল অঞ্চলটাতে। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গার পর দেশত্যাগ করা এই মানুষগুলোর সামান্য কিছু আবার ফিরে এসেছিল। মতিলাল হাজং বলছিলেন, আট ভাগের মাত্র এক ভাগ দেশে ফিরেছিল। হাজংরা সম্ভবত ১০০১ সালে এই অঞ্চলে এলো। মনে রাখা ভালো কয়েকশ বছর আগেও বাংলাদেশের অর্ধেক যদি সাগর, বাকি অর্ধেক ছিল পাহাড় বা জঙ্গল। অনেক আগে এই ভূমিতে বেশি মানুষ থাকার পরিস্থিতি ছিল না। সংগ্রাম সবার জীবনেই থাকে, তবে হাজং জাতিকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে রাজনৈতিক সংগ্রামে, বারবার। ব্রিটিশ আমলে সাহসী এবং শক্তিশালী এই জাতির পুরুষদের হাতি ধরার জন্য কাজে লাগানো হতো। হাতিশালে হাতি জমিদার-বাদশাদের শান বৃদ্ধি করলেও তার পেছনে ছিল হাজংদের ত্যাগ। হাতির খেদা বানিয়ে ফাঁদে ফেলে হাতি ধরতে জুড়ি ছিল না তাদের। কিন্তু এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে জীবন বাজি রাখতে হতো। টংক আন্দোলনেও কঠিন পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছিল তাদের। ১৯৩৮ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত এই কৃষক আন্দোলনের কথা সবার জানা। ফসল না হলেও টংক বা খাজনা দিতে হতো নির্দিষ্ট হারে।

টিকে থাকার সংগ্রাম যখন প্রকৃতির রূঢ়তার সঙ্গে, তার এক ধরন। কিন্তু সেই সংগ্রাম যদি হয় রাজনৈতিক ক্ষমতাধরের বিরুদ্ধে বেঁচে থাকার লড়াই, যখন একদিকে থাকে লোভ, অন্যদিকে থাকে জীবন বাঁচানোর অনিবার্যতা— তখন পেছনে ফেরা যায় না। হাজংদের নিকটকালেই এমন সব লড়াই করতে হয়েছে। ১৯৬৪ সালের বাংলাদেশে ৬০ হাজার হাজং জাতির মানুষ এখন ১১ হাজারে পৌঁছেছে। কারও কারও জায়গা হয়েছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে। মান্দিরা যেমন অত্যাচারিত হয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে পালাতো বলে শোনা যায়, হাজংরা তেমনটা করেনি। সোজাসুজি লড়াই করেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আদিবাসী নেভিগেটরের এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত একটি হিসাবে দেখা গেছে, হাজং শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার ৪০ শতাংশ। আমি শেরপুরের ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ীর হাজংদের কাছে গিয়ে বুঝতে পেরেছি, নিজের ভাষাটাই ভুলে গেছে, কথা বলে বাংলায়। নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও সিলেটে অবশ্য হাজংরা নিজেদের ভাষাতেই কথা বলে এখনও। শিক্ষাদীক্ষায় খুব পিছিয়ে তারা। হাজং নেতাদের ধারণা, সাক্ষরতার হার ২৫ শতাংশের মতো। দরিদ্র, সংগ্রামী সংসারের শিশুরা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়বেই। তার ওপরে আছে ভিন্ন ভাষায় পড়তে শেখার কঠিন চাপ। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে হাজং ভাষার কিছু বই স্কুলে পৌঁছেছে, তবে সেগুলো পড়ানোর জন্য শিক্ষক নেই, নেই কোনো নির্দেশনাও। বেসরকারিভাবেই হাজং শিশুদের মায়ের ভাষা শেখানোরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো কাজে লাগলেও ছিল অপ্রতুল। হাজং সংগঠনগুলো এখন কিছুটা তৎপর নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে নিতে। মাতৃভাষা শিক্ষা নিয়ে কেউ কেউ বলতে চায়, বর্ণমালা না থাকলে ভাষাচর্চা হবে কীভাবে। হাজংদের বর্ণমালা নেই, তবে বাংলা বর্ণমালায় আরও কয়েকটি সংকেত যুক্ত করে তারা হাজংভাষার বই তৈরি করেছে। এ ব্যাপারে নৃবিজ্ঞানী প্রশান্ত ত্রিপুরার পরামর্শ হলো, শিশুকালে লেখার ভাষা শিখলেও তো মুখে মুখে মায়ের ভাষায় শেখা যায় পরিবেশ পরিচিতি, গল্প, কবিতা, গান, ইতিহাস ইত্যাদি। তাই অসুবিধা না খুঁজে দরকারি কাজগুলো করার চেষ্টা করলেই ভালো হবে হয়তো। বীর পুরুষদের ঘরণীরা সচরাচর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ কম পায়। হাজং নারীরাও ঘরের কাজের সঙ্গে কৃষিকাজ করে, তবে সিদ্ধান্ত নেবার সুযোগ নেই তাদের। আমার অনুমান মায়েরা সিদ্ধান্ত গ্রহণে এগিয়ে থাকলে, যেমনটা আছে মান্দি সমাজে, সুস্থিত জীবন পেলে শিশুশিক্ষা এগিয়ে যায়। এ বিষয়ে গবেষণা কী বলে, তা অবশ্য জানি না।
মান্দিরা যেমন অত্যাচারিত হয়ে হঠাৎ আক্রমণ করে পালাতো বলে শোনা যায়, হাজংরা তেমনটা করেনি। সোজাসুজি লড়াই করেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আদিবাসী নেভিগেটরের এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত একটি হিসাবে দেখা গেছে, হাজং শিশুদের স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হার ৪০ শতাংশ। আমি শেরপুরের ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ীর হাজংদের কাছে গিয়ে বুঝতে পেরেছি, নিজের ভাষাটাই ভুলে গেছে, কথা বলে বাংলায়। নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও সিলেটে অবশ্য হাজংরা নিজেদের ভাষাতেই কথা বলে এখনও। শিক্ষাদীক্ষায় খুব পিছিয়ে তারা।
তবে হাজং নারীদের সম্ভ্রমবোধ আর লড়াইয়ের গল্প বলি একটা। কৃষক বিদ্রোহের সময় লড়াকুদের খুঁজে না পেয়ে নববধূ কুমুদিনী হাজংকে তুলে নিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ বাহিনী। সেই খবর জানতে পেরে রাশিমণি হাজং অপর নারীর সম্মান বাঁচাতে পুলিশ বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কুমুদিনীকে উদ্ধার করতে পারলেও রাশিমণি সেদিন নিহত হন। পরে রাশিমণিকে হাজংরা সম্মানিত করেছে হাজং মাতা অভিহিত করে।

আজও থেমে নেই সংগ্রাম। চীনা মাটির পাত্রে খাবার পরিবেশন না করলে ভদ্রলোকের মান থাকে না। কিন্তু হাজংপাড়ায় চীনা মাটি তুলে নিতে নিতে পাহাড়কে খাদ বানিয়েছে লোভীরা। শুনলাম সেই খাদে ডুবে মরে গিয়েছিল এক শিশু। দুর্ভাগ্যের ফাঁদে দুরূহ জীবন-যাপন করছে এই জাতির মানুষ। দুর্গাপুরের পথ সবসময় ভাঙা থাকে। কারণ, সিমসাংয়ের বালি ছাড়া নাগরিক ইমারত গড়া অসম্ভব। ‘সোনার রাজার মতোই, সব ধরনের প্রকরণ তাই কুৎসিত’। জীবনানন্দ দাশের কাছে মোটরকারকে তাই ‘খটকার মতো’ মনে হয়।
*বানান অপরিবর্তিত
*ছবি সৌজন্য- Flickr
*বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভূমধ্যসাগর পত্রিকা
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।