“শতরঞ্জ কে খিলাড়ি” ছবিতে মুনশি নন্দলালকে মনে পড়ে? জাইগিরদার মির্জা সাজ্জাদ আলি আর মির রওশন আলি বসেছেন দাবার ছক সাজিয়ে। বাজি শুরু হওয়ার মুহূর্তে মুনশিজির আবির্ভাব। দাবার ছক দেখে তাঁর সহাস্য উক্তি “বাদশাও কা খেল, খেলো কা বাদশা”! শতরঞ্জের উদ্ভাবন হিন্দুস্থানে এবং সেখান থেকেই সে পাড়ি দিয়েছে ইরান হয়ে বিলেতের পথে – তাঁর মুখ থেকে এ কথা জেনে দিবানিশি দাবার নেশায় মজে থাকা দুটি মানুষের বিস্ময়, বাগ মানে না !
আসলে উনিশ শতকের মধ্যভাগে মুনশি নন্দলাল শুনিয়েছিলেন যে ফলক ক্রীড়ার (Board games) কথা, তার যাত্রাপথের শুরু, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, ক্রমশ যা জনপ্রিয়তা লাভ করে গুপ্ত এবং হর্ষ বংশের শাসনকালে। মোটামুটি ভাবে খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ইতিহাস বলে সিন্ধু সভ্যতার কাল থেকেই ফলক ক্রীড়ার চল ছিল। খননের ফলে যে ছোট ছোট মাটির পুতুল বা পাথরের ঘুঁটি পাওয়া গেছে, তা আসলে মাটিতে বা পাথরের সমতলের ওপরে কোনও বোর্ড গেমে ব্যবহৃত হত। মিশরের “সেনেত” খেলার সঙ্গে এর ছক খানিক মিলে যায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে আর্যদের হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে এ দেশে আগমণ। এবার বোর্ড গেমে যুক্ত হয়– ছক্কা বা অক্ষ বা dice| যে খেলাগুলো বোর্ড নির্ভর, সেখানে দেখা যাচ্ছে বোর্ডের ওপরে ঘুঁটির গতিমুখ এবং অবস্থান পরিবর্তন নির্ধারিত হচ্ছে (race game) অক্ষপাতনের (throwing of dice) মাধ্যমে, এক বা একাধিক ছক্কায় প্রদর্শিত সংখ্যা বা সংখ্যার যোগফলের উপরে। সাধারণত ৮ x ৮ অথবা ১০ x ১০ ছকের বোর্ড ব্যবহারের চল ছিল – পতঞ্জলির “মহাভাষ্য”-এ এদের বর্ণনা করা হয়েছে যথাক্রমে “অষ্টপদ” ও “দশপদ” হিসেবে। মহাভারতের সভা পর্বের অন্তর্গত দ্যূত অধ্যায় মনে করায় “পাশা“ বা “পছিশি” যেখানে দুর্যোধনের প্রতিভূরূপে মাতুল শকুনি কপটতার আশ্রয় নিয়ে পরাজিত করছেন যুধিষ্ঠিরকে। পাশা খেলার আরেক অধ্যায়– নল–দময়ন্তীর উপকাহিনি। সেখানে ছলনার খলনায়ক কলি আর দ্বাপর। ভাই পুষ্করের হাতে পাশা খেলায় নলের বারংবার পরাজয় হয়।

১০ x ১০ দশপদ বোর্ডের খেলা “মোক্ষ পাতম”। যার পদে পদে ছিল মানব জীবনের পাপ ও পুণ্যের সোপান। পুণ্যের ঘরে মই বেয়ে উত্তরণ, পাপের ঘরে সর্প দংশনে অবতরণ। শততম ঘরে পৌঁছে মোক্ষ লাভ। কে পৌঁছবে সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে, তারই প্রতিযোগিতা। ছক্কার সংখ্যা মেনে পেরোতে হত ছক । ব্রিটিশ মোড়কে “মোক্ষ পাতম” উনিশ শতকে হয়ে গেছে “snakes & ladders”! অষ্টপদ ছকে দক্ষিণ ভারতের গ্রামে গ্রামে বহুযুগ ধরে চলে আসছে “থাইয়্যাম” খেলা। ক্ষেতের ধারে, আলের পাশে কাঠি দিয়ে আঁক কেটে তৈরি হয় থাইয়্যামের ছক। কখনও কড়ি, কখনও বা তেঁতুলের কালচে বাদামি বীজ দিয়ে বানানো ছক্কায় খেলা হয়।
থাইয়্যামের বোর্ডের সঙ্গে দাবার আদি রূপ “চতুরঙ্গ”-এর মিল স্পষ্ট আর এর উদ্ভাবনের পিছনে ছিল সে সময়ের ক্ষত্রিয় শ্রেণীর সামাজিক রীতি যার মূলে রাজ্য জয় এবং শাসন। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং সমারঙ্গনের কৌশলে পারদর্শী একজন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দ্যূতক্রীড়ার আমন্ত্রণে “না” বলা এবং যুদ্ধের আহ্বান অগ্রাহ্য করা দুইই অধর্ম! সুতরাং এই দুই রীতির সম্মীলন তৈরি করে দেয় চতুরঙ্গের ভিত্তি। সেকালে সম্মুখ সমরে ব্যবহৃত হত চতুরঙ্গ সেনা অর্থাৎ, পদাতিক, অশ্বারোহী, গজানীক এবং রথারোহী। তারাই ক্ষুদ্রকায় হয়ে উঠে আসে চতুরঙ্গের চৌষট্টি চৌখুপি জুড়ে যার মধ্যে দিয়ে আসলে প্রকাশ পায় রাজশক্তির গরিমা।
চতুরঙ্গের উপরে সেকালের নিরন্তর রাজনৈতিক পালাবদলেরও খানিক প্রভাব পড়েছিল। দীর্ঘকাল ভারত ছোট ছোট রাজ্য বা প্রদেশে বিভক্ত। শাসন কায়েমের লক্ষ্যে তাদের মধ্যে লেগে থাকত নিরন্তর যুদ্ধ-বিগ্রহ। চতুরঙ্গের চার খেলোয়াড় যেন সেই ছোট ছোট রাজ্যের প্রতিভূ। রাজা (শাহ) এবং তাঁর মন্ত্রী (পিল) এর নেতৃত্বে চার বোড়ে (বৈদ্যাক), এক নৌকো (রূক) ও এক ঘোড়া (ফরাস) নিয়ে তৈরি এক একটি বাহিনী। খেলা হয় চার মুখো দুটি ছক্কার চালের হিসেবে। বোড়ের মাথার দাম সবচেয়ে কম – এক পয়েন্ট, রাজার পাঁচ, মন্ত্রীর চার, নৌকো ও ঘোড়ার যথাক্রমে দুই ও তিন। খেলায় বিজয়ী হলে, অর্থাৎ, তিন বাহিনীর রাজা পরাজিত হলে পয়েন্ট হতে পারে সর্বাধিক ৫৪। ‘চতুরঙ্গ’-র স্থানে জনপ্রিয় হয়েছে ‘চতুরাজি’ অর্থাৎ চার রাজার খেলা। দাক্ষিণাত্য এবং সিংহলে তার পরিচয় ‘সাদুরঙ্গম’।
ইতিহাস আরও বলে, বহু প্রদেশে বিভক্ত রাজ্যগুলোকে একত্রিকরণের ভাবনা বা লক্ষ্য বা নীতি বরাবরই দেখা যেত প্রাদেশিক রাজাদের মধ্যে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দী – যে সময়ে এই ফলক ক্রীড়া উদ্ভাবন হয়েছে – মৌর্য্য, গুপ্ত এবং পুষ্যভূতি সাম্রাজ্যের সৃষ্টি এভাবেই। অর্থাৎ, দ্বিধা-বিভক্ত রাষ্ট্র ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছে একীকরণের দিকে যুদ্ধ জয় এবং বশ্যতা স্বীকারের মধ্য দিয়ে। চতুরাজির ফলকে তার সম্ভাব্য প্রভাব খেলোয়াড়ের সংখ্যা হ্রাসে – চার থেকে দুইয়ে। বাংলার কবি রঘুনন্দনের লেখায় পাওয়া যাচ্ছে ‘সিংহাসন’ কথাটি যা আসলে বোঝায় এক রাজার অপর রাজাকে পরাজিত করে সিংহাসন লাভ। শুধু সিংহাসন নয়, জয়ী রাজার করায়ত্ব হবে বিজেতার সৈন্য বাহিনী। প্রশ্ন হল, পরাজিত রাজামশাইয়ের কী হল? বিজেতা নৃপতিকে হত্যা না করে বশ্যতা স্বীকারান্তে তাঁকে রাজসম্মান দেওয়া। সুতরাং, রাজা বন্দি হলে খেলা শেষ হয় ‘শাহ মাত’ বা ‘চেকমেট’ কিংবা ‘কিস্তিমাত’ বলে অর্থাৎ রাজা মৃত নন তিনি বন্দি।
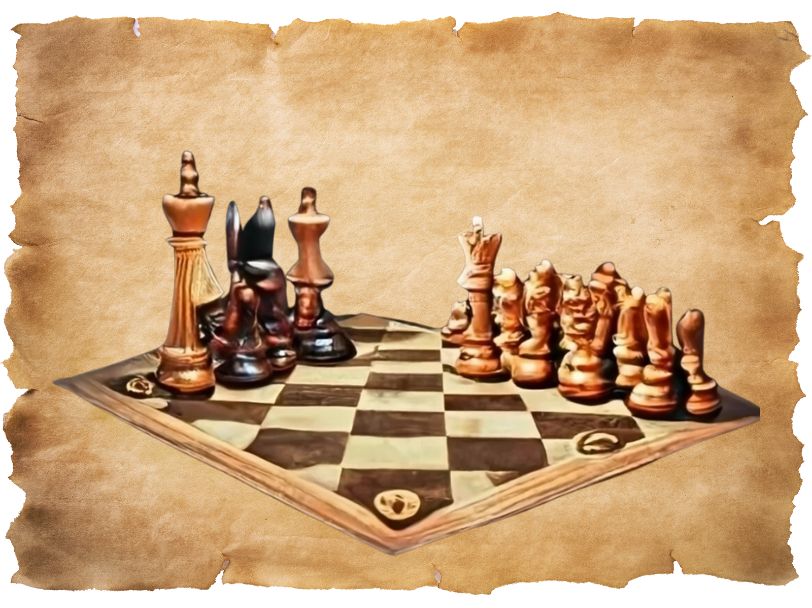
কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর খোঁজা এখনও বাকি! চতুরাজি বা দাবার বোর্ড কবে কী ভাবে হয়ে উঠল মানসিক চিন্তা দ্বারা চালিত সমর কৌশলের ক্রীড়া, সে মুক্তি পেল অক্ষপাতনের হাত থেকে? যদিও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দ্যূতক্রীড়া নিষিদ্ধ নয়– মনুসংহিতায় দেখা যায় তার বিপরীত মত। যারা দ্যূতক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে ও যারা তাদের সহায়তা করে- দুজনেরই শাস্তি বিধানের নির্দেশ এখানে স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, সাধারণের বিশ্বাস ছক্কার সাহায্যে যে কোনও বোর্ড গেম আসলে জুয়া খেলা। অতএব বের হল আইনের ফাঁক। সরে গেল ছক্কার ব্যবহার। কিন্তু খেলা এগোবে কী ভাবে? আর এখানেই হয়তো বা দিকনির্দেশ পাওয়া যায় অন্য এক বৈদেশিক প্রভাবের।
ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় কর্মতত্ত্ব বাদের প্রভাব। ব্যক্তিজীবন নির্দেশিত ও চালিত হয় কর্মফলের দ্বারা। সৎ অভিপ্রায় এবং সুকর্ম, ভবিষ্যৎ এবং পুনর্জন্মেও তার অবদান রাখে। ফলত, ব্যক্তির সাফল্য বা অসাফল্য আদপে তার কর্মফলের উপরে নির্ভরশীল – মনোগত ইচ্ছাশক্তির উপরে নয়। ছক্কার চালে দাবার হার জিৎ নির্ণয় একাধারে এই কর্ম তত্ত্বের দর্শনকেই সমর্থন করে। অতএব সেই কাঠামোকে ভেঙে, সম্পূর্ণ স্বাধীন চিন্তার মাধ্যমে নিজের ভাগ্যকে নির্ধারণ করবার বিষয়টি একদিক থেকে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলা যায় ।
আর এখানেই দাবার উপরে গ্রিক সভ্যতার প্রভাবের তত্ত্ব এসে পড়ে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকজান্ডারের হিন্দু কুশ পেরিয়ে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশের সঙ্গে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল জুড়ে গ্রীক আর দেশজ সংস্কৃতির মিশেল তার সাক্ষ্য রেখেছে স্থাপত্য ও শিল্পকলায়। বহিঃবাণিজ্যের যাত্রাপথ তৈরি হয়েছে ভূমধ্য সাগর ঘেরা গ্রীস থেকে কৃষ্ণ সাগর পেরিয়ে পারস্যের ব্যাকট্রিয়া অঞ্চল হয়ে গান্ধার প্রদেশ অবধি। সুতরাং দার্শনিক প্লেটো কুবিয়া (Kubeia) এবং পেটিয়া (Petteia) – যে খেলা দুটির কথা লিখেছেন তাও একদিন হয়তো দেশান্তরি হয়ে এসেছিল ভারতে। এর মধ্যে পেটিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভাবে মানসিক চিন্তা দ্বারা চালিত খেলা– যেখানে সমরাঙ্গনের কৌশলগত দিকটি ছিল খেলোয়াড়ের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের পরিণাম– অক্ষপাতনের কোনও ভূমিকা ছিল না। আর এখানেই জয়ী গ্রীসের যুক্তিবাদ! কিন্তু কীভাবে, কোথায় এবং কখন দুটি খেলা, অষ্টপদ এবং পেটিয়া মিলে গিয়ে দাবা খেলার বিকাশ ঘটিয়েছে দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের কাছে তার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কিন্তু এটুকু অনুমান করা যেতে পারে খ্রিস্টপূর্ব কালেই শুরু হয়েছিল মিলনের প্রক্রিয়া।
আজ বিশ্ব জুড়ে দাবা বা Chess এর জয় জয়কার! গ্র্যান্ডমাস্টার শিরোপা লাভের প্রতিযোগিতায় যা এক অর্থে মগজাস্ত্র চালনার রণভূমি। তৈরি হয়েছে Searching For Bobby Fischer, The Dark Horse, Queen of Katawe, Pawn Sacrifice, The Queen’s Gambit, The Luzhin Defense, Brooklyn Castle এর মতো ছবি যার কেন্দ্রবিন্দুতে ভারত উপমহাদেশে উদ্ভূত দাবা অথবা শতরঞ্জ। যন্ত্র দাবাড়ু “the Turk”, যন্ত্র গণক “Deep Blue” এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা “Fritz” বিভিন্ন সময়ে সুকৌশুলি দাবাড়ুকে জানিয়েছে চ্যালেঞ্জ। কখনও বা এই খেলা ঘিরে তৈরি হয়েছে প্রবঞ্চনা আর সন্দেহের আবহ। কিন্তু তার মধ্যেও থেমে থাকেনি শতরঞ্জের চৌষট্টি খোপ জুড়ে বত্রিশ মোহরার লড়াই। সময়ের সরণী বেয়ে দেশজ ‘চতুরঙ্গ’ হয়ে উঠেছে এক আন্তর্জাতিক খেলা, খেলো কা বাদশা!
সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।




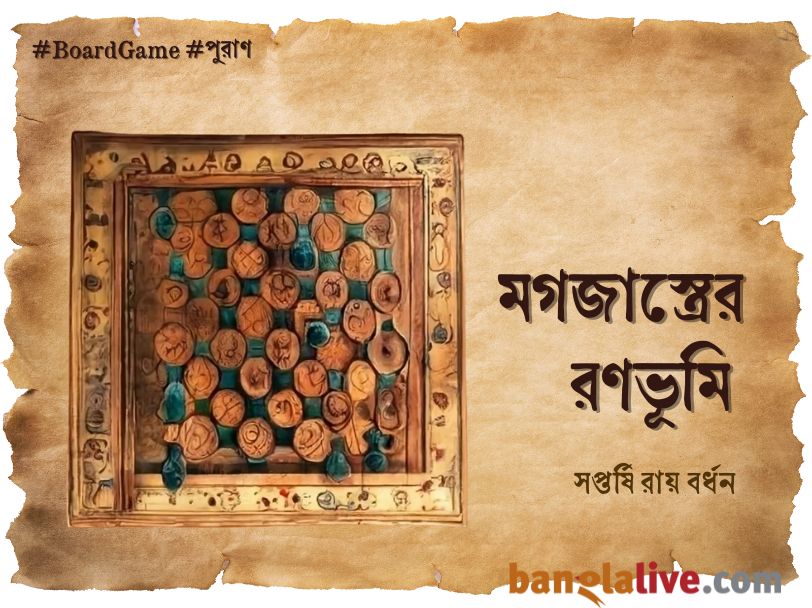





















One Response
বাঃ সুন্দর উপস্থাপনা। তথ্য সমৃদ্ধ।
তবে বড্ড তাড়াতাড়ি হঠাৎ শেষ হয়ে গেলো।