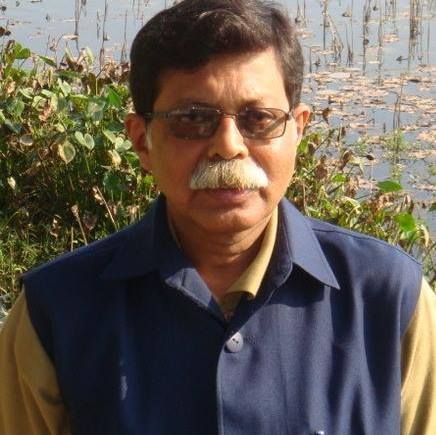ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা থেকে শুরু করে বরাক-সুরমা উপত্যকা সবই তো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দখলে এল। জল-জঙ্গল-পাহাড়ে ছড়িয়ে থাকা এত বড় এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলা-নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রীতিমতো একটা বিশেষ আরক্ষা বাহিনী সেই ১৮৩৫-এই গঠিত হল – অসম রাইফেলস। আজও সক্রিয়। ১৬৫ বছর ধরে উত্তর-পূর্ব ভারতের যাবতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা এই বাহিনীর দায়িত্ব। দায়িত্বপ্রাপ্তরা চিরকালই মাঝে মধ্যে দায়িত্বহীনের কাজ করে থাকে। তখন সংবাদমাধ্যম সাময়িকভাবে মুখর হয়। তারপর কী কারণে যেন সব আবার যথারীতি শান্ত হয়ে যায়। এটাই তো প্রচলিত রীতি।
কর্তৃত্ব কায়েম হল। কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বিশেষ বাহিনী তৈরি হল। প্রশাসনের কাজকর্ম চালু রাখতে নিত্যনতুন কর্মী নিয়োগ করতে হচ্ছে। সবই খরচ। উপার্জন কোথায়? রাজস্ব বাড়ছে না। জল-জঙ্গল-পাহাড় থেকে কীভাবে রাজস্ব বাড়ানো যায় তা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চিন্তার শেষ নেই। জমির জরিপ হয়নি। পাহাড় উপত্যকার চড়াই উৎরাই ঠেঙিয়ে জমিজিরেতের মাপজোক করতে যাওয়ার আমীন কোথায়? তার উপরে এখানে আবার সমভূমির মতো চাষবাসের বালাই নেই। পাহাড়ের খাঁজে কেউ হয়তো একটুকরো জমিতে চাষ করেছে। সে জমির মালিক কে? জানা নেই। পরের বছর সেই জমিতেই আবার চাষ হবে কিনা কেউ বলতে পারে না। বসতভিটারও একই হাল। সবমিলিয়ে রাজস্ব আদায়ের কোনও পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে সোহরা (চেরাপুঞ্জি) থেকে শিলং পর্যন্ত এলাকা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সোহরা-য় পাহাড়ের উপর একটানা অনেকটা সমভূমি। নিজেদের পছন্দ মতো জনপদ গড়ে তোলার জন্য আদর্শ জায়গা। কিন্তু বৃষ্টির দাপটে ঘরের বাইরে যাওয়া যায় না। যখন তখন বৃষ্টি শুরু হয়। কতক্ষণ চলবে জানান দেয় না। কখন থামবে তাও জানা নেই। তার উপরে গুয়াহাটি ঢাকা কলকাতা কোনওটাই সহজগম্য নয়। কী করা যায়? এইসব ভাবনা চিন্তা করতে করতে কেটে গেল প্রায় তিরিশ বছর। ইতিমধ্যে ১৮৫৭-র সিপাহী অভ্যুত্থানের পর ভারত শাসনের দায়িত্ব সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে গেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বদলে নতুন সরকারি প্রশাসন ভারতীয় উপমহাদেশের উপনিবেশে অনেক নিয়মকানুন প্রবর্তন করতে উদ্যোগী। অবশেষে স্থির হল খাসি পাহাড় আর জয়ন্তিয়া পাহাড়ের প্রশাসনিক সদর দপ্তর ইউ-শিলং দেবীর পাদদেশে অবস্থিত ‘ইয়েড্ডো’ বা ‘লিউডু’ এলাকায় স্থাপন করা হবে।
ইউ-শিলং স্থানীয় জনজাতির আরাধ্য সবচেয়ে শক্তিশালী দেবী। বরাক সুরমা উপত্যকার সর্বোচ্চ পাহাড়শিখরই প্রকৃতি উপাসক স্থানীয় জনজাতির প্রচলিত ধারণায় ইউ-শিলং দেবী। এই সমাজে মূর্তিপূজার অবকাশ নেই। কাজেই কোনও মন্দির অনুপস্থিত। গড় সমুদ্রতল থেকে প্রায় দেড় হাজার মিটার উপরে অবস্থিত এই পাহাড়শিখর থেকে বিহঙ্গের দৃষ্টিতে খাসি-জয়ন্তিয়া এলাকার পাহাড়-জঙ্গল ঝর্না-নদী অবলোকন করা যায়। তখনও যেত এবং এখনও যায়। স্থানীয় লোকজন অবরেসবরে সময় পেলেই এখানে চলে আসে। আর বাইরের মানুষ, তা সে দেশি হোক বা বিদেশি, বেড়াতে এসে সবার আগে এখানেই ছুটে আসে। জায়গাটার এখনকার নাম শিলং পিক। ১৮৬৪ সালে ইউ-শিলং দেবীর পাদদেশে অবস্থিত ‘ইয়েড্ডো’ বা ‘লিউডু’ এলাকার নতুন নাম হল শিলং।
১৮৭৮-এ তৈরি হল শিলং পুরসভা। শহরে জায়গা কম পড়ে যাওয়ায় লাগোয়া গ্রাম মাওখর ও লেবান শিলং পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। তখন তো আর জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। ঘটনাক্রমে এখনকার লেবান হল শিলং শহরের অন্যতম অভিজাত এলাকা। অবসর বিনোদনের জন্য ১৮৭৮-এই তৈরি হল শিলং ক্লাব।
শিলংয়ের আবহাওয়া ব্রিটিশের শরীর স্বাস্থ্যের অনুকূল। কলকাতা ঢাকা গুয়াহাটির মতো চিটচিটে ঘাম ঝরানো গরম নেই। মশার উৎপাত নেই বললেই চলে। সারা বছর মনোরম জলবায়ু। চোখ জুড়িয়ে যাওয়া প্রাকৃতিক পরিবেশ। কাজেই প্রশাসনিক সদর দপ্তর শিলংয়ে সরিয়ে এনে নিশ্চিন্তে মসৃণ জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত হল। দেখতে দেখতে ব্রিটেন থেকে সদ্য আগত যুবক প্রশাসকদের কাছে শিলং হয়ে গেল আদর্শ এবং আকর্ষণীয় কর্মস্থল। দেশের রাজধানী কলকাতা থেকে বেশ দূর। ঢাকা বা গুয়াহাটির মতো নিত্যকার সমস্যা শিলংয়ে অনুপস্থিত। সবচেয়ে বড় কথা কাজ কম, অবসর বেশি। শিলং-কে ‘প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড’ আখ্যা দিয়ে তারা দেশে চিঠি পাঠায়। নতুন জনপদ শিলং তাদের মনের কোনে নিজের দেশের আলতো ছোঁয়া বুলিয়ে দেয়।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক তো আর আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটানোর জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে শাসনের দায়িত্ব নেয়নি। ব্রহ্মপুত্র বরাক সুরমা উপত্যকায় আগেই আয়ত্বে এসেছে। এবার নজরে এল নাগা পাহাড় আর লুসাই পাহাড় (এখনকার মিজোরাম)। ১৮৭৪-এ শিলং-এ স্থাপিত হল মুখ্য কমিশনার-এর সদর দপ্তর। অবিভক্ত অসম, খাসি জয়ন্তিয়া গারো পাহাড়, নাগা পাহাড় আর লুসাই পাহাড় এবং অবিভক্ত সিলেট জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত হলেন একজন মুখ্য কমিশনার।
বাড়ছে কাজ। জনসংখ্যাও বেড়ে চলেছে। জীবনযাপন প্রক্রিয়া সহজ সরল ও সচল রাখার জন্য পৌর প্রশাসন গড়ে তোলা প্রয়োজন। মুখ্য কমিশনার বা তাঁর অধঃস্তন আধিকারিকরা তো শিলং শহরের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের জন্য দেশ ছেড়ে এতদূরে আসেননি। ১৮৭৮-এ তৈরি হল শিলং পুরসভা। শহরে জায়গা কম পড়ে যাওয়ায় লাগোয়া গ্রাম মাওখর ও লেবান শিলং পুরসভার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। তখন তো আর জমি অধিগ্রহণ নিয়ে কোনও সমস্যা ছিল না। ঘটনাক্রমে এখনকার লেবান হল শিলং শহরের অন্যতম অভিজাত এলাকা। অবসর বিনোদনের জন্য ১৮৭৮-এই তৈরি হল শিলং ক্লাব। শিলং ক্লাবের উদ্যোগে ১৮৮৯ (মতান্তরে ১৮৯৮) নাগাদ গড়ে ওঠে শিলং গল্ফ কোর্স।
প্রশাসন ও পর্যটন নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল শিলং এবং আশপাশের অঞ্চল। কৃষিজ উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের খবর নেই। এমনকি চা বাগিচা স্থাপনেরও চেষ্টা হয়নি। প্রতিবেশী এলাকার পাহাড়ে একের পর এক চা বাগান স্থাপনের কাজ ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চললেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে এখানে হয়নি। একইরকমভাবে এখানকার ভূগর্ভের সম্পদ সম্পর্কে কোনও সামগ্রিক ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষাও হয়নি।

ইতিহাসের নথি অনুসারে ১৮১৫ নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনৈক আধিকারিক (মি.স্টার্ক) কর্তৃপক্ষকে জানান যে সিলেটের সীমানার কাছাকাছি কোনও একটা জায়গায় কয়লার স্তর (পরিভাষায়,-সীম) তাঁর নজরে এসেছে। দুর্গম পাহাড়ি পথ পেরিয়ে সেই কয়লা বাজারে নিয়ে আসা সম্ভব নয় বলে প্রসঙ্গটি আর এগোতে পারেনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মি.ক্রোক্র্ফট নামের অন্য এক আধিকারিক ১৮৩২-এ জানালেন সোহরা এলাকায় মাটির গভীরে কয়লার স্তর আছে। এবার কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করল। খাসি পাহাড়ের সোহরা এবং জয়ন্তিয়া এলাকার লাকাডং গ্রামের মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা কয়লা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত হল। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি এবারেও কিছুই হল না উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব। ফলে উত্তোলন তথা উৎপাদন খরচ বেশি। তার থেকেও বড় বিষয়, মাটি খুঁড়ে কয়লা বের করার পর সেই পণ্য কিনবে কে? স্থানীয় মানুষের তো কয়লার ব্যবহার বিষয়ে কিছুই জানা নেই। কাজেই চাহিদার অভাবে এবারও কয়লা উত্তোলনের কাজ বাতিল করতে হল।
জয়ন্তিয়া পাহাড়ের লাকাডং এলাকায় ১৮৭৭-৭৮ শুরু হল কয়লা খনি খোঁড়ার কাজ। সিলেট সীমান্তের গ্রামটি তখন ‘লুম মুইয়ং’ নামে পরিচিত। কোনওরকম যন্ত্রপাতি ছাড়া একেবারে প্রচলিত পদ্ধতিতে সারা বছরে প্রায় ২ টন কয়লা উত্তোলন করা হল। নৌকায় করে টিসাং নদী পেরিয়ে কিছু কয়লা সিলেটে পাঠানো হল। আর বাদবাকি খরচ হল জোয়াই-তে বসবাসরত সরকারি আধিকারিকদের বাড়িতে। এক বছর পর দেখা যায় যে প্রকল্পটি লাভজনক হওয়া তো দূরের কথা কোনওভাবেই বাণিজ্যিক নয়। অতএব জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মাটির তলায় সঞ্চিত কয়লা উত্তোলন বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন অবিশ্যি কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে প্রায় একশো বছর পর জয়ন্তিয়া পাহাড়ের এই কয়লা স্থানীয় সামাজে নিয়ে আসবে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন। আর সেই আলোড়নের কেন্দ্রবিন্দু হবে জোয়াই।
প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদ ও পরিচিত পরিকল্পনাবিশারদ। পড়াশোনা ও পেশাগত কারণে দেশে-বিদেশে বিস্তর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। তার ফসল বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় বই। জোয়াই, আহোম রাজের খোঁজে, প্রতিবেশীর প্রাঙ্গণে, কাবুলনামা, বিলিতি বৃত্তান্ত ইত্যাদি।