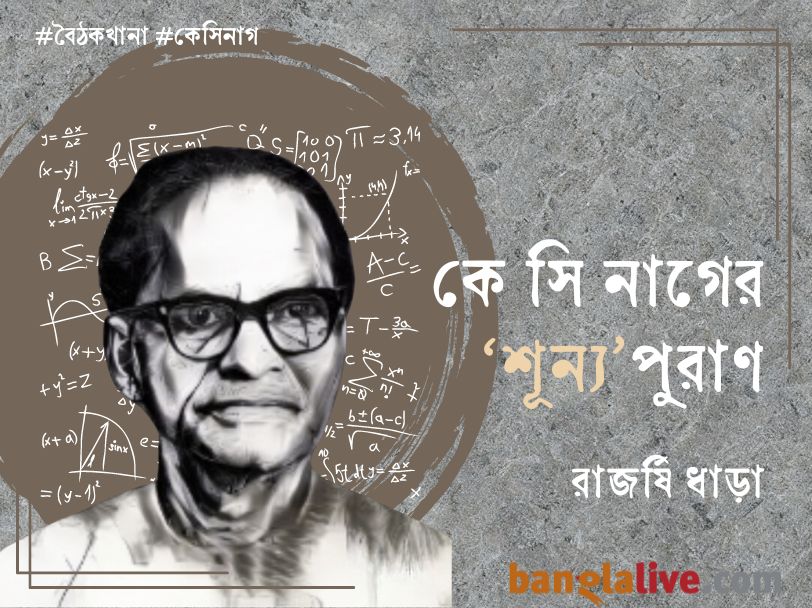(K C Nag)
“তেল মাখা বাঁশে উল্লাসে উঠেছে মাংকি।
সে বেটা চড়ছে তেরো সেমি তো পড়ছে চোদ্দ কিমি;
ভাঙবে ঠ্যাং কি?
বাম্বু ভর্তি তৈল, স্লিপ স্লিপারী ঐলো প্রমোশন।” (K C Nag)
‘চন্দ্রবিন্দু’-র ‘জুজু’ অ্যালবামের গান। গানের নাম ‘অঙ্ক কী কঠিন’। সত্যিই, অঙ্ক খুব কঠিন। একটি তৈলাক্ত বাঁশে একটি বাঁদর উঠছে-নামছে; দুটি ট্রেন পাশাপাশি বিপজ্জনকভাবে চলেছে; একটি ছাত্র ⅓ ভাগ রাস্তা হেঁটে, ⅓ ভাগ সাইকেলে আর ⅓ ভাগ নৌকায় করে স্কুল যাচ্ছে; একটি চৌবাচ্চায় একটি নল দিয়ে ২ লিটার প্রতি মিনিট বেগে জল ঢুকছে আর ৩ লিটার প্রতি মিনিট বেগে জল বেরোচ্ছে – এইরকম উদ্ভট পরিস্থিতিতে বাঙালিদের বছরের পর বছর যিনি ফেলেছেন, তিনি হলেন মিত্র ইনস্টিটিউশন স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। নাম? একটু ঘুরিয়েই নামটা বলা যাক। কিছুবছর আগে একটি মিম সমাজমাধ্যমে খুব ভাইরাল হয়; দু-জন ভদ্রলোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন, একজন বলছেন– আমি রসগোল্লা খাওয়ানোর জন্য বিখ্যাত, দ্বিতীয়জন বলছেন– আমি রসগোল্লা পাওয়ানোর জন্য বিখ্যাত। প্রথমজন হলেন কে সি দাস, এবং দ্বিতীয়জন গণিতশিল্পী কে সি নাগ (K C Nag)। আজ এই প্রবাদপ্রতিম গণিত শিক্ষকের জন্মদিন। (K C Nag)
কেশব চন্দ্র নাগ ১৮৯৩ সালের ১০ জুলাই হুগলির গুড়াপের নাগপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলাতেই বাবা রঘুনাথ নাগকে হারান তিনি। পড়াশোনা শুরু করেন গুড়াপের একমাত্র স্কুলে, তারপর ভাস্তাড়া যজ্ঞেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে ও কিষেণগঞ্জ হাইস্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ১৯১২ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় এসে রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ভর্তি হন ও সেখান থেকে আইএসসি পাস করেন। তারপর কর্মজীবনে শিক্ষকতা… না, লেখাটা ঠিক জমছে না। এইসব তথ্য তো আপনারা আন্তর্জাল ঘাঁটলেই খুঁজে পাবেন, আজ অন্য কয়েকটা বিষয় নিয়ে কথা বলা যাক। (K C Nag)
আমরা আসলে বুঝতেই পারিনি উনি কী বলতে চাইছেন? এখন ওঁর অঙ্কগুলোকে ফিরে দেখলে মনে হয়, উনি সময়ের থেকে হয়তো এগিয়ে ভাবতে পারতেন।
কেশব চন্দ্র নাগের অঙ্ক, আপাতভাবে মনে হতে পারে খুব অসংলগ্ন, কিন্তু সত্যিই কি তাই? না কি এও সেই সুকুমার রায়ের মতো বিষয়? আমরা আসলে বুঝতেই পারিনি উনি কী বলতে চাইছেন? এখন ওঁর অঙ্কগুলোকে ফিরে দেখলে মনে হয়, উনি সময়ের থেকে হয়তো এগিয়ে ভাবতে পারতেন। (K C Nag)
সেই শ্রমিকদের মনে আছে? হ্যাঁ, যারা কোনও কারণ ছাড়াই অর্ধেক কাজ করে, বাকি অর্ধেক কাজ অসমাপ্ত রেখে চলে যেত। আচ্ছা, ওরা কেন যেত? কোথায় যেত? ওরা কি মজুরি নিয়ে যেত না কি মজুরি ছাড়া যেত? এখন রাস্তাঘাটে কোনও অসম্পূর্ণ কন্সট্রাকশন দেখলে কেমন ভয় লাগে; এরাই সেই শ্রমিকরা নয় তো? আমরা বিগত বেশ কিছু বছরে রাজ্যের বা দেশের ক্ষেত্রে দেখেছি অনেক আকাশকুসুম উদ্যোগ, ঘোষণা, শিলান্যাস। কোনও বিখ্যাত মানুষের বিদেশে গিয়ে এদেশে করতে চাওয়া শিল্পের ঘোষণা হয়তো সবারই মনে আছে (সেই ঘোষণা এখনও পূর্ণতা পায়নি, তা অন্য ব্যাপার)। এই শ্রমিকরাও ঠিক ওঁদের মতোই অর্ধেক কাজ করে চলে যায়, অনেক সময় কাজ শুরু করব বলেও করে না। দূরদৃষ্টি ছিল বটে কেশববাবুর! (K C Nag)
ধরে নেওয়া যাক, আপনি খুব আশায় আশায় আছেন, আপনাকে দার্জিলিং চা পরিবেশন করা হবে, কিন্তু চায়ে চুমুক দিয়েই আপনার মুখ কুঁচকে গেল। কেউ একজন দার্জিলিং চায়ের সঙ্গে আসাম চা মিশিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলেছে। এই অঙ্কও অনেকেরই পরিচিত। আচ্ছা ধরুন দার্জিলিং চা’এর দাম পাঁচশো টাকা কেজি, আর আসাম চা আড়াইশো টাকা। দুটো মেলালে কী হবে? দামের হেরফের। এখানেও প্রকাশ পেল বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতাই। (K C Nag)
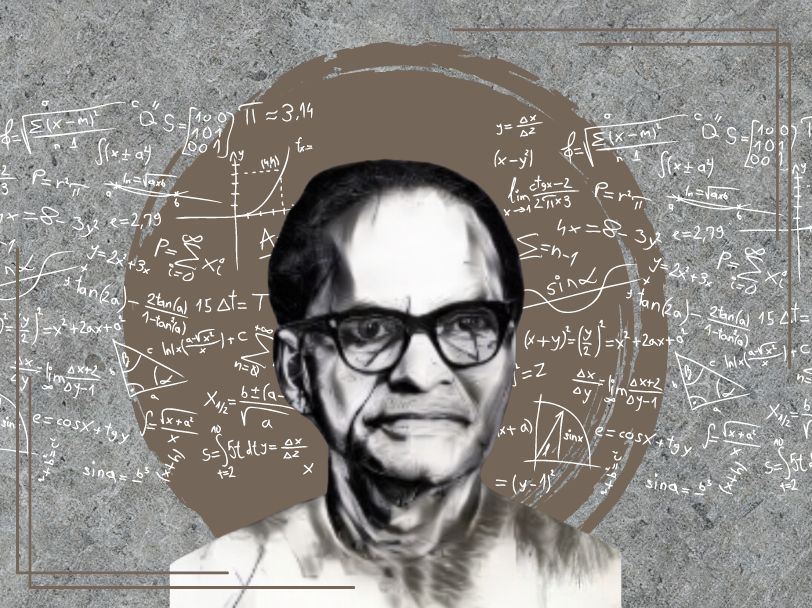
কিন্তু প্রিয় পাঠক, আপনি তো আবার সৌখিন মানুষ। আপনার এসব চা নিয়ে চাপানউতোর কি ভাল লাগবে? মেজাজটা বিগড়ে গেল তো? একটু ঘুরে আসি চলুন, মন ভাল হয়ে যাবে। (K C Nag)
নৌকাবিহার? চেপে বসুন দেখি। নদীর ঠান্ডা হাওয়া খান। কিন্তু এ কী! নদীর স্রোত আবার উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিল কে? ভাবুন তো, নৌকার মাঝিকে স্রোতের বিপরীতে যেতে কতটা পরিশ্রম করতে হবে! ঠিক যেন জীবন নৌকা। চাকরির আকাল, পরীক্ষা কেলেঙ্কারি, প্যানেল বাতিলের মতো প্রতিকূল স্রোতকে কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের। অথবা আমাদের ঘাড়ের উপর পা দোলাচ্ছেন যাঁরা, যে পা এক নয়, অদৃশ্য দুটি নৌকায় রয়েছে। স্রোত দেখে যাঁরা নৌকা বদলে নিচ্ছেন অহরহ, এঁদেরও কি অনুপ্রেরণা ওই অঙ্ক বই? (K C Nag)
নৌকা থেকে নামা যাক, তার চেয়ে চলুন বাড়িতে ফিরে যাই। আপনার ঐতিহাসিক পৈতৃক বাড়ির এককোণে ওই যে অভিমানী, ফুটো চৌবাচ্চা, যা জল খায়, তার চেয়ে বেশি কাঁদে! এখানেই বিপত্তি, এই চৌবাচ্চায় একটি নল দিয়ে জল ঢোকে আর দুটি ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায় জল! এখনও উত্তর নেই, এই ফুটোগুলো কেউ বুজিয়ে দিত না কেন? এ যেন মধ্যবিত্তের পকেট; কতটা ঢুকছে তার নেই ঠিক, কাঁচা-বাজার, গ্যাস আর মোবাইল রিচার্জ করাতে গিয়েই কিছুতেই আর ভরে উঠছে না। (K C Nag)
ধরুন, বাঁদরটা সিসিফাসের জান্তব সংস্করণ। সিসিফাসের পাথর গড়িয়ে তোলার মতো বাঁদরটির আরোহণও চলতে থাকবে অনন্তকাল।
দৃষ্টিপাত করা যাক জনপ্রিয় তৈলাক্ত বাঁশের প্রসঙ্গে। জীবনে আমরা যদি সম্পর্কের চেয়েও বেশি বাঁশ কোনও বিষয়ে খেয়ে থাকি, তা অবশ্যই অঙ্ক। তবে সে বাঁশে বাঁদর ওঠানামা করে। আচ্ছা, এই অঙ্কটা করতে গিয়ে কোনওদিন মনে হয়েছে, এই বাঁশ আর বাঁদর কোথাও যেন অ্যাবসার্ড নাটকের চরিত্র। বাঁদরটা বারবার ওঠার চেষ্টা করছে, আবার নেমে যাচ্ছে, আবার উঠতে চাইছে। এ যেন স্যামুয়েল বেকেটের অ্যাবসার্ড নাটক, বাঁদর আর বাঁশ দুটোই একটি অদৃশ্য বৃত্তে আটকে পরেছে, বেরোতে পারছে না। বা ধরুন, বাঁদরটা সিসিফাসের জান্তব সংস্করণ। সিসিফাসের পাথর গড়িয়ে তোলার মতো বাঁদরটির আরোহণও চলতে থাকবে অনন্তকাল। (K C Nag)
বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমরা বাঁদর এবং বাঁশ, দুটি বিষয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। কিছুদিন পরেই দুর্গাপুজো। স্মরণজিৎ চক্রবর্তী কোনও একটা লেখায় এরকম একটা কথা লিখেছিলেন যে, পুজো এলেই গোটা শহরটা বাঁশের কেল্লা হয়ে ওঠে। আচ্ছা, দেবী দুর্গার পুজো প্রথম যেন কে করেছিলেন? তাঁর যেন কীসের সেনা ছিল? পুরান থেকে উঠে সেই সেনা আবার নতুন করে কীভাবে যেন জেগে উঠেছে! আমি আর গভীরে যাচ্ছি না, কারণ ‘প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা’। (K C Nag)
উনি ছিলেন এবং ওঁর এই অঙ্কের বইগুলি ছিল বলেই অনেক অঙ্কে ভীতু ছাত্রছাত্রী আজ একটু হলেও অঙ্ককে ভালবাসতে পেরেছে।
কে সি নাগের অঙ্কের বিষয়গুলি নিয়ে অনেকটা মজা করার পরও যে কটি কথা না বললেই নয়– উনি ছিলেন এবং ওঁর এই অঙ্কের বইগুলি ছিল বলেই অনেক অঙ্কে ভীতু ছাত্রছাত্রী আজ একটু হলেও অঙ্ককে ভালবাসতে পেরেছে। প্রভাত দে সরকার রচিত কে সি নাগ সম্পর্কে ‘অঙ্ক বুড়ো’ নামে একটি কবিতা পেলাম; সেটির কিছু অংশ থাক শেষপাতে আপনাদের জন্য–
“পাড়ার মোড়ে হঠাৎ দেখি অঙ্ক-পাগল কেশব খুড়া
হাতটা চেপে বলল ডেকে– অঙ্কে ভয় ক্যানরে ছোঁড়া?
সংখ্যাগুলোয় অঙ্ক আছে, অঙ্ক আছে নিমের ডালে।
গোরুর চলায় অঙ্ক আছে, অঙ্ক আছে ঢাকের তালে।…
চল আনিগে অঙ্ক খানিক ছবির লাগি, ছড়ার তরে।
কল্পনাতে অঙ্ক দিলে ছবিও বাড়ে, ছড়াও বাড়ে।” (K C Nag)
রাজর্ষি ধাড়া। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। অ-মৃত লিটল ম্যাগাজ়িনের সম্পাদক। শখ ছবি আঁকা এবং থিয়েটার।