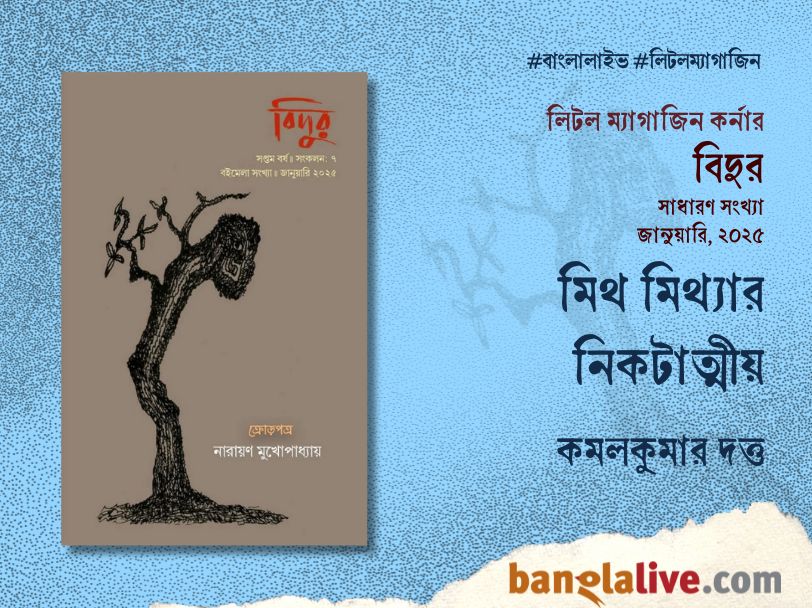(Little Magazine)
সংকট ও সম্ভাবনার প্রসঙ্গে আমি সরাসরি যাচ্ছি না। আগে লিট্ল ম্যাগাজিন হিসেবে ‘মিথ’ হয়ে যাওয়া ‘সবুজপত্র’ আর ‘কবিতা’, এই পত্রিকাদুটি একটু নেড়েচেড়ে তাদের ‘মিথোলজি’ বুঝে নিতে চাইব। সঙ্গে সঙ্গে ‘কৃত্তিবাস’-এর গায়েও একটু হাত বুলিয়ে তার মাপের আন্দাজ পেতে চাই। এসব থেকেই ঈষৎ পরোক্ষভাবে লিট্ল ম্যাগাজিনের সংকট ও সম্ভাবনার সঙ্গে পাঠকের দেখা হয়ে যাওয়ার কথা। বাকি কথা লেখার শেষদিকে, এবং সরাসরি। (Little Magazine)
তারও আগে লিট্ল ম্যাগাজিনের ধারণাটি বুঝে নেওয়া জরুরি। ‘ম্যাগাজিন’ অর্থে পত্রিকা বা সাময়িকপত্র তো ছিলই, কেন প্রয়োজন হল তার আগে ‘লিট্ল’ শব্দটির? এটা কি কোনো অভিধা, কোনো লেবেলিং? এর অর্থ যদি হয় ছোটো পত্রিকা, তাহলেও প্রশ্ন থাকে কোন দিক দিয়ে ছোটো? এই প্রশ্নের জায়গা থেকেই নানা বিকল্প নামের ব্যবহার দেখেছি আমরা। কেউ বলেছেন ‘চড়ুইপত্র’ তো কেউ বলেছেন ‘সবুজপত্র’। আমিও একটা নাম দিয়েছিলাম, ‘উজানপত্র’। (Little Magazine)
আরও পড়ুন: ভ্রমি: রুকমণিয়ার ঘরবাড়ি- শ্ৰীমা সেন মুখার্জি
একটু পশ্চিমে তাকাই। ইউনাইটেড স্টেট্স ও ইংল্যান্ডে বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকার বিপ্রতীপে নতুন ভাবনাচিন্তা নিয়ে একদল লেখক, যাঁদের ‘আভাঁ গার্দ’ বলা হয়েছে, অবাণিজ্যিকভাবে কয়েকটি পত্রিকার জন্ম দিয়ে নিজেদের লেখালেখি প্রকাশ করতে শুরু করেন। এর শুরুটা মোটামুটি ১৮৮০ সাল। পাশাপাশি ফরাসি ব্যতিক্রমী লেখকদল, বিশেষ করে ‘সিম্বলিস্ট’ কবি ও সমালোচকরা এরকম অবাণিজ্যিক পত্রিকাকে অবলম্বন করে তাঁদের সাহিত্য-আন্দোলন শুরু করেন। এই বিশেষ চরিত্রের পত্রিকার তিনটি প্রধান লক্ষণ ছিল:
১. সম্পাদনা, ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিষয়ে এইসব পত্রিকা অবাণিজ্যিক।
২. এই ধরনের পত্রিকার উদ্দেশ্য সেইসব সাহিত্যের প্রকাশ যা বাণিজ্যিক পত্রিকা ছাপতে আগ্রহী নয়। (আগ্রহী নয় তিনটি কারণে: ক. লেখক নতুন ও অপরিচিত, ফলে তাঁর লেখা ছাপলে বাণিজ্যিক ঝুঁকি রয়েছে, খ. লেখা পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক অর্থাৎ প্রচলিত রীতি মেনে নয়, গ. এইসব লেখা প্রচলিত সামাজিক, নৈতিক বা গণগ্রাহ্য নন্দনতত্ত্বের বিরুদ্ধগামী)। এরকম কয়েকটি পত্রিকার নাম Blast (১৯১৪-১৫), The Egoist (১৯১৪-১৯), Little Review (১৯১৪-২৯), Eugene Jolas’ Transition (১৯২৭-৩৮), Poetry (১৯১২)। (Little Magazine)
উপরের প্রথম তিনটি পত্রিকা যে বছরে আত্মপ্রকাশ করে সে বছরেই বাংলায় ‘সবুজপত্র’ প্রকাশিত হয় প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায়। অনেকেই এই পত্রিকাটিকে বাংলা লিট্ল ম্যাগাজিনের পথিকৃত বলে মানেন ও উল্লেখ করেন (কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’-কে এই স্থান দিতে চান)। আমরা যদি এই পত্রিকাটিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টির সামনে রাখি তাহলে ক্রমে বুঝতে পারব, সম্পাদক হিসেবে প্রমথ চৌধুরীর নাম ছাপা হলেও ‘সবুজপত্র’ আসলে ছিল রবীন্দ্রনাথের ব্রেন-চাইল্ড। (Little Magazine)
রবীন্দ্রনাথই প্রমথ চৌধুরীকে তাগাদা দিয়ে-দিয়ে পত্রিকাটির প্রকাশ ঘটান। তার আগে ‘সবুজপত্র’ নামকরণ করেন। চিঠিতে প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, ‘…সেই কাগজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে সুধু চিন্তা করলে হবে না— কিছু লিখ্তে সুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি ‘কনিষ্ঠ’ হয় ত কি রকম হয়।…’? এ চিঠির তারিখ দেওয়া নেই, তবে ৫ মার্চ ১৯১৪-র আগে, কেন না মার্চের ৫ তারিখে লিখছেন, ‘সবুজপত্র উদ্গমের সময় হয়েছে… আমি একটু ফাঁক পেলেই কিছু লেখবার চেষ্টা করব। বিবিকে সুরেনকেও তাড়া দিয়ো।’ এর আঠেরো দিনের মাথায় লিখছেন, ‘আচ্ছা, রাজি আছি। ১৫ই বৈশাখেই বের কর। ইতিমধ্যে দুই একটা লেখা দিতে পারব।…’ এর বারো দিনের মাথায়, ‘…একটু বৈঠক-জমানো রকমের অবকাশ না পেলে গল্প লেখার সুবিধা হয় না। তবু চেষ্টা দেখা যাবে। (Little Magazine)
তুমি নাটোরে গেছ কল্পনা করে তোমার কাছে না পাঠিয়ে মণিলালকে প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলুম সেটা কি এখনো সম্পাদকী ডেস্কের উপরে দাখিল হয়নি? তোমরা ১৫ই বৈশাখে কাগজ ত বের করচ কিন্তু হাতে দু-তিন মাসের সম্বল ত জমাও নি—’। ১৯১৬-র ফেব্রুয়ারির চিঠি, ‘সবুজপত্রেই তোমার গল্পটি এক সংখ্যাতেই কেন বের হবে না? আমার ‘ঘরে বাইরে’ ফাল্গুনেই শেষ করে দিয়েছি। গত বছর চৈত্রে যেমন ফাল্গুনী বের হয়েছিল এবারে তেমনি কেবলমাত্র তোমার গল্প বের হোক্। আমার প্রস্তাব হচ্চে এই: ফাল্গুনের সবুজপত্র বের করতে আর বেশি দেরি কোরোনা— তারপর চৈত্রের প্রথম সপ্তাহেই তোমার গল্পটি বেরিয়ে যাক্।… যদি প্রফুল্ল চক্রবর্তীর কিছু থাকে দিয়ে দিয়ো।…’
“পরবর্তীকালে এই কাগজে রবীন্দ্রনাথ দু-হাতে লিখেছেন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, এমনকী ধারাবাহিক উপন্যাস। এক একটি সংখ্যায় মোটামুটি তিন থেকে পাঁচটি লেখাই রবীন্দ্রনাথের।”
এরকম আরও চিঠি (প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি বিশ্বভারতী প্রকাশিত চিঠিপত্র-৫-এ পাওয়া যাবে) উদ্ধার করতে পারি যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে ‘সবুজপত্র’-র রথী কে, সারথিই-বা কে ছিলেন। মনে রাখতে হবে এসময়ে রবীন্দ্রনাথ ভারতে তো বটেই পৃথিবীর প্রেক্ষাপটেও বিখ্যাত (আগের বছরেই নোবেল পেয়েছেন) ও তাঁর লেখার ছাঁদ তৈরি হয়ে গেছে। এরকম একজন কবি ও লেখকের অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হচ্ছে বাংলার তথাকথিত প্রথম লিট্ল ম্যাগাজিন! যাই হোক, শেষপর্যন্ত বের হল, তবে ১৫য় নয়, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখে (১৩২১)। ১৫ থেকে সরে ২৫ কেন সে তথ্য আমার কাছে নেই, তবে আন্দাজ করা যায়। মনে রাখতে হবে এসময় সবুজপত্রের সম্পাদকের বয়স ৪৬ বছর। (Little Magazine)
সবুজপত্রের প্রথম সংখ্যা উলটে আমরা কী দেখতে পাই? দেখি প্রথমেই সম্পাদকের কথা শুরু হয়েছে মাথায় ‘ওঁ প্রাণায় স্বাহা’ লিখে। অনেকগুলি পাতা জুড়ে ধোঁয়াটে কথার মারপ্যাঁচ। তার পরেই ‘বীরবল’ ছদ্মনামে আরও কয়েক পাতা। এরপর সবুজপত্রের জন্যেই ছন্দে লেখা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ উপদেশক কবিতা ‘সবুজের অভিযান’। এর পরেই রবীন্দ্রনাথের আরেকটি গদ্য ‘বিবেচনা ও অবিবেচনা’। ঠিক তার পরে রবীন্দ্রনাথের বড়ো গল্প ‘হালদার গোষ্ঠী’। এরপর আরেকটি অন্ত্যমিলের কবিতা ‘সবুজ পাতার গান’, লিখেছেন সেসময়ে বিখ্যাত (ছন্দের জাদুকর) কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। (Little Magazine)
ব্যস, প্রথম সংখ্যা শেষ! পরবর্তীকালে এই কাগজে রবীন্দ্রনাথ দু-হাতে লিখেছেন গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, এমনকী ধারাবাহিক উপন্যাস। এক একটি সংখ্যায় মোটামুটি তিন থেকে পাঁচটি লেখাই রবীন্দ্রনাথের। এমন সংখ্যাও বেরিয়েছে যার প্রায় পুরোটাই রবীন্দ্রময়। হ্যাঁ, আরও লেখক সবুজপত্রে লিখেছেন, যেমন, কিরণশঙ্কর রায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, হারিতকৃষ্ণ দেব, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বরদাচরণ গুপ্ত, ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী প্রমুখ। এঁদের অনেকেই তখন ‘ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা’ নন। (Little Magazine)
তাঁদের অনেকের নামের পাশে আবার ডিগ্রির উল্লেখ থাকত, যেমন: আই-সি-এস, বার-অ্যাট-ল, সি-আই-ই, বি-এ, এম-এ, এম-এ বার-য়্যাট-ল, এম-এ ডি-এল। এই পত্রিকার পাতাতেই সম্পাদকের স্বীকারোক্তি: ‘সবুজপত্রের বিরুদ্ধে নানা বদনাম থাকা সত্বেও একটি বিশেষ সুনাম আছে। জনরব যে এ পত্রের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের বেনামদার। এ প্রবাদটি অক্ষরে-অক্ষরে সত্য না হলেও প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা নয়। সকলেই জানেন যে, প্রথম দু’বছর রবীন্দ্রনাথের লেখাই ছিল— কী ওজনে, কী পরিমাণে এ-পত্রের প্রধান সম্পদ। সবুজপত্র বাঙলার পাঠকসমাজে যদি কোনোরূপ প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা লাভ করে থাকে তো সে মুখ্যত তাঁর লেখার গুণে। রবীন্দ্রনাথের সাহায্য ব্যতীত আমি যে এ কাগজ চালাতে পারবো, এ ভরসা আমার আদপেই ছিল না। আমার ক্ষমতার সীমা আমি জানি।…’ (Little Magazine)
এরকম ক্ষমতা নিয়ে নতুন চরিত্রের কাগজ সম্পাদনা করতে এসেছিলেন বাংলা, ইংরেজিসহ ফরাসি ভাষা ও সাহিত্যের রসজ্ঞ পাঠক প্রমথ চৌধুরী? বিশ্বাস হয় না। বরং জানতে ইচ্ছে করে সেইসময়ের পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত থেকেও কীভাবে তিনি দীর্ঘ দশ বছর ধরে এরকম একটি সাধারণ মানের পত্রিকা সম্পাদনা করে যেতে পারলেন? রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পাদকসত্তাকে গ্রাস করেছিলেন?
“আমাকে প্রথম বাংলা লিট্ল ম্যাগাজিনের নাম করতে বললে আমি সবুজপত্রের ৯ বছর পরে প্রকাশিত ‘কল্লোল’ পত্রিকার নাম বলব, এবং বলব নির্দ্বিধায়।”
এমন সাবুত যথেষ্ট রয়েছে যা থেকে বলা যেতে পারে যে সবুজপত্রকে তাঁর ইচ্ছেমতো চালনা ও ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। ৬ জুলাই, ১৯২৫ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি লিখছেন, ‘প্রমথ, চরকার উপর একটা আমার মন্তব্য লিখেছি। তোমাকে দিতে পারি। …তোমার যদি বিলম্ব থাকে তাহলে অগত্যা আর কোথাও ছাপতে দিতে হবে। লেখাটা কিন্তু সবুজপত্রেরই সবর্ণ…।’ ওই বছরের ১০ ডিসেম্বরে লিখছেন, ‘প্রমথ, এইমাত্র দিলীপকে একখানি চিঠিতে আর্ট সম্বন্ধে দুচার কথা আলোচনা করে লিখেছি। যদি সে চিঠি সবুজপত্রে ছাপতে দিতে তার সম্মতি নিতে পারো তাহলে এই আলোচনাটির অনুবর্তন করে তোমরাও কিছু বলতে পারবে…।’ (Little Magazine)
এবার ভাবুন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বেঁচে আছেন এবং মূলত তাঁর দু-হাতে লেখা কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও নির্দেশ সম্বল করে একজন সম্পাদক একটি ‘লিট্ল ম্যাগাজিন’ বের করে চলেছেন দশ বছর ধরে! সাধু ভাষার বদলে চলিত ভাষা ব্যবহার করলেই একটি সাহিত্য পত্রিকা লিট্ল ম্যাগাজিন হয়ে ওঠে না। সবুজপত্রের চলিত ভাষাটাও ছিল অতি পরিশীলিত চলিত ভাষা। (Little Magazine)
জানি, এর পরেও বাংলার প্রথম লিট্ল ম্যাগাজিন হিসেবে ‘সবুজপত্র’-এর নামই বলা, লেখা ও ছাপা হতে থাকবে, এবং সেসবের বেশিরভাগটাই লিট্ল ম্যাগাজিনের পাতায়!
আমরা এতটাই সবুজ, আমরা এতটাই কাঁচা!
আমাকে প্রথম বাংলা লিট্ল ম্যাগাজিনের নাম করতে বললে আমি সবুজপত্রের ৯ বছর পরে প্রকাশিত ‘কল্লোল’ পত্রিকার নাম বলব, এবং বলব নির্দ্বিধায়। কেন, তার বিস্তারিত আলোচনায় গিয়ে লেখা অস্বাভাবিক বড়ো করতে চাই না। এ লেখার আরও কথা বলার আছে, এবং তার আনুমানিক আয়তন কম হবে না।
“এই ‘চরিত্র’ বলতে কী বুঝব আমরা? বাণিজ্যিক পত্রিকা সবসময় লাভের কথা ভাবে। সাহিত্য তার প্রোডাক্ট। সে বিভিন্ন চরিত্রের পাঠককে একযোগে ক্রেতা বানাতে চায়।”
‘লিট্ল ম্যাগাজিনের সংকট ও সম্ভাবনা’ নিয়ে লিখতে গিয়ে সবুজপত্র, কবিতা, কৃত্তিবাসের জন্যে যে অনেকটা জায়গা নিতে চাই তার কারণ ধন্দটা আগে পরিষ্কার হয়ে গেলে বাকিটা সংক্ষেপেই বোঝানো যাবে। (Little Magazine)
লিট্ল ম্যাগাজিন আর বাণিজ্যিক পত্রিকা নিয়ে তাঁর ধারণার কথা জানতে চাইলে কবি ও ‘পরমা’ পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্র গুপ্ত যা বলেছিলেন তার তিনটি বাক্যই যথেষ্ট, ‘বাণিজ্যিক পত্রিকার কোনো চরিত্র নেই। আর লিট্ল ম্যাগাজিনের চরিত্র না থাকলে তার কিছুই থাকে না। চরিত্রটা লিট্ল ম্যাগের কাছে খুব জরুরি’। (Little Magazine)
এই ‘চরিত্র’ বলতে কী বুঝব আমরা? বাণিজ্যিক পত্রিকা সবসময় লাভের কথা ভাবে। সাহিত্য তার প্রোডাক্ট। সে বিভিন্ন চরিত্রের পাঠককে একযোগে ক্রেতা বানাতে চায়। এজন্যে পত্রিকার দু-মলাটের মধ্যে পুরে দেওয়া হয় গল্প, প্রবন্ধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক চলতি প্রসঙ্গের উপরে লেখা, সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের বাজার-গরম গসিপ, রাশিফল, কোথায় কী হচ্ছে, এক বা একাধিক ধারাবাহিক উপন্যাস, এবং দু-চার পাতার কবিতা। এক কথায় ভ্যারাইটি স্টোর্স। খদ্দের যাতে ফিরে না যায়। অন্যদিকে লিট্ল ম্যাগাজিন একটি বিশেষ সাহিত্য-আদর্শ ধারণ করে। সে সাহিত্যের ভ্যারাইটি স্টোর্সের কাণ্ড-কারখানায় বিরক্ত। তার লক্ষ্য বিশেষ একশ্রেণির পাঠক ও লেখক যাঁরা বানোয়াট লেখায় বিশ্বাসী নয়। সে চায় অনুভূতির সৎ প্রকাশ। (Little Magazine)
প্রচলিত সাহিত্যের ফরম্যাটে তাঁদের কথা ঠিক করে বলা যায় না। এজন্যেই পাশ্চাত্যে যেমন বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল, বাংলায়ও তা ঘটতে শুরু করে। ছোটো ছোটো লেখকগোষ্ঠী প্রচলিত সাহিত্য-ধারণা ও লেখার আঙ্গিক ভাঙতে শুরু করেন। জন্ম হয় হাংরি, শাস্ত্রবিরোধী, শ্রুতি, ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো, নিম সাহিত্য, প্রকল্পনাসাহিত্য, ধ্বংসকালীন সাহিত্য, থার্ড লিটারেচার, নিওলিট মুভমেন্ট, ছোটোগল্প: নতুন রীতি প্রভৃতি সাহিত্য আন্দোলনের। এইসব আন্দোলনের মুখপত্রের নাম ফুঃ, ক্ষুধার্ত, ক্ষুধার্ত সাহিত্য, ক্ষুধার্ত খবর, চোখ, অক্ষর, শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য, ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো, এই দশক, নতুন নিয়ম, অব্যয় সাম্প্রতিক প্রভৃতি । এসব আগের শতকের ছয়-সাত দশকের ঘটনা। এইসব আন্দোলনের কিছু শ্লোগান:
হাংরি:
1. The merciless exposure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before it.
3. To catch a glimpse of the exploded self at a particular moment.
4. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
5. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation… প্রভৃতি।
“পাঠক সচকিত হয়ে ওঠেন, এ আবার কী! কেউ কেউ সেসব পত্রিকা উলটেপালটে দেখেন। ধীরে ধীরে এইসব অন্তর্ঘাতমূলক সাহিত্যের ছোটো ছোটো পাঠকবৃত্ত তৈরি হয়। কিছু পাঠকের কাছে বিবর্তিত হতে থাকে সাহিত্যের ধারণা।”
শ্রুতি:
১. কোনোরকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।
২. চিৎকার বা বিবৃতি এর কোনোটাই কবিতা নয়…।
৩. ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য দরকার ব্যক্তিগত রচনারীতি। আর রচনাপদ্ধতি এবং রচনার বিষয় অবিচ্ছেদ্য…।
৪. ভেঙে ফেলতে হবে সমস্ত প্রথার শাসন, ছিন্ন করতে হবে সংস্কারের সমস্ত বন্ধন…।
৫. ইতিপূর্বের সমস্ত শিল্পতাত্ত্বিক মতবাদই আমাদের কাছে মূল্যহীন।
৬. নতুন ধরনের মুদ্রণ বিন্যাসের সাহচর্যে কবিতায় দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুষঙ্গ সৃষ্টি। এছাড়া, ছেদচিহ্নের বিলোপ। ব্যাকরণের বিরোধিতা। প্রচলিত ছন্দকে বর্জন… প্রভৃতি। (Little Magazine)
শাস্ত্রবিরোধী:
১. গল্পে আমরা আমাদের কথাই বলব।
২. আমরা এখন বাস্তবতায় ক্লান্ত।
৩. অতীতের মহৎ সৃষ্টি অতীতের কাছে মহৎ আমাদের কাছে নয়।
৪. গল্পে এখন যারা কাহিনি খুঁজবে তাদের গুলি করা হবে।
৫. শিল্পের রাজ্য থেকে সমস্ত তত্ত্ব ও দর্শনের আমূল উৎখাত।
৬. শিল্প ও সাহিত্যে শাস্ত্রসম্মত পথকে বর্জন করতে হবে। শিল্পের ইতিহাস আঙ্গিকের বিবর্তনের ইতিহাস…প্রভৃতি (Little Magazine)
নিম:
১. ব্যারেলের ওপর থেকে প্রজাপতিটি উড়িয়ে দিন, লেখক হওয়ার বাসনা জাগামাত্র আত্মহত্যা করুন, অবিকৃত অভিজ্ঞতাই সাহিত্য।
২. জীবনের কোনো ব্যাখ্যা নেই, কার্যকারণের ভবিষ্যৎ নেই।
৩. শিল্পহীনতা থেকে বন্ধনহীনতার দিকে।
৪. বোধের মূলে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করুন।
৫. ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ চাই, সূর্যের দিকে সরাসরি তাকান… প্রভৃতি।
“আমরা প্রশ্ন করতেই পারি, যৌবন বলতে? দেহের যৌবন? মনের নয়? আসলে এই ‘ঋষিবাক্য’ তাঁকে বানাতে হয়েছিল যাতে নিজের লেখা লিখতে লিখতে তিনি বিখ্যাত, আরও বিখ্যাত, আরও আরও বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেন।”
পাঠক সচকিত হয়ে ওঠেন, এ আবার কী! কেউ কেউ সেসব পত্রিকা উলটেপালটে দেখেন। ধীরে ধীরে এইসব অন্তর্ঘাতমূলক সাহিত্যের ছোটো ছোটো পাঠকবৃত্ত তৈরি হয়। কিছু পাঠকের কাছে বিবর্তিত হতে থাকে সাহিত্যের ধারণা। (Little Magazine)
এর পাশাপাশি কোনো সাহিত্য আন্দোলনে অংশ না নিয়েও প্রকাশিত হতে থাকে লেখক-কবিদের নিজস্ব ধ্যানধারণার পরিবাহী কাগজ গল্পকবিতা, একক, কৌরব, ভাইরাস, প্রতিবিম্ব, অর্কিড, অন্ধযুগ, অজ্ঞাতবাস, কলকাতা (পরে ‘কলকাতা ২০০০’), কৃষ্ণপক্ষ, অভিমান, মহাদিগন্ত, কবিতাদর্পণ, পাগলা ঘোড়া, ক্রুসেড, আজকাল (পরে ‘আজকাল টাইটোনিডি’), ক্ষ্মা, বোবা, শহর, পুনর্বসুর মতো কাগজ (পুনর্বসুর সঙ্গে ‘শতজলঝর্নার ধ্বনি’ নামে অল্পসময়ের এক আন্দোলনের যোগ আছে অবশ্য)। এইসব কাগজের লেখক-কবি নিজেদের ও সমমনস্ক লেখক-কবিদের লেখালেখির মুক্তাঞ্চল হিসেবে এইসব কাগজকে হাতিয়ার করেছিলেন। (Little Magazine)
‘সবুজপত্র’ এবং এইসব আন্দোলন ও পত্র-পত্রিকার মাঝে যে প্রায় ৫০ বছর, সে সময়টায় প্রকাশিত হয়েছে কল্লোল (১৯২৩), কালিকলম (১৯২৬), প্রগতি (১৯২৭), পরিচয় (১৯৩১), পূর্বাশা (১৯৩২), কবিতা (১৯৩৫), নিরুক্ত (১৯৪০), শতভিষা (১৯৫১), কৃত্তিবাস (১৯৫৩) প্রভৃতি লিট্ল ম্যাগাজিন। (Little Magazine)
বাণিজ্যিক পত্র-পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের নীচে ফাঁকা জায়গা থাকলে তা পূরণ করা হত কবিতা দিয়ে। তা দেখে আহত বুদ্ধদেব বসু বের করেছিলেন শুধু কবিতার পত্রিকা ‘কবিতা’। তাঁর সামনে আদর্শ হিসেবে ছিল আমেরিকার ‘Poetry’ পত্রিকা। ‘কবিতা’-কে ২৫ বছরের উপর চালিয়ে এসেছিলেন। বেরিয়েছিল ১০৪টি সংখ্যা। সমসাময়িক ও তরুণ কবিদের কবিতার পাশাপাশি বিশ্বসাহিত্যের কবিতার সঙ্গে তিনি পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পেরেছিলেন অনুবাদের মাধ্যমে। পরে বন্ধ করে দেন, তার একটি কারণ হিসেবে শোনা যায়, পঞ্চাশের কবিদের কবিতা তিনি ঠিক ধরতে পারছিলেন না। জীবনানন্দের লেখা পরবর্তী পর্যায়ের কবিতাও তাঁর পছন্দ হচ্ছিল না। বরিশাল থেকে ২.৭.১৯৪৬ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে জীবনানন্দ লিখছেন:
‘‘আমার কবিতার জন্য বেশ বড়ো স্থান দিয়েছিলেন তিনি ‘প্রগতি’-তে এবং পরে ‘কবিতা’-য়, প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে ‘বনলতা সেন’-এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।’’ (Little Magazine)
আরও পড়ুন: ভ্রমি: স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড- ভাস্কর দাস
কেমন ছিল ‘কবিতা’ লিট্ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকের মনের গঠন? ৩০ বছর বয়সে, যখন কবিতা পত্রিকার বয়স তিন বছর, তখন ‘লেখার ইস্কুল’ (১৯৩৮) গদ্যে লিখছেন, ‘… আদর্শ সুখী জীবন আজকের দিনে যিনি ভোগ করেন, তিনি জনপ্রিয় ইংরেজ লেখক। সত্যি একজন আধুনিক কৃতী ইংরেজ লেখকের চাইতে সুখী লোক আমি তো ভাবতে পারি না।’ এরপর লিখছেন, ‘পুরস্কারে শুধু অর্থ নয়, যশও আছে; সে যশও উঁচুদরের…। যশ অবিমিশ্র মঙ্গল নয়, তবু মানুষমাত্রেরই কাম্য।’ এ লেখাতেই একটু পরে বলছেন, ‘যে-কোনো লেখকের বিষয়ে বিবেচনা করতে হলে তাঁর উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পরিমাণের কথাও বলতে হয়; কেননা দৈবক্রমে দুটি-একটি সদ্গ্রন্থ লিখে ফেলা যায়, কিন্তু একজন লেখকের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচুর্যও যখন দেখা যায় তখনই তিনি বড়ো লেখক হিশেবে গ্রাহ্য। …রচনা পরিমাণে বেশি না হলে সমসাময়িক সাহিত্যে ও সমাজে তার প্রভাব ব্যাপক কিংবা গভীর হতে পারে না। (Little Magazine)
‘কবিতা’ বন্ধ হওয়ার সাফাই হিসেবে তিনি ‘অন্যমনে’ পত্রিকায় দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম ‘কবিতা’ বন্ধ করে দেব। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাসের বন্ধন কাটাতে পারছিলাম না’। পরের বাক্য, ‘তারপর কয়েক বছর আগে অনেকটা স্বল্প ব্যবধানে আমাকে দু’বার বিদেশ যেতে হল এবং সেই সময়েই ‘কবিতা’ এত অনিয়মিত হয়ে পড়ল যে, আমি ফিরে আসার পর শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারলাম না।’ এ পর্যন্ত বলে বুঝলেন যে যুক্তিটা ঠিক জোরদার হল না, তাই পরক্ষণেই বলতে হল, ‘পারলাম না বললে ঠিক হয় না, ইচ্ছে করলেই পারতাম।’ এবং এরপর ঝুলি থেকে বেড়ালটিকে বের করলেন, ‘আসলে ইচ্ছেটাই মন থেকে চলে গিয়েছিল। তার কারণ কিছুদিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল যে বছরে চারটি সংখ্যা ভরাবার মতোও চলনসই রকমের ভালো কবিতা ও সমালোচনা পাওয়া যাচ্ছে না।’ এটা ভ্যালিড কারণ হতে পারত, যদি না পরক্ষণেই বুদ্ধদেব বলতেন, ‘কিন্তু একেবারে আসল কারণ বোধ হয় এই যে, আমি নিজেই পত্রিকা পরিচালনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের জন্য, নিজের লেখার জন্য আরও বেশি সময় চাচ্ছিলাম। পত্রিকা সম্পাদনা যৌবনের কাজ। যৌবন পেরিয়ে এসে তা না করাই উচিত’। শেষের বাক্য দু-টি আজ প্রবাদপ্রতিম হয়ে উঠেছে। (Little Magazine)
আমরা প্রশ্ন করতেই পারি, যৌবন বলতে? দেহের যৌবন? মনের নয়? আসলে এই ‘ঋষিবাক্য’ তাঁকে বানাতে হয়েছিল যাতে নিজের লেখা লিখতে লিখতে তিনি বিখ্যাত, আরও বিখ্যাত, আরও আরও বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেন। তিনি স্বভাবতই জীবনানন্দের কবিতা আর সহ্য করতে পারবেন না ও তাঁর পত্রিকার সম্পাদকীয়তে (আশ্বিন, ১৩৫৩) লিখবেন, ‘…জীবনানন্দ দাশ কী লিখছেন আজকাল? … দুর্বোধ্য ব’লে আপত্তি নয়; নিঃসুর ব’লে আপত্তি, নিঃস্বাদ ব’লে। হয়তো ওরই মধ্যে তাঁর পরিণতির সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন, কিন্তু প্রচ্ছন্নই। তা যে পরিস্ফুট হ’তে পারছে না তার কারণই এই যে হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। মনের অচেতনে তাঁর এই কথাই কাজ করছে যে আমি যদি এখনো মাকড়শার জাল, ঘাস আর শিশিরের কথা লিখি, তবে আর কি তার পাঠক জুটবে? তবু কবিতার মাঝে-মাঝে রোম- বার্লিন দেখলে লোকে এ-কথা অন্তত ভাববে যে লোকটা নিতান্তই ম’রে যায়নি। হয়তো তাঁর মন এখনো পড়ে আছে ঘাসে, শিশিরে, জলে, ছায়ায়, আকাশে— প্রকৃতির কবি তিনি, তাছাড়া কিছুই নন— হয়তো কেন, নিশ্চয়ই; কিন্তু সেই তাঁর স্বদেশ থেকে, তাঁর রাজত্ব থেকে মনকে সরিয়ে এনে তিনি নিজেকে বন্দী করেছেন চলিত আন্দোলনের আন্দামানে…’। (Little Magazine)
বুদ্ধদেবের আত্মবিশ্বাস যেন ফেটে বেরোচ্ছে এই মন্তব্য থেকে। আমাদের বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না যে মন্তব্যকারীর কবিতার আগাপাশতলা জানা-বোঝা হয়ে গেছে। যাঁর কবিতা সম্পর্কে এরকম ধারণা জন্মে গেছে, অদ্ভুত লাগে যখন দেখি, এর ৮ বছর পরে সেই কবির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ‘কবিতা’-র ‘জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা’ও (পৌষ ১৩৬১) বের হচ্ছে।
“মৃত্যুর পর তাঁর চিঠিপত্র, বইয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়ে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। আষাঢ়, ১৩৪৯ সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় ছাপা দুটি কবিতা ও ১৫ পৃষ্ঠা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার উপরে দুটি আলোচনা। আলোচক স্বয়ং সম্পাদক।”
সমসময়ের বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত একজন উচ্চশিক্ষিত মানুষ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য-বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা- অধ্যাপক, যিনি পৃথিবীর নানান দেশে সাহিত্য নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন; যিনি Poetry পত্রিকাকে আদর্শ করে ‘কবিতা’ পত্রিকার সম্পাদনা করছেন ও সেই পত্রিকায় বিদেশের বিভিন্ন গোত্রের কবিদের কবিতার অনুবাদ প্রকাশ করছেন, যিনি নিজে কবিতা লেখেন, যিনি ব্যোদল্যেরের কবিতার মুগ্ধ পাঠক ও অনুবাদক; তিনি কি না জীবনানন্দকে চিহ্নিত করছেন নিছক প্রকৃতির কবি বলে! সেখান থেকে সরে এলেই তিনি আর তাঁকে বুঝতে পারছেন না, ব্যঙ্গ করছেন, নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করছেন! জীবনানন্দের কবিতা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব এমনও লিখেছিলেন,‘‘আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম ‘আধ্যাত্মিক’, সবচেয়ে বেশি ‘শারীরিক’; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়গত।’’। আবার, অমিয় চক্রবর্তীর কবিকৃতি নিয়ে বুদ্ধদেবের বহু পৃষ্ঠার আলোচনা শুরু হচ্ছে এইভাবে,’ সমকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আধ্যাত্মিক কবি অমিয় চক্রবর্তী’। আধ্যাত্মিক কেন? না, তাঁর কবিতায় ‘একটি আশ্চর্য বৈদেহিকতা ব্যাপ্ত হ’য়ে আছে, রক্তমাংসের আক্রমণ সেখানে সবচেয়ে কম: ইন্দ্রিয়চেতনার কবি জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর বৈপরীত্য যেমন মেরুপ্রমাণ,…’ ইত্যাদি (‘কবিতা’, পৌষ ১৩৬২)। (Little Magazine)
জীবনানন্দের কবিতা পছন্দ হচ্ছে না অথচ কবিতার নামে ধারাবাহিকভাবে ছেপে চলেছেন কত যে পদ্য ও ছড়া! বিদেশ থেকে অমিয় চক্রবর্তী কবিতার নামে যা-ইচ্ছা-তাই পাঠাচ্ছেন, চিঠি লিখে পাঠাচ্ছেন, আর বুদ্ধদেব এক একটি সংখ্যায় ঢালাওভাবে সেসব ছেপে চলেছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের পদ্যনাটিকা (নাম ‘রাতের অতিথি’) ছাপছেন পত্রিকার একটি সংখ্যার একেবারে শুরু থেকে ১০ পৃষ্ঠা জুড়ে (যখন পত্রিকার বয়স ১৮ বছর, আগে ৭৬টা সংখ্যা বেরিয়ে গেছে এবং সম্পাদকের বয়স ৪৫)। সে পদ্যের নমুনা ‘‘(স্থান জঙ্গীপুরের ডাকবাংলা। কাল রাত দশটা। পাত্র মণ্টু গুপ্ত)। মণ্টু/ আজি কী মুরতি হেরিনু তোমার—’’/ মশার জ্বালায় হই জেরবার/ হাত চুলকায় পা চুলকায়/ চুপ ক’রে বসা হলো দেখি দায়।/ তাই বলে কত পায়চারি করি/ বাইরে আঁধার পা বাড়াতে ডরি।…’’ সংখ্যাটির তৃতীয় প্রচ্ছদ থেকে আমরা জানতে পারি যে এটি একটি কাব্যনাটিকা, যার বিশেষ সংস্করণ ‘কবিতাভবন’ থেকে অলরেডি প্রকাশিত। ‘বিশেষ সংস্করণ’, কারণ ‘প্রতিগ্রন্থ লেখক কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং সংখ্যাযুক্ত’। ‘এক পয়সায় একটি’ সিরিজের প্রথম পুস্তিকাটি স্বয়ং বুদ্ধদেবের। ‘কবিতাভবন’-প্রকাশিত। তার বিজ্ঞাপন, ‘এক পয়সায় একটি। বিখ্যাত গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তিকা। ষোলো পৃষ্ঠায় ষোলোটি লঘু রসের কবিতা। চার আনা।’ (‘কবিতা’, আষাঢ় ১৩৫৩)। (‘বিখ্যাত’ এবং ‘লঘু রসের কবিতা’ কথা দুটির পেছনের মন পড়া যাচ্ছে?)। আর আছেন রবীন্দ্রনাথ ‘সবুজপত্র’-র মতো অধিপতি হয়ে। (Little Magazine)
মৃত্যুর পর তাঁর চিঠিপত্র, বইয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়ে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। আষাঢ়, ১৩৪৯ সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় ছাপা দুটি কবিতা ও ১৫ পৃষ্ঠা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের লেখার উপরে দুটি আলোচনা। আলোচক স্বয়ং সম্পাদক। কার্তিক, ১৩৪৯ সংখ্যার পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১২, যার মধ্যে ৪৮ পৃষ্ঠা গেছে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ক্রোড়পত্রে, ১৮ পৃষ্ঠা গেছে রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’-র আলোচনায়। (এর কয়েকমাস আগেই ‘কবিতা’-র ‘রবীন্দ্রসংখ্যা’ বেরিয়েছে)।আলোচক (স্বয়ং সম্পাদক) আলোচনা শেষ করছেন এইভাবে, ‘আমাদের মানসলোকের বাণী তিনি আহরণ ক’রে যখন নিয়ে এলেন, নতশিরে গ্রহণ করলুম সেই অমূল্য উপঢৌকন, আর মনে-মনে বললুম, তুমি আমাদের প্রণম্য’। (Little Magazine)
এটি একটি কবিতার কাগজে উপন্যাসের আলোচনা, আয়তনে ১৮ পৃষ্ঠা! পরের সংখ্যা শুরু হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি (৬ পৃষ্ঠা) দিয়ে, শেষ হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ‘দুই বোন’ (উপন্যাস ) আর ‘মালঞ্চ’ (বড়ো গল্প)-র মাত্র ১৩ পৃষ্ঠার আলোচনা দিয়ে। আলোচনা করেছেন স্বয়ং সম্পাদক। এর ১৫ বছর পরে (পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬৪) দেখতে পাবো ১৬ পৃষ্ঠা জুড়ে ‘শেষের কবিতা’ নিয়ে আলোচনা করছেন নরেশ গুহ, ‘আধুনিক কবি অমিত রায়’ শিরোনামে। তেমনই কাগজ ধারাবাহিকভাবে পেয়ে চলেছে বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপন। ‘কবিতাভবন’ থেকে বেরোচ্ছে রাজশেখর বসু ও পরশুরামের পুস্তিকা ও কাগজ ধারাবাহিকভাবে পেয়ে চলেছে বেঙ্গল কেমিক্যালের বিজ্ঞাপন। সেজন্যেই কি তাঁর মৃত্যুর পর ৮ পৃষ্ঠার স্মরণলেখ লিখতে হয় সম্পাদককে, কবিতার সঙ্গে রাজশেখরের কোনো সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও।
‘এক পয়সায় একটি’ কবিতা-পুস্তিকার বিজ্ঞাপনের ভাষা, ‘এই গ্রন্থমালায় বিভিন্ন আধুনিক কবির কয়েকটি বাছাই-করা ভালো-ভালো কবিতা প্রকাশ করা হচ্ছে।’
এম.সি.সরকার থেকে বেরোচ্ছে প্রতিভা ও বুদ্ধদেবের উপন্যাস, মেঘদূতের অনুবাদ এবং ‘কবিতা’ পাচ্ছে প্রকাশকের বিজ্ঞাপন। ‘কবিতা’-র ৮০ পৃষ্ঠার একটি সংখ্যার (আষাঢ় ১৩৬৪) ১৫ পৃষ্ঠা জুড়ে থাকছে সম্পাদকের অনুবাদের উপরে আলোচনা। বুদ্ধদেবের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’, ‘কঙ্কাবতী’ বেরোচ্ছে ‘নাভানা’ থেকে আর ‘কবিতা’-য় পর পর ছাপা হয়ে চলেছে ‘নাভানা’-র বিজ্ঞাপন। ঠিক এর আগের সংখ্যাটি (চৈত্র ১৩৬৩) দেখে হতভম্ব হয়ে যেতে হয়। ৮৪ পৃষ্ঠার এ সংখ্যাটির ৬৫ পৃষ্ঠা জুড়ে স্বয়ং সম্পাদকের প্রবন্ধ ‘‘সংস্কৃত কবিতা ও ‘মেঘদূত’’! সংখ্যাটির শেষে ‘লেখকদের বিষয়ে’ অংশে জানানো হচ্ছে ‘‘বুদ্ধদেব বসুর ‘মেঘদূত’-অনুবাদ এম. সি. সরকার গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছেন; এই সংখ্যার প্রবন্ধ সেই গ্রন্থেরই ভূমিকা’’। সংখ্যাটির অবশিষ্ট ১৯ পৃষ্ঠার মধ্যে ৬ পৃষ্ঠা জুড়ে আবার বুদ্ধদেবের করা অনুবাদ, ৭ পৃষ্ঠায় ৪ জন কবির কবিতা এবং ৬ পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপন। (৭টি পৃষ্ঠা বাদ দিলেই চমৎকার একটি বুদ্ধদেব-সংখ্যা)। সম্পাদকের নিজের করা একটি অনুবাদের বইকে প্রমোট করতে নিজের কাগজকে এইভাবে ব্যবহার করতে দেখি আমরা! সমগ্র অনুবাদকর্মটিও নিজের কাগজে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। (Little Magazine)
‘এক পয়সায় একটি’ কবিতা-পুস্তিকার বিজ্ঞাপনের ভাষা, ‘এই গ্রন্থমালায় বিভিন্ন আধুনিক কবির কয়েকটি বাছাই-করা ভালো-ভালো কবিতা প্রকাশ করা হচ্ছে।’
এসবই সংকট, একটি লিট্ল ম্যাগাজিনের হাড়ে-মজ্জায় মিশে থাকা সংকট। এ সেই ভূত যে সরষের মধ্যেই ঘাপটি মেরে থাকে।
সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে পাতার পর পাতা কবিতা ছাপা হয়েছে বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, নরেশ গুহ ও স্বয়ং সম্পাদকের। ‘কবিতা’র নিয়মিত বিজ্ঞাপনের তালিকায় দেখতে পাই নানান ইন্সিওরেন্স কোম্পানি, এমনকী শেয়ার বাজারও (বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স সিন্ডিকেট লিঃ) রয়েছে (এর পেছনে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অবদান ছিল কি না জানি না)। একটি কবিতার পত্রিকা বিজ্ঞাপন পাচ্ছে, যা পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে, তাহলে এমন লিখছি কেন? লিখছি, লেখা ছাপা ও বিজ্ঞাপনের যোগসাজশের সম্ভাবনার আশংকা থেকে। বাজারে বহুকাল ধরে এই মিথ চালু আছে যে ‘কবিতা’ পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর অবদান অবিস্মরণীয়। ‘কবিতা’র সংখ্যাগুলি যদি কেউ খেয়াল করে দেখেন তো দেখতে পাবেন কী পরিকল্পিত কৌশলে নিজের কাগজ ‘কবিতা’ এবং নিজের প্রকাশনা ‘কবিতাভবন’-কে বুদ্ধদেব নিজের ও স্ত্রী প্রতিভা বসুর সাহিত্যিক কেরিয়ার তৈরির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করে গেছেন লাগাতারভাবে। ‘কবিতাভবন’-এর পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হতো তৃতীয় ও চতুর্থ মলাটে। (Little Magazine)
“এই অন্নদাশঙ্কর রায়ই লীলাময় রায় ছদ্মনামে ‘কবিতা’-র তৃতীয় বছরে ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ শিরোনামে দু-পৃষ্ঠার গদ্যে লিখেছেন, ‘…আমার স্থির ধারণা গদ্যে কবিতা হতে পারে না। যা হয় তা কবিতা নয়, কবিত্ব।”
সে মলাটলিখনে অনেকসময় শুধুই বুদ্ধদেব, ‘বুদ্ধদেব বসুর বই’ শিরোনামে। দ্বিতীয় মলাটে অনেক সময় দেখতে পাই বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বসুর কোন কোন উপন্যাস ও গল্পের বই বেরিয়েছে বা বেরোচ্ছে অন্যান্য প্রকাশনা থেকে তার বিজ্ঞাপন। ‘কবিতা’-য় সম্পাদকের বইয়ের দীর্ঘ আলোচনা করছেন তাঁর কাগজেরই কবিরা (তিনি তো আর লিখতে বলেননি, ছেপে দিয়েছেন মাত্র), যেমন, চৈত্র ১৩৬৫ সংখ্যায় রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর ৯ পৃষ্ঠাজোড়া আলোচনা, ‘বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: ‘যে আঁধার আলোর অধিক’,’ এর আগে পৌষ ১৩৫৯ সংখ্যায় রমেন্দ্রকুমারেরই ‘বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: ‘দ্রৌপদীর শাড়ি’, এমনকী দেখতে পাই সম্পাদকের একটি দীর্ঘ কবিতা নিয়ে দীর্ঘতর আলোচনা লিখছেন নরেশ গুহ। এর আগে পৌষ, ১৩৪৪ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে সম্পাদকের কবিতার বই ‘কঙ্কাবতী’-র ৭ পৃষ্ঠা জুড়ে দীর্ঘ আলোচনা, করেছেন জীবনানন্দ দাশ (এর ১১ বছর পরে ‘কবিতা’-র শেষ মলাটে যে বই বিজ্ঞাপিত হবে ‘বিরল বই’ শিরোনামে, তলিয়ে পড়লে বোঝা যাবে প্রথম সংস্করণের আর ২ কপি অবশিষ্ট আছে, তাই বিরল বই!)। বিভিন্ন সংখ্যায় এসবের পাশাপাশি অন্য কবিদের (একটি সংখ্যায় একসঙ্গে কয়েকজনের) বইয়ের আলোচনাও ছাপা হয়েছে, যার মধ্যে দুর্বল কবিতার বইও আছে, যেমন: অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘নতুন রাধা’, ছয় পৃষ্ঠা জুড়ে, করেছেন সমর সেন। (Little Magazine)
এই অন্নদাশঙ্কর রায়ই লীলাময় রায় ছদ্মনামে ‘কবিতা’-র তৃতীয় বছরে ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ শিরোনামে দু-পৃষ্ঠার গদ্যে লিখেছেন, ‘…আমার স্থির ধারণা গদ্যে কবিতা হতে পারে না। যা হয় তা কবিতা নয়, কবিত্ব। যাঁরা গদ্যকবিতা সুরু করেছেন তাঁদের পদ্য কবিতায় ফিরে আসতেই হবে, কেননা পদ্যকবিতাই কবিতা’…। এই বক্তব্য ‘কবিতা’ পত্রিকার সঙ্গে মেলে না, তবু ছাপা হল! আর একথা বলতে লেখককে ছদ্মনামের আশ্রয় নিতে হল কেন? (Little Magazine)
এই কাগজে সংক্ষেপে সেই সংখ্যার লেখক পরিচিতি থাকত অনেকসময়। যেমন, আষাঢ়, ১৩৬৩ সংখ্যায় : ‘‘জ্যোতির্ময় দত্ত-র জন্ম ১৯৩৬-এ; এঁর কবিতা গত এক বছর ধ’রে ‘কবিতা’য় প্রকাশিত হচ্ছে। বিকাশ দাশ নয়া দিল্লির বাসিন্দা; কয়েক বছর ধ’রে ‘কবিতা’য় লিখছেন।’’ এরপরেই— ‘বুদ্ধদেব বসু-র নতুন উপন্যাস ‘শেষ পাণ্ডুলিপি’ এম.সি.সরকার থেকে শীঘ্র প্রকাশিত হবে’। এইরকম পরিচিতি দেওয়া হয়েছে বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কেও, তবে কবিতার বই নিয়ে। এর কয়েকবছর আগের একটি সংখ্যা (চৈত্র ১৩৫৪) খুলে দেখতে পাচ্ছি ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী সম্পাদকীয়, যার এক জায়গায় লেখা হয়েছে, ‘সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের এই প্রকৃতিগত সংযোগ আছে ব’লে, বর্তমান জীবলোকে, সাহিত্যবহির্ভূত জগতে, আধুনিক সাহিত্যিক তার স্বপ্নের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলো একমাত্র মহাত্মা গান্ধীতে। …এই দীর্ঘ, তিক্ত, সুদীর্ঘ দিনের পর দিনে সাহিত্যিকের একমাত্র সান্ত্বনা ছিল সাহিত্যে, কবিতায়;— আর গান্ধীতে।…’ এরপর পত্রিকা শুরুর একটি বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল:
আরও পড়ুন: মথ: প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনির গল্প- অমিতাভ মৈত্র
প্রকাশিত হইল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- মহাত্মা গান্ধী।
মহাত্মাজী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের- কবিতা, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংগ্রহ মূল্য এক টাকা।
ইত্যাদি ইত্যাদি… শেষে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি বইয়ের নাম ও তারপর ‘বিশ্বভারতী’। অর্থাৎ বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপন। তখন বোঝা গেল। ব্যাক কভারে বুদ্ধদেব বসুর নামসই সবুজ রঙে, তার নীচে অতিকায় টাইপে ও লাল রঙে ‘দ্রৌপদীর শাড়ি’, তার নীচে ‘নতুন কবিতার বই’, তার নীচে ‘আড়াই টাকা’। (এরকম অতিকায় টাইপে আগেও আষাঢ় ১৩৫৯ সংখ্যায় সম্পাদকের ‘দময়ন্তী’ কবিতা বইয়ের বিজ্ঞাপনে, আশ্বিন ১৩৬৩ সংখ্যায় উপন্যাস ‘শেষ পাণ্ডুলিপি’-র বিজ্ঞাপনে দেখা গেছে)। তার নীচে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের বইয়ের নাম ও দাম, তার নীচে ধাম ‘কবিতাভবন’। (Little Magazine)
এসবই সংকট। একটি লিট্ল ম্যাগাজিনের কালান্তক ব্যাধির উপসর্গ এগুলি।
‘কবিতা’-র বয়স যখন ২৫ বছর (১৩৬৭), আর তার সম্পাদকের ৫২, তখন চৈত্র সংখ্যায় দেখছি ছাপা হয়েছে সম্পাদকের কয়েকটি চিঠি, যেগুলি তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্তকে লিখেছেন। লেখার ভঙ্গি অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো। এক চিঠিতে লিখছেন, ‘‘জনরব শুনছি আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমি আমার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ‘কবিতা’য় ছাপাবার মতলব আঁটছো— খবরদার, কখনো না, আমি যতদিন সম্পাদক আছি ‘কবিতা’য় আমার বিষয়ে কোনো প্রবন্ধ বেরোবে না, বড়ো জোর বুক-রিভিয়ু পর্যন্ত মার্জনীয়।’ (কে কাকে মার্জনা করবে!)। অথচ চিঠিগুলি ছাপা হল, এই কথাগুলি থাকল সেখানে, এবং চিঠিগুলির শেষে দেখতে পাচ্ছি লেখা, ‘‘এই পত্রগুচ্ছের কয়েকটি ‘অমৃত’ নামক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হয়েছে।’’ নিজের কাগজে নিজের চিঠির পুনর্মুদ্রণ পর্যন্ত বাদ যাচ্ছে না, নিজের একটা কবিতা নিয়ে পাতার পর পাতা আলোচনা করা (পড়ুন, করানো) হচ্ছে, এবং দু-দুটো কাগজে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে জানানো হচ্ছে, ‘খবরদার…’। মজা লাগছে না? (Little Magazine)
এসবই লিট্ল ম্যাগাজিনের সংকট। বিখ্যাত হবার এই লোভ— এই শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। শেষপর্যন্ত ঢাকা তো থাকে না। পত্রিকার জীর্ণ সংখ্যাগুলি তাদের পৃষ্ঠে সেসব সাক্ষ্য বহন করে চলে। যেমন, চৈত্র ১৩৬২ সংখ্যায় Voice of Bengal থেকে পুনরায় নিজের কাগজে প্রকাশ করছেন গুরুগম্ভীর গদ্য ‘ভাষা ও রাষ্ট্র’, যা শুরু হচ্ছে এইভাবে, ‘‘আমি রাজনৈতিক নই, কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত নই, আরাম-কেদারায় ব’সেও রাজনীতির চর্চা আমি করি না। এবং আমার মধ্যে দেশপ্রেম নেই। এই পৃথিবী নামক গ্রহের কোনো-একটি অংশে দৈবাৎ নিক্ষিপ্ত হয়েছি ব’লেই তার মধ্যে ষড়ৈশ্বর্য দেখতে পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। ‘সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি’— এই হৃদয়াবেগে আমার মন কখনো সাড়া দেয় না। আমি লেখক; বাঙালি লেখক না-হ’লেও বাংলা ভাষার লেখক।…’’
এ”রপর তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দবাজারে ঢুকে পড়েন। একটা সময়ে ‘কৃত্তিবাস’ বড়ো আকারে বের হতে শুরু করে, তার চরিত্রবদলও ঘটতে দেখি আমরা। তখন সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের ধারাবাহিক উপন্যাস ছাড়াও গল্প এমনকী উত্তমকুমারের কল্পিত সাক্ষাৎকার প্রকাশ হতেও দেখতে পাই।”
মণীন্দ্র গুপ্ত কবিতার কাগজ ‘পরমা’ বের করার সময়ের কথা বলেছেন, “বুদ্ধদেব বসুর ‘কবিতা’ পত্রিকার কথা আমার মাথায় ছিল— সেই পত্রিকার কবিতাবলিতে সম্পাদকের কাব্যাদর্শ, রুচি এবং প্রবণতার ছাপ বড়ো স্পষ্ট হয়ে পড়ত। এ একটা ছাঁচ। মনে হয়, সম্পাদক পছন্দ করবেন শুধু এমন লেখাই কবিরা পাঠাতেন সেখানে। এ এক সম্মিলিত আত্মপ্রবঞ্চনাও”। (সাক্ষাৎকার থেকে, ‘নির্জন’ বইমেলা ১৯৯৫)। ‘কবিতা’-র পাতায় পাতায় তার সাক্ষ্য আছে। সেখানে সুনীল-শক্তি অন্ত্যমিল মিলিয়ে মিলিয়ে সন্তর্পণে কবিতা লিখছেন, আমরা দেখতে পাই। (Little Magazine)
‘কবিতা’-র (১৯৩৫) ১৮ বছরের মাথায় ‘কৃত্তিবাস’ (১৯৫৩) বের হয়ে সাড়া ফেলে দেয়। দীপক মজুমদারের মানসপুত্র এই পত্রিকার তিনটি সংখ্যা বের হবার পরেই দীপক বেরিয়ে আসেন। তারপর থেকে মূলত (একটা পর্যায়ে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, বেলাল চৌধুরী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ও তত্ত্বাবধানে পত্রিকাটি চলতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ঠোঁটকাটা কৃত্তিবাসী শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ‘‘সুনীল আমেরিকা থেকে ফিরে এসেও ‘কৃত্তিবাস’-এর দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেনি। অর্থাভাব তার একটা কারণ। আর, ওর মনের মধ্যে তখন পেশাদার লেখক হওয়ার বাসনা। …সেই সময় বন্ধু সমীর রায়চৌধুরীকে একটি চিঠিতে সুনীল লেখে, ‘… আমি কৃত্তিবাস-এর ভার ছেড়ে দিচ্ছি। এই একটা সংখ্যা সম্পাদনা করেছেন শরৎ, আগামী সংখ্যা সমরেন্দ্র (সেনগুপ্ত) বা তারাপদ (রায়)-কে সম্পাদক হতে অনুরোধ করেছি। যে সংখ্যার যে সম্পাদক, সেই সংখ্যার সম্পূর্ণ ভার তার। আমার কোনো দায়িত্ব নেই” (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত সংকলন ‘কৃত্তিবাসের ঘরের কথা’)। (Little Magazine)
এরপর তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আনন্দবাজারে ঢুকে পড়েন। একটা সময়ে ‘কৃত্তিবাস’ বড়ো আকারে বের হতে শুরু করে, তার চরিত্রবদলও ঘটতে দেখি আমরা। তখন সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী ও অন্যান্য সাহিত্যিকদের ধারাবাহিক উপন্যাস ছাড়াও গল্প এমনকী উত্তমকুমারের কল্পিত সাক্ষাৎকার প্রকাশ হতেও দেখতে পাই। বাণিজ্যসফল হতে চাওয়া ‘কৃত্তিবাস’। এরপর আবার আগের আকারে ফিরে এলেও আমরা দেখি পত্রিকা হাতফের্তা হয়ে ঘুরছে এক প্রকাশক থেকে আরেক প্রকাশকের ঘরে। তাঁরাই প্রকাশ ও বিক্রি করছেন। (এখন সম্ভবত সেভাবে হচ্ছে না)। নবপর্যায়ে প্রকাশিত তৃতীয় সংখ্যায় (জানুয়ারি ২০০১) স্বয়ং সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ‘হতাশ’ হয়ে লিখছেন, ‘হয়তো লিট্ল ম্যাগাজিনের যুগ অবসিত হয়ে যাচ্ছে। লিট্ল ম্যাগাজিনে কবিতা প্রকাশের গৌরবের চেয়ে বহুল প্রচারের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই যুগোপযোগী’। (Little Magazine)
অথচ আমরা জানি ২০০১ সালে উলটোটাই সত্যি। এসময় লিট্ল ম্যাগাজিন অনেক বেশি জায়গা করে নিচ্ছে, তথাকথিত বিগ ম্যাগাজিনে লেখার গুরুত্ব কমে আসছে ক্রমে। (তাছাড়া সুনীল নিজেকে যেখানে বাণিজ্যিক কবি ও ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুলেছেন তিনি একথা কোন মুখে বলেন!) লিট্ল ম্যাগাজিনের যুগ শেষ হয়ে যাচ্ছে এটা সে-সময় কৃত্তিবাস-সম্পাদকের কেন মনে হয়েছিল? কৃত্তিবাস কি তাঁর গলগ্রহ হয়ে উঠেছিল? না কি ইচ্ছে করে বিভ্রম ছড়াচ্ছিলেন! কেননা ওই সম্পাদকীয়তেই একটু আগে বলেছেন, ‘এই পর্যায়ের কৃত্তিবাস সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিল না, তবু জোর করে ভাস্কর (দত্ত) আমার উপর দায়িত্ব চাপিয়েছিল। (Little Magazine)
ভাস্করের বাসনার মর্যাদা দেবার জন্যই আমাকে কৃত্তিবাস প্রকাশ ও পুরস্কার চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হলো। তিন বছর পর আবার আমার মনে খটকা লেগেছে। এই বার্ষিক সংকলন প্রকাশের সত্যিই কি বিশেষ কিছু মূল্য আছে? না কি নিয়মরক্ষা মাত্র।’ আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি যে সম্পাদক আসলে নিজের কাগজ আর নিজে করছেন না, তিনি উপরোধের ঢেঁকি গিলছেন! একটি লিট্ল পত্রিকার কাজ করার জন্যে মাইনে দিয়ে লোক রাখতে হচ্ছে। তাঁর আর সময় (না কি আগ্রহ?) নেই। ২০০৭ সালে প্রকাশিত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত ‘কৃত্তিবাসের ঘরের কথা’ সংকলনে সুনীল যে স্মৃতিচারণ করেছিলেন তার শেষ দু-টি বাক্য, ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকা বাংলা কবিতার কী উপকার করেছে, সে আলোচনা করা আমার পক্ষে সঙ্গত নয়। কিন্তু এই পত্রিকা যে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তাতে আর সন্দেহ কী!’
“নতুন অদীক্ষিত পাঠক এইসব পত্রিকাকেই আস্লি লক্ষ্মীবাবুকা সোনাচান্দি মনে করে ভক্তিভরে ক্রয় করেন। বইমেলায় এসব পত্রিকার স্টলের গতর দেখে পৌনে সরকারবাড়ি বলে মনে হয়।”
আমরা বুদ্ধদেব বসুর কণ্ঠই কি আর একবার শুনতে পাই না আর একজন কবি ও কবিতার কাগজের সম্পাদকের কাছ থেকে, যখন তিনি বলেন, ‘জীবনানন্দকে যদি আমরা গদ্য-লেখক হিসেবে দেখি, তাহলে দেখব যে ওঁর প্রচুর উপন্যাস-গল্প আছে, সতেরোটা উপন্যাস, ছেচল্লিশটা ছোটোগল্প আছে, এছাড়া ডায়েরি আছে প্রায় আটান্নটা খাতায়, প্রচুর লেখা এখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু এই গদ্যগুলো কোনোটাই সম্পূর্ণ বা খুব একটা উচ্চাঙ্গের লেখা নয়। জীবনানন্দের কবিতাগুলো বার বার পড়ে দেখেছি, প্রথম বয়সে যে মুগ্ধতা ছিল এখন আর তা নেই। সবমিলিয়ে আটাশটার মতন কবিতা যেগুলি খুবই ভালো এবং স্মরণযোগ্য, কিন্তু অন্য কবিতাগুলো বেশিরভাগই একঘেয়ে এবং সাধারণ মানের’ (‘কবিসম্মেলন, সেপ্টেম্বর ২০০৮, সাক্ষাৎকারের অংশ)। (Little Magazine)
তো, ‘সবুজপত্র’র পর আমরা দেখলাম ‘কবিতা’ ও ‘কৃত্তিবাস’ এই দু’টি ঐতিহাসিক পত্রিকার দুই ঐতিহাসিক সম্পাদকের মনের গঠন। দু’জনেই বাণিজ্যিক কাগজে প্রধানত গল্প- উপন্যাস লিখে লিখে বিখ্যাত, এবং তা-ই হতে চেয়েছিলেন। যে-সময় নিজেদের কাগজ থেকে তাঁদের মন উঠে গেল তখন কাগজ থেকে খ্যাতি যা পাওয়ার পাওয়া হয়ে গেছে, এবার বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাণিজ্যিক কাগজে ক্রমাগত উপন্যাস লিখে চলায় মন দিতে হবে। (Little Magazine)
বর্তমান সময়ের ঘটনা হল, লিট্ল ম্যাগাজিনের তরুণ সম্পাদকদের পাশাপাশি কিছু বোকাবয়স্ক সম্পাদক আছেন যাঁরা তাঁদের পত্রিকা বন্ধ করার কথা ভাবতেই পারেন না, কেননা পত্রিকা তাঁদের অস্তিত্বের অংশ হয়ে গেছে। (Little Magazine)
কয়েকটি সুমো ‘লিট্ল ম্যাগাজিন’-কে দেখতে পাই যাদের একেকটি সংখ্যা টেস্ট পেপারকেও লজ্জা দেবে। এইসব পত্রিকায় যত পাতা বিজ্ঞাপন ছাপা হয় শুধু সেই পরিমাণ পাতাতেই এক একটি লিট্ল ম্যাগাজিন বেরোতে পারে। মূলত অধ্যাপক-বিজড়িত এইসব পত্রিকায় একাধিক ক্রোড়পত্র দেখা যায়, একেকটি ক্রোড়পত্রের সম্পাদক একেকজন। কন্ট্রাক্টর যেভাবে সাব-কন্ট্রাক্ট দেয় আর কী। অনন্তকাল ধরে এইসব পত্রিকা নিয়মিত বেরিয়ে চলেছে, একেকটি সংখ্যার দাম চারশো থেকে সাতশোর টাকার মধ্যে ঘোরাফেরা করে। দোকানদারেরা এইসব পত্রিকাকেই খদ্দেরের মুখের সামনে সাজিয়ে রাখেন কেন না দাম বেশি তাই কমিশনের পরিমাণ বেশি। সাধারণ পাঠক বইপাড়ায় গিয়ে এইসব পত্রিকাকেই দোকান আলো করে থাকতে দেখতে পান বেশি। ‘দেশ’ পত্রিকায় এরাই পাতা জুড়ে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে চলেন। (Little Magazine)
নতুন অদীক্ষিত পাঠক এইসব পত্রিকাকেই আস্লি লক্ষ্মীবাবুকা সোনাচান্দি মনে করে ভক্তিভরে ক্রয় করেন। বইমেলায় এসব পত্রিকার স্টলের গতর দেখে পৌনে সরকারবাড়ি বলে মনে হয়। সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লিট্ল ম্যাগাজিন পড়ুয়া বাঙালির সিংহভাগ এদেরকেই fssai ছাপ মারা অর্গানিক লিট্ল ম্যাগাজিন মনে করেন। এরকম একটি পত্রিকা দেখে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, ‘‘একটি লিট্ল ম্যাগাজিনের ফোর্থ কভার জুড়ে বেরিয়েছে ‘ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সজাগ হোন’। নীচে পত্রিকার নাম লেখা। অর্থাৎ পত্রিকার তরফে। আচ্ছা, যদি একটা রেড়ির তেলের বিজ্ঞাপন পেত ওখানে, ওদের কি তাহলে ফ্যাসিবাদের কথা মনে পড়ত?’’ আসলেই তাই।
“মেলায় গিয়ে সাজিয়ে বসছেন বই। এইসব মেলায় থাকা-খাওয়া ফ্রি, যাতায়াত ছাড়া খরচ নেই। তাছাড়া জেলায় জেলায় লেখক-কবি হতে চাওয়া বধযোগ্যদের সঙ্গে এখানেই যোগাযোগ হয়ে যায়। যাকে বলে, মজার গরম গরম তেলেভাজা! তবে সবাই নয়।”
কবিতা দিয়ে পাদপূরণের হেনস্থা দেখে বুদ্ধদেব বসু ‘কবিতা’ বের করেছিলেন। তেমনই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে সেখানে ডাঁই করে ফেলে রাখা লিট্ল ম্যাগাজিন দেখে সন্দীপ দত্তের খারাপ লেগেছিল। সেজন্যেই শুরু করেছিলেন লিট্ল ম্যাগাজিনের (আগে ‘সাময়িকপত্র পাঠাগার’) লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্র। বইমেলায় মাথার টুপিতে কাগজ সেঁটে ঘুরতেন, ‘লিট্ল ম্যাগাজিন কিনুন, লিট্ল ম্যাগাজিন পড়ুন’। পরে দেখেছি, সেটা পালটে গেছে, বদলে লেখা, ‘লিট্ল ম্যাগাজিন কিনে পড়ুন, লিট্ল ম্যাগাজিন চিনে পড়ুন’। অনেকসময় দেখা হলে, লিট্ল ম্যাগাজিনের নামে বইমেলায় কত যে জঞ্জাল সেই দুঃখ করতেন। (Little Magazine)
আচ্ছা, লিট্ল ম্যাগাজিনের তো অনেক সমস্যা, এত বানান ভুলের সমস্যা কোন আর্থিক কারণে হয়? পি-ও-ডি-তে ছাপা, পারফেক্ট বাইন্ডিং, চকচকে ডিজিটাল কভার, আর পত্রিকার ভেতরে কেন শুধু ‘কাপড় পড়া’ ও ‘বই পরা’ চলতে থাকে? সেখানে মানুষ ‘বেরাতে বেড়োয়’? সেখানে ‘প্রতিযোগীতা’ নিয়ে পাতায় পাতায় ‘অসহযোগীতা’। ‘প্রুফ-রীডার’ একটুও ‘সহযোগি’ নয়। তাঁর ‘সত্বা’ ‘কী’ কাঁদে না! (Little Magazine)
চকচকে লিট্ল ম্যাগাজিন ওলটালে দেখতে পাই সম্পাদকের এরকম ‘ঝকঝকে’ বানানবোধ! লেখক-পাঠক কিছু বললেই প্রুফ-রিডারকে শিখণ্ডী হিসেবে খাড়া করা হয়। কেন ফাইনাল প্রুফ সম্পাদক নিজে যত্ন নিয়ে দেখবেন না? না কি দেখেছেন? তবে কি তাঁর অবস্থা প্রুফ-রিডারের থেকেও করুণ? (Little Magazine)
লিট্ল ম্যাগাজিনের ছদ্মবেশে আর এক উপদ্রব হয়েছে ‘বই-পত্রিকা’। ‘বাজারে খাবে’; এমন কোনো একটা বিষয় ঠিক করে কয়েকজনকে দিয়ে লিখিয়ে ও সেই বিষয়ে বাকিটা পুনর্মুদ্রণ করে বাজারে ছেড়ে দেওয়া। নামে লিট্ল ম্যাগাজিন, বোর্ডে বাঁধালেই বই। এরা পরে তাই করেও। কিছু সম্পাদক তো অদ্বৈতবাদী, বিশেষ সংখ্যা ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করেন না। সেসবের কাটতি এতই যে বইমেলার টেবিলে আর চলে না, স্টল দিতে হয়।
আরও পড়ুন: ‘আমি আর লীনা হেঁটে চলেছি’: কবিতা— ছাগলের তৃতীয় সন্তান- জাজরা খলিদ
বইবাজারে এখন সংগ্রাহকরাই খদ্দের-লক্ষ্মী, তাঁরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে এইসব ‘কাজ’ সংগ্রহ করেন। যে-কাজ নানান সরকারি প্রতিষ্ঠানের করার কথা সেই দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে এইসব ইয়ে, মানে ‘লিট্ল ম্যাগাজিন’। ফলে সংগ্রাহকদের বইয়ের র্যাকে শোভা পেতে থাকে বাংলার খাল-বিল-পুকুর-মন্দির-মসজিদ-কবরস্থান-শ্মশান-গঙ্গার ঘাট। তার পাশেই আলো ছড়াতে থাকে উত্তমকুমার, মহানায়িকা, খলনায়ক সংখ্যা। এখনও কার কার বাজার আছে এইসব তথাকথিত লিট্ল ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের বিশেষ সংখ্যা দেখলেই বুঝতে পারবেন। শৈলজানন্দ সংখ্যা, শরদিন্দু সংখ্যা, বিভূতিভূষণ সংখ্যা, তারাশংকর সংখ্যা, সত্যজিৎ সংখ্যা, তরুণ মজুমদার সংখ্যা, ঋতুপর্ণ সংখ্যা, তপন সিংহ সংখ্যা থেকে সোঁদরবনের ভোঁদর সংখ্যা। এসব সংখ্যার, যাকে বলে, মার নেই। ঘরে ঘরে এর পাঠক-ক্রেতা। দেখে আশা জাগে যে কালে কালে এইসব প্রণম্য সম্পাদকেরা অমিতাভ্ বচ্চন সংখ্যা, অমিতাভ্-রেখা সংখ্যা, মিঠুন-প্রসেনজিৎ-জিৎ-দেব থেকে কাঞ্চন-বিশ্বনাথ সংখ্যা বের করে ফেলতে পারবেন। শেফালিকে নিয়ে আনন্দ বই করে ফেলেছে তো কী হয়েছে, সংখ্যা করতে বাধা কোথায়? মারমার কাটকাট কাটতি হবে। ও, মনে করিয়ে দিই, সুপার-ডুপার পরিচালক সুখেন দাস আর অঞ্জন চৌধুরী এখনও ফাঁকা আছেন। সংখ্যা করলেই হিট। (Little Magazine)
আর একটা ফর্মুলা ‘লিট্ল ম্যাগাজিন’ সাজিয়ে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের রেফারেন্স বই সরবরাহ করা। লেখকদের অধিকাংশ ওইসব প্রতিষ্ঠানের মাস্টারমশাই। তাঁরা নানা কৌশলে সংখ্যাটির অপরিহার্যতা তুলে দেন তাদের কানে। এইসব পত্রিকার কামানো গাল, ব্র্যান্ডেড জামা দেখে কী যে ভালো লাগে! (Little Magazine)
একটা সময়ে আনন্দবাজার গোষ্ঠিকে লিট্ল ম্যাগাজিনের শত্রুপক্ষ মনে করা হত। তখন লিট্ল ম্যাগাজিনকে বলা হত কবি-সাহিত্যিকদের আঁতুরঘর। (এখনও মাঝে মাঝে শুনতে পাই)। আসল শত্রু বন্ধুশিবিরেই আছে। স্টিফেন হকিং বলেছিলেন না যে আছে আছে, এলিয়েন অবশ্যই আছে। তিনি কি মানুষদেরই এলিয়েন মিন করেছিলেন? এইসব ‘ছদ্ম লিট্ল ম্যাগাজিন’ গুলোই ‘লিট্ল ম্যাগাজিন’-এর আসল শত্রু। এরাই ঘুলিয়ে দিচ্ছে অদীক্ষিত পাঠকদের। পাঠক শবকে মনে করছে জ্যান্ত। পাঠককে পরিশ্রমী হতে হবে। তেমনই একটা নিরপেক্ষ স্ক্রুটিনি-কমিটি থাকা দরকার, যাতে মেলায় সত্যিকারের লিট্ল ম্যাগাজিনই জায়গা পায়। (Little Magazine)
মেলার কথায় মনে পড়ল জেলায় জেলায় লিট্ল ম্যাগাজিন মেলার কথা। বই-প্রকাশকদের সেখানে এন্ট্রি নেই। তাঁরা অনেকে এন্ট্রি-পাস হিসেবে নমো নমো করে বছরে অন্তত একটা পত্রিকা বের করছেন। তারপর মেলায় গিয়ে সাজিয়ে বসছেন বই। এইসব মেলায় থাকা-খাওয়া ফ্রি, যাতায়াত ছাড়া খরচ নেই। তাছাড়া জেলায় জেলায় লেখক-কবি হতে চাওয়া বধযোগ্যদের সঙ্গে এখানেই যোগাযোগ হয়ে যায়। যাকে বলে, মজার গরম গরম তেলেভাজা! তবে সবাই নয়। পত্রিকা ও বই প্রকাশ সমান সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে করে চলেছেন এমন দু-চার জনের কথা আমি জানি। তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।
“মেলা বা বইবাজার একটু সার্ভে করলেই দেখা যাবে এই ধরনের পত্রিকার তেমন কাটতি নেই, সীমিত পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে বিক্রি হয়। অনেকসময়েই খরচ ওঠে না। এবার একটু তলিয়ে ভাবুন।”
আগে কখনোসখনো শোনা যেত, এখন একটু বেশিই শোনা যাচ্ছে যে লিট্ল ম্যাগাজিন ডি-টি-পি, প্রেস, বাইন্ডার, কাগজ সব খাতে খরচ করতে পারে, শুধু লেখককে সাম্মানিক দেবার বেলায় টাকা থাকে না, লেখককে তাঁর লেখার জন্যে অর্থমূল্য কেন দেওয়া হবে না, ইত্যাদি। এখানে ‘লিট্ল ম্যাগাজিন’ বলতে আমি প্রকৃত অর্থে লিট্ল ম্যাগাজিনকেই ধরছি। এরকম পত্রিকার সম্পাদক খুঁজে খুঁজে তেমন লেখাই তাঁর কাগজে রাখতে চান যা চিন্তা-ভাবনা-আঙ্গিক-মননে ব্যতিক্রমী। সেসব লেখার লেখক-কবিও, লেখা বাহুল্য, ব্যতিক্রমী। এরকম লেখক-কবি ডজনে ডজনে জন্মান না। (Little Magazine)
তাঁরা যা লেখেন তাঁর পাঠকবৃত্তও ছোটো, কেন না এরকম লেখক-কবির লেখার পাঠক হতে হলে পাঠ-অভিজ্ঞতার অনেকটা পথ পেরিয়ে আসতে হয়। এইসব ভিন্ন চরিত্রের লেখা দিয়ে একজন প্রকৃত লিট্ল ম্যাগাজিনের সম্পাদক তাঁর পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে চান। মেলা বা বইবাজার একটু সার্ভে করলেই দেখা যাবে এই ধরনের পত্রিকার তেমন কাটতি নেই, সীমিত পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে ধীরে ধীরে বিক্রি হয়। অনেকসময়েই খরচ ওঠে না। এবার একটু তলিয়ে ভাবুন। এইসব ব্যতিক্রমী স্বরকে প্রকৃত পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যেই তো সম্পাদক পত্রিকার পেছনে যাবতীয় খরচ করেন। তাহলে প্রকারান্তরে এইসব ব্যতিক্রমী লেখক-কবির জন্যেই তো সম্পাদক যাবতীয় খরচ করছেন। (Little Magazine)
হ্যাঁ, সম্পাদকের একটা স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তা হল তাঁর পত্রিকা যেন প্রকৃত অর্থে ‘লিট্ল ম্যাগাজিন’ হয়ে ওঠে। নতুন একটি সংখ্যা যেন আগের সংখ্যাটিকে ছাপিয়ে যেতে পারে। এজন্যে বাড়তি ছাত্র পড়িয়ে, হাতখরচ বাঁচিয়ে, সংসার-খরচ থেকে বাঁচিয়ে, এমনকী প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে তাঁকে তাঁর অস্তিত্বের সমার্থক পত্রিকাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। এখানে লেখককে টাকা দেবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না। বরং ব্যতিক্রমী লেখক-কবিদের পক্ষে সম্ভব হলে পত্রিকাটিকে অর্থ-সাহায্য করা দরকার।
কারণ এই সেই পরিসর যা তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক লেখা প্রকাশ করার জন্য সম্পাদক প্রস্তুত করেছেন। এবার এরকম পত্রিকা যদি খরচ তুলে কিছু উদ্বৃত্ত আয় করতে পারে (যার সম্ভাবনা ক্ষীণ) তখন এই প্রশ্ন উঠতে পারে। এখানে আমি ছদ্ম লিট্ল ম্যাগাজিনগুলোর কথা বলছি না, সেইসব লেখক-কবিদের কথাও বলছি না যাঁরা এসব জায়গায় লিখে লিট্ল ম্যাগাজিনের লেখক বলে নিজেদের চিহ্নিত করতে চান ও লিখে টাকার দাবি তোলেন।
“১৯৭৫-এর আগে তো বইমেলাও ছিল না। কয়েকজন বন্ধু মিলে শুরু করা চূড়ান্ত অনিয়মিত রোগা একটি পত্রিকা, যাদের কেউই সংগঠক নয়। কিছু পত্রিকা পাঠকের কাছে পৌঁছত হাতে হাতে এলোমেলোভাবে, সবই ফ্রিতে। বাকিটা ডাঁই হয়ে পড়ে থাকত।”
বরাবর লিট্ল ম্যাগাজিনের লেখক ও জিরাফ পত্রিকার (কোচবিহার) সম্পাদক প্রয়াত অরুণেশ ঘোষ ঠিকই লক্ষ করেছিলেন যে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুটো নরকের সৃষ্টি হয়েছে, একটা কর্পোরেট হাউসের নরক, আরেকটা তথাকথিত লিট্ল ম্যাগাজিনসৃষ্ট নরক। (Little Magazine)
আমাকে বলা হয়েছে লিট্ল ম্যাগাজিনের সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা লিখে জানাতে। এ পর্যন্ত যা লিখলাম, আমার মনে হয়, তার মধ্যেই সেসব ঢুকে আছে। সরাসরি বললে, প্রকৃত লিট্ল ম্যাগাজিনের সংকট একটাই, তা হল, ধারাবাহিকভাবে ব্যতিক্রমী লেখা পাওয়া। এই শ্রেণির লেখকের আকাল দেখা দিয়েছে। চারদিকে দাদা ধরার, লেখা ছাপার আর মাচা বাঁধার যে মোচ্ছব চলেছে তাতে একটি ভিন্ন স্বর দেখা দিলে, তাকে লালন করার বদলে, অবিলম্বে তার মাথা খেয়ে ফেলা হচ্ছে। তাকে চটজলদি বিখ্যাত বানিয়ে নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। তার স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধির কোনো সুযোগই দেওয়া হচ্ছে না। এইভাবে কয়েক বছরের মধ্যে খান পাঁচেক বই বেরিয়ে যাবার পর তার নিজেরও মনে হতে শুরু করছে যে লেখক হতে আর বাকি কী! এ এক ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি! আর্থিক সংকট আগের মতো আর নেই বলেই মনে হয়। আগের মতো মানে ছয় বা সাত দশকের কথা বলছি, যখন একটা (ট্রেডল) প্রেসে ভাঙা টাইপে অর্ধেক পত্রিকা ছেপে, টাকা দিতে না পেরে, বাকি অর্ধেক আরেকটা প্রেসে লুকিয়ে ছাপতেও হয়েছে। (Little Magazine)
স্থানীয় মিষ্টির দোকান, হার্ডওয়ারের দোকান, স্টেশনারি দোকানের মালিকদের তেল দিয়ে সামান্য টাকার দু-চারটে বিজ্ঞাপন ছাপতে হয়েছে, যার অর্ধেকের পেমেন্টই পাওয়া যায়নি। তখন কোনো লিট্ল ম্যাগাজিন মেলা ছিল না। ১৯৭৫-এর আগে তো বইমেলাও ছিল না। কয়েকজন বন্ধু মিলে শুরু করা চূড়ান্ত অনিয়মিত রোগা একটি পত্রিকা, যাদের কেউই সংগঠক নয়। কিছু পত্রিকা পাঠকের কাছে পৌঁছত হাতে হাতে এলোমেলোভাবে, সবই ফ্রিতে। বাকিটা ডাঁই হয়ে পড়ে থাকত। লিট্ল ম্যাগাজিন যে কিনে পড়তে হয় সেই সচেতনতাটাই ছিল না। এক ছিল পাতিরাম (তার কথা আর নাই-বা বললাম)। অথচ সে সময়ের, সেই ছয় আর সাত দশকের কিছু পত্রিকা নিয়ে আমরা গর্ব করে থাকি, সেখান থেকে পুনর্মুদ্রণ করি। লিট্ল ম্যাগাজিন নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে সেইসময়ের পত্রিকার উল্লেখ ছাড়া। সেসব পত্রিকার পাতা এখন ওলটালে মনে হয় সস্তা কাগজে, ট্রেডল মেশিনে ছাপা, দেখতে অকিঞ্চিৎকর সেইসব পত্রিকার মধ্যে একটা সততা ছিল, নতুন কিছু করার আন্তরিক জেদ ছিল, একটা টাটকা মেজাজ ছিল, যা আমরা ক্রমেই হারিয়ে ফেলছি। (Little Magazine)
এখন চাকচিক্যে বেড়েছে, গায়ে-গতরে বেড়েছে, নেটওয়ার্কে বেড়েছে, খুব দুঃখের সঙ্গে বলছি— ধূর্ততায় বেড়েছে, সস্তায় বাজিমাত করার প্রবণতায় বেড়েছে। এসবই সংকট, আমাদের ভেতরের সংকট, ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, যা বেড়ে চলেছে। সমাধান রয়েছে নিজেদের সুস্থ করে তোলার সদিচ্ছার উপরে। এখন দেখতে পাই অনেক তথাকথিত লিট্ল ম্যাগাজিনের সম্পাদক প্রচুর নতুন কবি-লেখকের অদৃশ্য মিছিলের সামনে চলেছেন কৃপা বিলোতে বিলোতে। ফেসবুকে তার একটি পোস্টে লাইক, কমেন্টের বন্যা বয়ে যায়। এবং সংখ্যাগুলি পড়া যায় না। রাজ্যের জঞ্জাল সুন্দর ডিজিটাল মলাটের মধ্যে দামি বুকপ্রিন্ট কাগজে ছেপে দেওয়া। তার মধ্যে অসংখ্য ছাপার ভুল ও বানানের ভুল।
“সম্পাদক হেরে গেলে ক্রমশ যাচ্ছেতাই লেখায় ভরে উঠবে। আর লেখকরা হটে গেলে প্রতিশোধের চেহারা হবে চরম— পত্রিকাটি স্রেফ উঠে যাবে। … যুদ্ধ যত ভিতর-শিবির পর্যন্ত চলে আসে পত্রিকা তত পরিশুদ্ধ হয়।”
বানান-ভুল দেখলেই বোঝা যায়, বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সম্পাদক সঠিক বানান জানেন না। বললেই উত্তর আসবে, স্যরি, প্রুফ রিডারের চোখ এড়িয়ে গেছে। যদি একথা সত্যি হয় তাহলে প্রশ্ন জাগে যে কেন সম্পাদক নিজে অন্তত ফাইনাল প্রুফটা দেখবেন না? ব্যস্ততা থাকলে পত্রিকা দেরি করে বেরোবে, অসুবিধে কোথায়? (এই কথা আগেও একবার বলেছি)। আসলে সম্পাদক তার লেখক-কেরিয়ার তৈরিতে ব্যস্ত। পত্রিকা হল তার মই, তার লেখা বিনিময়ের মাধ্যম, রাজ্য জুড়ে এমনকী রাজ্যের বাইরে বিভিন্ন মাচায় ওঠা ও সংবর্ধনা লাভের উপায়। একজন সম্পাদক যদি তার কাগজে একটিও দুর্বল লেখা ছাপতে না চান তাহলে তিনি ১০০ জনের মধ্যে অন্তত ৯০ জন কবির কাছে অপ্রিয় হতে বাধ্য। ভালো কাগজ করা একটি অপ্রিয় কাজ। (Little Magazine)
কবি ও ‘পরমা’ পত্রিকার সম্পাদক মণীন্দ্র গুপ্ত এ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন: ‘সমাজ ছাড়া পত্রিকা অস্তিত্বশূন্য, এবং সামাজিক হওয়া সম্পাদকের পক্ষে অসম্ভব; নিষ্ঠাবান যে-কোনো পত্রিকা সম্বন্ধে এই হচ্ছে একমাত্র তীক্ষ্ণ সত্য। কবিতাপত্রিকার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সম্পাদক যদি আপোষহীনভাবে ক্রমাগত উৎকর্ষকামী হতে থাকেন— সে সত্য নীল বিদ্যুতের মতো ধারালো হয়ে সমস্ত সৃষ্টিসন্ধি ছারখার করে দিতে পারে।… এরকম কাগজের দুই দিকে দাঁড়িয়ে আছে দুই শক্তি মুখোমুখি, সর্বদা। একটি শক্তির নাম উদ্যোক্তা তথা কর্মনির্বাহক তথা সম্পাদক। অন্য শক্তিটি সমগ্র কবিসমাজ। মনে হতে পারে, বুঝি এঁদের পারস্পরিক সহযোগিতাতেই এগোয় কাগজ। কিন্তু না, কাগজ চলে ডায়লেকটিকসের নিয়মানুযায়ী— যতটা সহযোগিতা, ততটাই অসহযোগিতা। সম্পাদকের বাড়ানো দু-হাত বা কবির সৌজন্যমগ্ন চোখ দেখে প্রথমটা বোঝা যায় না এঁরা কী সাংঘাতিক প্রতিপক্ষ। সম্পাদকের বাড়ানো দু-হাত আসলে বন্ধুর নয়, রত্নান্বেষী রোবটের। (Little Magazine)
কবির সৌজন্যমগ্ন চোখ আসলে উদ্দেশ্যময় পরভৃত পাখির, নষ্ট ডিমেও তা না দিলে যা মুহূর্তে ড্রাগনের মতো হয়ে যায়। দু-দলই সবসময় চেষ্টা করছে প্রতিপক্ষকে হটিয়ে দিয়ে কাগজটাকে দখলে আনতে। সম্পাদক হেরে গেলে ক্রমশ যাচ্ছেতাই লেখায় ভরে উঠবে। আর লেখকরা হটে গেলে প্রতিশোধের চেহারা হবে চরম— পত্রিকাটি স্রেফ উঠে যাবে। … যুদ্ধ যত ভিতর-শিবির পর্যন্ত চলে আসে পত্রিকা তত পরিশুদ্ধ হয়। এই দীপ্তির কাছে সামাজিকতা, বন্ধুত্ব এবং সর্ববিধ কটূক্তি তৃণবৎ।’ (‘পরমা’ পত্রিকার একটি সংখ্যার শেষ মলাট থেকে)।
আরও পড়ুন: ‘সূত্রপাত’ পত্রিকা নবপর্যায়: নাসের রাবাহ-র কবিতা: ভাষান্তর: অরিত্র সান্যাল
এই যুদ্ধ করতে রাজি আছেন এমন সম্পাদকের সংখ্যা স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যালঘু হতে বাধ্য। তাঁদের পত্রিকার বিরুদ্ধে নানান চক্রান্ত চলবে, নানা কথা বাতাসে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। বইমেলা, লিট্ল ম্যাগাজিন মেলায় যাতে পত্রিকাটি জায়গা না পায় তার জন্যে কলকাঠি নাড়া হবে। সম্পাদক যে এলাকায় থাকেন সেখানকার স্থানীয় কবিসমাজ এবং সাহিত্যের ধারক ও বাহকেরা তাঁকে তাঁর পত্রিকাসহ একঘরে করে দেবে। কোনো প্রসঙ্গেই যাতে তাঁর পত্রিকার উল্লেখ না ঘটে, অত্যন্ত যত্ন নিয়ে তা দেখা হয়। এইসব অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে নিজের আদর্শমতো কাগজটিকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন এতটা সবল কলিজা বেশি সম্পাদকের থাকে না। (Little Magazine)
‘গল্পকবিতা’র শেষ সংখ্যার সম্পাদকীয় ‘শেষ কিছু কথা’-য় পত্রিকাটির জীবনকালের হিসাব দেওয়া হয়েছিল ‘১৮ কোটি ১৬ লক্ষ ১২ হাজার ৮০০ সেকেন্ড’। হ্যাঁ, এটাই সঠিক হিসাব, কারণ একটি লিট্ল ম্যাগাজিন প্রতিটি মুহূর্তে বেঁচে থাকে। তা না হলে সে আর লিট্ল ম্যাগাজিন থাকে না।
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।