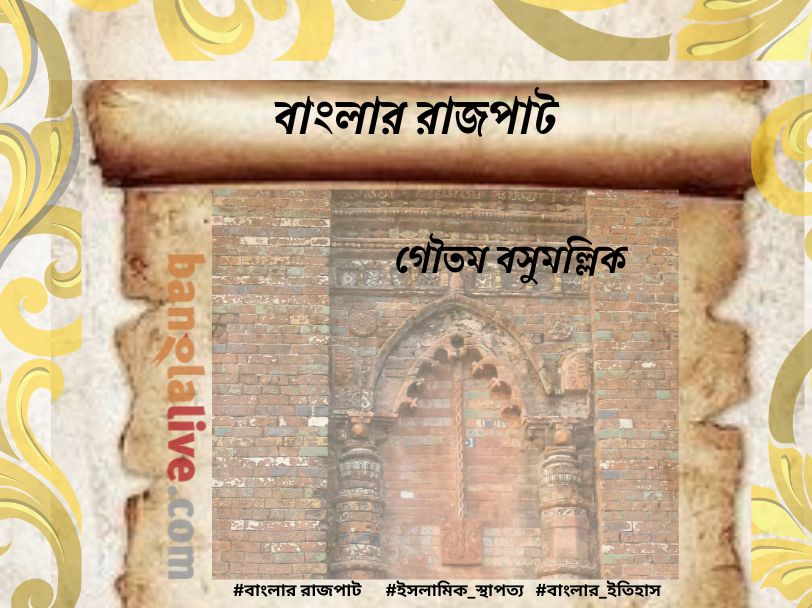বাংলার রাজপাট: দশম পর্ব
এই পর্বে আমরা গৌড়ের চিকা মসজিদ ও লোটন মসজিদ নামের দুটো তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ সৌধের কথা আলোচনা করবো।
চিকা বা চামকান মসজিদ:
প্রথমে আসা যাক, চিকা বা চামকান মসজিদ বা সৌধের কথায়। কদম-রসুলের সামান্য দক্ষিণ দিকে এক গম্বুজওয়ালা একটা সৌধ রয়েছে। ইটের তৈরি প্রায় ৪২ বর্গ ফুট আয়তনের এই সৌধটাকে বাইরে থেকে মসজিদের মতো দেখতে হলেও এটা সম্ভবত কোনও মসজিদ নয়। এটা যে মসজিদ নয় তার কারণ হল, এই সৌধের পশ্চিম দেওয়ালে কোনও মেহরাব নেই। আলেকজান্ডার ক্যানিংহামের দেওয়া বিবরণ অনুসারে, এর দেওয়াল ১৪ ফুট ৯ ইঞ্চি পুরু এবং সৌধের বাইরের দিকের দালান ৭১ ফুট ৯ ইঞ্চি মাপের।
হেনরি ক্রেইটন যদিও এই সৌধের কোনও নামকরণ করেননি। কিন্তু এই সৌধের মধ্যে যেহেতু এককালে প্রচুর বাদুড় থাকতো তাই পরবর্তীকালে স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসরণ করে এটাকে চিকা বা চামকান মসজিদ বা সৌধ নামে চিহ্নিত করা হয়। গৌড়ের অবশিষ্ট স্থাপত্যগুলো সংরক্ষণের সময়ে এই সৌধটাকেও সারিয়ে তার দরজায় জাল বসিয়ে দেওয়ার ফলে এখন আর বাদুড়ের উপদ্রব নেই।

চিকা বা চামকান সৌধ ক্রেইটনের বর্ণনায় ‘গম্বুজে আচ্ছাদিত একটি ছোট গেটওয়ে’। কিন্তু আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম এটাকে সমাধিসৌধ বলেছেন অথচ ওই ঘরের মধ্যে কোনও সমাধি নেই। ওই সৌধ হজরৎ পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধিসৌধের মতোই বর্গাকার আকৃতির।
হেনরি ক্রেইটনের আঁকা ১০ নম্বর ছবিতে এই সৌধের কথা ছোট করে বলা আছে। সেখানে তিনি ওই সৌধকে ‘গম্বুজে আচ্ছাদিত একটি ছোট গেটওয়ে’ বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং কাছাকাছি পাওয়া একটা পাথরের ফলকে ৯০৯ হিজরি, অর্থাৎ ১৫০৩ সাধারণাব্দে তৈরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই অনুসারে ক্রেইটন ওই সৌধ আলাউদ্দিন হোসেন শাহর তৈরি বলে জানিয়েছেন। কিন্তু ক্রেইটনকে উদ্ধৃত করে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে ক্যানিংহাম এই সৌধটা সম্পর্কে ভিন্ন মত দিয়েছেন। তিনি এটাকে হজরৎ পাণ্ডুয়ার একলাখি সমাধি সৌধের অনুরূপ একটা সমাধিসৌধ বলেই লিখেছেন।
আরও পড়ুন: যে ঠিকানা লেখা যায় না, সেই ঘরে যাদের বাস! পর্দার ভবঘুরেরা
স্থানীয় জনশ্রুতি উল্লেখ করে আবিদ আলি খান লিখেছেন যে ওই সৌধকে হুসেন শাহ কারাগার হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং চৈতন্যের সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি চাইলে মন্ত্রী সনাতন গোস্বামীকে নাকি হোসেন শাহ এই কক্ষেই বন্দী করে রেখেছিলেন। পরে নাকি তিনি ওই কারাগারের রক্ষীকে ঘুষ দিয়ে নদীপথে পালিয়ে যান। অর্থাৎ, হোসেন শাহ ওই সৌধকে কারাগার হিসেবে ব্যবহার করতেন।
ওই সৌধের পরিচিতিতে ‘ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ’ চিকা মসজিদ ১৪৫০ সালে নির্মিত বলে লেখা রয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, কীসের ভিত্তিতে চিকা মসজিদের নির্মাণকাল ১৪৫০ সাল লেখা হল।
হেনরি ক্রেইটন যদিও এই সৌধের কোনও নামকরণ করেননি। কিন্তু এই সৌধের মধ্যে যেহেতু এককালে প্রচুর বাদুড় থাকতো তাই পরবর্তীকালে স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসরণ করে এটাকে চিকা বা চামকান মসজিদ বা সৌধ নামে চিহ্নিত করা হয়। গৌড়ের অবশিষ্ট স্থাপত্যগুলো সংরক্ষণের সময়ে এই সৌধটাকেও সারিয়ে তার দরজায় জাল বসিয়ে দেওয়ার ফলে এখন আর বাদুড়ের উপদ্রব নেই।
পাণ্ডুয়া থেকে রাজধানী ঠিক কবে আবার গৌড়-নগরীতে উঠে আসে তা নিয়েও ইতিহাসবিদেরা একমত নন। তবে অন্যান্য সাক্ষপ্রমাণের উপরে ভিত্তি করে অনুমান করা হয়, আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পাণ্ডুয়া থেকে গৌড় নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে নাসিরউদ্দিন মামুদ শাহর রাজত্বকালেই তা হয়েছিল। সেই সময়ে গৌড়ে কোনও রাজপ্রাসাদ ছিল কি না তা স্পষ্ট নয়। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ যে অংশটাকে সম্ভাব্য রাজপ্রাসাদ বলে চিহ্নিত করেছে তা নির্মিত হয়েছিল রুকনুউদ্দিন বারবাক শাহর সুলতানি আমলে। সেই সমস্ত সূত্র থেকেই তাহলে অনুমান করা যেতে পারে বর্তমানে যেটা চিকা মসজিদ নামে চিহ্নিত তা কোনও মসজিদ তো নয়ই, সমাধিসৌধও নয়। ক্রেইটন ওই সৌধের পাশে আরও অন্য ভবনের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলেন, যেগুলোর সামান্য চিহ্ন আজও বর্তমান। সব মিলিয়ে ওই সৌধ এবং পার্শ্ববর্তী অংশের ভেঙে যাওয়া ভবনগুলো সরকারি দপ্তর ছিল বলেই মনে করা যেতে পারে।

লোটন বা লট্টন মসজিদ:
গৌড়ের ভারতীয় অংশে এখনও যে সামান্য কয়েকটা স্থাপত্য তুলনামূলক ভালো অবস্থায় রয়েছে, লোটন বা লট্টন মসজিদ তার মধ্যে অন্যতম। বলা হয়ে থাকে, নটু নামের এক নর্তকী এই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর বইতে জানিয়েছেন যে নটু নামের ওই নর্তকীর অপর নাম মীরাবাঈ, তিনি একটা তালুকও ভোগ করতেন, সেটা মীরা-তালুক নামে পরিচিত। খান সাহেব আবিদ আলি অবশ্য ওই মসজিদ কোনও নর্তকীর অর্থে নির্মিত হয়েছিল বলে মানতে চাননি। তিনি বলেছেন, নর্তকীরা যেহেতু তৎকালীন সমাজে ব্রাত্য বলে গণ্য হতেন, তাই লোটন বা লোট্টন রাজ-নর্তকী হলেও তাঁর টাকায় তৈরি মসজিদে সে যুগের ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের নমাজ পড়তে না যাওয়াই স্বাভাবিক।
ওই মসজিদের কাছাকাছি মহাজনটোলা এলাকা থেকে পাওয়া একটা পাথরের ফলক বা শিলালিপি অনুসারে ক্রেইটন তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন যে, সুলতান ইউসুফ খানের রাজত্বকালে ৮৮০হিজরি বা ১৪৭৫ সাধারণাব্দে এই মসজিদ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সেই শিলালিপিটা যে ওই লোটন মসজিদেরই সেটা নিয়ে ক্যানিংহাম সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ওটা চামকাটি মসজিদের ফলক।

ক্যানিংহামের ওই ধারনার কারণ হল, দুটো মসজিদের ভূমিতলের নকশা প্রায় একই রকম। সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে এই মসজিদ সম্পর্কে যে বিবরণ ক্যানিংহাম দিয়েছেন, সেখানে তিনি বলেছেন, উভয় মসজিদেই এক গম্বুজবিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ একটা মাত্র প্রকোষ্ঠ রয়েছে এবং তার সামনে একটা বারান্দা রয়েছে। লোটন মসজিদের প্রধান প্রকোষ্ঠ বা ঘরটা ৩৪ ফুট সমচতুষ্কোণ এবং বারান্দাটা ৩৪ ফুট লম্বা ও ১১ ফুট চওড়া। মসজিদের দু’পাশের দুটো দেয়াল এবং বারান্দার সামনের দেয়ালটা ৮১/২ ফুট পুরু। আবার ওই একই ঘরের সামনের ও পেছনের দেয়াল ১০ ফুট ৭ ইঞ্চি পুরু।

বারান্দার সামনের দিকে তিনটে ও দু’পাশে দুটো করে খিলান করা দরজা রয়েছে। মধ্যবর্তী দরজার খিলানটা ৬ ফুট ১১ ইঞ্চি চওড়া, এবং দু’পাশের অন্য দুটো খিলান ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি মাপের এবং দুই প্রান্তের দুটো খিলান ৪ ফুট ৯১/২ ইঞ্চি চওড়া। মূল মসজিদ-ঘরের সামনের দিকে তিনটে দরজা ছাড়া পাশের দরজাগুলোও রয়েছে এবং সেই দরজাগুলো মাপের দিক দিয়ে বারান্দার দরজার মতোই। মসজিদের পেছনের দেওয়ালে সম্মুখের দরজার ঠিক সামনাসামনি তিনটে কুলুঙ্গি রয়েছে। প্রধান বর্গাকার কক্ষের চার কোণে চারটে কালো পাথরের স্তম্ভের উপর খিলান উঠে থাকায় কক্ষটা অষ্টভুজের আকার ধারণ করেছে।

গ্রন্থঋণ:
১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে‘জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩
২। মালদহ: জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
৩। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা
৪। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা
৫। কেদারনাথ গুপ্ত, গৌরবময় গৌড়বঙ্গ, সোপান, কলকাতা
৬। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
৭। প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস: প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
৮। সুখময় মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাসের দু’শো বছর: স্বাধীন সুলতানদের আমল (১৩৩৮—১৫৩৮), ভারতী বুক স্টল, কলকাতা
৯। Alexander Cunningham, ASI Report of A Tour in Bihar and Bengal in 1879-80 from Patna to Sunargaon_Volume XV, ASI, New Delhi
১০। Creighton Henry, The Ruins of Gour described and represented in eighteen views; with a topographical map, Londan
১১। John Henry Ravenshaw, Gaur its Ruins and Inscriptions, C. Kegan Paul & Co. London.
১২। Khan Sahib M. Abid Ali Khan, Memoirs of Gour and Pandua, Bengal Secretariat Book depot, Calcutta.
১৩। Ghulam Husain Salim, The Riyazu-S-Salatin: A History of Bengal, Asiatic Society, Calcutta (মূল বইটা ফার্সি ভাষায় লেখা। ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন Maulavi Abdus Salam.)
*ছবি সৌজন্য: লেখক
*পরবর্তী অংশ প্রকাশ পাবে মে, ২০২৪
গৌতম বসুমল্লিকের জন্ম ১৯৬৪ সালে, কলকাতায়। আজন্ম কলকাতাবাসী এই সাংবাদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার সুবাদে। মূলত কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও, এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন’ [UGC, Human Resource Development Centre (HRDC)]-র আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন দীর্ঘকাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো’।