এখনও অনেক দূর গ্রামের বাড়িতে লণ্ঠনে পড়াশোনা হয়। এমন কোনও বাড়িতে, এই গভীর রাতে কোনও কিশোর হয়তো দুলতে দুলতে একটা পাঠ্যবই থেকে বারবার একই লাইন পড়ে যাচ্ছে এখন, ‘মালদা, মুর্শিদাবাদের আম খুব বিখ্যাত। মালদা, মুর্শিদাবাদের আম খুব বিখ্যাত।’
বিখ্যাত? সত্যি? এখনও?
মালদা, মুর্শিদাবাদের অজস্র চেনা মানুষজনের মুখ ভাসে চোখের সামনে, যাঁরা প্রায়ই আক্ষেপ করেন, কলকাতার সব বাজারে আমের এত ভালো চেহারা, মালদা-মুর্শিদাবাদে আমের চেহারা দিনদিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে কেন? কেমন কালচে ভাব, ক্ষয়াটে। দিন দিন আরও শুকনো হয়ে যাচ্ছে। কতদিন পুরনো নাম ভাঙিয়ে চলবে স্পষ্ট নয়।
কলকাতার বাজারে যে আম দেখা যায়, তা সাধারণত বারুইপুর, বসিরহাট, হুগলি, নদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের আম। সে আমের চেহারা এত ভালো, যে মালদা-মুর্শিদাবাদের আমকে বলে বলে গোল দেবে। বিশ্বাস না হলেও সত্যি এটা। মালদা-মুর্শিদাবাদে বরং এখন দক্ষিণবঙ্গ থেকে আম যায় অনেক সময়। তখন চেহারার ফারাকটা বোঝা যায় আরও বেশি করে। আমের দেশের লোক হওয়ার সুবাদে ভালো গাছপাকা আমের একটা সংজ্ঞা আমার কাছে স্পষ্ট। গাছপাকা আমের শর্ত এ রকম। এক, আমের বোঁটার চারদিকটায় আঠালো রস থাকবে। দুই, বোঁটার চারপাশে গেরুয়া আভা দেখা দেবে এবং গেরুয়া রংয়ের ওপর কালো কালো বিন্দু। নীচের অংশ সবুজ থাকে, থাকুক। সে আম অবধারিত গাছপাকা। কিছু আম আছে বর্ণচোরা আম। রং দেখে কাঁচা ও টক মনে হলেও আসলে পাকা ও মিষ্টি আম। বুঝতে পারলে ওই স্বাদের কিন্তু তুলনা নেই।
গাছপাকা আমের কথা বললে, আমার সবার আগে মনে পড়ে ‘ঠুসি’ আর ‘জাবি’র কথা। আম পাড়ার জন্য এ দুটো উপকরণ একান্ত জরুরি। ‘ঠুসি’ হল একটা সরু বাঁশ। তার মাথায় পাটের দড়ি দিয়ে ছোট একটা জাল থাকবে। ‘জাবি’ হল, বড় বৃত্তাকার জাল। আম পাড়ুয়ারা একটা ‘ঠুসি’ নিয়ে, কোমরে ‘জাবি’ বেঁধে গাছে উঠত। আম পাড়ার সময় ‘ঠুসি’ দিয়ে সাবধানে একটা একটা করে পাকা আম পাড়তে হয়। সেগুলো জমা রাখা হয় ‘জাবি’তে। খুব সাবধানে নেমে গাছের নীচে একটা একটা করে সাজিয়ে রাখতে হত আম। একটা গাছের সব আম একদিনে পাড়া হত না।

এখন শুনি, আম পাড়ার ওই বিশেষত্বই আর পালন হয় না। একে তো গাছপাকা হওয়ার জন্য অপেক্ষাই হয় না। তার পর ঝাঁকিয়ে পেড়ে নেওয়া হয় গাছের সব আম। অযত্ন করে পাড়ার জন্য আমের ভিতরটা নষ্টই হয়ে যায়। মালদা, মুর্শিদাবাদের আমের স্বাদ ক্রমশ খারাপ হওয়ার পিছনে আর একটা কারণ, দুটো জেলাতেই পুরনো আম গাছের রমরমা। একে বয়স বেশি, তারপর গাছগুলোর আর ভালো রক্ষণাবেক্ষণ হয় না। কৃষিবিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে এগনো হয় না দীর্ঘদিন। বরং আমের আশায় অবৈজ্ঞানিকভাবে দেওয়া হয়েছে রাসায়নিক।
অবাক লাগে ভাবলে। পলাশ বা রডোড্রেনডনের মতো আমের মুকুলও বেশি আসে এক বছর অন্তর। যেবার উপচে পড়ার কথা আমের মুকুলের, সেবার মরসুমে একটা আমবাগানের হাতবদল হয় অনেকবার। আসল মালিক হয়তো সে বছরের জন্য বিক্রি করল কাউকে। সে আবার আর একজনকে। তারা আর কেউ ভবিষ্যতের কথা ভাবে না। যা হয়ে দাঁড়ায়, ‘পাকা আম দাঁড়কাকে খায়’ প্রবাদের মতো। অপাত্রে সুপাত্রী দান। তা ছাড়া একটা গাছ কত যুগ ধরে ভালো ফল দেবে? এতদিনে নতুন গাছ লাগানো শুরু হয়েছে। সে তো ফল আসতে দেরি অনেক।
দুটো জেলার ক্ষেত্রেই খেয়াল করলে দেখা যাবে, যে সব অঞ্চলের পাশে নদী, সেখানেই আমের আবাদ ভালো। মুর্শিদাবাদে গঙ্গার ধারে মুর্শিদাবাদ, আজিমগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, ভগবানগোলা, লালগোলা। মালদায় গঙ্গা-মহানন্দা-ফুলহারের ধারে মাণিকচক, ইংরেজবাজার, রতুয়া, হরিশচন্দ্রপুর, চাঁচল, সামসি। দুটো জেলার একটা দিকে কিন্তু আম হয় না। এ দুটো জেলার আমের বিশেষত্ব কী? সমস্যা হল, ওখানে এমন অনেক আম হয়, যা কলকাতার দিকে আসেই না। কলকাতার লোক জানেনও না, সে আমের নাম। মালদা জেলার সবচেয়ে নামকরা আমের মধ্যে থাকবে ‘ফজলি’, ‘ল্যাংড়া’, ‘গোপালভোগ’ এবং ‘ক্ষীরসাপাতি’। নিয়ম হল, ‘গোপালভোগ’ উঠবে আগে। তা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ‘ল্যাংড়া’। মালদায় ‘ক্ষীরসাপাতি’ দু’রকম। ‘মালদাইয়া ক্ষীরসাপাতি’ এবং ‘কুমারখাঁ ক্ষীরসাপাতি’। ‘ফজলি’ হবে শেষ দিকে। অত গুরুত্ব পায় না অভিজাত মহলে। অতিথি এলে ফজলি আম কেটে দেওয়া হত না।

‘হিমসাগর’ হল সত্যিই রহস্যসাগর। কলকাতায় দেখবেন, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মতো আমভক্তরা দুটো ভাগে বিভক্ত। একদল হিমসাগরের সমর্থক। একদল ল্যাংড়ার। কিন্তু আমের জন্য দুটো জেলায় হিমসাগর নিয়ে প্রশ্ন করলে বিভ্রান্তি বেড়ে যাবে। মুর্শিদাবাদের পরিচিত অনেককে বলতে শুনেছি, ওখানকার বিখ্যাত ‘শাদুল্লা’ আমই হল ‘হিমসাগর’। কেউ আবার বলেন, ‘রানিপসন্দ’ বা ‘রানিভোগ’ই হল ‘হিমসাগর’। মালদায় আবার অনেককে বলতে শুনেছি, ‘মালদাইয়া ক্ষীরসাপাতি’ই নাকি ‘হিমসাগর’। এই মতের লোক সবচেয়ে বেশি। যদিও আমার দুটো আম খেয়ে কখনও এক মনে হয়নি। মালদায় আবার ‘শাদুল্লা’ নামে অন্য আম রয়েছে।
‘হিমসাগরে’ যাঁরা মজেছেন, তাঁদের অনেকটাই চেনা চেনা লাগবে মালদার ‘গোপালভোগ’-এর স্বাদ। দেখতেও অনেকটা এক। গায়ের ওপর ছিটে ছিটে দাগ। আমার তো প্রথমে মনে হত, হিমসাগর মানে গোপালভোগ। পরে দেখলাম, ব্যাপারটা তা নয়। ‘মুম্বই’ বলে একটা আম আছে। তার সঙ্গেও হিমসাগরের মিল। ‘শাদুল্লা’, ‘ক্ষীরসাপাতি’, ‘মুম্বই’, ‘গোপালভোগ’, যে নামেই ডাকুন না, খোঁজ নিয়ে শুনলাম, সবই এক জাতীয় প্রজাতির। তাই স্বাদে খুব মিল।

দুঃখজনক হল, ‘গোপালভোগ’ গাছ মারাত্মক কমতে শুরু করেছে মালদায়। খুব কম দিনই মেলে ‘গোপালভোগ’। ‘কুমারখাঁ ক্ষীরসাপাতি’রও একই দুর্দশা। সে জায়গায় দুটো আম ভালো জায়গা নিয়েছে। ‘আম্রপালি’ ও ‘মল্লিকা’। দুটো আমের ভালো দিক হল, খুব কম দিনেই ফল হয়। মালদায় ‘ফজলি’রও দুঃসময় চলছে। আমাদের ছোটবেলায় দেখতাম, দু’রকম ‘ফজলি’। ‘সাধারণ ফজলি’ এবং ‘সুরমা ফজলি’। ‘সুরমা ফজলি’ কাঁচা অবস্থায় কাঁচামিঠের মতো লাগত খেতে। এখন সে দিন আর নেই।
‘ল্যাংড়া’ ছিল দু’রকম। ‘হাজিপুরি ল্যাংড়া’ এবং ‘বেনারসি ল্যাংড়া’। দুটোর স্বাদ পুরো আলাদা। ‘হাজিপুরি ল্যাংড়া’কেই বলা হত আসল ‘ল্যাংড়া’। এখন ‘ল্যাংড়া’ নিয়ে ইন্টারনেটে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি, ল্যাংড়াকে বলা হচ্ছে ‘বেনারসি ল্যাংড়া’। দেখি, পটনায় বিখ্যাত ‘ল্যাংড়া’ আমের নাম আবার ‘দুধিয়া মালদা’। সেখান থেকে বিদেশে যায় এই আম, যার সঙ্গে মালদার নাম জড়িয়ে। এই হয়! কার নাম কোথায় চলে যায়! এ সব ভেবে আবার পুরোনো আমবাগানগুলোর কথা মনে পড়ে।
বহু যুগ আমাদের মালদার গ্রামের বাড়ির আমবাগানগুলোয় যাওয়া হয়নি। তবু এখনও চোখ বুজলে দেখতে পাই, পুকুরের এক দিকে ‘গোপালভোগ’, ‘মোহনভোগ’, ‘সবজা’, ‘আরাজন্মা’, ‘মিছরিভোগ’, ‘বৃন্দাবনি’, ‘কালুয়াদাগি’। অন্য দিকে ‘মধুচুসকি’, ‘জেঠুয়া’, ‘ছুরিকাট্টা’, ‘চেপ্টিয়া’, ‘লক্ষণভোগ’, ‘হাজিপুরি ল্যাংড়া’, ‘কাঁচামিঠে’, ‘শিপিয়া’, ‘টকিয়া’, ‘বেনারসি ল্যাংড়া’। আর একটা বাগানের আম ছিল, নাম ‘কাউয়াডিমি’। সত্যি সত্যিই কাকের ডিমের মতো ছোট ছোট আম হত। ‘গুটি আম’ থেকে কতরকম নামের আম আছে মালদায়। ‘চৌসা’, ‘আশ্বিনা’, ‘ভারতী’, ‘দুধকুমার’, ‘চিনি লটপট’, ‘আশুয়া’, ‘ফানিয়া’, ‘রাখালভোগ’। আমাদের বাগানে একটা গাছে একটা দিকে আসল ‘ল্যাংড়া’ মিলত, আর একদিকে ‘গুটি আম।’
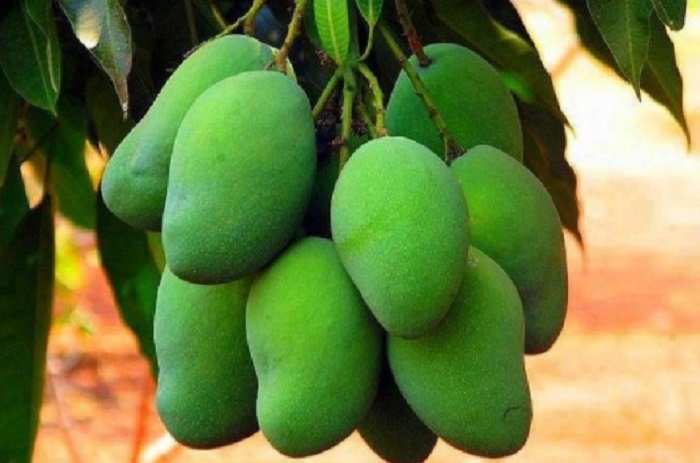
মুর্শিদাবাদে আবার সবচেয়ে জনপ্রিয় আম ‘চম্পা’। তারপর ‘শাদুল্লা’। ‘চম্পা’ আমের সত্যিই নাকি চাঁপার মতো স্বাদ। খাওয়া হয়নি কোনওদিন। কোথাও একটা পড়লাম, এ আমের আসল নাম ‘চম্পাবতী’। চম্পাবতী ছিলেন মুঘল দরবারের বাঈজি। চম্পাবতী থেকেই ‘চাঁপা’। মালদা, মু্র্শিদাবাদের আমের ফারাক কী, জানতে চাইলে বলব, প্রথম জেলায় আমের সংখ্যা বেশি, দ্বিতীয় জেলায় আমের আভিজাত্য বেশি। মালদার মতো ইদানীং মুর্শিদাবাদেও বেশি জায়গা করে নিয়েছে ‘আম্রপালি’ ও ‘মল্লিকা’। বড় দ্রুত বাড়ে যে! স্বাদও ভালো।
আকবরের আমল থেকে আম রয়েছে মুর্শিদাবাদে। তবে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সৌজন্যেই মুর্শিদাবাদে আমের রমরমা। আকবরের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে ১৭০৪ সালে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী নিয়ে আসার পর মুর্শিদকুলি খাঁ জোর দিয়েছিলেন আমবাগান তৈরির ওপরে। চট করে একটা অন্য কথা বলে নিই এখানে। জানেন কি, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আবিষ্কার করেছিলেন, মুর্শিদকুলি ছিলেন আসলে হিন্দু। নাম ছিল সূর্যনারায়ণ মিশ্র। দশ বছর বয়সে তাঁকে বিক্রি করে দেওয়া হয় এক পারসি হাজি সফিকে। তখনই ধর্মান্তরে নাম হয় মহম্মদ হাদি।
নবাবদের সৌজন্যে লালবাগে নানা রকম পরীক্ষা হয়েছে আম নিয়ে। ‘চাঁপা’ তো তারই নমুনা। ‘চন্দন কসা’ নামে আমে নাকি চন্দন গন্ধ। ‘মোলামজাম’ বলে আম রয়েছে, তাতে জামের স্বাদ। ‘আনারস’ আমও আছে ওই স্বাদ নিয়ে। ‘কুমড়োজালি’ আম আবার কুমড়োর মতো বড়— মালদার ‘কাউয়াডিমি’র একেবারে উল্টো। ‘মিয়াঁ কা বাচ্চা’ নামেও মেলে আম। এবং তা সব মুর্শিদাবাদ নবাববাড়ির কাছাকাছি। অন্য ব্লকে এ সব মেলে না। নবাবদের সৌজন্যে আছে ‘কালাপাহাড়’, ‘চন্দন কষা’, ‘বিমলি’, ‘কালাসুর’, ‘ভবানী’র মতো আম।
‘কোহিতুর’ বলে একটা আম রয়েছে, তুলো দিয়ে রাখতে হয়। বারো ঘণ্টা অন্তর উল্টে রাখতে হয়। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, সবচেয়ে দামী আম ‘কোহিতুর’-এর জন্য জিআই ট্যাগ দাবি করতে পারে বাংলা। ‘কোহিতুর’ আমের এক একটার দাম দু’বছর আগে শুনেছিলাম ১৫০০ টাকা। কেউ বলেন, আকবরের আমল থেকে রয়েছে ‘কোহিতুর’। কেউ বলেন সিরাজদৌল্লার কথা। কাশিমবাজারের রাজার বাগানে ছিল অনেক ‘কোহিতুর’ গাছ।

এত আমের আসল ইতিহাস আর পাওয়া যাবে না কোনওদিন। হারিয়েও যাচ্ছে সব প্রজাতি। তবে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ‘পসন্দ’ওয়ালা নামগুলোর গল্প শোনা যায় আজও। ‘নবাবপসন্দ’, ‘দিলপসন্দ’, ‘মির্জাপসন্দ’, ‘রানিপসন্দ’, ‘এনায়েতপসন্দ’, ‘সবদারপসন্দ’। এনায়েত খান নামে এক ওমরাহ, সবদার খান নামে স্থানীয় প্রধান চিরজীবী হয়ে থেকে গিয়েছেন এ আমের জন্য। ‘সবদারপসন্দ’কে আবার অনেকে বলেন, ‘বীরা’। এ জেলার অতি পরিচিত ‘শাদুল্লা’ নাকি তৈরি করেছিলেন মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত শাহরা। ‘বিমলি’ আম কী জন্য নাম? মিরজাফরের আমলে এক পরিচারিকার নাম ছিল বিমলি। তিনি নাকি নিত্য নতুন আমগাছ বানাতেন। তাঁর জন্যও করা হয়েছে একটা আম। ‘সারঙ্গা’ আম কেন? নবাবের হাভেলিতে সারেঙ্গিবাদকদের কথা ভেবে।
আম নিয়ে এত কথা লেখার পর নিজেরই একটা পুরনো লেখা মনে পড়ে গেল। মন্ত্রের মতো নাগাড়ে বলে যাওয়ার মতো কথা। কাট অ্যান্ড পেস্ট করে বসাতে গিয়ে মন কেমন করে ওঠে নিজেরই। তবু বসাই–
‘এই সময়টা মন মাতাল একটা হাওয়া দেয় কোন তেপান্তরের মাঠ থেকে। সূর্য আর মেঘের চু কিৎকিৎ খেলার সময়। লিচুবাগান আর আমবাগানের মাঝে খড়ের চালা দেওয়া ছোট্ট চালাঘর। চারদিক খোলা। কয়েকটা পাকা বাঁশের সঙ্গে দড়ি বেঁধে একটা খাট। ব্যস। বেশ।
রাতে তো আমবাগান, লিচুর গাছ পাহারা দেবে মনুয়া, অসনদা, নগেনদা-রা। দুপুরটা আমাদের। স্কুলে গরমের ছুটি! শীতলপাটি নিয়ে অঙ্ক করার নাম করে বাগানের ওই চালাঘরে গিয়ে বসব। বাগানের মাঝে কতরকম লোক যায়! মানুষ দেখব। ঝড় আসার রাস্তাটা দেখব। চালাঘরে থাকে ঠুসি আর জাবি। ঠুসি দিয়ে গাছের মগডালের পাকা আমটাকে পেড়ে আনা যায়! জাবি আবার সব আম জড়ো করার জন্য। দেখব কোন গাছের কোন ডালে গাছপাকা আম!
মেঘ কালো হয়ে এল, পুকুরের জলে ঘূর্ণি! পাড় থেকে দেখি বাড়ছে মাছেদের ঘাই। বাতাসের নানা রকম শব্দ। আম, লিচুর গন্ধ মাখামাখি! দুরন্ত হাওয়ার মাঝে ধুপ, ধুপ করে শব্দ। ছুটে যাব আম কুড়োতে। কত রকম আমের নাম! মধুচুস্কি, বৃন্দাবনী, ক্ষীরসাপাতি, মোহনভোগ, গোপালভোগ, লক্ষণভোগ, সব্জা, কুমারখাঁ…।
অত তীব্র হাওয়া। আম পড়ার পর ঝড়ের অবশ্যম্ভাবী সঙ্গী হয়ে আসে শিলাবৃষ্টি। শিল পড়ার শব্দ আবার আলাদা। সে সব কুড়োতে লাগে ছাতা। ভিজে যাই বৃষ্টির ছাঁটে। বাগানে পাহারাদারদের ছোট খোলা ঘরগুলো অটুট থাকে। ঝড়ে, বৃষ্টিতে।
শুধু অঙ্কের খাতাগুলো ভিজে যায়! উধাও হয়ে যায় সব অঙ্ক।’
লেখক উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রাক্তন কার্যকরী সম্পাদক। এর আগে এই সময় সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। ছিলেন ক্রীড়া সম্পাদকও। অতীতে যুক্ত ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে। আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন দীর্ঘদিন। বাঙালির সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফুটবলের যোগসূত্র ঘটানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা তাঁর। পাঁচটি ফুটবল বিশ্বকাপ, তিনটি অলিম্পিক, একটি ইউরো কাপ ফুটবল, দুটি হকি বিশ্বকাপ, একটি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-সহ অসংখ্য ঘরোয়া টুর্নামেন্ট কভার করলেও প্রথমদিন থেকে লিখে থাকেন নানা বিষয়ে। ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সংস্কৃতি, গানবাজনা, সিনেমা, খাবার, ভ্রমণ। এখন বলতে গেলে লেখার দুনিয়ায় খেলা বাদে সর্বত্র বিচরণ।

























