নবনীতা দেবসেনের কবি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কবি তাঁকে হতেই হত। তিনি নিজেই এক জায়গায় মন্তব্য করেছেন “এক কবির গর্ভে আরেক কবির ঔরসে আমার জন্ম।” অর্থাৎ কাব্যচর্চার রুচি বা কুশলতা তাঁর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। অতি অল্প বয়স থেকে তিনি কবিতা লেখেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘প্রথম প্রত্যয়‘ প্রকাশ পায় ১৯৫৯ সালে। তখন তাঁর মাত্র একুশ বছর বয়স।
[the_ad id=”266918″]
নবনীতা দেবসেন যখন কবিতা লিখতে শুরু করেন, তখন বাংলা কবিতার জগতে বহু ভাঙচুর ঘটে চলেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের অনেক আগে থেকেই এই পালা শুরু হয়েছিল। নবনীতা যখন আত্মপ্রকাশ করেন, ততদিনে কবিতার পুরনো স্থাপত্যকীর্তির উপর নির্মম বুলডোজার চালিয়ে নব্যরীতির ইমারত খাড়া করতে মরিয়া একদল কবি। কিন্তু ‘প্রথম প্রত্যয়‘ পড়লে সেই ভাঙচুরের তেমন কোনও শব্দ পাওয়া যায় না। তাঁর সেই কবিতাগুলি সেকেলে ছিল না নিশ্চয়ই, কিন্তু এক নতুন কবির হাত ধরে কবিতার পথ তেমন কোনও আশ্চর্য বাঁক বদল করল বলেও মনে হয় না।

নবনীতা স্বীকার করেছেন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার আগে পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কিছু পড়েননি। প্রেসিডেন্সি কলেজের বন্ধু সংসর্গেই এক নতুন কাব্যমহলের দরজা ওঁর সামনে খুলে যায়। হয়তো সেই কারণেই ‘প্রথম প্রত্যয়‘ রচনাকালে তাঁকে কবিতার যে ভাষা বেছে নিতে হয়, তার আত্মা তুলনামূলকভাবে নতুন হলেও তার শরীর পুরনো। সেই কারণে কবিতাগুলিকে মন দিয়ে না পড়ে আধুনিক হিসেবে বিবেচনা করতে অনেকের অসুবিধা হতে পারে। আধুনিকতা দৃশ্যগত পোশাকের থেকেও বেশি মননের উপর নির্ভর করে। তাই নবনীতা দেবসেনের কবিতা পড়ার সময়ে সচেতন পাঠকের সে কথা মনে রাখা উচিত।
‘প্রথম প্রত্যয়‘-এর অন্তর্গত ‘বৃন্তহীন একটি গোলাপ‘ কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। কবিতার শুরু এই রকম: “কিন্তু, তুমি এখন তো জানো/ বর্ণ গন্ধ ফুলের জঞ্জালে/ বুক রেখে কিংবা মুখ রেখে/ কোনো লাভ নেই।” বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। কিন্তু চোখে লাগে ‘জঞ্জালে‘ শব্দটি। বর্ণ গন্ধ ফুল তাঁর পূর্ববর্তী সব কবিদের কাছে মহার্ঘ ছিল। নবনীতা এক কালোপযোগী তিক্ততা হানেন বর্ণ গন্ধ ফুলের প্রতি, ওই ‘জঞ্জালে‘ শব্দটি প্রয়োগ করে। কবিতাটিতে শুধুমাত্র ওই একটি শব্দই আধুনিকতার নিশান ওড়ায়।
[the_ad id=”266919″]
নবনীতার কবিতাগুলিকে মনে হয় তাঁর স্পষ্টশ্রুত স্বগতোক্তি। কবিতার মধ্যে দিয়ে নবনীতা আসলে যেন নিজের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছেন, তাঁর সব দুঃখ-শোক বা প্রণয়বাণী নিজেকেই শোনাতে চেয়েছেন। ওঁর সারাজীবনের কবিতাতেই এক অতৃপ্ত প্রেমতৃষ্ণা ধিকিধিকি জ্বলতে দেখা যায়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘স্বাগত দেবদূত‘-এর অন্তর্ভুক্ত ‘রথের মেলায়‘ কবিতার শুরু এই ভাবে: “রথের মেলায় তুমি বলেছিলে সঙ্গে নিয়ে যাবে।” তার পরের কয়েকটি পঙক্তি “…আমি এক খুরি পয়সা জমিয়ে বসে রইলাম দাওয়ায়…” কিন্তু দেখা যায়, অভীষ্টের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে “…আমার হাত-পা লম্বা হয়ে গেলো, ফর্দটা উড়ে গেলো হাওয়ায়,/ আমার খুরি ভরা ফুটো পয়সা তোরঙ্গ ভর্তি মোহর/ হয়ে গেলো- তোমার রথের মেলা থেকে আমার আর কেনবার কিছু রইল না।/ এবার আমি দাওয়া ছেড়ে উঠে যাব।” নবনীতার অনেক কবিতাতেই পাই এরকম নিষ্ফল প্রতীক্ষার হুতাশ।

নবনীতার কবিতার আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য, তার একাকীত্বের সুর। প্রেমের ডাকে সাড়া দিতে আকুল কবি। কিন্তু প্রণয়মুকুটের বদলে তাঁকে যেন চিরদিন শিরোধার্য করতে হয়েছে বিরহের বা নিঃসঙ্গতার কাঁটা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ‘ছুটি‘ কবিতাটি। কবি এক জায়গায় লিখছেন: “বকুল ফুলের গন্ধ তোমার সয় না বলেছিলে,/ আমার প্রপিতামহের বকুল গাছটা/ আমি তাই কেটে ফেলেছি।” এবং শেষে ভগ্নহৃদয়ের হতাশোক্তি “কিন্তু, কী আশ্চর্য প্রিয়, মানুষের অন্তরের খেলা!/ তবুও আমাকে তুমি ছুটি দিয়ে দিলে।”
আবার ‘দ্বীপান্তরী‘ কবিতায় পাই: “…বিনা প্রত্যাশায় আমি/ নিরাকার প্রিয়মন্যতায় পকেট ভরিয়ে নিয়ে/ এইবার দ্বীপে চ‘লে যাবো।/ সেই দ্বীপে কোনোদিন তোমাদের জাহাজ যাবে না।” ছুটি নিয়ে নির্বাসনে চলে যেতে চাওয়া অভিমানাহত মনকেই বারবার নবনীতা প্রকট করতে চেয়েছেন তাঁর কবিতায়।
[the_ad id=”270084″]
আত্মজাদের নিয়েও তাঁর কবিতা আছে। প্রথম সন্তান অন্তরাকে নিয়ে একটি ছোট সিরিজ ‘অন্তরা‘ ও দ্বিতীয় সন্তান নন্দনাকে নিয়ে ‘পুনশ্চ পুতুল‘ কবিতাটি ‘স্বাগত দেবদূত‘ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। ‘অন্তরা‘ কবিতাতে ফুটে উঠেছে স্নেহশীল মায়ের শঙ্কা– “সে যদি জিজ্ঞেস করে কিসের আশ্বাসে/ আমাকে এনেছো এই ঝলমলে আজব আলয়ে,/ কোন মহৎ উৎসবে আমি যোগ দেবো,যাবো?/ আমি ম‘রে যাবো ভয়ে।” আবার দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর উৎসারিত হয় এই রকম সত্যোপলব্ধি: “দুবার ঈশ্বরী সেজে গড়লুম ঈপ্সিত মানব/ কিন্তু মজা, সেখানেই নকল ঈশ্বর সাজা শেষ।/ তারপর থেকে তুমি পুনর্মূষিক মানুষিনী।” প্রেমের ব্যর্থতাই হয়তো সবরকম ভাবালুতার ঘোমটা খসিয়ে কবিকে মোহহীন বাস্তবে অভিজ্ঞ করে।
ব্যক্তিগত পরিসরেই বিচরণ করতে স্বচ্ছন্দ নবনীতার কবিসত্তা। আর সেই ব্যক্তিগত পরিসর যেন মুখরিত ক্লিষ্ট প্রলাপে।একটি উদাহরণ দেওয়া যাক –‘ প্রভুর কুকুর ‘ কবিতার প্রথম পঙক্তি: “প্রভুর কুকুর হয়ে কেটে গেছে অগুনতি বছর।/ কেবল বাতাস শুঁকে শত্রুতার গন্ধ চিনে নেওয়া…” আর শেষ এইরকম: “…বহুকাল প্রভুহীন,বহুকাল পথের কুকুর।/ বহুকাল নিজেই শিকার।” ব্যক্তিগত জীবনে তথাকথিত সাফল্য নবনীতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সেই সাফল্য তাঁর মনের বিধুরভাবকে মুছে দিতে পারেনি। তাঁর কবিতায় এই নিঃস্বতার সুর হয়তো উঠে আসে ব্যক্তিগত সম্পর্কের দীর্ণতা থেকেই।
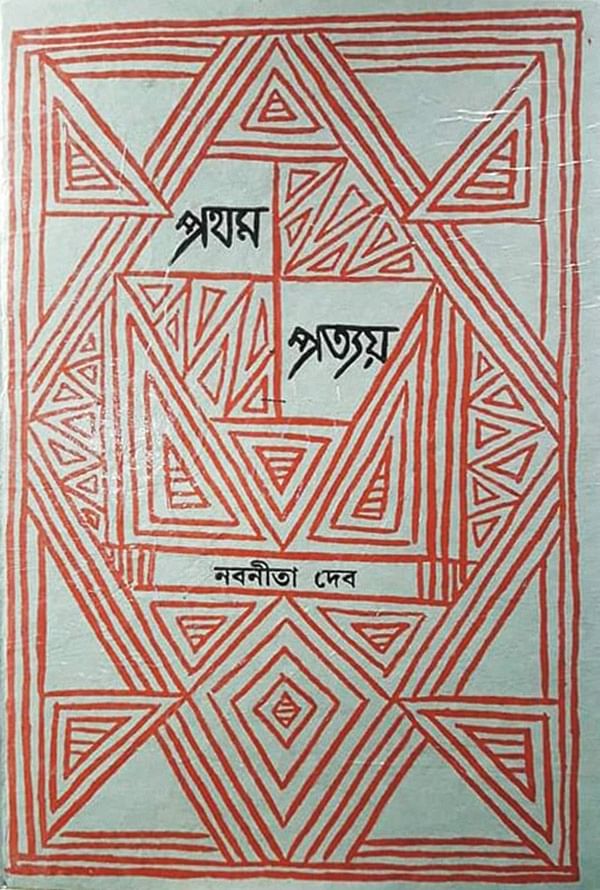
নবনীতা সেই শ্রেণির কবি, যিনি নিজের বক্তব্যকে পাঠকের কাছে জটিল অস্পষ্টতায় পেশ করতে চান না। তাই তাঁর কাব্যভাষা খুব সহজ। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর কবিতা সবলে সমস্ত পেশি ফুলিয়ে এক অত্যাশ্চর্য শক্তিরূপ প্রকাশ করতে পারে না। বড় বিনম্র তাঁর কাব্যভাষা। তাঁর উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির সঠিক পরিচয় পাঠককে পেতে হয় সেই নম্রতা স্পর্শ করে। কবিতার প্রচ্ছন্ন ব্যঞ্জনার ছটা আটপৌরে প্রকাশভঙ্গিতে হয় হৃদয়ের সম্পদ। যেমন ‘মশারি’ কবিতাটি। কবিতার শেষটি গভীর ব্যঞ্জনাময়: “…মোটমাট তুমি এখন/ কলকাতাতে নেই। কিংবা শান্তিনিকেতনেও না।/ মোটকথা, মশারির মধ্যে আমি আর/ এক মশারি রক্তখেকো মশার পিন পিন পন পন।”
সঙ্গী থাকা সত্ত্বেও এখানে একজনের নিঃসঙ্গ অবস্থা আর মশারি টাঙিয়েও মশার উৎপাত সইবার মধ্যে কবি যেন এক অদ্ভুত সমীকরণ তৈরি করলেন।
[the_ad id=”270085″]
আবার ‘রক্তে আমি রাজপুত্র‘ কাব্যগ্রন্থের ‘সময়: যৌবনকাল, ঠিকানা:পৃথিবী‘ নামের কবিতাটিও এই ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এই কবিতাতেও পাই এক প্রেমিকার দীর্ঘ প্রতীক্ষার কথা। কিন্তু যা ভাল লাগে তা হল, কবিতার শুরুতে ব্যঞ্জনাময় শব্দপ্রয়োগ। শুরুটা এই রকম: “কথা ছিল, দেখা হবে।/ টুকরো টুকরো ব্রিজ ও মিনার/ হাতে নিয়ে, প্রেমিক আমার-” কী সুন্দর লাগে এখানে এই ‘ব্রিজ ‘ও ‘মিনার‘ শব্দের সুষম ব্যবহার। ‘ব্রিজ‘ যেন মিলনের আর ‘মিনার‘ যেন স্মৃতির প্রতিশব্দে পরিণত হয়। এই রকম ব্যঞ্জনার প্রয়োগ দেখা যায় কবির মা-কে নিয়ে লেখা ‘বাতিটা ‘নামের কবিতায়। অসুস্থ মা-কে দিনরাত নার্স দেখভাল করছে। রাতে মা পড়ালেখায় ব্যস্ত। নার্স বাতি নেবাতে চাইলে শুনতে পাই “না,না,বাছা/ নিবিয়ে দিয়ো না আলো।” শেষে কবিকে বলতে শুনি “আরও একটি শব্দ দাও, নার্স মেয়ে, /আরও একটি দিন।” এখানে ‘শব্দ‘ই যেন ওষুধ হয়ে চিকিৎসার শক্তি জোগায়।
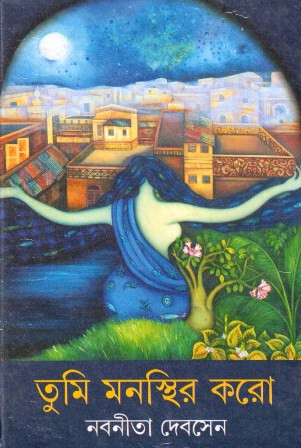
নবনীতার কবিতার ভাষার বেশি বিবর্তন হয়নি। ওঁর প্রথম যুগের কবিতার সঙ্গে শেষ দিকের কবিতার ভাষাগত ফারাক খুব বেশি চোখে পড়েনি। অর্থাৎ কবিতার ভাষা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন না তিনি।
তবে আরও একটি জিনিস চোখে পড়ে‒ ওঁর কবিতায় সময়ের ছাপ তেমনভাবে কোথাও পড়েনি। বাইরের ঘটনার অভিঘাত যেন ধাক্কা দিয়ে ওঁর লেখনীকে জাগাতে পারে না। তবে কিছু কবিতায় আমরা সময়ের পদশব্দ শুনতে পাই। আশির দশকের শেষার্ধে লেখা একটি কবিতার নাম ‘পৃথিবী বাড়ুক রোজ।‘ বিশ্বায়নের কবলে পড়া মানব সভ্যতার পরিসর দিনে দিনে সঙ্কুচিত হতে শুরু করেছে তখন। টেলিভিশন ও টেলিফোনের প্রসারে দেশকালের ব্যবধান ঘুচে যাবার সূচনা তারও আগে থেকেই। এই অবস্থার বিরুদ্ধে কবির দৃঢ় ঘোষণা: “বিশ্ব ছোটো হয়ে যাক হস্তধৃত আমলকির মতো,/ এ আমার প্রার্থনীয় নয়। আমি চাই পৃথিবী ছড়াক/ আমার পৃথিবী আমি পরিশ্রম করে খুঁজে নেবো।” এবং শেষে মানবসভ্যতার প্রতি দার্শনিকসুলভ সতর্কবাণী: “পশুপাখি উদ্ভিদেরা কিছুমাত্র বিস্মিত হবে না/ ওরা সব জেনে গেছে, মানুষের বেশি দেরি নেই।”
‘নাজমা‘ নামের কবিতাটিতেও এক জ্বলন্ত সময়ের তাপ লেগে থাকতে দেখা যায়। আজকের দিনেও কবিতাটি প্রাসঙ্গিক। কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। নাজমার বর অফিস থেকে ফিরলে দু’জনের টিভি কিনতে যাবার কথা। কিন্তু নাজমার বরের আর ফেরা হয় না। হিন্দু মৌলবাদী দলের আক্রোশের আগুনে তাকে পুড়ে মরতে হয়। কবির গলায় কবিতার শেষে বেজে ওঠে এক বিপ্লবী সুর: “আমরা ওকে অন্য জগৎ দেব/ প্রতিজ্ঞাতে বুক বেঁধে তুই দাঁড়া / অন্য জগৎ এই মাটিতেই আছে/ আমরা ওকে আস্ত আকাশ দেব/ নাজমা,আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না।” গুজরাত দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লেখা এই কবিতা পাঠকের মনোযোগ অবশ্যই কাড়বে। ‘আসাম, ১৯৮০‘ নামের কবিতাটিতেও ফুটে ওঠে অসহায়ের উপর অত্যাচারের ছবি। কয়েকটা পঙক্তি এইরকম: “কাচের গেলাস ভাঙছে এতে আর আশ্চর্য কী আছে/ আশ্চর্য কেবল এই রক্তের নিনাদ/ এই মত্ত আলোড়ন/ ভূকম্পনের মতো নড়ে ওঠা পায়ের জমিন/ এই রুদ্ধশ্বাস…..”

সামগ্রিকভাবে নবনীতার কবিতায় আছে এক নির্জন এককের সুর। এমনকী যখন পুরাণ বা পূর্ববর্তী সাহিত্য থেকে কোনও চরিত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটাচ্ছেন কবিতায়, তখন সেই চরিত্রের সঙ্গেও যেন ওতপ্রোত হচ্ছে তাঁর আত্মিক যোগ। ‘পুতুল নাচের ইতিকথা‘ উপন্যাসের চরিত্র কুসুমকে তিনি নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করতে চেয়েছেন। ‘শশীকে কুসুম‘ নামের এই কবিতায় কুসুমের ব্যাকুল আর্তির সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত আর্তি হাত মিলিয়ে দোস্তি করে নেয়। আবার ‘সীতার পাত্রসন্ধানে‘ কবিতায় পাওয়া যায় জনক রাজার স্নেহের দুলালী ঘরোয়া সীতার ছবি। নারীর বিবাহকেন্দ্রিক বিপন্নতা এই কবিতায় সাধারণ সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়।
আগেই বলেছি যে নবনীতা দেবসেন সহজ ভাষার কবি। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা নিতান্তই কম। এই স্বল্প পরিসরেই নবনীতা একজন সার্থক বিরহজর্জর কবি। যথাযোগ্য প্রেমের জন্য হয়তো তাঁর এক চিরকালীন প্রতীক্ষা ছিল। নবনীতা এক জায়গায় স্বীকার করেছেন “আমার কোনো কাব্যাদর্শ নেই।” তবে আমার মনে হয়েছে, এই আত্মসমাহিত ও নিঃসঙ্গ সুরের সাধনাই তাঁর অন্যতম কাব্যাদর্শ ছিল।
প্রীতম পেশায় শিক্ষক। পড়াশোনা ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে। লেখালিখির শখ ছোটবেলা থেকেই। 'একুশ শতাব্দী' নামক একটি লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত দীর্ঘ ছয় বছর। মূলত ছোটগল্পকার হিসেবেই তাঁর পরিচিতি। বহু লিটল ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয়। দেশ পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হয় ২০১৬ সালে।


























5 Responses
পরিশীলিত কথন,ভালো লাগলো
চিন্তার প্রসারেতায়,মননের প্রত্যয়ে,প্রকাশের সপ্রতিভতায়
ঝকঝকে নিবন্ধটি পাঠ করে মুগ্ধ হলাম। তরুণ নিবন্ধকার প্রীতম বিশ্বাসের জন্যে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রকাশক ও সম্পাদকের নির্বাচনের প্রতিও রইল অশেয শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।
ধন্যবাদ
ধন্যবাদ l
চিন্তার প্রসারেতায়;মননের প্রত্যয়ে;প্রকাশের সপ্রতিভতায় দীপ্র নিবন্ধটি পাঠ করে মুগ্ধ হলাম। তরুণ নিবন্ধকার প্রীতম বিশ্বাসের জন্যে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। প্রকাশক ও সম্পাদকের বিদগ্ধ এযণার প্রতিও রইল অশেয শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন।