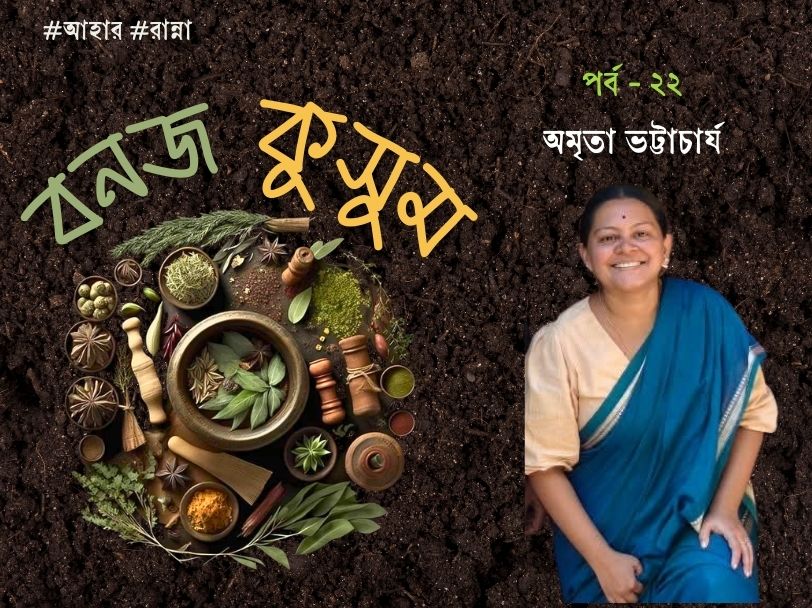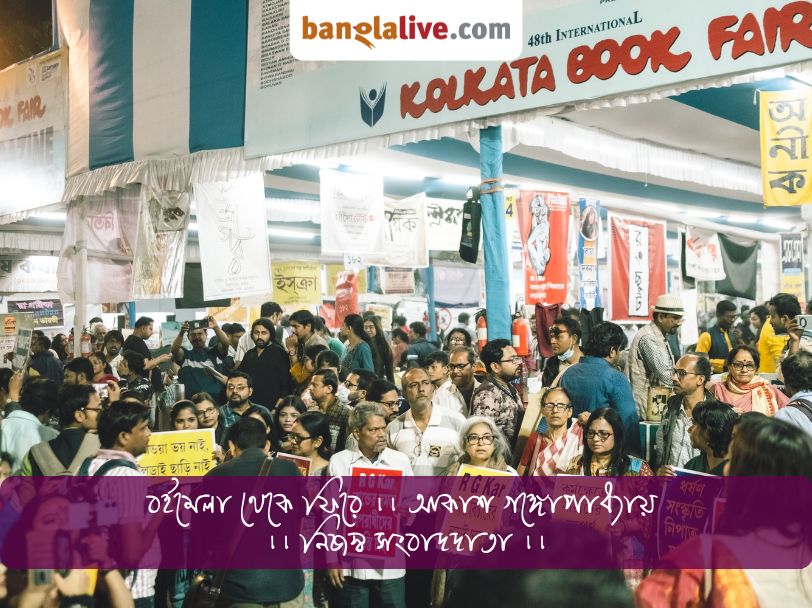এ কোন মাঠ?
“সে তাহার বাবার মুখে, দিদির মুখে, আরও পাড়ার কত লোকের মুখে কুঠীর মাঠের কথা শুনিয়াছে, কিন্তু আজ তাহার প্রথম সেখানে আসা! ঐ মাঠের পরে ওদিকে বুঝি মায়ের মুখের সেই রূপকথার রাজ্য? শ্যাম-লঙ্কার দেশে, বেঙ্গমা-বেঙ্গমীর গাছের নিচে, নির্বাসিত রাজপুত্র যেখানে তলোয়ার পাশে রাখিয়া একা শুইয়া রাত কাটায়? ও-ধারে আর মানুষের বাস নাই, জগতের শেষ সীমাটাই এই। ইহার পর হইতেই অস্মভবের দেশ, অজানার দেশ শুরু হই হইয়াছে।”
এ পান্তীর মাঠের নয় কথা নয়। এ কুঠীর মাঠের কথা। সেই কুঠীর মাঠ, যার অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে আছে অপু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি অপু। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অপু, কুঠীর মাঠ কী করে এসে পৌঁছয় এমন এক রচনায়, যে রচনার সঙ্গে আপাতভাবে কুঠীর মাঠের কোন যোগসাজসই থাকা সম্ভব নয়। কারণ আমাদের রচনার কেন্দ্রে আছে অন্য একটি গ্রন্থ, যা এখনও পর্যন্ত অনামী, অজানা এক লেখিকার সৃষ্টি।
কে সে লেখিকা? বইয়ের নামটাই বা কী? অনুলেখকের বক্তব্য জেনে নেওয়া যাক।
“কৃষ্ণকামিনী দাসী (দত্ত) (বাং ১৩১০…) বাঁকুড়ার এক গ্রামে জন্ম নেন। অল্প বয়সে বিবাহ হয়ে কলকাতা আসেন ১৩১৯ বঙ্গাব্দে। থাকেন ১৩২৬ অব্দি। তাঁর আট বছরের কলকাতা বাস নিয়ে এই আত্মকাহিনী – পান্তীর মাঠ।”
তবে কি পান্তীর মাঠ ভৌগোলিকভাবে কুঠীর মাঠের নিকটবর্তী কোনও স্থানে? অপুর কুঠীর মাঠ তো সেই তার গ্রাম নিশ্চিন্দিপুর থেকে কিছু দূর, পায়ে চলা পথে। “দুইপাশে ঝোপে-ঝাপে ঘেরা সরু মাটির পথ বাহিয়া।” নিশ্চিন্দিপুরের কয়েকজন লোক সরস্বতীপুজোর বিকেলে নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে গ্রামের থেকে একটু দূরে কুঠীর মাঠে গেছিল। কিন্তু পান্তীর মাঠ? তার ভৌগোলিক অবস্থান কোথায়? আন্তর্জাল উত্তর দিচ্ছে পান্তীর মাঠ কিন্তু মোটেই অলীক কোনও স্থানাঙ্ক নয়। বাস্তবের মাটিতে একান্ত নির্দিষ্টভাবেই ছিল পান্তীর মাঠ। এবং তা ছিল অধুনা বিধান সরণী, তৎকালীন কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের শিবনারায়ণ দাসের গলির গা ঘেঁষে। আরও অবাক করা কথা, শিবনারায়ণ দাসের গলির অবস্থান রীতিমত মানচিত্র স্থানাঙ্ক-সহ খুঁজে পাওয়া যায়, প্রায় একশো বছর পরেও।
আরও পড়ুন: বাংলালাইভের বিশেষ ক্রোড়পত্র: সুরের সুরধুনী
অতএব, এই সেই পান্তীর মাঠ, এই সেই শিবনারায়ণ দাসের গলি, যাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে সমগ্র কাহিনিপট। তাই পান্তীর মাঠ, শিবনারায়ণ দাসের গলি তো শুধু কোনও ভৌগোলিক নাম নয়, তা ভূগোলকে ছাপিয়ে ইতিহাসের অংশ, কখনও নিজেও ইতিহাস। কাজেই ‘পান্তীর মাঠ’ গ্রন্থটির আলোচনার ভরকেন্দ্রে থেকে যায় তারা, শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে তারা নামকরণের যাথার্থ্য বহন করছে। এই কারণেও যে, কলকাতাবাস যদি হয় এই আত্মচরিতের প্রেক্ষাপট, সেই কলকাতাবাসের কেন্দ্রে আছে পান্তীর মাঠ। যদি ধরে নেওয়া যায়, এক অপূর্ব অলৌকিক সম্পর্কের অনুভূতি থাকে এই গ্রন্থের কেন্দ্রে– সেখানেও লগ্ন হয়ে আছে পান্তীর মাঠ, সেখানেও আছে শিবনারায়ণ দাসের গলি। আর তৎকালীন কলকাতার যে ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা অনুলেখক তাঁর ভূমিকায় বলেছেন– ‘সবার ওপর, টুক্টুক করে ফুল ফোটার মতো নিঃশব্দে উপস্থিতি সেকালিনী কলকাতার” – সেই কলকাতাকে যে দূরবিনে চোখ রেখে দেখা হয়েছে, সে দূরবিনও পান্তীর মাঠের কোনও বাড়ির খড়খড়িতেই রাখা।
কৃষ্ণকামিনী দেবীর নিজের কথাতেই ফেরা যাক। ঠিক কীভাবে বাঁকুড়ার গ্রাম থেকে এসে পৌঁছলেন কলকাতায়? কীভাবে পান্তীর মাঠ হয়ে উঠল সেই বালিকা থেকে কিশোরী হয়ে ওঠা মেয়েটির জীবনকেন্দ্র? আর যে কারণে এই স্মৃতিচরিত লিপিবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছেন বলে লেখিকার দাবি, সেই ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং সম্পর্কের এক পরত থেকে অন্য পরতে উত্তরণের কথা, সেই কারণটি, সেই তথাকথিত সামাজিক নিয়মের বহিভূর্ত সম্পর্কের লেখচিত্রটি? তবে কৃষ্ণকামিনী দাসী তাঁর নিজের নাম নয়। অনুলেখক নিজেই স্পষ্টভাবে বলেছেন– ‘সবদিক বিবেচনা করে লেখিকার নাম পরিবর্তন করাই সাব্যস্ত হল।“
কী সেই সবদিক? অনুলেখকের ভাষায়: “কিন্তু একই সঙ্গে আবার তিনি নিজের পরিবারের সম্মান নিয়েও চিন্তিত। জীবনীর মধ্যেই সেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি…।” অনুলেখকের দুঃশ্চিন্তার কারণ অমূলক নয়। কারণ লেখিকা যে নিজেই বলেছেন… “প্রথমেই বলি, আমার এ কাহিনী কেহ পড়িবে না। আমি ইহা লুকাইয়া রাখিব স্থির করিয়াছি সকলের চক্ষুর অন্তরালে। কারণ পড়িলে অনর্থ হবে।” তবু তিনি একথা লিপিবদ্ধ করেন কেন?
তার কারণ স্বপ্ন। ভোররাতের স্বপ্ন। মূল ঘটনার বহুদিন পরে, তিনি যখন প্রায় বৃদ্ধা, সেই সময় স্বপ্নে আসেন এই ‘কাহিনির নায়ক’। ধুতি ও পিরান পরিহিত তার চেহারা, মুখে মিষ্টি হাসি সবই যেন তার অবিকল আছে, সে লেখিকাকে দেখে রসিকতা করে বলে সে কেমন বৃদ্ধা হয়েছে। আনন্দে কান্না আসে লেখকার – “স্বপ্নে নয়, বাস্তবে। এই স্বপ্ন প্রতিদিন, প্রায় দুমাস ধরে দেখেন তিনি এবং বুঝতে পারেন – “এই অপূর্ব অতীতই আমার মূল, তাহা হইতেই আমার জীবনবৃক্ষ বাহির হইয়াছে, অতএব তাহাকে ভুলিলে চলিবে না।” তাই যেন লিখতে বসা। “এক্ষণে এই রচনার সাহায্যে অনেককাল পরে আবার যেন তাহার সহিত কথা বলিতেছি।”

লেখিকা যাই বলুন, এ কাহিনি স্মৃতিচারণ হলেও সে স্মৃতি কিন্তু একটি মাত্র স্মৃতির কথকতা হয়ে থেমে থাকেনি, হয়ে উঠেছে উনবিংশ শতকের একটি গ্রামের মেয়ের সত্যকার জীবনচরিত। নয় বছর বয়সে বিয়ে হয় তার, স্বামীর বয়স চোদ্দো, বাংলায় ১৩১৯ সালে। মনে পড়ে যায় আরও বিখ্যাত চরিত্রদের কথা। তারা সত্যবতী, সুবর্ণলতা– আশাপূর্ণা দেবীর সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী, অথচ চূড়ান্ত বাস্তব চরিত্ররা। সত্যবতীরও বিয়ে হয় নয় বছর বয়সে, পরে কলকাতায় আসে সেও। কিন্তু সে ছিল নামী লোকের মেয়ে, আমাদের লেখিকার পিতা যোগেশচন্দ্র ছিলেন সজ্জন ও সম্বলহীন। “সহায়সম্বলহীন পিতা সুপাত্র পাইয়া অনেক যোগাড়যন্ত্র করিয়া চাহিয়া চিন্তিয়া এই বিবাহের আয়োজন করিয়েছিলেন।” তাই লেখিকার জীবন চলল অন্য খাতে। “এক নয় বছর বর্ষীয়া বালিকা কেবল শাঁখা-সিন্দুর সম্বল করিয়া কোন তেপান্তরে যাত্রা করিল।”
কলকাতার যাত্রা পথের বর্ণনা যে কী অপরূপ, কী নিখঁত। সেখানে প্রথম দেখা রেলগাড়ির উত্তেজনা যেমন আছে, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দেখা নানারকম মানুষ যেমন আছে, তেমনই মাটির ভাঁড়ে আনা লুচি তরকারির কথাও আছে। “চুপসানো লুচি চিরকালই আমার দু’চক্ষের বিষ, কিন্তু এক্ষণে খাইতে বেশ লাগিল।” দীর্ঘ যাত্রাপথ পেরিয়ে ন’বছরের বালিকাবধূ তার স্বামী ও মামাশ্বশুরের সঙ্গে এসে পৌঁছয় শিবনারায়ণ দাসের গলিতে, যেখানে নিঃসন্তান মামাশ্বশুরের বাড়িতে থাকবে তারা। এই গলির ঠিক পাশেই পান্তীর মাঠ পেরিয়ে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট। শিবনারায়ণ দাস গলির ভেতর থেকে পান্তীর মাঠ পেরিয়ে দেখা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটের যে অপূর্ব বর্ণনা, তাতে প্রশ্ন জাগে, এই একটি কিশোরী চোখ এত খুঁটিনাটি দেখল কী করে?
সে বর্ণনায় রাস্তার দুধারে “দশ বিশ হাত অন্তর সুন্দর কৃষ্ণচূড়া গাছ”-ও যেমন আছে, খোলা চালের ঘরের বর্ণনাও যেমন আছে, তেমন ‘ব্রাহ্মসমাজ বাটী’র কথাও আছে। এই তথ্যেরা ঐতিহাসিকভাবে সত্য, তা বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। কারণ ব্রাহ্মসমাজ বাটীর ঠিকানা ১৩নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, আর যে সময়কালের কথা লেখিকা বলছেন, তখন কেশবচন্দ্র সেন আর আসেন না সেখানে– কারণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে বিভক্ত হয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন ইন্ডিয়ান ব্রাহ্মসমাজ। তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আসেন সেখানে। লেখিকাও তাই বলেন “ঐ স্থলে আমি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বেশ কয়েকবার দেখিয়াছিলাম।”
এই সেই পান্তীর মাঠ, এই সেই শিবনারায়ণ দাসের গলি, যাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে সমগ্র কাহিনিপট। তাই পান্তীর মাঠ, শিবনারায়ণ দাসের গলি তো শুধু কোনও ভৌগোলিক নাম নয়, তা ভূগোলকে ছাপিয়ে ইতিহাসের অংশ, কখনও নিজেও ইতিহাস। কাজেই ‘পান্তীর মাঠ’ গ্রন্থটির আলোচনার ভরকেন্দ্রে থেকে যায় তারা, শুধুমাত্র এই কারণে নয় যে তারা নামকরণের যাথার্থ্য বহন করছে। এই কারণেও যে, কলকাতাবাস যদি হয় এই আত্মচরিতের প্রেক্ষাপট, সেই কলকাতাবাসের কেন্দ্রে আছে পান্তীর মাঠ।
এইভাবে ইতিহাসের কলকাতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি আমরা, ভুলে যাই কোনও এক সম্পর্কের ইতিহাস রচনা করতে এর অবতারনা। আর সেই কাহিনি যে কী সুনিপুণ গদ্যকৌশলে লেখা, তার খুঁটিনাটি পাঠকের কাছে উন্মোচন না করাই উচিত। সাহিত্যের রসের এই প্রকার ক্ষতি না করাই উচিত। কারণ শেষপর্যন্ত স্নায়ু টানটান হয়ে থাকে, কী হবে নায়িকার? কোনও অন্যায় না করে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়ে দুটিকে সমাজের রক্তচক্ষুর কাছে শাসিত হতে হবে না তো? সেই উত্তরের জন্য পড়তেই হবে পান্তীর মাঠ। খুঁজে নিতে হবে সাহিত্যের, কলকাতার ইতিহাসের গুপ্তধন যা অপঠিত থাকলে, পাঠের ক্ষতি পাঠকের ক্ষতি। চলুন, অপুর চোখ দিয়ে, সত্যবতীর চোখ দিয়ে, কৃষ্ণকামিনীর চোখ নিয়ে ঘুরে আসি পান্তীর মাঠ।
পরিশেষে, যে কথা না বললেই নয়, এ বইটি প্রকাশ করে তামাম পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ হয়েছে অভেদ ফাউন্ডেশন। অভেদ ফাউন্ডেশনের তরফে বিশ্বজিৎ মিত্র বইটির মুখবন্ধ রচনা করেছেন। বইটি অনুলিখন ও প্রকাশের যাবতীয় উদ্যোগ তাঁরই। কৃষ্ণকামিনীকে তাঁর ‘একান্ত আপনার জন’ বলে উল্লেখ করে বিশ্বজিৎবাবু জানিয়েছেন, কীভাবে পাণ্ডুলিপি হাতে পাওয়ার পর কৃষ্ণকামিনীর ভাষা ও বক্তব্যের দৃঢ়তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। অভেদ ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। আরও অনেক কৃষ্ণকামিনীর মনের কথা, প্রাণের ব্যথা এভাবে ছাপার অক্ষরে তুলে আনার অঙ্গীকার থাকুক অভেদ ফাউন্ডেশনের পাথেয় হয়ে, এই শুভকামনা জানাই।
বই: পান্তীর মাঠ
লেখক: শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী
অনুলেখন: বিশ্বজিৎ মিত্র
প্রকাশক: অভেদ ফাউন্ডেশন
প্রকাশকাল: ২০২১
বিনিময়: ৩৭৫ টাকা
ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।