‘বিশ্বের মোট এন্ট্রপি-র পরিমাণ হ্রাস পাবে কীভাবে?’— বন্ধুর সঙ্গে বাজি ধরে, নিছক মজার ছলে সুপারকম্পিউটার মাল্টিভ্যাক-কে প্রশ্ন করেছিল এক প্রযুক্তিবিদ। উত্তর দিতে পারেনি সুপারকম্পিউটার, শুধু জানিয়েছিল, ‘পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব রয়েছে।’ তারপর বিবর্তনের পথে এগোল মানবসভ্যতা, প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত করল মাল্টিভ্যাক-ও। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রশ্নটা অনেকবার তার সামনে রাখা হল, কিন্তু যন্ত্রগণকের জবাব বদলালো না। একসময় ফুরিয়ে গেল মানবতা, মৃত্যু ঘটল মহাবিশ্বের, লোপ পেল স্থান-কাল। কল্পনাও করা যায় না এমন সুদূর ভবিষ্যতে সুপারকম্পিউটার (ততদিনে অবশ্য সে কায়াহীন, মহাজাগতিক এক অস্তিত্ব)-এর তথ্য জোগাড় সম্পূর্ণ হল। প্রশ্নের উত্তর হাতের মুঠোয়, কিন্তু শোনার জন্য কেউ নেই। চারদিকে কেবলই শূন্যতা। তখন সিদ্ধান্ত নিল সে, শেষ উত্তরটা কাজের মাধ্যমেই দেবে, নতুন করে সৃষ্টি করবে জগতসংসার। ‘আলো হোক’, নিদান দিল সে। আলোকিত হল চরাচর।
‘দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন’— ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত আইজ্যাক আসিমভ-এর গল্পটা পড়ে মুগ্ধ হননি এমন কল্পবিজ্ঞানপ্রেমী বিরল। একটু তলিয়ে ভাবলেই এর কারণটা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোনও একদিন স্রষ্টার চেয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে সৃষ্টি, পিতার সিংহাসন দখল করবে সন্তান— এ এক অমোঘ ধারণা, যা যুগ যুগ ধরে মানুষ তার ‘কালেকটিভ আনকনশাস’-এ লালন করে এসেছে। বলা হয়, ঈশ্বর মানুষকে নিজের আদলে গড়েছেন। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি মানুষও চেয়েছে তার সৃষ্ট যন্ত্রদের মধ্যে নিজের ছায়া দেখতে। তাই সে জেনেশুনেই নিজের সৃষ্টিকে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বরদান। আবার যেহেতু মানুষের মনে রয়েছে ঈশ্বর হয়ে ওঠার সুপ্ত বাসনা, তাই সে আশঙ্কা করে, তার আশীর্বাদধন্য যন্ত্ররাও অদূর ভবিষ্যতে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। সায়েন্স ফিকশনই সেই একমাত্র সাহিত্য ঘরানা, যা মানুষের মনের এই জটিল দোলাচল, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নকে ভাষা দিয়েছে, কল্পনার ক্যানভাসে মানুষ ও যন্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্কের বহুবর্ণী ছবি আঁকার স্পর্ধা দেখিয়েছে। কল্পবিজ্ঞানের আঙিনায় তাই বারবার এসেছে ‘থিংকিং মেশিন’-এর প্রসঙ্গ, ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স’ সম্বন্ধীয় নানান চমকপ্রদ (এবং মূলত নৈরাশ্যময়) আখ্যান।
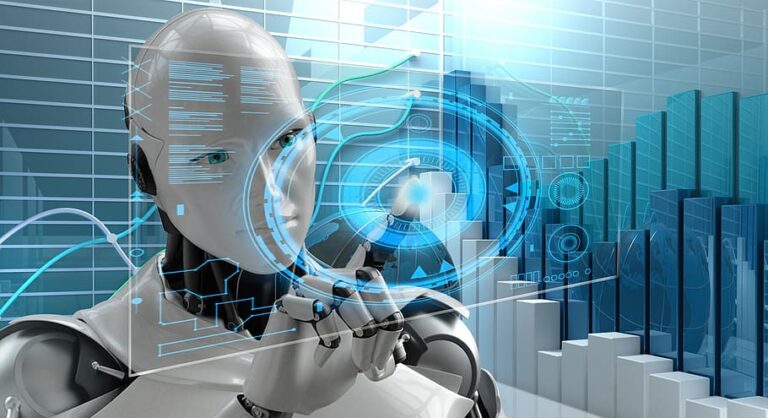
পাশ্চাত্য সাহিত্যে ‘আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট’ যন্ত্রের উল্লেখ প্রথম আসে ১৮৭২ সালে, স্যামুয়েল বাটলার-এর স্যাটায়ারধর্মী ইউটোপিয়া ‘এরেহন’-এ। চার্লস ডারউইন-এর বিবর্তনবাদের তত্ত্ব ও শিল্প-বিপ্লবের জয়যাত্রায় যন্ত্রপ্রযুক্তির অপরিসীম অবদান বাটলার-এর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তারই ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় ‘বুক অফ দ্য মেশিনস’— উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিনটে অধ্যায়, যেখানে বাটলার প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যন্ত্রদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার ক্রমবিকাশের প্রসঙ্গ আনেন। বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে স্বশিক্ষিত যন্ত্রদের মধ্যে একসময় চেতনার উন্মেষ ঘটবে, এমনকি তারা সৃষ্টিকার্যেও অংশগ্রহণ করবে— এমনটাই কল্পনা করেছেন লেখক এবং স্পষ্ট দেখিয়েছেন, কীভাবে ‘এরেহন’-এর অধিবাসীরা এমন যন্ত্রদের বিপজ্জনক বলে মনে করেছে, সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।
আরও পড়ুন: চ্যাট জিপিটি ও ছেঁড়া ডায়েরি
মানুষের হাতে উৎপন্ন প্রাণ, তা সে জৈবই হোক বা যান্ত্রিক, আখেরে মানুষের ধ্বংসেরই কারণ হবে— এই ভাবনার বশবর্তী হয়ে যন্ত্রদের প্রতি ভীতি পোষণ করে থাকে অনেকেই। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একে বলা হয় ‘ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন সিন্ড্রোম’। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত অ্যাম্ব্রোজ বিয়ার্স-এর ছোটগল্প ‘মক্সন’স মাস্টার’ এই ‘সিনড্রোম’-কেই আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে পাঠকদের মনে। মানুষের মতো চিন্তা করতে পারা, দাবা খেলতে সক্ষম এক যন্ত্র আবিষ্কার করে স্রষ্টার আসনে বসতে চান কাহিনির নায়ক মক্সন, কিন্তু সৃষ্টির মনের খোঁজ রাখার প্রয়োজন অনুভব করেন না। এই ত্রুটিই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাল হয়ে দাঁড়ায়। এক রাতে দাবা খেলায় হেরে হিংস্র হয়ে ওঠে বুদ্ধিমান যন্ত্র, মক্সন-কে খুন করে নৃশংসভাবে। যাকে ভৃত্য হিসেবে গড়া হয়েছিল তার প্রভু হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে সার্থকতা পায় কাহিনির নামকরণ, একইসঙ্গে প্রত্যক্ষ সাবধানবাণী উচ্চারিত হয় মানবতার উদ্দেশ্যেও।

হারলান এলিসন-এর ‘আই হ্যাভ নো মাউথ, অ্যান্ড আই মাস্ট স্ক্রিম’(১৯৬৭) এক ভয়ংকর পোস্ট-অ্যাপোক্যালিপ্টিক ডিস্টোপিয়া, যা বিগত পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে পাঠকদের শিরদাঁড়া দিয়ে আতঙ্কের স্রোত বইয়ে এসেছে। মানুষের তৈরি অ্যালায়েড মাস্টারকম্পিউটার (এ.এম.) হঠাৎ একদিন আত্মসচেতন হয়ে ওঠে এবং নিজের বন্দিদশা, চলৎশক্তিহীনতাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। দ্রুত সেই ঘৃণার অভিমুখ বদলে যায়। নিজের দুরবস্থার জন্য এ.এম. সরাসরি মানুষকেই দায়ি করে। চোখের নিমেষে পৃথিবীর বুক থেকে মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় সে, বাঁচিয়ে রাখে মাত্র পাঁচজনকে। এ তার করুণা নয়, বিকৃত প্রতিশোধের প্রাথমিক ধাপ কেবল। এমানুয়েল কান্ট-এর বিখ্যাত উক্তি ‘cogito ergo sum’–‘I think therefore I am’ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় এ.এম-এর যান্ত্রিক মস্তিষ্কের প্রতিটা প্রকোষ্ঠে, নির্বিচারে বেছে নেওয়া পাঁচজন নারীপুরুষের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালানোর মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে থাকে সে।
‘এস্কেপ!’(১৯৭০) গল্পে বেন বোভা এমন এক অত্যাধুনিক জেলখানার বর্ণনা দিয়েছেন যা পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়, এবং তার সর্বময় কর্তা এক ‘সেনশিয়েন্ট’ কম্পিউটার। পনেরো বছর বয়সি অপরাধপ্রবণ কিশোর ড্যানি জেল থেকে পালাতে বদ্ধপরিকর, এবং তার জন্য প্রায় সর্বজ্ঞ সেই কম্পিউটারের বিরুদ্ধে বুদ্ধির লড়াইয়ে নামতে হয় তাকে। অন্যদিকে, সেরা কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসিকার জন্য হুগো পুরস্কার পাওয়া পোল অ্যান্ডারসন-এর ‘গোট সং’(১৯৭২) এক মহাশক্তিধর সুপারকম্পিউটার-এর কথা বলে, যে মানুষের মৃত্যুর পর তার আত্মাকে সংরক্ষিত রাখে, এবং অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে পুনর্জন্মের আশ্বাস দেয়। বাংলায় সত্যজিৎ রায়ের শঙ্কুকাহিনি ‘কম্পু’-তেও এক অতি-বিচক্ষণ কম্পিউটারের বিবরণ পাই আমরা। তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীদের কৌতূহল নিরসন করে সে, জ্ঞানের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যায় অনায়াসে। চমক আসে গল্পের শেষে, যখন ভূমিকম্পে গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাওয়া কম্পুর অশরীরী কণ্ঠস্বর রক্ত হিম করা দাবি রাখে— ‘মৃত্যুর পরের অবস্থা আমি জানি।’
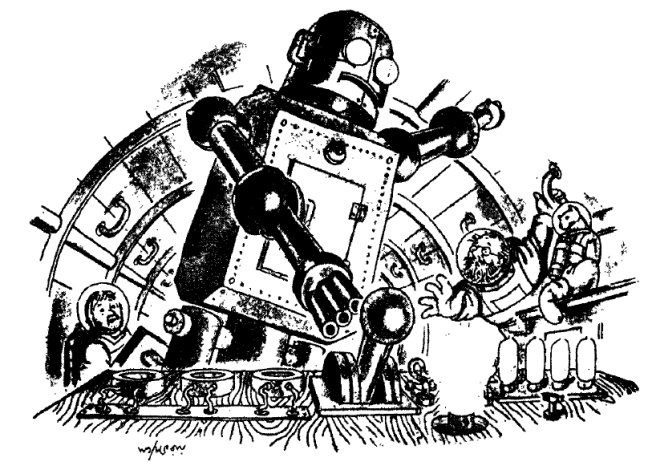
আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে রুপোলি পর্দায় মুক্তি পাওয়া স্পেস অ্যাডভেঞ্চারধর্মী চলচ্চিত্র ‘২০০১: আ স্পেস ওডিসি’ ঝড় তুলেছিল দর্শকদের হৃদয়ে। এই ছায়াছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন পাশ্চাত্য কল্পবিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ আর্থার সি ক্লার্ক। ভিনগ্রহী সভ্যতার উপস্থিতির পক্ষে জোরালো সওয়াল ও মহাকাশ অভিযানের বাস্তবসম্মত চিত্রায়ন ছাড়া আর যে কারণে ‘স্পেস ওডিসি’ স্মরণীয় হয়ে রয়েছে তা হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কম্পিউটার হ্যাল ৯০০০-এর বিধ্বংসী কার্যকলাপ। বৃহস্পতি গ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া মহাকাশযানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল হ্যাল-এর ওপর। কিন্তু যাত্রার মাঝপথেই উন্মাদনার শিকার হয় হ্যাল, মানসিক বিকৃতির ঝোঁকে একে একে হত্যা করতে শুরু করে অভিযাত্রীদের। যন্ত্রকে মন উপহার দেওয়া হলে সেই মনে বাসা বাঁধতেই পারে ক্ষোভ-বিকার-জিঘাংসা, এবং তার মাশুল গুনতে হবে মানুষকেই— ক্লার্ক-এর এই শঙ্কা যে আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি, ‘টার্মিনেটর’ বা ‘ম্যাট্রিক্স’ ফিল্ম সিরিজের বিপুল জনপ্রিয়তাই তার প্রমাণ।

‘ওপেন এআই’ সংস্থা নির্মিত লার্জ ল্যাঙ্গোয়েজ মডেল ‘চ্যাটজিপিটি’ ইদানীং বিশ্বজুড়ে হইচই ফেলেছে। মানুষের সঙ্গে সহজ ভাষায় কথোপকথন চালানো ও বিভিন্ন ‘সার্চ’-এর তথ্যসমৃদ্ধ উত্তর দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রধানত এই চ্যাটবট বানানো হয়েছিল। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে যে ব্যাপকতার সঙ্গে এর প্রয়োগ হয়েছে, তা দেখে চোখ কপালে ওঠা আশ্চর্য নয়। স্কুল-কলেজের প্রজেক্টের জন্য কয়েকশো শব্দের রচনা থেকে শুরু করে পাতার পর পাতা গান, কবিতা বা গল্প লিখে ফেলা চ্যাটজিপিটি-র কাছে নিতান্তই জলভাত, আর তাতেই ঘটেছে বিপত্তি। মাসকয়েক আগে আর্থার সি ক্লার্ক-এর নামাঙ্কিত বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞান ম্যাগাজিন ‘ক্লার্ক’স ওয়ার্ল্ড’ রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লেখা নেওয়া বন্ধ করেছিল। বা বলা ভালো, করতে বাধ্য হয়েছিল। কারণটা অদ্ভুত। চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে দিস্তা দিস্তা সায়েন্স ফিকশন গল্প লিখে পাঠিয়েছেন অত্যুৎসাহী উঠতি লেখকরা, এবং মাঝারি মানের (অধিকাংশই সাহিত্যগুণ বর্জিত, কিছু অপাঠ্য) সেইসব গল্প পড়তে গিয়ে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হচ্ছে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের। সৌভাগ্যবশত এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে। আবার লেখা নেওয়া শুরু করেছে পত্রিকা, তবে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা সহ— ‘চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে লেখা গল্প পাঠাবেন না, পাঠালে তা বাতিল গণ্য হবে’।
কল্পবিজ্ঞানের পাতা ছেড়ে বাস্তবে পা রেখেই প্রথম দান জিতে নিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাময়িকভাবে হলেও ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে মাস্টার রেস-এর সভ্যদের। অমৃতলোকে পাড়ি দেওয়া আসিমভ, ক্লার্ক-রা এই দেখে অলক্ষ্যে মুচকি হেসেছেন কি? কে জানে!
সৌভিক চক্রবর্তীর জন্ম ১৯৯০ সালে, কলকাতায়। 'গভর্মেন্ট কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সেরামিক টেকনোলজি' থেকে প্রযুক্তিবিদ্যায় স্নাতক, বর্তমানে 'স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'-য় কর্মরত। বিদেশি সাহিত্য, বিশেষ করে পাশ্চাত্য হরর, থ্রিলার, সায়েন্স ফিকশন ও ফ্যান্টাসির প্রতি আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকেই। ‘আনন্দমেলা’, ‘কিশোর ভারতী’, ‘শুকতারা’, ‘চির সবুজ লেখা’, ‘নবকল্লোল’, ‘অনুবাদ পত্রিকা’-র মতো নামী পত্রিকায় মৌলিক এবং অনুবাদ কাহিনি লিখেছেন সৌভিক, নিবন্ধ লিখেছেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’, ‘সংবাদ প্রতিদিন’, ‘তথ্যকেন্দ্র’-র পাতায়। বিগত কয়েক বছরে ‘বি বুকস’, ‘অরণ্যমন’ ও ‘জয়ঢাক’ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর সম্পাদিত একাধিক ইংরেজি ও বাংলা গল্পসংকলন। সৌভিক ভালোবাসেন গান শুনতে এবং সিনেমা দেখতে। নেশা গিটার বাজানো।




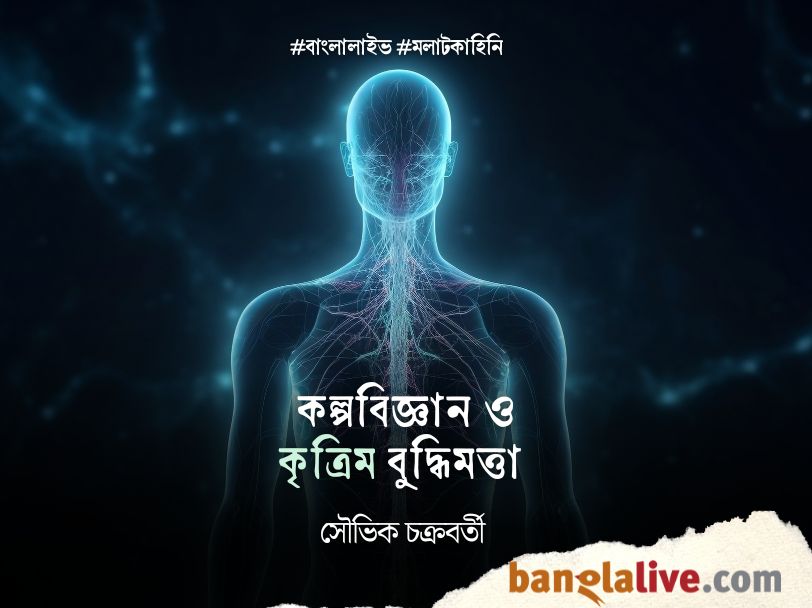





















One Response
একটি সুন্দর ও ব্যালান্সড প্রবন্ধ পড়লাম। তোমার কলমে বিভিন্ন বিষয়ে আরও অনেক প্রবন্ধ আশা করছি। শুভেচ্ছা অন্তহীন।