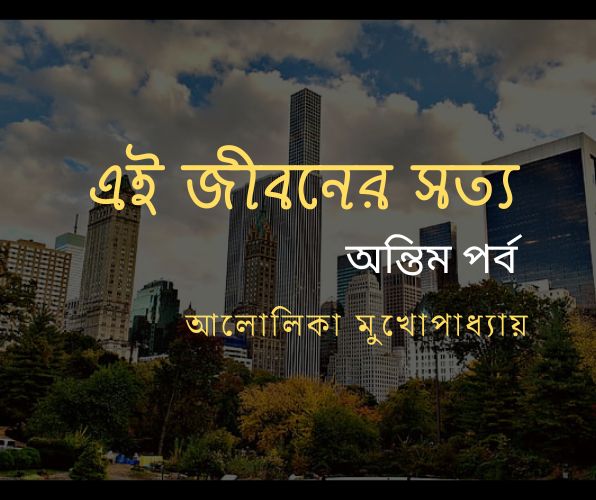শমীকের অফিসে কাজের চাপ বেড়েছে। সুখবিন্দর, যসপাল মার্ডার কেস-এর ট্রায়াল শেষ হয়েছে। তার রিপোর্টিং ছিল। ওদিকে নিউইয়র্কের মেয়রের অফিসের সামনে ট্যাক্সিওয়ালাদের ডেমনস্ট্রেশন। রাশিয়ান, ইস্ট-ইউরোপিয়ান ড্রাইভারদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান, পাকিস্থানী, বাংলাদেশী ট্যাক্সিওয়ালারা হাতে পোস্টার নিয়ে দাবি-দাওয়া জানাচ্ছে। ম্যানহ্যাটনের হট-ডগ, হ্যামবার্গার ভেন্ডারদের আন্দোলনেও ইন্ডিয়ানরা আছে। শমীক দু-তিনটে স্টোরি নিয়ে ব্যস্ত। তার মধ্যে তেলুগু অ্যাসোসিয়েশন থেকে চিঠি ছেড়েছে। তাদের অ্যানুয়্যাল কনফারেন্স। শমীক ওটা ট্রেসির ঘাড়ে চাপাবে। ট্রেসি পয়সা খরচা করে ম্যাড্রাস গার্ডেনে দোসা খেতে যায়। তার বদলে একবেলা তেলুগু কনফারেন্সে যাক। দু’ঘণ্টা অ্যাটেন্ড করে ব্রোশিওর থেকে জিস্ট দেখে নিক। সেই তো এক কথা! হেরিটেজ, ডাইভারসিটি, অ্যাসিমিলেশন অ্যান্ড ভিসন। ওদের কমিউনিটির দুজন ডাক্তারকে সাইটেসন দেবে। ইন্ডিয়া থেকে একজন মন্ত্রী এসে সব এন.আর.আই-দের ইন্ডিয়ার সত্যিকারের অ্যামব্যাসাডর বলবে। একটু ইনভেস্ট করতে বলবে। তারপর ভায়োলিন। তারপর ভারতনাট্যম। ভেজিটেরিয়ান ডিনার। ট্রেসি চলে যাক। দেখেশুনে লিখুক। এথনিক স্টোরি মানেই শমীককে ছুটতে হবে, তার কোনও মানে নেই।
শমীক কিছুদিন ছুটি নেবে ভাবছে। প্রায় দু-বছর দেশে যাওয়া হয়নি। মাকে ফোন করলে আগে বাবা অনেক কথা বলবে। তারপর মাকে দেবে। মা দু-চার কথার পরেই জিজ্ঞেস করবে— কবে আসবি? ইদানীং মা বোধহয় শমীকের বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছে। সুদেষ্ণার বাড়ি থেকে চলে এসে শমীক বাবা-মাকেই সবচেয়ে স্বস্তি দিয়েছে। আজকাল যে লোকেরা অন্যের খবর-টবর নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়, তা নয়। আসলে সময়ের টানাটানি। তাও টুকটাক চালিয়ে যায়। পাড়া থেকে একটা ছেলে বস্টনে তবলা বাজাতে এসেছিল। পরে নিউইয়র্কে এসে শমীকের কাছে দু’দিন ছিল। সে বলল, শমীক যে সুদেষ্ণাকে ‘ছেড়ে দিয়েছে’, সে খবর নিউ জার্সির কোন চন্দ্রাবলী দেশে গিয়ে দিয়ে এসেছে। মা তো এই নিয়েই অশান্তি করত। শমীক নিউইয়র্কে এসে নতুন ঠিকানা, ফোন নম্বর জানানোর পর বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েছে। দেশে যাওয়া মানে ডিসেম্বরের আগে হয়ে উঠবে না। ক্রিসমাসের সঙ্গে দু-সপ্তাহ নিয়ে নেবে। কিন্তু এখন একটা ব্রেক দরকার। অ্যানার সঙ্গে কোথাও ঘুরে আসা যায়।
শুক্রবার অ্যানার ফ্যাকালটি মিটিং ছিল। লাঞ্চের পরে দুটো ক্লাস শেষ করে বাড়ি ফিরল। প্যাকিং করতে আধ ঘণ্টা। শমীক ওকে বাড়ি থেকে তুলে নেবে। শেষ অবধি নিউ হ্যাম্প্শায়ারে যাওয়াই ঠিক হল। শমীক বাড়ি রেন্ট করে নিয়েছে। সোমবার অ্যানার ডে-অফ। শমীক ছুটি নিয়েছে। উইক-এন্ডের ট্র্যাফিক পার হয়ে ওরা যখন হাই-ওয়ে ধরল, তখনও বিকেলের আলো ছিল। পথে একবার থামল। নিউ হ্যাম্প্শায়ারে পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গেল। পরদিন ভোরবেলা অ্যানার ঘুম ভাঙল। নতুন জায়গায় ঘুম প্রায় হলই না। ঘড়িতে মাত্র পাঁচটা কুড়ি। অ্যানা উঠে পর্দা সরালো। চারদিকে পাহাড়। দূরে জ্যোতির্বলয়ের মতো আলো ফুটে উঠেছে।
ইদানীং মা বোধহয় শমীকের বিয়ে-টিয়ের কথা ভাবছে। সুদেষ্ণার বাড়ি থেকে চলে এসে শমীক বাবা-মাকেই সবচেয়ে স্বস্তি দিয়েছে। আজকাল যে লোকেরা অন্যের খবর-টবর নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়, তা নয়। আসলে সময়ের টানাটানি। তাও টুকটাক চালিয়ে যায়। পাড়া থেকে একটা ছেলে বস্টনে তবলা বাজাতে এসেছিল। পরে নিউইয়র্কে এসে শমীকের কাছে দু’দিন ছিল।
অ্যানা বিছানায় ফিরে এল। একটু পরে উঠে স্নান সেরে নেবে। শমীক আটটায় তৈরি থাকতে বলেছে। বিছানায় শুয়ে থেকে ঘরের ভেতরটা দেখছিল। হোটেলটা বেশ পুরনো। কারও কান্ট্রি হাউস ছিল বোধহয়। অ্যান্টিক ফার্নিচার দিয়ে সাজানো। উঁচু ফোর-পোস্টার বেড। খাটে ওঠার জন্য ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি। মাথার ওপর গোটানো মশারির মতো লেস-এর ঝালর। অ্যানার মামার বাড়ির ঘরটা মনে পড়ল। দিদিমার উঁচু খাট। মাথার দিকে ঝাপসা হয়ে আসা চৌকো আয়না। শক্ত পাশবালিশ। ছোটবেলায় ইন্ডিয়ায় গিয়ে মার সঙ্গে ওই উঁচু খাটটায় শুত। ও পড়ে যাবে বলে মা ওকে দেওয়ালের দিকে দিতেন। সিলিং-এর ওপাশ থেকে পিজিয়নের ডাক শুনে ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে যেত। সেই ডাক, সেই ঘর আর বিছানা ওর স্মৃতি থেকে উঠে এল। মা সবকিছু সঙ্গে নিয়ে গেছেন।
হোটেলে ব্রেকফাস্টের পর ওদের বেরনোর কথা। শমীক নিজের ঘর থেকে ফোনে তাড়া দিল, ‘তোমার কত দূর? তাড়াতাড়ি রেডি হও। নীচে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়ব।’
‘লস্ট রিভারেই যাচ্ছি তাহলে?’
‘কাল তো তাই ঠিক হল। রোড ম্যাপ-ট্যাপ দেখে রাখলাম।’
‘ঠিক আছে। আমি অলমোস্ট রেডি। দশ মিনিটের মধ্যে নীচে আসছি।’
হোটেল থেকে প্রায় এক ঘণ্টার পথ। পাহাড়ের ধারে গাড়ি রেখে ওরা হাঁটতে শুরু করল। ওই রেস্ট এরিয়াতে গাড়ি পার্ক করে আরও কয়েকজন টুরিস্ট লস্ট রিভার দেখতে চলেছে। হারানো নদীর খোঁজে রেইন ফরেস্টের ভেতর দিয়ে যাওয়া। কোনকালে এক পাহাড়ি নদী এখানে এসে সমতলের পথ হারিয়েছিল। বনের সুঁড়ি পথ ধরে নতুন পাহাড়ের গর্ভে নেমে গেছে। অন্ধকারে সুড়ঙ্গে চলতে চলতে তার ছলছল শব্দ শোনা যায়। নদীকে দেখা যায় না। পাথরের দেওয়ালের আড়ালে ফার্নের জঙ্গলে শ্যাওলাভেজা পথ ধরে নদী চলেছে। পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। দুদিকে ঘন সবুজ অন্ধকার।
হারানো নদীর খোঁজে ওরা সুড়ঙ্গ পার হয়ে চলেছে। মাথার ওপর পাহাড়ের ছাদ। দেওয়ালে ঝিরঝির শব্দে জলের ধারা নামছে। পায়ের তলায় ভেজা মাটি। অ্যানার পা পিছলে যাচ্ছে। শমীকের হাত ধরল।

সুঁড়ি পথ শেষ হয়ে এল। তখনও নদীর দেখা নেই। সামনে বিশাল পাথরের চাতাল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। অনেক উঁচুতে ঘন নীল আকাশ। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে, তার কাছাকাছি কোনও পথ নেই। দূর থেকে দেখছে অনেক নীচে পাহাড়ের খাঁজে ঝরনার মতো জলধারা নেমেছে। শমীক বলে উঠল, ‘ওই তো নদীটা! দেখতে পাচ্ছ?’
অ্যানা ঝুঁকে দেখল, ‘নদী, না ঝরনা?’
‘পাহাড়ে এসে ঝরনা হয়ে নেমেছে। চলো, আমরাও নেমে যাই।’
অ্যানা তখনো ঝুঁকে পড়ে দেখছে, ‘অত নীচে যাব কী করে?’
‘ওই তো দূরে কাঠের সিঁড়ি দেখতে পাচ্ছি। কিছু লোক ফিরেও আসছে। এসো, আমার হাত ধরো।’
কাঠের ছোট্ট পুল পার হয়ে ওরা সিঁড়ি ধরে-ধরে গভীর খাদের ভেতরে নেমে এল। গাছের ছায়ার আধো অন্ধকারে হারানো নদী বয়ে চলেছে। নুড়ি-পাথরের ওপর দিয়ে অবিস্তীর্ণ আঁকাবাঁকা পথ কোথায় চলেছে, পাথরের আড়াল থেকে দেখা যায় না।
জলের ধারে এসে অ্যানা শুধু বলল, ‘নদী তো হারায়নি।’ নিঃস্তব্ধ নিথর মুহূর্তে শুধু জলের ছলছল শব্দ। শমীক অ্যানাকে জড়িয়ে ধরেছিল। অ্যানা মুখ ফেরাল। দীর্ঘ চুম্বনের মাঝে ওর চোখের জল বাধা মানছিল না।
হোটেলে ফিরে এসে ডিনারের পর শমীক একবার নিজের ঘরে গেল। অ্যানা জিন্স্-টি শার্ট বদলে স্নান সেরে রাতের পোশাক পরে নিল। ফ্লানেলের রোব জড়িয়ে জানলার পাশে এসে বসল। বাইরে ঘন অন্ধকার। দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট রূপরেখা। আকাশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অসংখ্য নক্ষত্রের দীপ। অ্যানা হারানো নদীর কথা ভাবছিল। পাহাড়ের অতল গর্ভে গভীর অন্ধকারে প্রবহমাণ সেই জলধারা কোথায় চলেছে। নদী কি সঞ্জিবীত করার মন্ত্র দেয়? বলে, পথ আছে, পথ খুঁজে নাও। বিষাদ থেকে আনন্দে, দুঃখ থেকে সুখে, বিচ্ছিন্নতা থেকে বন্ধনে ফেরার জন্যে নতুন করে পথ খুঁজে নাও।
দরজায় শব্দ হল। শমীক এসেছে। অ্যানা লক খুলে দিয়ে বিছানায় এসে বসল। ঘরে ঢুকে শমীক বলল, ‘কী ব্যাপার? ঘুমের জন্যে রেডি? এখন তো দশটাও বাজেনি।’
অ্যানা হাসল, ‘আমার তো সুবিধে। তোমার মতো হল-ওয়ে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে হচ্ছে না। তাই শাওয়ার নিয়ে একেবারে রাতের জামাকাপড় পরে নিলাম।’
‘হ্যাঁ, তোমার সব দিকেই সুবিধে। জানলা খুললেই চাঁদ, তারা।’
‘কেন, তোমার জানলায় নেই?’
শমীক সোফায় পা উঁচিয়ে বসে পড়ল, ‘পাহাড় আর যাবে কোথায়? সঙ্গে অ্যাডেড ভিউ পার্কিং লট, ম্যাকডন্যাল্ড, গ্যাস স্টেশন। যা-যা চাও।’
অ্যানা হাসছে, ‘তার মানে ঘরটা বাজে দিয়েছে। চেঞ্জ করলে না কেন?’
‘করা উচিত ছিল। পাশের ঘরেও একটা লোক জুটেছে বটে! সারারাত টয়লেটে ফ্লাশের আওয়াজ! ডায়াবেটিস না ডায়ারিয়া ধরতে পারছি না।’
‘যাক গে। কালকে কী প্ল্যান বলো?’
‘ড্রাইভিং, না হাইকিং। সেটা আগে ঠিক করো।’
শমীকের হাই উঠল, ‘আজ তো অনেক হাইকিং হল। তার চেয়ে মাউন্ট ওয়াশিংটনে চলো। গাড়ি নিয়ে দশ হাজার ফিট উঠে যাব।’
হোটেলে ফিরে এসে ডিনারের পর শমীক একবার নিজের ঘরে গেল। অ্যানা জিন্স্-টি শার্ট বদলে স্নান সেরে রাতের পোশাক পরে নিল। ফ্লানেলের রোব জড়িয়ে জানলার পাশে এসে বসল। বাইরে ঘন অন্ধকার। দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট রূপরেখা। আকাশের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে অসংখ্য নক্ষত্রের দীপ। অ্যানা হারানো নদীর কথা ভাবছিল। পাহাড়ের অতল গর্ভে গভীর অন্ধকারে প্রবহমাণ সেই জলধারা কোথায় চলেছে।
অ্যানা বলল, ‘কাল আমি ড্রাইভ করব। শেষের দিকটা ভীষণ স্টিপ।’
‘কেন? আমার ড্রাইভিং স্কিলের ওপর ভরসা নেই?’
অ্যানা নিজের পায়ের পাতা টিপে ধরে বলল, ‘ব্যথা-ব্যথা করছে। কম হাঁটিনি আজ।’
‘তাহলে কালকের ট্রিপ বাদ দাও না। আবার তো সাত সকালে উঠতে হবে।’
‘না গেলেই হয়। তার চেয়ে এখানেই রিল্যাক্স করি।’
‘হ্যাঁ, কাছাকাছি একটু ঘুরে আসব। ঘরে বসে গল্প করা যাবে। আর তো একটা দিন।’
অ্যানা শমীকের কাছে এসে বসল। শরীরে স্নানের সাবান, শ্যাম্পু, পাউডারের গন্ধ মিলেমিশে স্নিগ্ধ পরিচ্ছন্ন সুবাস। ওর ভেজা চুলে, কপালে ঠোঁটে সেই ঘ্রাণ নিতে-নিতে শমীক এক সময় বলল, ‘নিজের অনেক কথা তোমায় বলিনি অ্যানা। তুমি জানতে চাও না?’
অ্যানা মৃদু স্বরে উত্তর দিল, ‘পুরনো কথা জানা না জানায় আমার কিছু এসে যায় না।’
শমীক আহত হল, ‘কেন? তুমি কেয়ার করো না? আমি ভালো হই, খারাপ হই, তোমার কিছু এসে যায় না?’
‘দ্যাট্স্ নট দ্য কোয়েশ্চেন। তোমার একটা রিলেশনশিপ থাকতেই পারে। তুমি ব্রেক-আপ করেছ, তাই তো?’
‘ক্যারেন বলেছে বোধহয়? কিন্তু কেন এত বছর পরে সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে এলাম, জানতে চাও না?’
‘তুমি বলতে চাইলে, বলো। আমি শুধু ক্যারেনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওই মহিলাকে তুমি বিয়ে করেছিলে কিনা। তাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে চলে এসেছ কিনা। ক্যারেন বলেছিল কোনওটাই নয়। আর কিছু জানতে চাইনি।’
শমীক স্তব্ধ হয়ে গেল। অ্যানার বাবার অপরাধটা ওর কাছে সবচেয়ে বড়। তাই শমীকের সুদেষ্ণার সঙ্গে লিভটুগেদার করা, ব্রেক-আপ করার জন্যে কোনও প্রশ্ন করছে না। শমীক নিজে হলেও হয়তো কোনও পুরনো অ্যাফেয়ার নিয়ে বিশেষ কৌতূহল দেখাত না। তবু মনে হল অ্যানাকে কিছু কথা বলার আছে। হয়তো নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্যেও। একটু চুপ করে থেকে বলল, ‘ক্যারেন তোমাকে ঠিক কতখানি বলেছে জানি না। হয়তো আরও কথা আছে। তুমি কি জানো অ্যানা, ওই মহিলার জন্যে আমি এ-দেশে আসতে পেরেছিলাম? লিবারাল-আর্টস্-এর ছাত্র ছিলাম। বাড়ির অবস্থাও সাধারণ। আমেরিকায় পড়তে আসা আমার কাছে তখন স্বপ্নের মতো। সুদেষ্ণা আমার বন্ধুর দিদি। আমাকে স্পন্সর করে এনেছিল। প্লেনের টিকিট পাঠিয়েছিল। ওর বাড়িতে থেকেই কমিউনিটি কলেজে পড়াশোনা। ছোটোখাটো অড-জব। একটা ছোট কাগজের অফিসে চাকরি। সে-ও সুদেষ্ণার কনট্যাক্ট থেকে। এইচ ওয়ান ভিসা হল। তারপর এই চাকরি। সুদেষ্ণার কাছে আমার অনেক ঋণ।’

অ্যানা শুনছিল। শমীকের শেষ কথাটার যেন মৃদু প্রতিবাদের চেষ্টা করল, ‘তোমাকে ওঁর প্রয়োজন ছিল। ওঁর ডিফিকাল্ট সময়ে তুমি ওঁর পাশে ছিলে। দুজনে দুজনকে দেখেছ।’
‘সেই যুক্তিটাই ধরে আছি।’
অ্যানার মুখ ম্লান দেখাল, ‘শমীক, ডু ইউ হ্যাভ এনি রিগ্রেট? চলে এসে ভুল করোনি তো?’
শমীক উত্তর দিল, ‘না, অনেকদিন থেকে ভেবেছি। ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। শুধু লীনার জন্যে সুদেষ্ণাকে ছেড়ে আসতে পারিনি।’
‘লীনা কে?’
‘সুদেষ্ণার মেয়ে। মেন্টালি রিটার্ডেড। সিভিয়ার গ্রেড অফ রিটার্ডেশন না হলেও ওকে নিয়েই ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়েছিল। নীল যখন একটু বড় হল, সুদেষ্ণার স্বামী লীনাকে আর বাড়িতে রাখতে চাইছিলেন না। সুদেষ্ণাও লীনাকে কিছুতেই ইনস্টিটিউশনে রাখতে দেবে না। নীলের পক্ষে যে পরিবেশটা স্বাভাবিক থাকছে না, সুদেষ্ণা মানতে চাইত না। শেষপর্যন্ত ওর স্বামীই ওদের ছেড়ে চলে গেলেন। ছেলের কাস্টডি চেয়েও পাননি। ডিভোর্সের পর আবার বিয়ে করলেন। এখনও ওদের জন্য অ্যালিমনি দিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িটাও সুদেষ্ণা পেয়েছে।’
‘ভদ্রমহিলা হঠাৎ তোমাকে স্পনসর করে নিয়ে এলেন কেন?’
‘ওর একজন পুরুষের দরকার ছিল। আমি তখন ওর পাড়ার চেনা ছেলে, আমেরিকায় আসার সুযোগ, একটা নিশ্চিত আশ্রয়…’
‘লীনাকে তুমি টেক কেয়ার করতে পারতে?’
‘দেখতে হত। একটা অসহায় ছোট মেয়ে। সুদেষ্ণার ফুল টাইম চাকরি। নীলও ছোট। সুদেষ্ণা একা পেরে উঠত না। আমি আসার পর যেটুকু সময় পেতাম সাহায্য করতাম।’
‘লীনা এখন কোথায়?’
‘শেরউড ইনস্টিটিউশনে। অ্যাডোলেসেন্সের পর থেকে বাড়িতে আর হ্যান্ডল করা যাচ্ছিল না।’
অ্যানা দু-হাঁটুর ওপর হাত রেখে মাথা নিচু করে বসেছিল। এক সময় মুখ তুলে বলল, ‘আমি এত কথা জানতাম না। ক্যারেনও বোধহয় জানে না।’
শমীক উত্তর দিল, ‘অফিসে দু-চারজন জানে। ক্যারেনের সঙ্গে আগে তো সেরকম আলাপও ছিল না। তোমার পাঠানো সেই মাদার্স ডে-র কবিতার ফ্যাক্স পড়তে গিয়ে, কথায়-কথায় বন্ধুত্ব হয়ে গেল। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা।’
নিউইয়র্কে জুলাই-এর এক বৃষ্টির সকালে ওদের বিয়ে হল। অ্যানার বাবা এসেছিলেন। নীল এসেছিল। আর ওদের কয়েকজন বন্ধু বিয়ের পর রিসেপশনে অ্যানার নিজের লেখা থেকে পড়ল—
‘এভরি থিং ইজ রিয়েলি গুড রাইট নাউ
এভরি থিং ইজ হারমনিয়াস্
দিস্ ওয়ান অফ দোজ টু মিনিটস ইন লাইফ
হোয়েন সাড্নলি এভরি বডি ইজ ও.কে
দোজ টু মিনিটস্ ইন লাইফ…’
শমীকের মনে পড়ছিল—
‘এই জীবনের সত্য তবু পেয়েছি এক তিল
পদ্ম পাতায় তোমার আমার মিল…’
অঙ্গীকার আর প্রতিশ্রুতি পরে সেই নীরবিন্দুর জন্যে শমীক এক আশ্চর্য মায়া অনুভব করছিল।
(সমাপ্ত)
ছবি সৌজন্য: Flickr
দীর্ঘকাল আমেরিকা-প্রবাসী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখালিখির সূচনা কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে। আমেরিকার নিউ জার্সির প্রথম বাংলা পত্রিকা "কল্লোল" সম্পাদনা করেছেন দশ বছর। গত আঠাশ বছর (১৯৯১ - ২০১৮) ধরে সাপ্তাহিক বর্তমান-এ "প্রবাসের চিঠি" কলাম লিখেছেন। প্রকাশিত গল্পসংকলনগুলির নাম 'পরবাস' এই জীবনের সত্য' ও 'মেঘবালিকার জন্য'। অন্য়ান্য় প্রকাশিত বই 'আরোহন', 'পরবাস', 'দেশান্তরের স্বজন'। বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য নিউইয়র্কের বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ থেকে ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।