
সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন বাংলার ক্রীড়াজগতের অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র চুনী গোস্বামী। ফুটবল এবং ক্রিকেট দুই খেলাতেই তাঁর অবিস্মরণীয় অবদানের কথা কোনও ক্রীড়ামোদী বাঙালির পক্ষেই ভোলা সম্ভব নয়। তাঁকে বেশ কয়েকবার খুব কাছ থেকে দেখার এবং তাঁর কথা শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল চন্দননগরের বাসিন্দা অভীক চট্টোপাধ্যায়ের। অভীকবাবু শুধু ক্রীড়াপ্রেমী নন, বাংলার খেলার ইতিহাস বিষয়ে তাঁর পড়াশোনা ঈর্ষণীয়। এ ব্যাপারে প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁর বাবা অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাংলালাইভের একান্ত অনুরোধে অভীকবাবু কলম ধরলেন, ম্যান-ইউ-বার্সা নিয়ে মাতামাতি করা, আইপিএলে মজে থাকা নবীন প্রজন্মের সঙ্গে এক অচেনা রত্নের পরিচয় করাতে। তাঁর লেখায় পঞ্চাশের দশকের বাংলা তথা ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে চুনীর উত্থানের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় আরও একবার খুলে যাবে আমাদের পাঠকদের সামনে, এই আশা রাখি।
১৯৪৬ সালের শেষের দিক। ওই বছর ১৬ অগস্ট থেকে শুরু হওয়া ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে কলকাতা রক্তাক্ত। অনেক কিছুর মতো ময়দানে খেলাও বন্ধ। আই.এফ.এ শিল্ড বাতিল। এক কালের প্রখ্যাত ফুটবলার ও বক্সার বলাই চট্টোপাধ্যায় (বি.ডি.চ্যাটার্জি) সেই সময় দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে বসে ছেলেদের খেলা দেখতেন। তখন তুলনামূলক ভাবে এ অঞ্চল ছিল শান্ত। আজীবন মোহনবাগানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বলাইবাবু তখন ফুটবল প্রশিক্ষক। ক্লাব-তাঁবুতে তো যেতে পারছেন না। তাই পার্কে বসে খেলা দেখতেন। আর তাঁর চোখ ঘুরে বেড়াত নতুন প্রতিভার সন্ধানে।
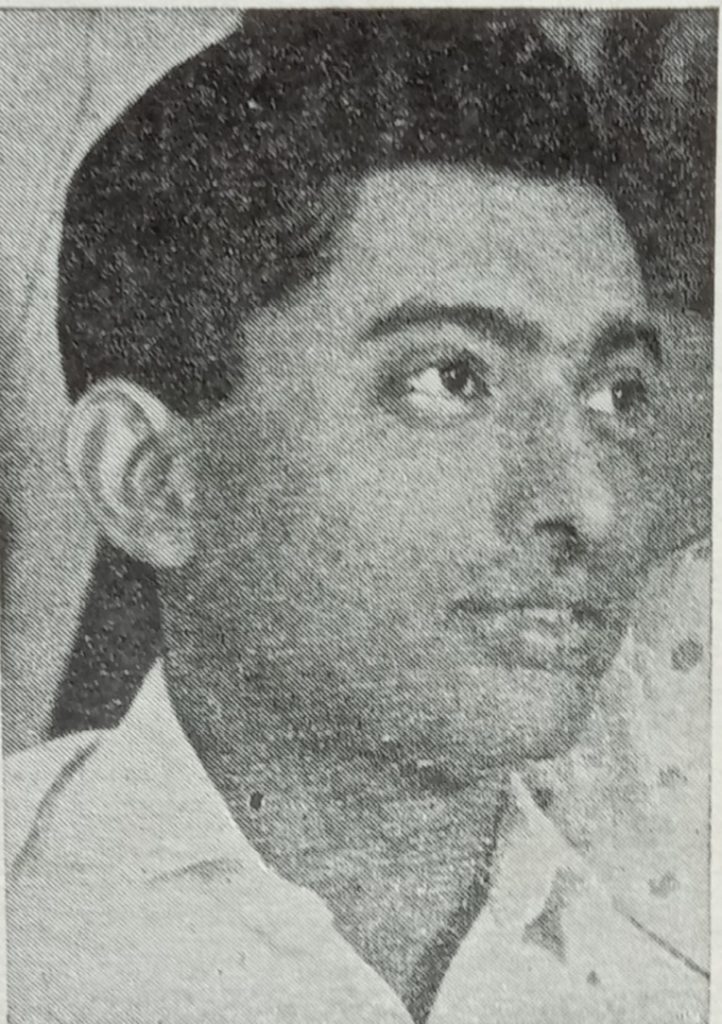
এরকমই একদিন দেখলেন ছোট ছেলেরা দলে ভাগ হয়ে ফুটবল নিয়ে দাপাদাপি করছে। খেলা জমে উঠেছে। এরই মধ্যে একটি রোগা চেহারার বছর আষ্টেকের বাচ্চা ছেলে কয়েকজনকে কাটিয়ে গোলে মারল এক শট। দু’প্রান্তে চটি দিয়ে গোল পোস্ট করা হয়েছে। সেই জোরালো শট চটিশুদ্ধু গোলে ঢুকে গেল। ‘গো-ও-ল’ বলে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটি। সঙ্গে দলের বাকিরাও। কিন্তু বিপক্ষ দল মানবে না। কারণ বল তো চটিতে লেগেছে। তাঁর মানে গোল পোস্টে ধাক্কা খেয়েছে। লেগে গেল তর্কাতর্কি। সেই ছেলেটির দাদা আবার খেলছিল বিপক্ষ দলে। দু’ভাইয়ে লেগে গেল তুমুল বাদানুবাদ। পুরো ঘটনাটাই একটু দূরে বসে লক্ষ করছিলেন বলাইবাবু। এবার তিনি এগিয়ে এসে সেই গোলে শট মারা ছেলেটিকে বললেন, গোল হয়নি। সে ছেলে জানেই না কে বি.ডি.চ্যাটার্জী। অতএব গ্রাহ্যই করল না তাঁর কথা। ওখানকার কয়েকজন পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর ছেলেটি নিমরাজি হল। বলাইবাবু বোঝালেন, যদি চটির জায়গায় গোলপোস্ট থাকত, তাহলে বল পোস্টে লেগে ফিরে আসত। চটি বলে সেই শুদ্ধু নিয়ে চলে গেছে। এবার বিবাদের নিস্পত্তি হল। ততক্ষনে কিন্তু বলাইবাবু যা দেখার দেখে নিয়েছেন। ছেলেটির মধ্যে যে প্রতিভার আগুন রয়েছে, তা তাঁর নজর এড়ায়নি। তখনই তিনি বলেন তাঁকে – ‘তুমি তো সুন্দর খেল, আমি তোমাকে খেলা শেখাব।’ এরপর সেই বি.ডি.চ্যাটার্জীর হাত ধরেই মোহনবাগানে প্রবেশ চুনী গোস্বামীর। এবং খেলোয়াড় জীবনের সূচনা দাদা মানিক গোস্বামীকে সঙ্গী করেই।
বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার যশোদল গ্রামে জন্ম চুনী গোস্বামীর। দিনটা ছিল ১৯৩৮ সালের ১৫ জানুয়ারি। দাদা মানিক ছিলেন তিন বছরের বড়। চুনীর ভালো নাম ছিল ‘সুবিমল’, মানিকের ‘সুনির্মল’। কিন্তু দু’জনেরই এই নাম দু’টো ডাকনামের ধাক্কায় বিখ্যাত হতে পারেনি। মধ্যবিত্ত পরিবার হলেও শিক্ষায় ভরপুর। বাবা প্রমথনাথ গোস্বামী ইস্টার্ন রেলের অডিট অফিসার পদে কাজ করতেন। ছাত্র জীবনে তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে আই.এ ও বি.এ তে ফার্স্ট হয়েছিলেন। দাদু মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য সরস্বতী ছিলেন পণ্ডিত মানুষ। গৌহাটির কটন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। কাজেই শিক্ষার আবহেই বেড়ে ওঠেন চুনী। কিন্তু দেশভাগের আগেই তাঁদের এপার বাংলায় চলে আসতে হয়। ফলে নতুন পরিবেশে নতুন ভাবে সবকিছু গড়ে তোলার লক্ষ্যে খুব চাপ তৈরি হয় চুনীর বাবার উপর। কিন্তু ছোটবেলায় আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও জিনগত বৈশিষ্ট্যে বুদ্ধিমত্তা ও স্বতন্ত্র ক্রীড়া-প্রতিভার আদর্শ মিশেল ঘটেছিল চুনী গোস্বামীর মধ্যে।
চুনীকে বলাইবাবু মোহন বাগানের জুনিয়র দলে ঢোকানোর পর থেকেই শুরু হল নিরলস প্রশিক্ষণ। তীর্থপতি ইন্সটিটিউশনে পড়ার সময় থেকেই স্কুল পর্যায়ে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলেছেন চুনী। তখন আন্ডার হাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট দারুণ জনপ্রিয় ছিল সারা বাংলায়। সে রকমই একবার স্কুলে পড়ার সময় বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের হয়ে একটি প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচ খেলেন চুনী। মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর বাড়ির মাঠে সেই খেলায় সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজু। খেলার শেষে ছোট্ট চুনীকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘চুনীর ইংরেজী কী বলো তো?’ উত্তর এল- ‘রুবি’। কাটজু বলেছিলেন, ‘আমি তোমার নাম রাখলাম ‘ডায়মন্ড’।’ সে নামকরণ যে এমন অমোঘ হয়ে দাঁড়াবে কেউ কি কল্পনা করেছিল?
ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটটাও খুব স্বাভাবিক দক্ষতায় চুনীর আয়ত্তে এসেছিল স্কুল-জীবন থেকেই। তখন এবং তার বহু আগে থেকেই বাঙালিদের মধ্যে সবরকম খেলার প্রবণতা দেখা যেতো। স্বতর্স্ফুত মানসিকতায় সবাই মেতে উঠতেন নানা খেলা নিয়ে। ভেদাভেদের মনোভাব ছিল না। গোষ্ঠ পাল, কানি দেব, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, পঙ্কজ রায় এরকম আরও অনেকের নামই এ প্রসঙ্গে চলে আসে। এঁদের মধ্যে অনেকে তো একাধিক খেলায় রাজ্যস্তরেও খেলেছেন। আবার রবি দাস, সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের মতো খেলোয়াড়েরা দু’ ধরনের খেলাতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। এ ব্যাপারে শেষ উজ্জ্বল তারকা বোধহয় চুনী গোস্বামীই, যিনি আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে ফুটবল ও ক্রিকেট খেলেছেন।
ক্রিকেটে চুনী প্রথমবার কী ভাবে নজর কাড়লেন, সেই ঘটনাটা বলি। তখন তিনি তীর্থপতি-র ছাত্র। ক্রিকেটের ধারেকাছেও নেই। ইন্টার-স্কুল খেলা সাউথ সুবার্বন স্কুলের সঙ্গে। খেলা দেখার নেশায় চুনী দেশপ্রিয় পার্কে হাজির। তাঁর স্কুল তীর্থপতি-র অধিনায়ক তখন বুদ্ধদেব গুহ (পরবর্তীতে বিখ্যাত সাহিত্যিক)। খেলা প্রায় শুরুর মুখে, কিন্তু তখনও তীর্থপতি-র কয়েকজন খেলোয়াড় আসেনি। গেম টিচার শিবদাসবাবু ও ক্যাপ্টেন বুদ্ধদেব চিন্তিত টিম নামানো নিয়ে। চুনী যেচে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তিনি খেলতে চান। বুদ্ধদেব একটু তাচ্ছিল্য করেই সেদিন বলেছিলেন – ‘এটা তোর ফুটবল খেলা নয়। ক্রিকেট।’ সে তো ঠিকই! তার আগে চুনী কোনও দিন ক্রিকেট খেলেননি। মাঝে মাঝে পাড়ায় ক্যাম্বিস বলে ছাড়া। কিন্তু সেদিন চুনীকে মাঠে নামাতে হয়েছিল, কারণ, এগারোজন খেলোয়াড়ই হচ্ছিল না। সে দিন চুনী ৪৭ রান করেছিলেন এবং শূন্য রানে দখল করেছিলেন চারটি উইকেট! একেই বোধহয় বলে জন্মগত ক্রীড়া-প্রতিভা! এরই জেরে কোচবিহার ট্রফিতে বেঙ্গল স্কুল দল নির্বাচনের ট্রায়ালে চুনীর ডাক পড়লো স্পোর্টিং ইউনিয়নের মাঠে। সেখানেও নাটক! ট্রায়াল নিচ্ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত কোচ বার্ট ওয়েন্সলি। তখন তিনি কলকাতায়। সঙ্গে ছিলেন বিশিষ্ট বেতার-ভাষ্যকার পিয়র্সন সুরিটা, যিনি ভালো বোলার হিসেবে দীর্ঘদিন ক্লাব ক্রিকেট খেলেছিলেন। ওয়েন্সলি যখন চুনীকে জিজ্ঞেস করেন, ‘ব্যাট না বল – কী কর?’ উত্তরে চুনী বলেছিলেন – ‘ব্যাট, অ্যান্ড আই বোল টুউ – লেগ ব্রেক।’ লেগ ব্রেক শুনে চমকিত হয়েছিলেন সাহেব, কারণ লেগ স্পিনার তখন ছিল দুর্লভ! চুনীর বল দেখে ওয়েন্সলি শুধু সন্তুষ্টই হননি, তাঁকে দলে স্থান দিয়েছিলেন এবং নাম দিলেন – ‘টিচ’। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত লেগ-স্পিনার হলেন ‘টিচ ফ্রিম্যান’। অত অল্পবয়েসে চুনীর কাছে এ কত বড় সম্মান, সেটা অনুমান করলে মালুম হয় তাঁর প্রতিভা!

১৯৪৬ সাল থেকে মোহনবাগানের হয়ে জুনিয়র দলে পাওয়ার লিগ, ট্রেডস কাপ ইত্যাদি প্রতিযোগিতায় ফুটবল চলল কয়েক বছর। অবশেষে ১৯৫৪ সালের ২৯ মে শনিবার, কলকাতা প্রথম ডিভিসন লিগে ইস্টার্ন রেলের বিরুদ্ধে প্রথমবার সবুজ-মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামলেন চুনী গোস্বামী। তাও এক নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে। সে বছর ভেঙ্কটেশ এসেছেন মোহনবাগানে। সঙ্গে রয়েছেন রুণু গুহঠাকুরতা, বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়, কেষ্ট পাল, কেষ্ট দত্ত-র মতো ডাকসাইটে ফুটবলাররা। এরকম ফরোয়ার্ড লাইনে তো ষোলো বছরের চুনীর জায়গা পাওয়ার কথা নয়। তাই খেলার দিন বাড়িতেই ছিলেন। অপেক্ষা করছিলেন খেলা দেখতে যাবার। হঠাৎ বাড়িতে গাড়ি নিয়ে হাজির মোহনবাগানের কর্মকর্তা মন্মথনাথ ঘোষ। চুনীকে ক্লাবে নিয়ে গেলেন। তাঁকে নাকি আজ খেলতে হবে। কারণ রুণু গুহ ঠাকুরতা, সাত্তার ও বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের ম্যাচে খেলতে পারবেন না। চুনী ক্লাবে পৌঁছতেই বলাইবাবু আগে তাকে একটা জার্সি পরে নিতে বললেন। কারণটা পরে বোঝা গেল।
তখন ২-৩-৫ সিস্টেমে খেলা হত। চুনী খেলতেন রাইট ইনসাইড ফরওয়ার্ড হিসেবে। সে বছর রবিন পাত্র নামে আরও একজন ইনসাইড ছিলেন মোহনবাগানে। কথা ছিল সেদিন রাইট ও লেফট-ইন হসেবে মাঠে নামবেন চুনী ও রবিন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে বদ্রু চলে এলেন। অতএব রাইট ইনসাইড তো অবশ্যম্ভাবী তিনিই। পড়ে রইল লেফট-ইনের জায়গা। উমাপতি কুমার ড্রেসিংরুমে ঢুকলেন। জার্সি পরে দাঁড়িয়ে চুনী। রবীন পাত্র তখনও গায়ে সবুজ-মেরুন চড়াননি। কুমারবাবু চুনীকে জিজ্ঞেস করলেন সে লেফট-ইনে খেলতে পারবে কিনা। না হলে, রবীন খেলবে। চুনী বললেন- ‘পারব’।
ব্যাস, মোহনবাগানের হয়ে ময়দানে অভিষেক হয়ে গেল চুনী গোস্বামীর। তখন মোহনবাগানে একটা প্রথা ছিল, যদি কেউ জার্সি পরে নেন, তার গা থেকে সেটা আর খোলা হত না একান্ত প্রয়োজন না হলে। এই কারণেই সেদিন ক্লাবে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বলাইবাবু চুনীকে আগেভাগে জার্সি পরে নিতে বলেছিলেন। রবীন পাত্র জার্সি পরেননি। ফলে প্রথা মেনেই মাঠে নামার ব্যাপারে অগ্রাধিকার হল চুনীর! আর এর ফলেই ভারতীয় ফুটবলে এক নতুন যুগের সূচনাও হতে পারল। এদিন মোহনবাগান ইস্টার্ন রেলকে হারিয়েছিল ৩-০ গোলে, যার মধ্যে একটি এসেছিল চুনীর পা থেকে। বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাস থেকে করা সেই গোলটি সবার মুখ হাঁ করিয়ে দিয়েছিল। ফুটবল মাঠকে কোন বিশিষ্টতার অর্ঘ্য তিনি দিতে এসেছেন, তার শিল্প-স্পর্শ প্রথম দিনেই প্রতিভাত হয়েছিল চুনীর খেলায়।
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনবাগান থেকে শুরু করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত চুনী গোস্বামীর যে স্বর্ণমণ্ডিত ক্রীড়া-অভিযান, তার খুঁটিনাটি বিবরণের কথা বহু আলোচিত ও মুদ্রিত। ফলে সে নিয়ে বিশদে তেমন কিছু লেখার নেই। আমরা বরং দেখি চুনী গোস্বামীর মতো জিনিয়াসদের আগমন ও প্রদর্শন কোন নতুনত্বের দিকটিকে মেলে ধরল। কোন জায়গায় তিনি বা তাঁর সময়ের ভারতীয় ক্রীড়াজগৎ অনন্যতার আখ্যা পেতে পারে? এর প্রমাণ হিসেবে অবশ্যই কিছু ক্রীড়া-ঘটনার কথা অবশ্য বলতেই হবে।
১৯৫০ এর দশকে উত্থান চুনী গোস্বামীর। স্বাধীনতার পর ক’বছর মাত্র কেটেছে। ২০০ বছর পরাধীনতার পর একটি দেশ গড়ে উঠতে চাইছে নিজের মতো করে। সঙ্গে রকমারি সমস্যা। স্বাধীনতার হাত ধরে আসা ‘দেশভাগ’-এর দগদগে ক্ষত তখনও টাটকা। কাতারে কাতারে শরণার্থী আগমনের পাশাপাশি সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক রেষারেষি, ইতস্তত সংঘর্ষে বাংলা তখন মহাসংকটে। এসবের মধ্যেই ধ্যানধারণা, মতবাদ ইত্যাদিতে আন্তর্জাতিক ভাবধারার প্রবেশ ঘটছে। যার ফলে, সমাজ-রাজনীতি তো বটেই শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে চলছে নানা ভাঙাগড়ার খেলা। নতুন প্রতিভারা উঠে এসে সৃষ্টিশীলতার নবদিগন্ত দেখাচ্ছেন। পুরনো ধ্যানধারণার অনেক কিছুই পালটে যাচ্ছে। খেলার মাঠই বা এসবের বাইরে থাকবে কেন? সেখানেও লেগেছিল নতুনত্বের ছোঁয়া। চুনী গোস্বামী এই নবযুগ আনার ক্ষেত্রে অবশ্যই অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাই নতুন যুগের ব্যাপারে বলার আগে দেখা যাক চুনীর ফুটবলে প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য কী ছিল।
মূলত ডান-পায়ের ফুটবলার ছিলেন তিনি। বাঁ-পা তুলনামূলকভাবে অনেকটাই দুর্বল থাকা সত্ত্বেও ক্লাব পর্যায়ে ও বাংলার হয়ে মূলত লেফট-ইনসাইড হিসেবে খেলেছেন চুনী। ভারতের হয়ে রাইট-ইনসাইড বেশি। কারণ সেখানে খেলার সময়ে তুলসীদাস বলরামকে তাঁর অভ্যস্ত লেফট-ইনসাইড পজিশন ছেড়ে দিতেন চুনী। দলগত সংহতির যা অসাধারণ দৃষ্টান্ত! বল চুনীর পায়ে যেন কথা বলত। ড্রিবল যে একসঙ্গে কতখানি শিল্পময় ও কার্যকরী হতে পারে, তা বারবার অনায়াসে দেখিয়েছেন তিনি। নিজে বেশি গোল করতে না চেয়ে, খেলা গড়ার দিকেই মূলত লক্ষ্য ছিল তাঁর। অসাধারণ স্কিমার হিসেবে গেম মেকিং-এর অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল। আর ছিল বল ট্র্যাপিং-এ বিশ্বমানের দক্ষতা। তাঁর সতীর্থ আর এক অসামান্য ফুটবলার বলরামের সঙ্গে চুনীর তুলনা, তখনকার ফুটবলপ্রেমীদের অন্যতম বিতর্ক-বিষয় ছিল। বলরামও একজন কমপ্লিট ফুটবলার ছিলেন। হেডিং-এ চুনীর থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু গেম-মেকিং–এ তুল্যমূল্য বিচারে একটু পিছনেই থাকবেন হয়তো। তবে গোল করতে বেশি দেখা গিয়েছে বলরামকে। আর চুনী বেশি প্রতিভাত হয়েছেন গোল করানোর ক্ষেত্রে। এমনকি তাঁর সময়ের আর এক যুগন্ধর পি.কে. বন্দ্যোপাধ্যায় দুরন্ত রাইটআউট হয়েও গোল করেছেন নিয়মিত। আসলে ভারতীয় ফুটবলে চুনী-পিকে-বলরাম ছিলেন একে অপরের পরিপূরক। এখান থেকেই অন্য একটা ভাবনা উঠে আসে।

পি.কে, চুনী বা বলরাম এঁরা কেউই ক্লাব পর্যায়ে এক দলে খেলেননি। শুধুমাত্র মোহনবাগান ১৯৫৬ সালে যখন ইন্দনেশিয়া-সিঙ্গাপুর সফরে খেলতে যায়, তখন ওঁরা ইস্টার্ন রেল থেকে পি.কে-কে রাইট আউট হিসেবে নিয়ে যায়। সেই সফরের কয়েকটি ম্যাচে পি.কে-চুনী মোহনবাগানের হয়ে খেলেছিলেন। অন্যদিকে, বলরাম তো কোনও সময়েই পি.কে বা চুনীর সঙ্গে এক ক্লাবে খেলেননি। অথচ এক নিশ্বাসে এঁদের তিনজনের নাম উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে যা লক্ষ্যনীয়, এই কথাটি কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ভারতীয় ফুটবলের নিরিখে – ক্লাব বা রাজ্যস্তরে নয়। এটাই বোধহয় চুনী গোস্বামীর প্রজন্মের ফুটবলারদের অনন্যতার দিক, যাঁরা ফুটবল বলতেই ভারতীয় ফুটবল–এই ধারণাটা স্পষ্ট করে তুলতে পেরেছিলেন। চুনীর আগের ব্যাচের ফুটবলার শৈলেন মান্না-আমেদ খানের সময় থেকে এই ধারণার কিছুটা সূত্রপাত হলেও, চুনী-পি.কে-দের আমলেই ‘ভারতীয় ফুটবল’ বিষয়টি গরিমার শীর্ষে ওঠে। এ বিষয়ে প্রবাদপ্রতিম প্রশিক্ষক রহিম সাহেবের একটা বিরাট অবদান ছিল।

পরাধীন ভারতে এদেশীয়দের সঙ্গে সাদা চামড়াদের ফুটবল, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। অনেক অসাধারণ খেলোয়াড় সমাবেশ তখন গড়ে উঠলেও, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যই প্রাধান্য পেত বেশি। বিদেশিদের দলকে হারানো বা তাঁদের সঙ্গে শারীরিক ভাবে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে তীব্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা কাজ করত। স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮ সালে লন্ডন অলিম্পিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের দুর্দান্ত লড়াই প্রথমবার এদেশের ফুটবল ধ্যানধারণায় একটা নাড়া দিয়েছিল। এরপর ১৯৫১ সালে শৈলেন মান্নার নেতৃত্বে দিল্লি এশিয়াডে সোনা জয় আরও একটা মাত্রা এনে দিল, যেখানে ভারতীয় দলের প্রশিক্ষণে ছিলেন রহিম সাহেব। মাঝখানে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে (১৯৫২) যুগোস্লোভিয়ার কাছে ভারত ১০-১ গোলে পর্যুদস্ত হল। তখন রহিম কোচ ছিলেন না।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। কোচিংকে দু’টি ধরনে ভাগ করা যায় – জেনারালাইজড কোচিং এবং স্পেশালাইজড কোচিং। প্রথম ক্ষেত্রে ফুটবলের প্রাথমিক পাঠ দিয়ে ফুটবলার গড়ার কাজটা করা হয়। প্রতিভার সন্ধান করে তাকে ভাল ফুটবলার তৈরি করাই এই কোচিং-এর প্রধান দিক। স্পেশালাইজড কোচিং-এ আসে সিস্টেম, স্ট্র্যাটেজি, মেথড, ইম্প্রোভাইজেশান ইত্যাদি বিষয়। এক্ষেত্রে তৈরি খেলোয়াড়দের একসূত্রে বেঁধে টিমওয়ার্ক তৈরি করে পরবর্তী সাফল্যের পথে এগনোটাই মূল লক্ষ্য থাকে। সেখানে অনেক আধুনিক ও পেশাদারি মনোভাবের দরকার হয়। প্রবাদপ্রতিম প্রশিক্ষক স্যার দুখিরাম মজুমদার থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বাঘা সোম, অচ্যুত বন্দ্যোপাধ্যায়, ল্যাংচা মিত্র প্রমুখের মতো অসামান্য কোচেরা ফুটবলার গড়ে তোলায় তাঁদের অবদান রেখেছিলেন। রহিম সাহেবও গোড়ার দিকে হায়দ্রাবাদ পুলিশে কোচিং করার সময়ে জেনারালাইজড কোচিং-এর উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়েছেন।
কিন্তু যখনই তিনি ভারতীয় দলের দায়িত্ব নিলেন, নিজের ধরন বদলে ফেললেন। একঝাঁক প্রতিভাবান পরিণত ফুটবলারদের মধ্যে প্রয়োগ করলেন তাঁর ফুটবল-বুদ্ধিমত্তা। টিম-গেম বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিজেকে তাঁদের কাছে দারুণ শ্রদ্ধাভাজন করে তুললেন এবং সর্বোপরি ক্লাব বা রাজ্যের চেয়েও দেশ সবার উপরে – ধারণাটা তিনি গেঁথে দিলেন খেলোয়াড়দের মধ্যে। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখি, তাঁর প্রশিক্ষণে ১৯৫৬ মেলবোর্ন অলিম্পিকে বদ্রু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চতুর্থ স্থান দখল, ১৯৬০ রোম অলিম্পিকে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অধিনায়কত্বে ভারতীয় ফুটবল দলের স্মরণীয় লড়াই এবং ১৯৬২ জাকার্তা এশিয়ান গেমস-এ চুনী গোস্বামীর নেতৃত্বে সোনা জয়। ১৯৫০-৬০ দশকের এই সময়টা জুড়েই সম্ভবত ক্রীড়া-প্রেমীরা মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-কেন্দ্রিক ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় ফুটবল নিয়ে গর্বে মেতে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন। তারপর থেকে আবারও আমাদের ফুটবল উন্মাদনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল সেই ক্লাবকে কেন্দ্র করে। চুনীদের এই অবদান কিন্তু ভোলার নয়।
চুনী গোস্বামী যে জনমানসে গ্ল্যামার আইডল হয়ে বিরাজ করলেন চিরকাল, তার নির্দিষ্ট কারণ খোঁজা সম্ভব নয়। তবে আন্তর্জাতিক মানের একজন ফুটবলারের পাশাপাশি রাজ্য ও পূর্বাঞ্চলে তাঁর ক্রিকেটারের ভূমিকা বোধহয় এ ব্যাপারে একটা অন্য মাত্রা দিয়েছিল।

১৯৬২-৬৩ মরসুমে প্রথম রঞ্জি ট্রফিতে অভিষেক হয় চুনীর। এ সময় ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা ওয়েস্ট ইন্ডিজ থেকে চারজন প্রথম সারির ফাস্ট বোলারকে এদেশে নিয়ে আসেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের ফাস্ট বোলিং খেলায় অভ্যস্ত করা। এই চারজন ভারতের চারটি অঞ্চলের গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন দলের হয়ে রঞ্জি কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায় থেকে অংশ নিয়েছিলেন। যেমন – লেস্টার কিং (বাংলা), রয় গিলক্রিস্ট (হায়দ্রাবাদ), চার্লি স্টেয়ার্স (মুম্বই) এবং উইলি ওয়াটসন (দিল্লি)। ২৩ ফেব্রুয়ারি(১৯৬৩) ইডেনে হয় বাংলা-হায়দ্রাবাদ কোয়ার্টার ফাইনাল। যেখানে গিলক্রিস্ট বিধ্বংসী হয়ে উঠেছিলেন। বলা যায় খেলার মানসিকতা ছেড়ে সেদিন রীতিমতো মারমুখী মনোভাব দেখিয়েছিলেন। এরকম অবস্থায় বাংলার অধিনায়ক পঙ্কজ রায়ের বুক চিতিয়ে লড়াই আজও ইতিহাস হয়ে আছে। দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। জয়সীমার নেতৃত্বে শক্তিশালী হায়দ্রাবাদ দল সে বার পরাজিত হয়েছিল বাংলার কাছে। রঞ্জি অভিষেক হওয়া চুনী গোস্বামী ভয়াবহ গিলক্রিস্ট-এর বোলিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে করেছিলেন ৪১ রান। বোলার হিসেবে দখল করেছিলেন দু’টি উইকেট এবং অসামান্য দক্ষতায় তালুবন্দি করেছিলেন দু’টি ক্যাচ। চুনী ছিলেন একজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান, স্লো মিডিয়াম পেসার (সঙ্গে লেগ ব্রেক) এবং বিশ্বমানের ফিল্ডার। ডিপ অঞ্চলে ফিল্ডিং করে বেশ কিছু অবিস্মরণীয় ক্যাচ নিয়েছেন। ফুটবল প্লেয়ার হওয়ার সুবাদে তাঁর ছিল অফুরন্ত দম ও হরিণ-গতি। তাই অনেকটা অঞ্চল কভার করে দাপটের সঙ্গে ফিল্ডিং করতেন। ভারতীয় দলে তাঁর সুযোগ পাওয়া অবশ্যই উচিত ছিল। (চলবে)
জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।


























One Response
অসাধারণ। আমি দ্বাদশ শ্রেণীর একজন ছাত্রী। এই আর্টিকেল টি আমায় ওনার জীবনী তৈরিতে খুবই সাহায্য করেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ 😌