দ্বিতীয় পর্ব শুরু করা যাক সুরকার হেমন্তের প্রসঙ্গ দিয়ে। আধুনিক গানের এক কুশলী কারিগর অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন: ‘হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গায়ক হিসেবে পাঁচজনের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাংলা চিত্রসঙ্গীত জগতে তিনি সম্রাট, সুরস্রষ্টা হিসেবে।’ কথাটা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছায়াছবির গানেই বেশি সুর করেছেন, বেসিক আধুনিক গানে কম। কিন্তু যখনই সুর করেছেন তখনই তা আদৃত হয়েছে দু’-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। তার কারণ, তিনি যেমন বুঝতেন ছবির সিচুয়েশন, তেমনি বুঝতেন বাঙালির মন। তাঁর সুরের চলন সাধারণভাবে সরল, মেলোডিতে ভরপুর, আর তেমনই হৃদয়গ্রাহী।

তাঁর সুরের মাহাত্ম্য এমনই যে, কোনও কোনও সময় দেখা গেছে ছবি হয়তো তেমন জোরাল নয়, কিন্তু গানের জন্যে মানুষ ছবিটিকে মনে রেখেছে। যেমন, ‘অদ্বিতীয়া’ (১৯৬৮) ছবিতে লতা মঙ্গেশকর- হেমন্তের দ্বৈত কণ্ঠে ‘চঞ্চল মন আনমনা হয়’, লতার ‘চঞ্চল ময়ূরী এ রাত’, হেমন্তের ‘আহা প্রজাপতি’ মানুষ ভুলতে পারে না।
[the_ad id=”266918″]
তরুণ মজুমদার পরিচালিত ‘পলাতক’ (১৯৬৩) ছবিতে কাহিনি, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী হেমন্ত লোকসুর-নির্ভর, কিন্তু স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। স্বকণ্ঠে ‘জীবনপুরের পথিক রে ভাই’, রুমা গুহ ঠাকুরতার ‘মন যে আমার কেমন কেমন করে’ বা রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্মেলক কণ্ঠে ‘আহারে, বিধিরে তোর লীলা বোঝা দায়’— প্রতিটি গানের আমেজই আলাদা। ‘অদ্বিতীয়া’ ও ‘পলাতক’ ছবিতে গীতিকার হিসেবে মুকুল দত্তের কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ‘সপ্তপদী’ (১৯৬১)-তে হেমন্ত ও সন্ধ্যার যুগ্ম কণ্ঠে ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ এবং ‘হারানো সুর’-এ (১৯৫৭) গীতা দত্তের মোহময়ী কণ্ঠে ‘তুমি যে আমার’ প্রেমের চিরকালীন গান। দু’টিরই রচয়িতা গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার।
মুম্বই থেকে কলকাতায় খুব কম সময়ের জন্যে এসে সুর ও রেকর্ডিং করলেও ‘শাপমোচন’ (১৯৫৫) ছবির প্রতিটি গান জনাদৃত: হেমন্তের ‘ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস’, ‘শোনো বন্ধু শোনো প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা’ বা ‘সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা’ (কথা: বিমলচন্দ্র ঘোষ)।
গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন যেন নিজেকে ছাপিয়ে যান ‘নীল আকাশের নীচে’ (১৯৫৯) ছবির এই গানে: ‘নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী, আর পৃথিবীর পরে ওই নীল আকাশ, তুমি দেখেছ কী?’— একটা প্রশ্ন জাগিয়ে দেয় মনে। ‘…দেখেছ কি মানুষের অশ্রু… শুনেছ কি মানুষের কান্না…’ পঙক্তির মধ্যে দিয়ে হেমন্ত আমাদের হৃদয় ছুঁয়ে যান মরমী সুরে আর দরদী গায়নে। এই ছবির ‘ও নদী রে’–ও উল্লেখযোগ্য।
[the_ad id=”266919″]
‘মরুতীর্থ হিংলাজ’ (১৯৫৯) ছবিতে ঈশ্বরের টানে দুর্গম পথ পাড়ি-দেওয়া তীর্থযাত্রীদের কণ্ঠে স্বতঃ উঠে আসে ‘পথের ক্লান্তি ভুলে’ বা ‘তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ’। হৃদয়স্পর্শী সুরে ও গায়নে হেমন্ত গান দু’টিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যান। এখানে হেমন্তের কথায় সমবেত অংশে গলা মিলিয়েছেন লতা মঙ্গেশকর ও গীতা দত্ত।
কী মিষ্টি করেই না হেমন্ত গাইলেন ‘কুহক’ (১৯৬০) ছবিতে: ‘আরও কাছে এসো’। পাশেই ‘বিষ্ণুপ্রিয়া গো’ গানে আবার কীর্তনের ছোঁয়া। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় হেমন্তের মেলোডি-ভরা সুরকে মান্যতা দেন ‘সূর্যমুখী’ ছবিতে (১৯৫৫) ‘আকাশের অস্তরাগে’ বা ‘নায়িকা সংবাদ’-এর (১৯৬৭) ‘কী মিষ্টি দেখ মিষ্টি’, ‘কেন এ হৃদয়’ গানে। কোনও কোনও গান আগে বোঝা যায়নি, পরবর্তীকালে শ্রোতারা সেসব গানের মাধুর্য অনুভব করেছেন, যেমন ‘বিভাস’ (১৯৬৪) ছবির ‘আজ তারায় তারায় জ্বলুক বাতি’ বা ‘এতদিন পরে তুমি’। একেবারে আনকোরা শিল্পী সুজাতা চক্রবর্তী, তাঁকে দিয়ে হেমন্ত গাওয়ালেন ‘অতল জলের আহ্বান’ (১৯৬২) ছবিতে: ‘ভুল সবই ভুল’— মানুষ আজও মনে রেখেছেন সেই গান।
[the_ad id=”270084″]
নবীন সম্ভাবনাময় শিল্পীদের প্রতি হেমন্ত বরাবরই সদয়। অরুন্ধতী হোম চৌধুরীকে ব্যবহার করলেন ‘স্বাতী’ (১৯৭৭) ছবিতে: ‘যেতে যেতে কিছু কথা’ বা ‘গোধূলির স্বর্ণরাগে’। ‘ভালোবাসা ভালোবাসা’-ছবিতে (১৯৮৬) তরুণ শিবাজী চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে গাওয়ালেন ‘খোঁপার ওই গোলাপ দিয়ে’ বা ‘এই ছন্দ এই আনন্দ’। দু’জনেই তারপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।
কোনও কোনও ছবিতে আবার হেমন্ত অন্য ধারার, অন্য ক্ষেত্রের শিল্পীকে সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ‘ফুলেশ্বরী’-তে (১৯৭৪) প্রবীণ প্রতিভাধর অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে গাওয়ালেন ‘আমি তোমায় বড় ভালোবাসি’— একটা অন্য আমেজ নিয়ে এল সেই গান। সঙ্গীতবহুল এই ছবি হেমন্ত মাতিয়ে দেন গানে গানে: ‘টাপুর টুপুর বৃষ্টি ঝরে’, ‘ফুলেশ্বরী ফুলেশ্বরী’ বা ‘তুমি শতদল হয়ে ফুটলে’ প্রভৃতি।
এমনই আরও একটি মন-মাতানো গানের ছবি ‘রাগ অনুরাগ’ (১৯৭৫) ভরে রইল হেমন্তের বৈচিত্র্যময় গানে গানে: ‘কী গান শোনাব বলো’, ‘সেই দুটি চোখ’। সুরযোজনার ক্ষেত্রেও হেমন্ত সবসময় কিন্তু সহজ পথে হাঁটেননি। এ ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চয় মনে পড়বে কিশোরকুমারের ‘শিং নেই তবু নাম তার সিংহ’ ( লুকোচুরি, ১৯৫৮), লতা মঙ্গেশকরের ‘কেন গেল পরবাসে’ বা ‘আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন’ (মনিহার, ১৯৬৬), আশা ভোঁসলের ‘যখন তোমার গানের সরগম’ (প্রক্সি, ১৯৭৭) কিংবা মান্না দে-র কণ্ঠে ‘এই মাল নিয়ে চিরকাল’ (অদ্বিতীয়া, ১৯৬৮)।
বেসিক রেকর্ডে কম সুর করলেও যখনই করেছেন তা সমাদর পেয়েছে। যেমন, লতা মঙ্গেশকরের ‘প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে’, ‘ও পলাশ ও শিমুল’, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বড় সাধ জাগে’, ‘আঁধার আমার ভাল লাগে’, হৈমন্তী শুক্লার ‘ওগো বৃষ্টি আমার’, অমল মুখোপাধ্যায়ের ‘এই পৃথিবীতে সারাটি জীবন’, চন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়ের ‘সেই শান্ত ছায়ায় ঘেরা’, রানু মুখোপাধ্যায়ের ‘আমিও শ্রাবণ হয়ে’, অমৃক সিং অরোরার ‘রূপসী দোহাই তোমার’ ইত্যাদি। নিজের সুরে হেমন্তের নিজের বেসিক গান ‘আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি’, ‘অলির কথা শুনে’ বা ‘না যেও না’ আজও মনে দোলা দিয়ে যায়।
[the_ad id=”270085″]
মুম্বইয়ের হিন্দি সিনেমার জগতেও হেমন্ত সুখ্যাত শিল্পী ও সুরকার হিসেবে। সেখানে তিনি সবার প্রিয় হেমন্তকুমার। ১৯৪২-এ ‘মীনাক্ষী’ ছবিতে পঙ্কজকুমার মল্লিকের সুরে প্রথম প্লেব্যাক করলেও হিন্দি চলচ্চিত্রের সঙ্গে তাঁর প্রথম প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে গত শতকের পাঁচের দশকের গোড়ায়, যখন হেমেন গুপ্তের আহ্বানে মুম্বই গেলেন ‘ফিল্মিস্তানে‘ যোগ দিতে, সুরকার হিসেবে। প্রথম সুর দিলেন ‘আনন্দমঠ‘ (১৯৫২) ছবিতে। সুরকার রূপে মুম্বইয়ে প্রতিষ্ঠা পেলেন ‘নাগিন’ ছবিতে (১৯৫৪)। এই সিনেমায় লতার গাওয়া ‘মন ডোলে’ সকলের মন দোলাল। তার আগেই অবিশ্যি গায়ক রূপে হেমন্ত শ্রোতাদের মন জয় করেছেন শচীন দেব বর্মনের সুরে ‘জাল’ (১৯৫২) ছবিতে ‘ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনি’ গেয়ে।
মোটামুটিভাবে সাতের দশকের শেষ পর্যন্ত তিনি হিন্দি ছবিতে সুর দিয়েছেন, গেয়েছেন। তাঁর সুরে মনে রাখার মতো গান: লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে ‘কহি দীপ জ্বলে কহি দিল’ (বিশ সাল বাদ, ১৯৬২), ‘কুছ দিল নে কাহা’ (অনুপমা, ১৯৬৬), আশা ভোঁসলের ‘মেরি বাত রহি’, গীতা দত্তের ‘না যাও সইয়াঁ’ (সাহেব বিবি ঔর গুলাম, ১৯৬২), কিশোরকুমারের ‘ও শাম’ ( খামোশী, ১৯৬৯) প্রভৃতি। স্বকৃত সুরে নিজের গলায় স্মরণযোগ্য গান: ‘বেকারার কারকে হমে’ (বিশ সাল বাদ), ‘ইয়া দিল কি শুনো’ (অনুপমা), ‘তুম পুকার লো’ (খামোশী), ‘ইয়ে নয়ন ডরে ডরে’ ( কোহরা) প্রভৃতি। অন্যান্য সুরকারের সুরে তাঁর উল্লেখযোগ্য গান: শচীনদেবের সুরে ‘জানে ও ক্যায়সে’ ( পিয়াসা, ১৯৫৭), ‘হ্যায় আপনা দিল’ (সোলভা সাল, ১৯৫৮), সলিল চৌধুরীর সুরে ‘গঙ্গা আয়ে কাঁহা সে’ (কাবুলিওয়ালা, ১৯৬১ )।
হেমন্তের বিশেষ ভালবাসার জায়গা ছিল রবীন্দ্রনাথের গান। প্রথম জীবনে যাঁর সঙ্গীত-সান্নিধ্যে সর্বাধিক উপকৃত হয়েছিলেন, সেই শৈলেশ দত্তগুপ্তই হেমন্তকে এই রত্নখনির সন্ধান দেন। সঙ্গীতজীবনের প্রায় শুরু থেকেই আধুনিক, ছায়াছবির গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন, রেকর্ড করেছেন।

এখানেও সহায়ক তাঁর মধুর কণ্ঠ, স্পষ্ট উচ্চারণ এবং স্বচ্ছন্দ গায়ন। যে কোনও শ্রোতারই পছন্দের গান তাঁর ‘যখন পড়বে না মোর’, ‘প্রাঙ্গণে মোর শিরীষ শাখায়’, ‘এই কথাটি মনে রেখো’, ‘চলে যায়, মরি হায়’, ‘ওগো নদী আপনবেগে’ ইত্যাদি। নানা ছবিতেও রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছেন, সার্থকভাবে প্ৰয়োগও করেছেন।
এই সূত্রে বিশেষ ভাবে মনে পড়ে ‘বিভাস’ (১৯৬৪), কুহেলী’ (১৯৭১), ‘অগ্নীশ্বর’ (১৯৭৫), ‘দাদার কীর্তি’ (১৯৮০) প্রভৃতি ছবির কথা। আলাদাভাবে অবশ্যই বলতে হবে ‘দাদার কীর্তি’ ছবিতে তাপস পালের লিপে তাঁর গাওয়া ‘চরণ ধরিতে দিও গো’ গানটি। স্মরণীয় নিবেদন। অন্যান্য গীতিকারের গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ছায়াছবিতে অতুলপ্রসাদী ‘কে তুমি বসি’ ( ক্ষণিকের অতিথি), ‘আমায় রাখতে যদি’ (চেনা অচেনা), নজরুলগীতি ‘পথ চলিতে যদি চকিতে’ (বারবধূ), তাছাড়া বেসিক রেকর্ডে রজনীকান্তের ‘ওই বধির যবনিকা’, ‘আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে’।
[the_ad id=”270086″]
এমন এক ক্ষণজন্মা প্রতিভাশালী শিল্পীর কিন্তু কোনও সরকারি সম্মান জোটেনি। সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে যথোচিত সম্মান জানিয়েছে। কালের নিয়মেই মানুষ আসে, চলে যায়। থেকে যায় তাঁর কৃতি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত-কৃতিকে আমাদের মনে রাখতেই হবে, কেননা তাঁকে ভুললে বাংলা সংস্কৃতিকেই ভুলে যেতে হয়।
স্বপন সোম এ কালের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সংগীত গবেষক। গান শিখেছেন মোহন সোম, মায়া সেন ও সুভাষ চৌধুরীর মতো কিংবদন্তীদের কাছে। দীর্ঘদিন ধরে 'দেশ' পত্রিকায় সংগীত সমালোচনা করেছেনl গান নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দেশ', 'আনন্দলোক', 'সানন্দা', 'আজকাল', 'এই সময়', 'প্রতিদিন' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়l



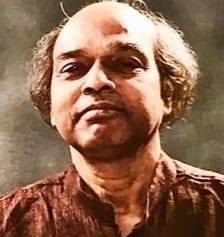





















2 Responses
ভারি সুন্দর লেখা।
hemanta babur smrticharan ti porhe mone anek kathai phire elo. sei dirghadehi manushti, chokhe chasma, parane haat gutano sada shirt ar dhutir knochati shirter pockete gnoja. Charakdangar morher A C Pal er kagajer dokane ek dista lekhar kagaj kinte esechhen. Oti nomra kantthaswar – takhan thakten Indira cinema haller samne Indra Ray Roader ekti flat barhir tin tolay , dak bakse lekha thakto Hemanta Mukhopadhyay – achhe / nai !! uni porhechhilen Bhabanipur Mitra Institutione , jekhane amio porhechhilam –
ami thaktam kachhei – Harish Mukherjee Rd e Parimal Sen chhilen onar tabalchi – prai asten tnar barhi !!! e sab ki ajker katha — ki manush ! ki kahini! Ki jiban – ar ki kanttha!! ami jakhankar katha bolchhi , takhono Gayer Bodhu beroy ni – Columbia theke bachhare dui ki tnti vinyl disc; duti gan thakto -ar amra adhir agrohe kono recorder dokaner samne dnarhie suntam !!!! Bhabishyate aro asankhya bar onar samne bose gaan sunechhi – asadharan daradia golar Rabindrasangeet — se ki bholbar !!!! porhe borho ananda pelam anek anek dhanyabad lekhakke….