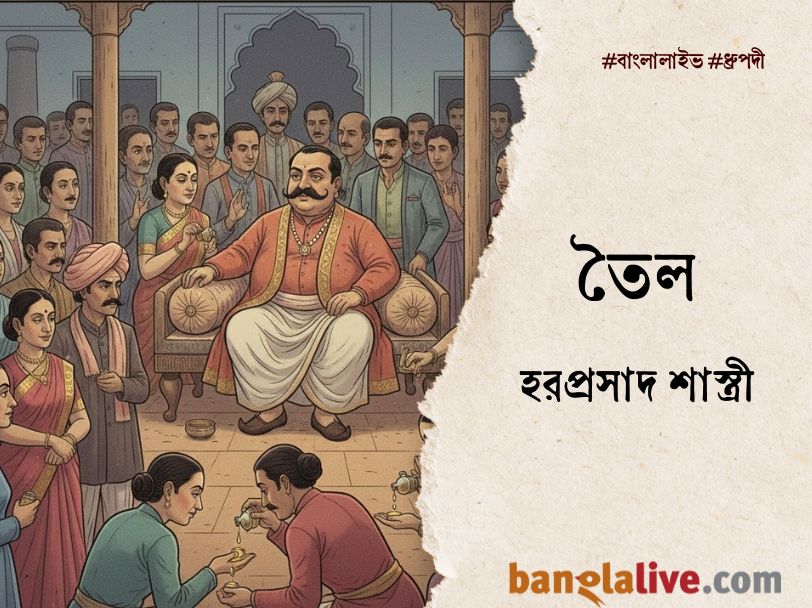জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন যখন ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন ১৮৪৯ সালে, স্কুলের নাম তখন হিন্দু ফিমেল স্কুল। ভারতবর্ষের মাটিতে প্রথম মহিলা স্কুল স্থাপিত হল, মানবী ইতিহাসে পড়ল প্রথম আঁচড়। এই বিদ্যালয় স্থাপনের প্রেক্ষাপটে, প্রবল বিরোধিতা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সুবিশাল অস্তিত্ব যদিও আজ আমাদের গর্বিত নথি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
সময়রেখার প্রায় একই বিন্দুতে মেয়েদের পড়াশোনা শেখাবার জন্য তৈরি হতে চলেছে আর এক বিশাল কর্মকাণ্ড। আগের পর্বে আমরা দেখেছি সাবিত্রীবাঈ নিজেকে রীতিমতো প্রস্তুত করছেন এই কর্মকাণ্ডের অংশ হতে। মিস মিচেলের নরমাল স্কুল এবং মিস ফারারের টিচিং ইন্সটিটিউটের পাঠ একসঙ্গে শেষ করে মহিলা শিক্ষয়িত্রী হতে চলেছেন সাবিত্রী।
১৮৫১ সালে আহমেদনগর থেকে শিক্ষা সম্পূর্ণ করে ফেরেন সাবিত্রী। ১৮৫১ সালেই প্রথম দলিত মেয়েদের স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সাবিত্রীবাঈ ফুলে, জ্যোতিবা ফুলে ছাড়াও এই ইতিহাসের গর্বিত অংশ হয়ে থাকেন তত্তসাহেব শিন্ডে, ঠিক যেমনভাবে ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার ‒ কারণ, তত্তসাহেবের বাড়িতেই প্রথম শুরু হয় সাবিত্রী বাঈ-এর পরিচালনায় স্কুল। ১৮৫১-১৮৫৩ এই দু’বছরের মধ্যে পুণে ও তার সংলগ্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয় মেয়েদের তিনটি স্কুল। দু’টি দলিত মেয়েদের জন্য, একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীভুক্ত মেয়েদের জন্য। জ্যোতিবা, সাবিত্রী ছাড়াও সঙ্গে ছিলেন উসমান শেখ, কেশরাম বাভালকর-সহ অন্য অনেকে।
দলিত মেয়েদের বাড়ি থেকে বের করে আনতে সমর্থ হন সাবিত্রী, ফতিমারা। এমনিতেও উচ্চবর্গের মেয়েদের মতো পর্দাপ্রথার খুব একটা প্রচলন ছিল না দলিত মেয়েদের মধ্যে। জীবিকার প্রয়োজনে মাটির অনেক কাছাকাছি থাকতে হয় তাঁদের। সাবিত্রী মেয়েদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে থাকেন, তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা উন্নত হতে পারে, যদি তাঁরা সাবিত্রীর স্কুলে আসেন। কারণ, সেখানে শুধু পড়াশোনা তো নয়, মাটির বাসন তৈরি করা, কাঠের জিনিস তৈরি করার মতো অসংখ্য বৃত্তিমূলক শিক্ষারও সুযোগ ছিল।
তাছাড়া সাবিত্রীদের স্কুলের চেহারাও তো আর গ্রামের পাঠশালার মতো নয়। বিদেশি কায়দার কালো বোর্ড আছে সেখানে, চক দিয়ে লেখা হয়। তালপাতায় লিখতে হয় না– পাতায় দোয়াত কলম দিয়ে লেখা যায়। আর সবথেকে বড় কথা, তাঁদের পড়ানোর জন্য আছেন মেয়ে মাস্টারমশাইরা – সাবিত্রীবাঈ, ফতিমা, সাগুনাবাঈরা।
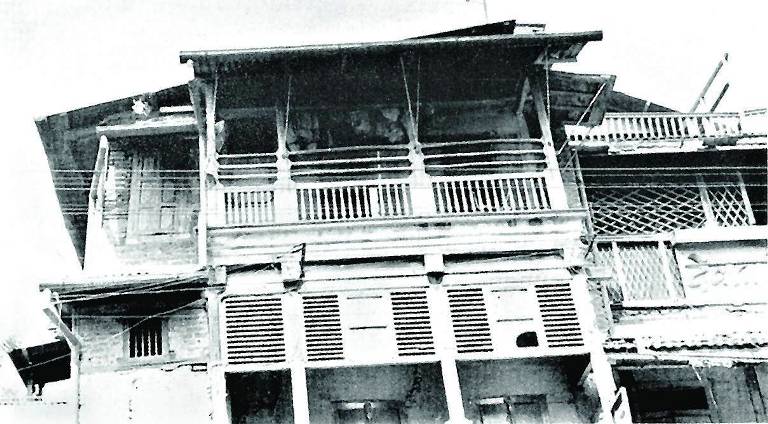
সাবিত্রীবাঈয়ের সঙ্গে ফতিমার আলাপ হয়েছিল উসমান শেখের বাড়িতে, আমরা আগেই দেখেছি। ভবিষ্যতে সাবিত্রীবাঈ, জ্যোতিবার কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবেন ভাইবোন দু’জনেই– মানবীবিদ্যার ইতিহাস, দলিত শিক্ষার ইতিহাস মনে রাখবে তাঁদের। ফতিমা শেখের কথা বলব আমরাও, পরবর্তী পর্বে। দলিত সাবিত্রী মানবী ইতিহাসের মূলধারাকে ছুড়ে দেওয়া এক সাহসী প্রশ্নচিহ্ন হলে ফতিমা শেখও সংখ্যালঘু অবস্থান থেকে তোলা আরও এক প্রশ্ন।
মাহার আর মাঙদের পড়াবার অপরাধে বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়ে কীভাবে জ্যোতিবা তাঁর সংখ্যালঘু বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় পান, পরে কীভাবে সস্ত্রীক সে বাড়িতে থাকতে শুরু করেন, ফতিমা কীভাবে সমানতালে যুক্ত হয়ে পড়েন তাঁদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে– তা আজকের ধর্মবিভক্ত বর্তমানের কাছে দগদগে বিস্ময় হয়ে দাঁড়ায়। এই সাহসী অবস্থান, এই ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থান, উচ্চবর্গের সামনে বা উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে মাথা তোলার অবস্থান, এই শিক্ষা আন্দোলনকে অবাক করা সাফল্যে মুড়ে দেয়।
১৮৫১ থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে তৈরি হয় ১৮টি স্কুল– ছেলেদের এবং মেয়েদের। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার কাছাকাছি সময়, বম্বে প্রেসিডেন্সিতে মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, মিশনারিদের উদ্যোগে। সাফল্যের মুখ দেখেনি এই প্রচেষ্টা, ছাত্রীর অভাবে বন্ধ হয়ে যায় দু’বছরের মধ্যে। ছাত্রীসংখ্যার অকুলানের নথি বেথুনস্কুলের ক্ষেত্রেও অবশ্য গোড়ায় পাই আমরা।
সাবিত্রী-জ্যোতিবাদের স্কুলের ইতিহাস কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই আঠেরোটি স্কুলের মধ্যে যে তিনটি স্কুল ছিল পুণেতে, তার ছাত্রীসংখ্যা ছিল দেড়শো, যা তৎকালীন প্রশাসন বা সমাজের চোখেও যেমন অবাক করা, ইতিহাসের দূরবীন দিয়ে বিচার করলেও বিস্ময়কর। কারণ সেই একইসময়ে বেথুনস্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র একুশ! পুণের স্কুলে চোখ ধাঁধানো পরিকাঠামো, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ, মহিলা শিক্ষয়িত্রীদের উপস্থিতি বদলে ফেলছিল নারীশিক্ষার সোপানের ইতিহাস। আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের নিরিখে এ কম কথা নয়।
আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করছেন, হয়তো আর্থ-সামাজিক ভেদাভেদ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে। উচ্চশ্রেণীর মেয়েদের তুলনায় কম পর্দাপ্রথায় থাকা, আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন, দলিত বা নিম্নবর্গীয় মেয়েদের বেশি সংখ্যায় স্কুলে যোগদানের কারণ হতে পারে। ইতিহাস বলে যে বেথুনস্কুলে পড়তেও মূলত উৎসাহী ছিলেন বৈষ্ণব বা বৈরাগ সম্প্রদায়ের ছাত্রীরা। স্কুলে তখন ছাত্রীসংখ্যা কম, তাই স্কুল কর্তৃপক্ষও উৎসাহী হন। কিন্তু সেই ছাত্রীদের সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থান নিম্নবর্গীয়, এই কারণে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রীদের অভিভাবকেরা আপত্তি জানান। তাই নিম্নবর্গের ছাত্রীরা সেখানে প্রবাশাধিকার পায় না, ফলে ছাত্রীসংখ্যার সমস্যার স্থায়ী সমাধানও হয় না।

ইতিহাস পরবর্তীকালে নিজের অনেক ভুল নিজেই সংশোধন করে নিয়েছে। মেয়েদের পড়াশোনা করার অধিকার নিয়ে ক্ষতবিক্ষত সমাজ বাধ্য হয়েছে, সেই অধিকার দিতে। একই কথা সম্ভবত দলিতশিক্ষা, দলিত মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে প্রযোজ্য। শুধু অবাক করে সময়রেখা। ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লড়ছেন বিধবাবিবাহ আইন নিয়ে, সাবিত্রীবাঈ প্রতিষ্ঠা করছেন দলিত মেয়েদের স্কুল।
তারপর প্রায় দেড়শো বছর কেটে গেছে। অনেক সংবিধান সংরক্ষণের পরেও দলিতদের পড়াশোনার হার উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৬%, মাত্র ২.৭% দলিত উচ্চশিক্ষা পেয়েছেন, দলিত মেয়েদের ক্ষেত্রে এই শতাংশ হিসেব আরও কম।
ইতিহাস, তুমি দ্রুত হাঁটতে শেখোনি?
*ছবি সৌজন্য: লেখক
*আগের পর্বের লিংক: [পর্ব ১], [পর্ব ২]
* তথ্যসূত্র:
১. ‘দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অফ ধ্যানজ্যোতি ক্রান্তিজ্যোতি সাবিত্রীবাঈ ফুলে’; আলোক, নূপুর প্রীতি; ২০১৬
২.‘কাস্ট, কনফ্লিক্ট অ্যান্ড আইডিওলোজিঃ মাহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে অ্যাড লো কাস্ট প্রোটেস্ট ইন্ নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া’; ও’হানলন, রোজালিন্ড; ২০০২
৩.‘এ টেল অফ টু রিভোল্টস্’; গান্ধী, রাজমোহন; ২০০৯
‘কালেক্টেড ওয়ার্কস্ অফ্ মাহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে’ ভলিউম ১-২, গভর্নমেন্ট অফ মহারাষ্ট্র, ১৯৯১
ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।