আমি একজন চাকরি-করা মা। মানে সোজা বাংলায় ওয়র্কিং মাদার। আচ্ছা ওয়র্কিং ফাদার এই শব্দবন্ধটি কেউ শুনেছেন কখনও? আমি কিন্তু শুনিনি। কেন? কারণ, বাবারা চাকরি বা বাইরের কাজ করবেন সেটাই তো স্বাভাবিক। তাই না? সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই শ্রম ও উপার্জন পুরুষের অধিকার। তাই আর আলাদা করে বলার কী আছে? কিন্তু মা যদি বাইরের জগতে গিয়ে কাজ করেন সেটাকে আলাদা করে দেখার দরকার আছে। তাই এই শব্দবন্ধের সৃষ্টি।
বাবা বাজার, দোকান, অফিস, কেনাকাটা সামলাবেন আর মা বাড়িতে রান্না বা ঘরের কাজ করবেন, সন্তানপালন করবেন, এই আদর্শ চিত্র একটা সময় পর্যন্ত খুবই স্বাভাবিক ছিল বাড়িতে বাড়িতে। খুব জানতে ইচ্ছে করে যে এই ছবিটা, অবয়বটা তৈরি হল কীভাবে? শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই হয়তো মায়েদের কাজের প্রয়োজনে বাইরে বেরনো শুরু। প্রথম দিকে কিছু পেশা, যেমন সেবিকা বা নার্স, শিক্ষিকা, টাইপিস্ট, এ ধরনের কিছু চাকরি নির্দিষ্ট ছিল মেয়েদের জন্যে এদেশে। শ্রীমতী সুধা মূর্তির একমাত্র মহিলা ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে টেলকো-তে চাকরি পাওয়ার ঘটনা এখনও জীবন্ত ইতিহাস।
চাকরি-করা মা বললেই যে ছবিটা ভেসে ওঠে চোখে, সেটা একজন খুব ক্লান্ত অথচ নিরন্তর কাজ করে চলা নারীর ছবি, যিনি ঘরে বাইরে সমানে দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কোনও সুবিধা আলাদা করে আমাদের সমাজ অন্তত দেয় না তাকে। অফিসে তাকে মনে রাখতে হয় সংসার, আবার বাড়িতে মনে রাখতে হয় অফিসের কথা। দু’ জায়গাতেই ভাব এমন করতে হয় যেন তাঁর অন্য জগতটা সে ভুলে এসেছে।
বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই হয়তো ছবিটা পালটাতে সুরু করে এদেশে। ষাটের দশকে স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন, এমন একজনের কাছে শুনেছি, ভোর চারটেয় উঠে কয়লার উনুন ধরিয়ে রান্না করে ছুটে ছুটে স্কুলে যেতেন। স্কুল থেকে ফিরেই আবার রাতের রান্না। এর মধ্যেই ঘরের যাবতীয় কাজ। বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে জীবন সংগ্রাম কাকে বলে তাঁরা জানতেন। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বিয়ের পরে চাকরি ছেড়ে দিতেন অধিকাংশ মেয়ে। আর বাচ্চা হলে তো কথাই নেই।

আমাদের ছোটবেলায় অনেকেই কোনও চাকরি-করা মেয়ের বিয়ের সময় বলতেন, “শ্বশুরবাড়ি খুব ভাল, চাকরি করতে দেবে বলেছে।” আবার তাঁরাই বাচ্চা হবার পরে বলতেন “অনেক চাকরি করেছ, এবার মন দিয়ে বাচ্চা মানুষ কর। মনে রেখ তুমি একজন মা।” অবাক লাগছে? তাহলে বলি, ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশেও বিয়ের পরে চাকরি করতে গেলে স্বামীর লিখিত অনুমোদন লাগত। বেশিদিন আগের কথা নয়, ১৯৬৫-তে বাতিল হয় এই নিয়ম। আয়ারল্যান্ড ১৯৭৫ সালে এসে বিবাহিত মহিলাদের বাড়ির বাইরে কাজ করার স্বাধীনতা দেয়। সেখানে আমাদের দেশে, শ্রীমতী সুচেতা ক্রিপালনি ১৯৬৩-তে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন। কিন্তু সে তো কোটিতে গুটিক মাত্র!
বেশি দূরে যেতে হবে না, আমার বাড়ির স্মৃতি বলি। আমার মা–বাবা, দু’জনেই চাকরি করতেন একই অফিসে। বাবা সকালে বাজার করে এনে স্নান করে খেয়ে দৌড়ে অফিস চলে যেতেন। খুব গর্ব করতেন নিজের সময়ানুবর্তিতা নিয়ে। আর মা সকালে উঠে রান্না করে, আমাদের স্নান-খাওয়া করিয়ে, অসুস্থ ঠাকুমার সারা দিনের ওষুধ ও পথ্য বুঝিয়ে দিয়ে, অধিকাংশ দিন নিজে না-খেয়ে, দৌড়ে বাস ধরে, লাল কালির দাগ খেতেন মাঝেমাঝেই। অফিস থেকে দুপুরে মা ফোন করতেন আমি স্কুল থেকে ফিরলাম কিনা, খেয়েছি কিনা, জানতে।
এর মধ্যেই কবে আমার ও দিদির পরীক্ষা, কবে বিয়েবাড়ি, কবে বন্ধুর জন্মদিন, কবে দিদিমার আসার কথা, কবে গ্যাস বুক করতে হবে, কবে ঠাকুমার ওষুধ ফুরিয়ে গেল, টিফিন খেলাম কিনা, কবে লন্ড্রি থেকে কাপড় আনতে হবে, কে পাড়ায় অসুস্থ তার খোঁজ নেওয়া, রবিবার দুপরে আমার আঁকার ক্লাস, নাচের স্কুলের অনুষ্ঠান, লাইব্রেরি থেকে বই বদল, শীতকালে সোয়েটার বোনা বা মেলায় যাওয়া, এই জাতীয় কাজের বা অকাজের বিরাম ছিল না। আশির দশকে অতিথিরাও সত্যিই যখন তখন এসে পড়তেন। আমার স্কুলে ভর্তির ইন্টারভিউতে শিক্ষিকারা বলেছিলেন চাকরি করা মায়ের মেয়েকে আমরা ভর্তি নিই না। যেন মা প্রতি পদে সঙ্গে না থাকলেই সন্তানের পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী।

তার অনেকগুলো বছর পরে যখন আমি মা হলাম, তখনও দেখলাম ছবিটা খুব একটা পালটায়নি। বহুদিন চাকরি করার পরে এক অভিজ্ঞ সহকর্মী দিদি চাকরি ছেড়ে দিলেন। কারণ জিগ্যেস করাতে বললেন “শাশুড়ি মারা গেছেন, মেয়ে বড় হচ্ছে, ওকে কে দেখবে বল?” এই ‘মেয়েকে দেখার জন্যে চাকরি ছেড়ে দেবার দায়’ তাঁর স্বামীর নেই স্বাভাবিকভাবেই।
আর একটি খুব সম্ভাবনাময় যোগ্য মেয়ে মিষ্টি করে হেসে একদিন বলল, “চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি। কিছুদিন পরে ডেলিভারি, আমার সন্তানকে দেখার মত বাড়িতে কেউ নেই। এইটুকু তো করতেই হবে বল?” নারী দিবসের এক অনুষ্ঠানে অফিসের একজন বলেছিলেন “আমাদের বাড়ি খুবই আধুনিক, আমার স্ত্রী এখনও চাকরি করছেন, ছেলে হবার পরেও।”
একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ের আগে পুরুষ সহকর্মী ভাবেন প্রেজেন্টেশনটা কেমন হবে, বস কি কি প্রশ্ন করতে পারেন, এইসব। আমি কী ভাবি? “মেয়ে স্কুল থেকে এল কি না, আমার ড্রেসটা ঠিক আছে কিনা, মেয়ের স্কুলের প্রজেক্ট-এর কোনও জিনিস কেনা হয়নি” এইসব। মিটিংয়ের মধ্যে হঠাৎ করে ফোন আসে, “মা আমার অঙ্কের বই কোথায়?” পুরুষ সহকর্মী যখন বলেন “কাল তাড়াতাড়ি বেরব, ছেলের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান আছে”, বেশ প্রচ্ছন্ন গর্ব ঝরে পড়ে স্বরে। আর মায়েরা কোনওরকমে কাঁচুমাচু করে বলেন। চাকরির ইন্টারভিউতে মেয়েদের কিছুদিন আগে পর্যন্ত জিগ্যেস করা হত শিগগিরই বিয়ের কোনও প্ল্যান আছে কিনা, কিম্বা “আপনার বাচ্চাকে বাড়িতে কে দেখবে?” কোনও মেয়ে সেটার জবাবে বলেন না “নিশ্চয়ই আপনি দেখবেন না !”
অনেকসময় মেয়েরা অফিসে সন্তান সম্ভাবনার কথা জানাতেই চান না প্রথম দিকে, কারণ বস শুধু ভাববেন নানা কারণে এর তো শুধু ছুটি দরকার হবে। পদোন্নতি হাতছাড়া হবে, গুরুত্বপূর্ণ কাজও, রাতারাতি আপনি সবার চোখে একটি ‘লায়াবিলিটি’তে পরিণত হবেন, যার কাছ থেকে কোনও উৎপাদনশীলতা না পেলেও মাস মাইনে দিয়ে যেতে হবে। ‘আমি অকর্মণ্য নই’, তা প্রমাণিত করার দায়বদ্ধতা কর্পোরেট পৃথিবীতে শুধু মায়েদেরই।
সন্তানকে যদি বাবা সময় দেন, ন্যাপি চেঞ্জ করে দেন, পড়াতে বসেন, গল্প শোনান, তিনি খুবই ভাল ও দায়িত্ববান বাবা। সমাজে বা আত্মীয়মহলে তাঁর প্রশংসা হয়। মা একই কাজ করলে, সে আবার আলাদা করে বলার কী আছে? সন্তানের আগমন সব মায়ের কাছেই খুশির খবর, চাকরি-করা মায়ের কাছে কিন্তু কিছুটা ত্রাসেরও।
সংগঠিত ক্ষেত্রে আগে সব মিলিয়ে সবেতন ছুটি পাওয়া যেত ৮৪ দিন, এখন বেড়ে ১৮০ দিন। তার মধ্যেই সন্তানকে আয়া মাসি বা শাশুড়ি বা মায়ের কাছে রেখে ঘুম ঠেলে কাজের জায়গায় ফিরে যাওয়া। সদ্যোজাত শিশুকে সারা রাত সামলে, খাইয়ে, ঘুম পাড়িয়ে, নিজে জেগে, পরের দিন আবার অফিস। সেখানে নতুন বাবাকে মা কিম্বা শাশুড়ি মা বলেন, “তুমি অন্য ঘরে গিয়ে শোও, বিশ্রাম নাও।”

কিন্তু মা অফিস থেকে ফিরলেই আয়ামাসি দৌড় লাগাবেন। তাঁরও তো সময়ের দাম আছে! অতএব দ্বিতীয় শিফটের কাজ শুরু বাড়িতে। দিনের পর দিন যাঁরা এটা করেছেন শুধু তাঁরাই জানেন, কেমন কেটে যায় দিনগুলো। বাথরুমে গিয়ে কান্না মোছেন মা, মনে হয় আজই চাকরিটা ছেড়ে দেব। তারপরে আবার চোখেমুখে জল দিয়ে ফিরে যেতে হয় নিজের জায়গায়। ভাব করতে হয় যেন কিছুই হয় নি। ১৮০ দিন পর কাজে ফিরে কেমন অভিজ্ঞতা হয়? একটু জেনে নেবেন আশেপাশের কোনও নতুন মায়ের কাছে! দিন বদলায় মাসে বা বছরে, অভিজ্ঞতা পালটায় না।
সন্তান একটু বড় হয়ে স্কুলে ঢুকলেই আবার অন্য সমস্যা। স্কুল গেটে রোজ নিতে যান যে মায়েরা, তারা সবই ভাল জানেন, বেশি জানেন। ক্রমাগত হোঁচট খেতে থাকি, কোনও কোনওদিন ভুল বই পাঠিয়ে ফেলি। সেই অন্য মায়েরাও আমাদের অবস্থা দেখে কিছুটা সাহায্য করে দেন। মেয়েও প্রশ্ন করে, ‘তুমি আমাকে স্কুলে নিতে যাও না কেন?’ কোনওদিন বন্ধুর জন্মদিনে বিকেলে নেমন্তন্ন করলে ভয় পাই, নিয়ে যাবে কে?
সন্তান একটু দুষ্টু হলে বাড়ি ঢোকামাত্রই দাদু ঠাকুমা নালিশ জানাতে থাকেন সমস্বরে। আমরা মায়েরা ভাবি বাচ্চাটা নয়, আমাদেরই বলা হচ্ছে। মা একটু দেরি করে ফিরলে তো কথাই নেই। অফিস পার্টিতে সুরা বা সিগারেট হাতে কোনও মহিলাকে দেখলে এখনও কেউ কেউ বলেন “তাহলে ভাব ওর বাচ্চা কী শিখবে? মা-ই যদি এ রকম হয়?” অবশ্যই যে বাবা বাড়িতে নিজের সংগ্রহে গর্ব করে সাজিয়ে রাখেন দামি সুরা, তাঁকে দেখে বাচ্চারা কিছুই শেখে না।

টাইম ম্যানেজমেন্টের পাঠগুলো আপনি বাস্তবে শিখে নিতে পারবেন এই মায়েদের থেকে। মুম্বইতে ট্রেনে করে ফেরার সময় সবজি কাটা হোক আর কাপড় কাচার সাবানের বিজ্ঞাপনে রাতে ঘুম থেকে উঠে কাপড় কাচা হোক, ঘড়ির বিরুদ্ধে সর্বদাই দৌড়চ্ছেন এঁরা। অবসাদ আসে, বিষণ্ণতাও, তবু তার চেয়েও বেশি ভয় পরের দিনের ঘড়ির অ্যালার্মকে। আক্ষরিক অর্থেই এঁরা আমাদের দশভুজা। শুধু চার দিন নিয়ম করে পুজো হয় না এঁদের।
একটু বড় হলে ছেলেমেয়েরা নিজেরা নিজেদের জগতে ঢুকে যায়। যেখানে মাকে বলা যায়, “তুমি তো সারাদিন ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকবে।” সন্তানের পরীক্ষার ফল ভাল না হলে দোষ সেই মায়ের। “মা চাকরি করলে তো এটা হবেই।” সন্তানকে রোজ নিত্যনতুন টিফিন বানিয়ে দেওয়ার সময়টুকু থাকে না অনেক মায়েরই। অনেকেই মনের অস্বস্তি ঢাকতে বাচ্চাকে দিয়ে দেন টাকা, দামি উপহার বা মোবাইল। লকডাউনে কর্মরতা মা বাসন মাজতে মাজতে কনফারেন্স কল করছেন বা ঘর মুছতে মুছতে মেয়েকে পড়া বোঝাচ্ছেন, সে চিত্রটাও ফেরত এল। ঘর আর বাহির ভেঙেচুরে মিলেমিশে একাকার। তসলিমা নাসরিন তাঁর একাকী জীবনযাপনের চিত্র নিয়ে সামাজিক মাধ্যমেই লিখে ফেললেন, যে ঘরের কাজ করতে গিয়ে তিনি লেখার সময় টুকুও পান না, অথচ তাঁর প্রতিবেশি দিব্যি রোজ নিয়ম করে লিখছেন। প্রতিবেশির স্ত্রী ঘরের কাজ সেরে গান নিয়ে বসার সময় পান কিনা তা তাঁর জানা নেই।
এসবই অবশ্য শহুরে শিক্ষিতা মায়ের সমস্যা। তাহলে ভাবুন আমার-আপনার অফিসে নিরাপত্তারক্ষী বা সাফাইকর্মীর কাজ করেন যে মা, তাঁর কথা? যিনি পার্লারে কাজ করেন? বা যিনি ফুলের দোকান বা রোলের দোকান চালান? যাঁর সন্তান সন্ধেটা ওই দোকানের নীচে রাস্তার আলোতে বসেই কাটিয়ে দেয়? কিম্বা একদম অসংগঠিত জায়গায় কাজ করা শ্রমিক মা? এ এক আশ্চর্য দোলাচল, যা প্রতিটি মুহূর্তে চলতে থাকে মায়েদের, মেয়েদের মনে।
তাহলে ভবিষ্যতে কি মা হবার আগে মেয়েরা আর একটু ভাববে? উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকলে মা না হওয়াই ভাল, এমনটা ভাববে? কিম্বা হাজারো সমস্যাতেও মুখ বুজে থাকবে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে, যাতে বাচ্চা যত্নে থাকে? নাকি আয়া মাসি বা ক্রেশই সম্বল এঁদের? হাজার হোক, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে সব মেনে নেওয়া। প্রশ্নগুলো সহজ হলেও উত্তর অজানা।
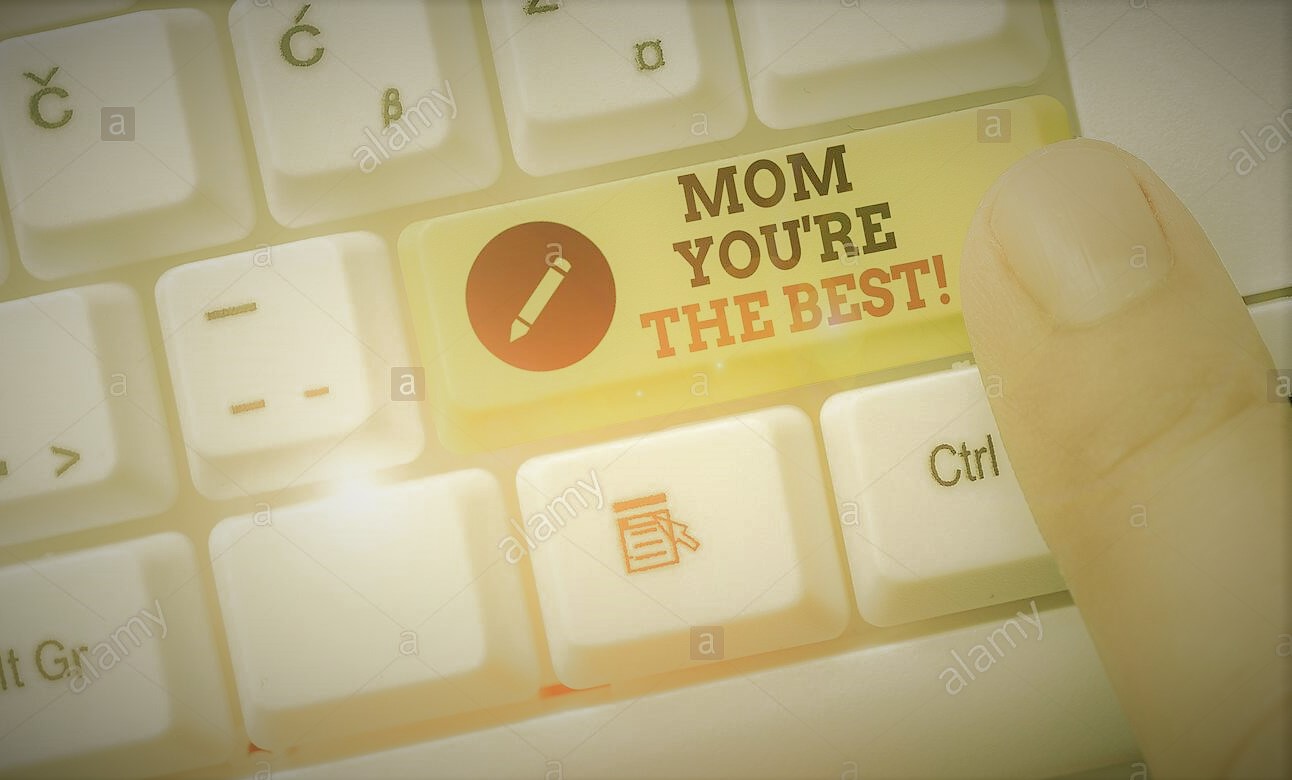
ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, থাকবেও। বাবারাও গত এক দেড় দশকে পালটেছেন অনেকটাই। এত সবকিছুর মধ্যে আশার আলো এই যে আপনার সন্তান একদিন হয়তো বুঝবে এই দোটানা। একদিন হয়তো বুঝবে, মাথা উঁচু করে থাকার জন্যে কতখানি ঝুঁকতে হয়েছিল আপনাকে? বাচ্চারাও বুঝে যায়, স্বাবলম্বী হয়। অফিস থেকে মা ফিরলে জলের বোতল এগিয়ে দেয়, বেরনোর সময় রোজ বলে “সাবধানে যেও মা।” মা কে একদিন ছোট্ট হাতে লিখে দেয়, “you are the best”… অনেক না পাওয়ার মধ্যে ওইটুকুই তো পরম পাওয়া!
*ছবি সৌজন্য: thriveglobal.com, wellable.com, texasdiversitymagazine.com
কর্পোরেট সংস্থায় এইচ আর-এর ভূমিকায় যুক্ত সিলভার পছন্দ গান, খাওয়াদাওয়া আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা। লেখালেখি করেন শখে আর অনুরোধে।
























6 Responses
Bhishon bhalo laglo pore, chele howar por shara raat na ghumie bhor 7 theke onsite call bikele shongshar er kaaj abar raat jaga die onek bochor kete gelo. Tomar proti ta kotha bhishon mon ke chue gelo. Thank you for voicing for us. I really hope this will be an eye opener for the society and they will not judge a new mother and try to help as much as they can. Khub bhalo theko ar aro lekhar opekhyaye roilam.
Khub sotti kotha likhecho.
ashadharan madam. porchi abar porchi.. kemon jeno khub shotti kotha gulo sundor kore sajiye tullen apni lekhar modhye diye.. amar maa chakri koren ni..ebang na korar karon hoyto anek tai amra dui bhai.. jai hok apnake kurnish ei satyer samne amake dar koranor jonno… karon satyo ekdom nirbhejal… namaskar
একদম খাঁটি কথা লিখেছিস,অসংখ্য ‘working mother’দের রোজনামচা এরকমই । আর অহরহ তারা এক অসম্ভব অনুতাপ এবং guilt বয়ে নিয়ে বেড়ায়। তবে আজকালের বাবারা ও বদলেছে অনেক … আমার বাড়িতেই সকলের কাজ ভাগ করা, যাতে সবাই contribute করে সংসার চালানোর কাজে।
একদম খাঁটি কথা লিখেছিস,অসংখ্য ‘working mother’দের রোজনামচা এরকমই । আর অহরহ তারা এক অসম্ভব অনুতাপ এবং guilt বয়ে নিয়ে বেড়ায়। তবে আজকালের বাবারা ও বদলেছে অনেক … আমার বাড়িতেই সকলের কাজ ভাগ করা, যাতে সবাই contribute করে সংসার চালানোর কাজে।
সিলভা খুব ভালো লিখেছ তুমি। তোমার লেখা পড়ে বুকের মধ্যে চাপা অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা কিছু কথা বেরিয়ে আসতে চাইল। জীবন টাকে অন্যভাবে মেয়েরা সাজাতে চায় কিন্তু সে ভুলে যায় সমাজ তাকে সেই কাজ করতে দেবেনা।আমার মনে হয় নারীরা দশোভূজা এই আখ্যাটা জবরদস্তি চাপানো হয়েছে। “নারী স্বাধীনতা” কথাটার সাথে পরিচয় হয়েছে মাত্র আমরা নারী স্বাধীনতা এখনো আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি।তুমি আরও লেখ সিলভা,অপেক্ষায় থাকলাম।