১৩৭৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বই প্রকাশ পায়, যার নাম ‘অন্য দেশের কবিতা’। সেই গ্রন্থের মধ্যে ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কবিতার অনুবাদ। প্রত্যেক কবিরই দু’টি করে অনূদিত কবিতা ছিল সেখানে। সে-বইয়ে, পূর্বলেখ হিসেবে ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখিত নাতিদীর্ঘ কিন্তু অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধ। সেই প্রবন্ধে পাওয়া যায় এমন একটি বাক্য: ‘অবচেতনের উদ্ধার‒ এছাড়া স্বর্গ ও পৃথিবীকে মেলাবার আর কোনও উপায় নেই সাহিত্যে।’ এখন ১৪২৭ বঙ্গাব্দের মাঘ মাস। অর্থাৎ ঠিক চুয়ান্ন বছর আগে লিখিত হয়েছিল এই বাক্যটি। ফরাসি কবিতায় সুররিয়্যালিজ়মের উন্মেষ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই বাক্য ব্যবহার করেন সুনীল।

‘অবচেতনের উদ্ধার’ কাকে বলে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম যুগের কবিতায় আছে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ‘হে প্রেম হে নৈঃশব্দ’, ‘ধর্মে আছ জিরাফেও আছ’, ‘সোনার মাছি খুন করেছি’, ‘অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে’, ‘হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান’‒ এইসব কাব্যগ্রন্থ ষাটের দশকে একের পর এক প্রকাশিত হয়ে চলেছিল‒ সত্তর সালে প্রকাশিত হয় শক্তির ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলি’ নামক একশোটি সনেটের সংগ্রহ, সেইসব সনেটও লেখা হয়েছিল ষাটের দশকে। অর্থাৎ ষাটের দশকে লিখিত শক্তির অজস্র কবিতার মধ্যে লক্ষ করা যাবে ‘অবচেতনের উদ্ধার’, এই কথাটি কী ধরনের কাব্যের উদ্ভাসন আমাদের সামনে নিয়ে আসছে।
শক্তির বিখ্যাত কবিতা ‘জরাসন্ধ’ থেকে কয়েকটি লাইন বললে হয়তো আভাস পাওয়া যাবে ‘অবচেতনের উদ্ধার’ বলতে ঠিক কী বোঝায়।
‘…পচা ধানের গন্ধ, শ্যাওলার গন্ধ, ডুবোজলে তেচোকো মাছের আঁশগন্ধ সব আমার অন্ধকার অনুভবের ঘরে সারি-সারি তোর ভাঁড়ারের নুন-মশলার পাত্র হল, মা। আমি যখন অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না, তখন তোর জরায় ভর করে এ আমায় কোথায় নিয়ে এলি। আমি কখনও অনঙ্গ অন্ধকারের হাত দেখি না, পা দেখি না।
কোমল বাতাস এলে ভাবি, কাছেই সমুদ্র। তুই তোর জরার হাতে কঠিন বাঁধন দিস। অর্থ হয়, আমার যা-কিছু আছে তার অন্ধকার নিয়ে নাইতে নামলে সমুদ্র সরে যাবে শীতল সরে যাবে মৃত্যু সরে যাবে।
তবে হয়তো মৃত্যু প্রসব করেছিস জীবনের ভুলে। অন্ধকার আছি, অন্ধকার থাকব, বা অন্ধকার হব।
আমাকে তুই আনলি কেন, ফিরিয়ে নে।।’
এই কবিতায় যে আবহাওয়া তৈরি হল, সে-আবহাওয়া অর্থের অতীত। বাইরে থেকে কোনও মানে করা যাবে না এ-কবিতার। এ কেবল মনের একেবারে অতল থেকে উঠে আসা আলো-অন্ধকারময় এক রহস্যময় চলচ্ছবির ধারা, যার ভিতর ঢুকে পড়লে পথ হারায় পাঠক। কিন্তু কবিতার এই অলৌকিক ভূতগ্রস্ত আবহাওয়া তাকে টানে, টেনে নিতেই থাকে নিশির ডাকের মতো।
[the_ad id=”270088″]
অথবা অন্য একটি কবিতায় পাওয়া যায় শক্তি কী বলছেন, কীভাবে বলছেন, তার স্বরপ্রয়োগ কীরকম আলাদা হয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টান্ত। সেই লেখাটি আমরা দেখি বরং।
অন্ধকারে বেজে ওঠে‒ ‘যাই’
চেয়ে দেখি, কেহ কোথা নাই
দেওদার-সড়কে
এ-নিশুতি রাতে গাড়ি ঢোকে
শুকতারা পুবে
আমারই অস্তিত্ব যেন আছে মেঘে ডুবে
গাড়ি থেকে তার
লুণ্ঠন সমাপ্ত হলে রক্তমাখা হাড়
এসে পড়ে
বহুদিন ছিলাম না ঘরে
দুয়ার জানালা খোলা নাই
তুমি এসেছিলে‒ চিহ্ন পাই
প্রিয়, পথ জুড়ে
অন্ধকারে বেজে ওঠে‒ ‘যাই’
চেয়ে দেখি, কেহ কোথা নাই
তৃণে ও অঙ্কুরে
এই কবিতার নাম ‘অন্ধকারে’। এ কবিতা থেকে গোটা গোটা করে ধরবার মতো কোনও মানে কি পাওয়া গেল? না। শব্দের বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে চলে এসেছে এ কবিতা। শক্তি তাঁর প্রথম যৌবনের অনেক কবিতার মতো এখানেও কবিতায় উল্লম্ফন ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, যেন জলস্রোত বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদীর— তার মাঝখানে একটা দু’টো তিনটে চারটে প্রস্তরখণ্ড রাখা। সেই প্রস্তরখণ্ডে ধাক্কা দিয়ে চলেছে বেগময়ী জলধারা। কেউ একজন প্রথম পাথর থেকে লাফ দিয়ে তৃতীয় পাথরে পৌঁছে টাল সামলে দাঁড়াল। পরক্ষণেই তৃতীয় পাথর থেকে চতুর্থ পঞ্চম প্রস্তর পার হয়ে তার পরের পাথরের মাথায় চলে গেল। এইভাবে শক্তিও, অর্থের পর অর্থস্তর লাফ দিয়ে পার হয়ে চলেছেন। সঙ্গে চলেছে কবিতাটি। পাঠকের শুধু তাঁকে যথাসাধ্য অনুসরণ করে চলা ছাড়া আর কিছু করার নেই।
***
শক্তির কবিতা, প্রধানত ‘অবচেতনের উদ্ধার’ যেমন, তেমনই জঙ্গল-নদী-পাহাড়-গ্রাম সব আত্মসাৎ করতে করতে চলা এক ভ্রমণপ্রিয় পথিকের যাত্রাপথও। ‘বনের ভিতরে তিনি গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ।’ অথবা ‘পাতার সহস্রতম চোখ’‒ এইসব টুকরো লাইনে বোঝা যায়, গাছ ও অরণ্য শক্তিকে কীরকমভাবে আকর্ষণ করত। একটি কবিতার আরম্ভ এরকম: ‘অস্থিরতার সূত্র কোথায়?/ ভাবতে ভাবতে বনস্থলীর সবক’টি ঘাট পেরিয়ে এলাম, সামনে নদী‒’ এখন, এই অস্থিরতার সূত্র কোথায়? এই লাইনটির কি কোনও নির্দিষ্ট, একক, একটিমাত্র মানে করা সম্ভব? আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়। এ-কবিতা প্রকাশ পায় ১৯৭১ সালের একটি পুজোসংখ্যায়। আজ পঞ্চাশ বছর হতে চলল, লাইনটি আমার মুখস্থ। বারবার মনে হানা দেয়। কিন্তু স্থির একটি অর্থ নিয়ে দাঁড়ায় না। গত পঞ্চাশ বছরে জীবন কত বদলেছে আমার। সেই সঙ্গে এই লাইনটিও তার অর্থসঙ্কেত বদল করেছে।
[the_ad id=”270086″]
সঙ্কেত। এই হল শক্তির কবিতার আরও একটি আবশ্যিক ধর্ম। শক্তির শ্রেষ্ঠ সময়ের কবিতা, তাঁর প্রথম দিকের অন্তত দশটি বই, কবিতার সঙ্কেতধর্মকে প্রমাণ করে। নিয়ে আসে আশ্চর্য সব চিত্রমালা। আমরা ছবির পর ছবির ভেতরে হারিয়ে যাই আর কেবলই সন্ধান করতে থাকি, কবি এখানে কোথায় লুকিয়ে আছেন। সেই সঙ্গে দিশাহারার মতো কবিতাটির মর্মে প্রবিষ্ট হতে থাকি। কবিতাটি আমাদের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট একটি অর্থ পায় কি?
এই অবিস্মরণীয় রহস্যময়তাও শক্তির প্রধান একটি কাব্যসামর্থ্য। যেমন, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত ‘প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই’ গ্রন্থের দু’টি লাইন বলি: ‘বনের মধ্যে কে যায়?/ মনের মধ্যে দৃষ্টি আমার বর্ষাতিটা ভেজায়/ কে যায় এবং কে কে?/ এক ভাঙা ইট থাকল পড়ে হায় রে আমার থেকে।’
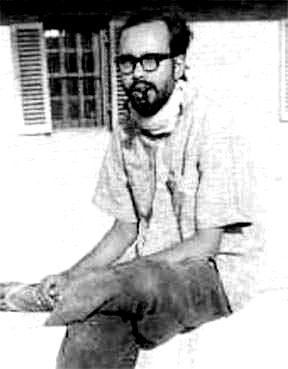
এই যে লাইনগুলি তুললাম, এর মধ্যে ‘বনের মধ্যে কে যায়?’ এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা পেলাম ‘মনের মধ্যে বৃষ্টি আমার বর্ষাতিটা ভেজায়।’ বনের মধ্যে কে যায়, তার কথা কিন্তু আর ফিরে এল না কবিতায়। এল, এইভাবে, ‘কে যায় এবং কে কে?’ অর্থাৎ একজন নয়। সংখ্যায় একের অধিক বনযাত্রীরা আছেন এখানে। তারও উত্তর মিলল শুধু এই কথায় যে, ‘এক ভাঙা ইট থাকল পড়ে হায় রে আমার থেকে।’ বনযাত্রীদলের কোনও উল্লেখই আমরা কবিতায় আর দেখতে পেলাম না।
এরকমই হল কবিতা রচনাকালে শক্তির উল্লম্ফনরীতির প্রয়োগ। তা ছাড়া, শক্তির কবিতায় থাকত বহু অর্থস্তর। সঙ্কেত দিয়ে সেইসব অর্থস্তরকে স্পর্শ করতে করতে অগ্রসর হত শক্তির কবিতা। এবং তিনি যখন লিখতেন, তখন নিজের মধ্যে থেকে যেন বেরিয়ে যেতেন অথবা নিজের অন্তঃস্থলে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হতেন। ঠিক কী ঘটত, তা কি আমাদের মতো বাইরের লোকের পক্ষে বলা সম্ভব?
[the_ad id=”270085″]
‘পদ্যাপদ্য সম্পর্কে সামান্য’ এই শিরোনামের তলায় শক্তি একটি সংক্ষিপ্ত গদ্যরচনা লিখেছিলেন, নিজের কবিতা-লেখা বিষয়ে। বইয়ের ছাপা পৃষ্ঠায় আড়াই পাতার বেশি নয় সেই রচনা। সেখানে শক্তি বলছেন: ‘তারপর কীভাবে যে প্রকৃতপক্ষে একা হয়ে গেলাম। সবাই একদিন একা হয়। এতে বৈশিষ্ট্য নেই কিছুই। তবে আজন্মই একা ছিলাম আমি। এখন সেই একাকিত্বেও ভাঙন ধরল। একার থেকেও একাতম হলাম। পদ্য আমি আকাশ বাতাস জল হাওয়া থেকে কুড়িয়ে পাইনি কোনোদিন।… লিখতে বসলে তবেই লেখা। তার আগে আমি কেমন যেন! যখন লিখতে বসতাম তখন জলের মতো অনর্গল পদ্য‒ এমনকী একটি বসায় পঁচিশ-তিরিশ পদ্য লিখে চিৎপাত হয়েছি। পদ্য লেখার পর আর আমার কোনো কায়িক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তখন আমি শক্তির মড়া।’
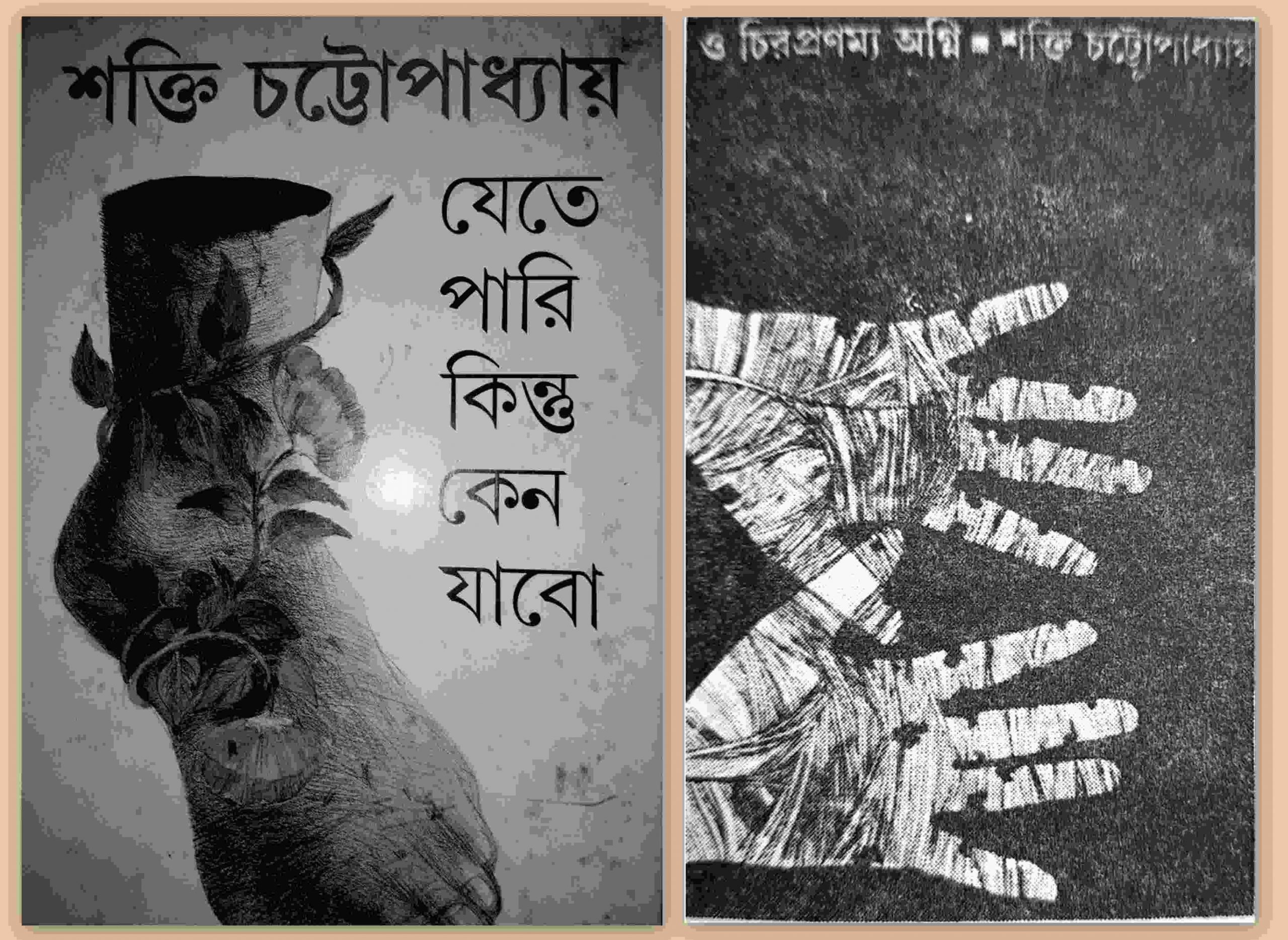
এই তো বলছেন, কবিতা লেখার পর ‘আমি শক্তির মড়া’‒ অথচ এর বিপরীত দৃষ্টান্ত যে অন্যের সাক্ষ্যে পাইনি, তা নয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উপরে সবচেয়ে বেশি কাজ যিনি করেছেন, সবচেয়ে প্রামাণ্য কাজ, তাঁর নাম সমীর সেনগুপ্ত। ২০১২ সালে তিনি প্রয়াত হন। শক্তির অন্তত দু’টি আশ্চর্য বই, যা আসলে ছড়ানো-ছেটানো লেখা জড়ো করে তৈরি হয়েছিল, যথাক্রমে ‘অগ্রন্থিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়’ ও ‘অগ্রন্থিত পদ্যগদ্য’‒ সে-বই দু’টিরই পরিশ্রমী সংগ্রাহক ছিলেন সমীর সেনগুপ্ত। এই সংগ্রাহক একটি লেখায় জানাচ্ছেন,
‘যে কোনো জায়গায় যে কোনো অবস্থায় অনুরুদ্ধ হয়ে বা না-হয়েও, শক্তির কবিতা লিখে দেওয়ার অজস্র কাহিনী লোকমুখেমুখে চলিত আছে। ‘মুল্যাঁ রুজ়’ বার-এর নামাঙ্কিত ও ঝোললাঞ্ছিত কাগজের রুমালের ওপরে আশ্চর্য কবিতা ‘কিছু আছে’, যার প্রথম লাইন ‘দুঃখের সমস্তকিছু আছে, শুধু অলঙ্কার নেই’-এর পাণ্ডুলিপি আমি নিজের চোখে দেখেছি। বইমেলার মাঠে ক্ষুদ্র উজানপত্রের কবিতাপ্রার্থী তরুণ সম্পাদকের পিঠকে টেবিলের মতো ব্যবহার করে তৎক্ষণাৎ কবিতা লিখে দিতে দেখেছি শক্তিকে।’
এই বিবরণ জেনে আমরা বিমূঢ় হয়ে পড়ি। তবে এখানেই না-থেমে সংগ্রাহক ও বন্ধু সমীর সেনগুপ্ত আরও জানিয়েছেন, যেকোনও সময়েই যেন কানায় কানায় টইটম্বুর হয়ে থাকতেন শক্তি, কবিতা লেখার ব্যাপারে‒ সামান্যতম নাড়া লাগলেই তা উক্তি হয়ে উপচে পড়ত।
[the_ad id=”270084″]
এক্ষুণি যে শক্তির ‘পদ্যাপদ্য সম্পর্কে সামান্য’ নামক গদ্যলেখা থেকে তুলে দিয়ে বললাম, শক্তি বলছেন ‘পদ্য লেখার পর আর আমার কোনো কায়িক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। তখন আমি শক্তির মড়া।’ এর বিপরীত সাক্ষ্যও পেয়েছি বললাম না? সেই সাক্ষ্যই সমীর সেনগুপ্তর রচনা থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ‘অগ্রন্থিত পদ্যগদ্য’ নামক সংকলনের সম্পাদক হিসেবে কথা বলতে বলতে এই সাক্ষ্য দিয়েছেন সমীর সেনগুপ্ত। তিনি জানাচ্ছেন, হিজলি হাইস্কুলে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোয়ার্টারে চিরভ্রাম্যমাণ শক্তি উপস্থিত হয়েছেন বন্ধু সমীর সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে। সমীরের লেখা থেকে অবিকল কথাগুলি যদি তুলে দিই, তা হলে পাই:
‘মহুয়াসিক্ত দ্বিপ্রহরে যেদিন ‘অবনী বাড়ি আছ’ আর ‘আমি স্বেচ্ছাচারী’ লিখে প্রথম শ্রোতা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিল (শক্তি)‒ সেদিন সেইসঙ্গে আরো তিন চারটি সদ্যরচিত কবিতা শুনেছিলাম ওর মুখে। ঘরের মধ্যে আমি আর শক্তি, বাইরে জ্বলন্ত দ্বিপ্রহর। লেখা শেষ করে একহাতে গেলাসে মহুয়া পাশের সাঁওতাল গ্রাম চিত্রাপাথর থেকে সংগ্রহ করে আনা, অন্যহাতে সদ্যরচিত পাণ্ডুলিপি, উন্মত্ত দরবেশের মতোই লুঙ্গি পরা খালি গায়ে শক্তি পদদাপ করে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঈষৎ স্খলিত উচ্চকণ্ঠে সেই টাটকা কবিতা পড়তে পড়তে। পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু সুকৃতির পুণ্য সঞ্চিত থাকলে তবে এমন ঘটনার সাক্ষী হওয়া যায়‒ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঈশ্বরের এমন একজন ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বীর।’
সমীর সেনগুপ্ত যে তাঁর শক্তি-বিষয়ক এই অভিজ্ঞতা আমাদের জন্যে লিখে রেখে গেছেন, এও এক সৌভাগ্য আমাদের।

তাহলে আমরা দেখলাম, কবিতা লেখার পরেই শক্তি যে নিজের সম্পর্কে বলছেন, তিনি শক্তির মড়া হয়ে যান‒ সে কথার সঙ্গে মেলে না, এমন দৃষ্টান্তও শক্তি নিজেই রেখে গেছেন।
‘অবচেতনের উদ্ধার’‒ এই কথাটির প্রমাণ শক্তির পরিণত বয়সের কাব্যেও আমরা দেখতে পাই। যেমন: ‘লেজে ভর দিয়ে আমি দাঁড়াইনি চাঁদ খাব বলে…’ কী ভয়ঙ্কর এক চিত্রকল্প। কোন অতিদীর্ঘ মহানাগ লেজে ভর দিয়ে উঠে গেছে চাঁদ পর্যন্ত? অতিপ্রাকৃতিক এমন ছবি পাওয়া যাবে শক্তির সনেটেও। যেমন: ‘জিরাফের রক্তাপ্লুত গলা দেখা যায়’‒ লিখেছিলেন তিনি।
মাত্র ৬১ বছর বয়সে প্রয়াত হন শক্তি। তাঁর জীবনপ্রান্তের কবিতা অনেক শান্ত হয়ে এসেছিল। জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর শেষ বইয়ের নাম ‘জঙ্গল বিষাদে আছে’। জঙ্গলে অকস্মাৎ বেড়াতে চলে যাওয়া ছিল শক্তির বিশেষ প্রিয় একটি কাজ। সে বিষয়ে কবিতাও আছে অনেক। স্ত্রী মীনাক্ষী সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন শক্তিকে নিয়ে, যার নাম ‘আন্তরিক পর্যটনে’। সে-বই পড়লে শক্তিকে গভীরভাবে চেনা যায়। জানতে পারি আমরা, যে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত ছিলেন তিনি শেষের কয়েকটি বছর। আর কবিতায় আবারও ফিরে এসেছিল নিসর্গ। তবে, এবারের নিসর্গচিত্রে তাঁর নিজের বাড়ি, ‘পূর্বাঙ্গনা’ নামক আবাসনে নিজহস্তে তৈরি ফুলের বাগিচার উপস্থিতি বেশি। কবিতাগুলির মধ্যে বয়স, বিষাদ, মৃত্যুকল্পনা এসে দাঁড়িয়েছিল।
[the_ad id=”266919″]
শক্তির প্রয়াণের সময় তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ছিল ৪৭টি। তারও পরে আরও দু’টি একক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পায় স্ত্রী মীনাক্ষীর যত্নে, যথাক্রমে ‘কিছু মায়া রয়ে গেল’ এবং ‘সকলে প্রত্যেকে একা’। ১৯৯৫-এ তাঁর প্রয়াণের প্রায় আট বছর পরে বেরয় সমীর সেনগুপ্ত সম্পাদিত ‘অগ্রন্থিত পদ্যগদ্য’। অর্থাৎ তাঁর কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা ৫০। আর সম্প্রতি বেরিয়েছে শক্তির অনুবাদ করা সমস্ত কবিতা নিয়ে ‘অনুবাদিত পদ্য’ নামক খুবই মূল্যবান এক গ্রন্থ। শক্তি যে এত কবিতা অনুবাদ করে গেছেন, শক্তির জীবৎকালে সে কথা যেন কেউ মনে রাখিনি আমরা।
শক্তির কবিতার কথা ভাবতে গেলে আমাদের মনে পড়বেই সেই ‘অবচেতনের উদ্ধার’ বাক্যবন্ধটি। কারণ শক্তির কবিতায় আমরা যা খুঁজে পাব, তা হল অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব। অপ্রত্যাশিতকে ডেকে এনে বারবার তাঁর কবিতাকে ঐশ্বর্যময় করে তুলেছিলেন শক্তি, সে কথার প্রমাণ হিসেবে আমাদের জন্যে রয়ে গেছে তাঁর সমস্ত কবিতার বই।
[the_ad id=”266918″]
প্রয়াণের কিছুকাল আগে স্নায়ুরোগ থেকে আমর্ম মুক্তি প্রার্থনা করে তিনি লিখেছিলেন এক অসামান্য কবিতা ‘আমাকে জাগাও’। ‘সেগুনমঞ্জরী হাতে ধাক্কা দাও, আমাকে জাগাও’ বলে উঠেছিলেন শক্তি। তাঁর সেই কবিতা এ কথাও বলে উঠেছিল, ‘আমাকে জাগাও তুমি সেই পদ্মবনে/ যেখানে ছোবল দেবে সাপে সর্বক্ষণ’‒ কী মর্মদাহ করে দেওয়া উচ্চারণ, ভাবলে অবাক লাগে। দাহের কথা যখন উঠলই, তখন না বলে পারছি না ‘আমাকে জাগাও’ কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতার প্রথম দু’টি লাইন:
তুমি গোটা জীবন যা জ্বলতে পারতে আমিও জ্বলেছি
জ্বলেছি বলেই আছি জ্বলন্ত সংসারে এক স্তব…
প্রথম লাইনটি আমাদের বেদনার্ত করে, কিন্তু দ্বিতীয় লাইনে এসেই আমরা দেখতে পাই সমস্ত জ্বলন এক স্তবে রূপান্তরিত হচ্ছে। একদিকে আগুন আর আগুন‒ আর অন্যদিকে স্তব। অরণ্যের স্তব, নদী প্রান্তর বৃক্ষ পুষ্করিণী, পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ির স্তব, এই বাংলার সমস্ত নিসর্গের স্তব স্পর্শ করে করে শক্তির কবিতা পৌঁছে যায় এক অলৌকিকের কাছে। সেই অলৌকিক কাব্যমালা আমাদের কাছে রেখে এক চিরপলায়মানতার দিকে পৌঁছে যান শক্তি।
জয় গোস্বামীর জন্ম ১৯৫৪ সালে, কলকাতায়। শৈশব কৈশোর কেটেছে রানাঘাটে। দেশ পত্রিকাতে চাকরি করেছেন বহু বছর। আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দু'বার - ১৯৯০ সালে 'ঘুমিয়েছ ঝাউপাতা?' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ১৯৯৮ সালে 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' কাব্যোপন্যাসের জন্য। ১৯৯৭ সালে পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি পুরস্কার। দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন কবিতার সাহচর্যে। ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি.লিট পেয়েছেন।




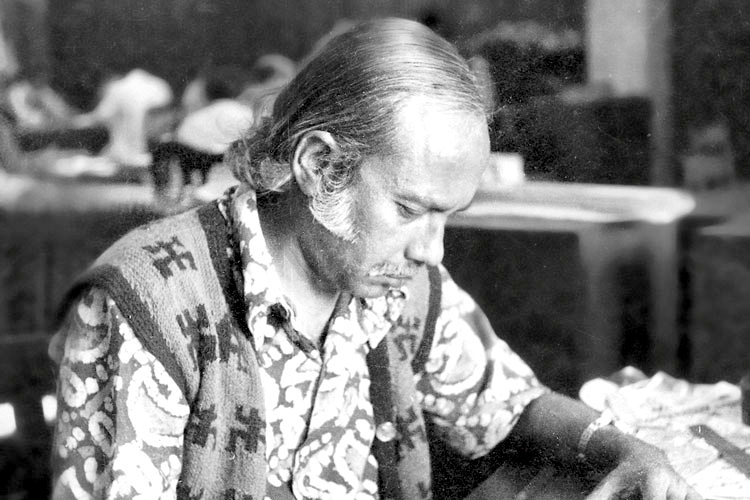





















One Response
এ লেখা নিয়ে মন্তব্য করা দুঃসাহসের পরিচায়ক। যাঁকে নিয়ে এই লেখা এবং যিনি লিখেছেন দুজনের জন্যই হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন পাতা। কোন বিশেষণই তাই মনের ভাবটি তুলে ধরার উপযুক্ত মনে হচ্ছে না।