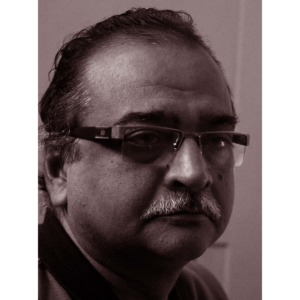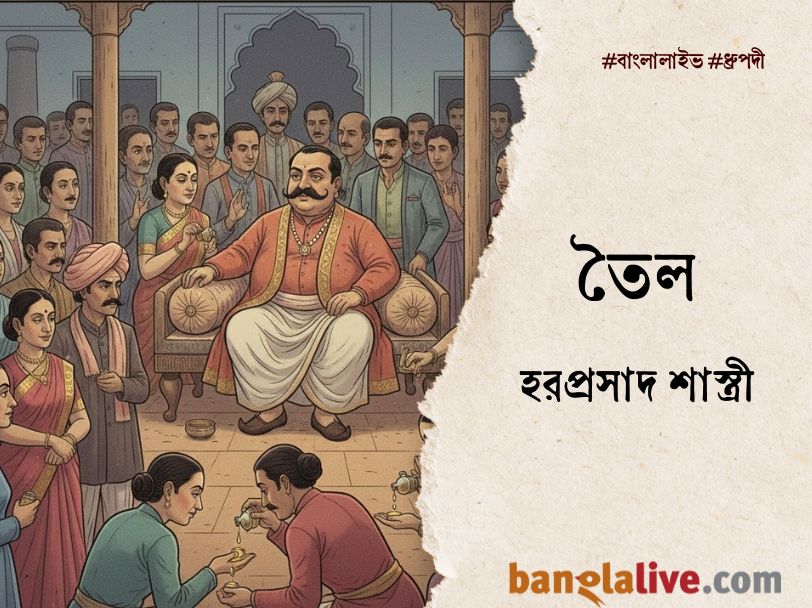দুর্গাপুরে যে স্কুলে আমি পড়েছি, সেই স্কুলটা খুব একটা পদের না হলেও, মাস্টারমশাইদের পদমর্যাদা যে ছিল ষোলোর উপর আঠেরো আনা, তা পদে পদে বোঝা যেত তাঁদের পদক্ষেপ আর ক্লাসের বাইরে ছাত্রদের পদসন্ধির (নিলডাউন) বহর দেখে। মাস্টারমশাই জিনিসটি যে ঠিক কী, সেটা আমাদের গাঁট্টা-নিলডাউন চড়–থাপ্পড় বেতের আদর সহযোগে পা থেকে মাথা অবধি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল ইংরিজি আর অঙ্ক খুবই কঠিন বিষয়। এগুলোকে ভয় পাওয়াই শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহ্য। পিতা প্রপিতামহরাও পেয়ে এসেছেন।
এরকম এক ইস্কুল থেকে– মানে যাকে বলে জ্বলন্ত কটাহ থেকে উঠে এসে ঝপাস্ করে পড়লাম বিশ্বভারতীর প্রশান্ত মহাসাগরে। আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশী কেউ কেউ বিজ্ঞের মতো মুখ করে বলেছিল– বাংলা পড়বে তাও আবার হোস্টেলে থেকে! কলকাতায় চাকরি করে এমন একজন জানাল তাদের মেসের ঠাকুর বাংলায় এম.এ। যারা মুখ ফুটে বলল না, তারা নীরবে মাথা নাড়ল– ঠিক ঠিক! সরবে বা নীরবে মোটের উপর সিদ্ধান্ত হল আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।
অন্ধকারই হত, যদি না জায়গাটা হত শান্তিনিকেতন, বিশ্ববিদ্যালয়টা হত বিশ্বভারতী আর বিভাগটা হত বাংলা। যদি না সেই বিভাগে থাকতেন পশুপতিদা, গোপিকাদা, ভূদেবদার মতো মাস্টারমশাই।
ইন্টারভ্যু দিতে এসে প্রথমদিনেই বিভ্রাট। আমি কল্পনাই করতে পারি না ছাত্র আর মাস্টারমশাই কখনও একাসনে বসতে পারেন। মাস্টারমশাই থাকবেন উঁচু প্ল্যাটফর্মের সিংহাসনে, ছাত্ররা কয়েদির মতো বেঞ্চে। এটাই দস্তুর। কিন্তু ঘরে ঢুকে দেখি সবাই শতরঞ্চির উপর বসে। সবার সামনে একটা করে ছোট ডেস্কের উপর কাগজপত্র। সামনে আর একটা ডেস্ক আমার দিকে মুখ করে সাজানো। আমার অভ্যাস বেঞ্চের উপরে বসা। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তার উপরেই বসলাম। একজন বললেন– আমাদের দেখে বসো। অন্যজন যোগ করলেন– সব শুনে বা পড়ে শেখা যায় না। আর একজন প্রশ্ন করলেন– হাইট কত? এর পরের প্রশ্নটা হওয়া উচিৎ ছিল, ওজন কত? কিন্তু তিনি আমার পজিটিভ দিকটাই দেখেছিলেন। নেগেটিভ দিক নিয়ে প্রশ্ন করেননি। ঝাঁটা কিনতে গিয়ে ক্রেতা ঝাঁটার হাইটটাই দেখে। কাঠির ওজন মাপাটা কাঠির পক্ষে সম্মানজনক নয়।
পরে বুঝেছিলাম শুধু তিনি নন, বিভাগের সব মাস্টারমশাই ছাত্রদের পজিটিভ দিকটা নিয়েই চিন্তিত। নেগেটিভ দিকটা ওই বানান ভুল, উত্তর প্রাসঙ্গিক হতে হবে, এইসব নিছক কেজো বিষয়েই সীমাবদ্ধ। অবশ্য সেক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়ার ভঙ্গিটা হত ইতিবাচক। আমার অজস্র বানান ভুল নিয়ে পশুপতিদার (পশুপতি শাশমল) মন্তব্য, ওটা নাকি আমার ট্রেডমার্ক। প্রথমজন যূথিকাদি (যূথিকা বসু), দ্বিতীয় জন পশুপতিদা, তৃতীয় জন সোমেনদা (সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
আমার মেজমামা বিশ্বভারতীর ছাত্র ছিল। মামার কাছে শুনেছিলাম এখানে স্যারেদের দাদা বলা হয়। সে কথা মনে পড়তেই স্কুলের অভিজ্ঞতায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে আর কি! এ কেমন নিয়ম! যমকে বলতে হবে দাদা! এ যেন ফাঁসির আসামিকে নির্দেশ দেওয়া জেলারকে শ্বশুরমশাই বলে ডাকতে হবে। ইন্টারভ্যুর সময়ে তাঁরা চোখ রাঙিয়ে, চোখা চোখা প্রশ্নে নিজেদের জাহির করে আমাকে বাজিয়ে নিতে চাননি। যেন সমপর্যায়ের একটা মানুষের সঙ্গে তাঁরা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছেন। আমাকে চিনে নিচ্ছেন, চিনিয়ে দিচ্ছেন নিজেদেরকেও। ইন্টারভ্যুর দিনেই তানপুরাটা বাঁধা হয়ে গেছিল। তাই সুরে গাইতে সময় লাগল না। কখন যে তাঁরা শুধুমাত্র যান্ত্রিক সম্বোধনে নয়, মন–মননের দাদা হয়ে উঠলেন, বুঝতেই পারলাম না।
কোনও একদিনের একটা ক্লাস একজন মাস্টারমশাইকে চিনিয়ে দেয়। সেই দিনটাই ‘প্রথম দিনের সূর্য’, স্মৃতির উজ্জ্বল-উদ্ধার হয়ে থাকে আজীবন। পরে মানুষটার কথা ভাবতে বসলে, সেই দিনটাই সবার আগে মনে পড়ে, যেদিন পরীক্ষা–সিলেবাসের গতানুগতিকতা অতিক্রম করে ভিতরের মানুষটা সামনে চলে আসেন। সোমেনদা একদিন বললেন– চলো! আজ উত্তরায়ণে ক্লাস করব। যেতে যেতে পথের দু’পাশের সব ভাস্কর্য আর বাড়ির ইতিহাস ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে করতে গেলেন। সেও এক ক্লাস। তাঁর কাছেই রবীন্দ্রনাথের অজস্র ছবির স্লাইড শো দেখেছি। ছবির ভালোমন্দ বোঝবার চেষ্টা করেছি, যা আমাদের সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তিনি ছিলেন শিল্পী মনের মানুষ।

আর সুখময়দা (সুখময় মুখোপাধ্যায়) ভ্রমণবিলাসী খাদ্যরসিক। একমাত্র তিনিই ক্লাস নিতেন ডেস্কের উপর বসে, একটা পায়ের উপর পা তুলে। তার জন্যে তাঁকে কেউ কোনওদিন অরাবীন্দ্রিক বলেনি। এঁদের মনে রবীন্দ্রনাথের আসন ছিল পাকা। ঠুনকো রবীন্দ্রতান্ত্রিকতা বা যান্ত্রিকতা এঁদের স্পর্শ করেনি কখনও। তিনি আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস পড়াতেন। কতজন চণ্ডীদাস ছিলেন, আর তাঁরা কোথায় জন্মেছিলেন, এ বিষয়ে চার–পাঁচটি মত আছে। তিনি জানালেন সব চণ্ডীদাসের সব বাসস্থান তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন।
খেতে ভালোবাসতেন বলে আড়ালে তাঁকে মুখোময় সুখোপাধ্যায় বলে ডাকা হত। মাঝেমাঝেই তিনি উধাও হয়ে যেতেন। ফিরে এসে বলতেন– এই একটু ব্রাজিল থেকে ঘুরে এলাম। যেন বোলপুর হাটতলায় হাট করতে গেছিলেন। বিদেশভ্রমণ থেকে ফিরে এলে সেমিনার হলে একটা সেমিনারের আয়োজন করা হত। তিনি অনবদ্য ভঙ্গিতে আমাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা শোনাতেন। বলার জাদু আর রঙ্গরসিকতায় সারা বিশ্বের প্রতিটি রাস্তা রেস্তোরাঁ মিউজিয়াম যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম। গোটা বিশ্ব হাজির হত বিশ্বভারতীর নীড়ে, যেমনটা রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন।
কোনও একদিনের একটা ক্লাস একজন মাস্টারমশাইকে চিনিয়ে দেয়। সেই দিনটাই ‘প্রথম দিনের সূর্য’, স্মৃতির উজ্জ্বল-উদ্ধার হয়ে থাকে আজীবন। পরে মানুষটার কথা ভাবতে বসলে, সেই দিনটাই সবার আগে মনে পড়ে, যেদিন পরীক্ষা–সিলেবাসের গতানুগতিকতা অতিক্রম করে ভিতরের মানুষটা সামনে চলে আসেন। সোমেনদা একদিন বললেন– চলো! আজ উত্তরায়ণে ক্লাস করব। যেতে যেতে পথের দু’পাশের সব ভাস্কর্য আর বাড়ির ইতিহাস ও সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে করতে গেলেন। সেও এক ক্লাস।
গোপিকাদা (গোপিকানাথ রায়চৌধুরী) একটা বিশেষ ভঙ্গিতে, একটু লাফ মেরে, সাইকেল থেকে নামতেন। আমরা বলতাম ল্যান্ড করলেন। তাঁর ক্লাস ছিল একদম মাপা। যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু। বেশি জানতে চাইলে চলে এসো বাড়িতে। অবারিত দ্বার। আর পশুপতিদা ক্লাসে আমাদের মাঝসমুদ্রে ছেড়ে দিতেন। পারলে সাঁতরে উঠে এসো। সব মাস্টারমশাইদের বাড়ির দরজা খোলা ছিল ছাত্রদের জন্যে। প্রত্যেকের পড়ানোর ভঙ্গি বা বড় করে বললে প্রকাশের ভঙ্গি ছিল আলাদা। তাঁদের পড়ানো দেখে শিখেছিলাম, পড়ানোটাকে ব্যক্তিত্বের ছোঁয়ায় প্রকাশভঙ্গি করে তুলতে না পারলে তা নিছক তথ্যের ভাণ্ডার হয়ে পড়ে থাকে, প্রজ্ঞার সম্ভার হয়ে ওঠে না। তাঁরা আমাদের নোটসর্বস্ব বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই করতে চাননি। সহিত্যরসের রসিক করে তুলতে চেয়েছিলেন। খুলে দিতে চেয়েছিলেন সারা বিশ্বের সাহিত্যের দরজা। অচলায়তনের দাদাঠাকুরের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় তাঁদের আমরা ‘প্রণাম’ করিনি, তাঁদের সামনে ‘প্রণত’ হয়েছি।
আজ এই কথাগুলো আরও বেশি করে বলার সময় এসেছে। বিশ্বভারতী নিয়ে গেল গেল রব চিরকালই ছিল। আজ যেন অন্ধকার আরও ঘন হয়ে উঠছে। তবে কি ট্র্যাজেডির ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গেছি আমরা? অথচ ভিতর থেকে কোনও প্রতিবাদ নেই। না মাস্টারমশাই, না কর্মী, কেউ রাস্তায় নেই। ছাত্রদের একটা সামান্য অংশ টিম টিম করে জ্বলছে। সবাই যেন ‘পাঁচ ফুট জমিনের শিষ্টতায় মাথা পেতে রেখেছে আপসে’। পাঁচিল দেওয়া, বসন্ত উৎসব না-হওয়া, মেলা না-হওয়া এসব নিয়ে হুজুগে বাঙালি মধ্যবিত্তের হাহুতাশের মাঝে ভিতরের ক্ষতটা যে আরও গভীর হয়ে ঘনিয়ে উঠেছে, সেটাই বড় বিপদ। মনের ভিতরে পাঁচিল তোলার কাজ শুরু হয়েছে। আঘাত করা হচ্ছে রবীন্দ্র–আদর্শের মর্মে। তবে কি শেষের সেদিন ঘনিয়ে এল?
এইখানেই মাস্টারমশাইদের একটা বড় ভূমিকা থাকার কথা। একমাত্র মাস্টারমশাইরাই পারেন প্রাতিষ্ঠানিকতার মধ্যে থেকেও প্রতিষ্ঠানের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাত করতে। আর তার উপযুক্ত রণক্ষেত্র ক্লাসরুম। যদি সদিচ্ছা থাকে, আর থাকে রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, পাঁচিলের ঘেরাটোপে তপোবনের পরিবেশ হারিয়ে গেলেও মনের ভিতরে তা বেড়ে উঠতে বাধা কোথায়?! বিপদটা এখানেই– সেটাই হারিয়ে যাচ্ছে। হয় রবীন্দ্র আদর্শে বিশ্বাস করি না, অথবা সদিচ্ছার অভাবে সক্রিয়ভাবে প্রয়োগ করি না! আজকের সংঘাত শুধু দেওয়াল তোলা নিয়ে প্রশাসনিক সংঘাত নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানেই প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রবীন্দ্রবিরোধী ভাবনার চর্চা করা হচ্ছে।
আমরা যে মাস্টারমশাইদের কাছে পড়েছি, তাঁরা ঘটা করে নিজেদের রাবীন্দ্রিক বলে জাহির করেননি। কিন্তু ক্লাস ও ক্লাসের বাইরের জীবনাচরণে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের মর্মে যিনি, তাঁর আদর্শের মর্মটি তাঁরা বুঝেছেন। তাঁরা দাদা–দিদির মতো পাশে থেকে অচলায়তনের দাদাঠাকুরের মতো পথ দেখিয়েছেন। আশা করি আমার মাস্টারমশাইদের মতো আজও কোনও কোনও ‘দাদা–দিদি’ নীরবে এই অন্তর্ঘাতটা চালিয়ে যাচ্ছেন। যদি তা সত্য হয়, তাহলে গেল গেল করেও অনেক কিছু থেকে যাবে। থেকে যাবে ফিনিক্স পাখির মতো।
ছবি সৌজন্য: বিশ্বভারতী
লেখক ও নাট্যকার অসীম চট্টরাজের জন্ম ১৯৬৪। প্রতিষ্ঠিত বাংলা সংবাদপত্র ও পত্রিকার পাঠকদের কাছে তিনি এক পরিচিত নাম। পেশায় অধ্যাপক অসীম চট্টরাজের লেখালেখির শুরু নাটক দিয়ে এবং গল্প উপন্যাসের জগতে প্রবেশ নব্বই-এর দশকে। প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ 'হারাধন মণ্ডলের গল্প', 'কিছুতো নেপথ্যে থাক', 'অলৌকিক তীর্থযাত্রা', 'টিলা'।