সেদিন ফোন করলাম এক বিখ্যাত লেখককে। পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে থাকলে, এ তো প্রায়ই করতে হয়। ওঁর লেখা দেওয়ার কথাই ছিল। আমার তাগাদা দেওয়া উদ্দেশ্য। ভীষণ ব্যস্ত লেখক। হরদম ভুলে যান। তাই বললাম
— মনে আছে তো? লেখাটা কবে দেবেন?
— তোমার কবে দরকার?
— যত তাড়াতাড়ি হয়। এই মার্চের মধ্যে হলে সবচেয়ে ভালো।
— ঠিক আছে। এপ্রিলের এক তারিখ পেয়ে যাবে।
উনি স্নেহ করেন আমায় খুব। শুধুমাত্র একগাদা লেখার মধ্যে ভুলে যান বলে, প্রায় সবসময়ই যেদিন বলেন সেদিন দিতে পারেন না। অবশ্য, নির্দিষ্ট সংখ্যায় লেখাটা আরামসে বেরিয়ে যেতে কোনও অসুবিধে হয় না। বললাম
— আমায় ঠকাতে চাইছেন নাকি?
অবাক হয়ে উনি বললেন—তার মানে?
— দিনটা কবে দিলেন, খেয়াল করেছেন? পয়লা এপ্রিল!
— হাঃ হাঃ হাঃ… না না, আমি এটা ভেবে বলিনি। ওই দিনই পেয়ে যাবে। তোমায় ঠকাব না।
—কিন্তু, আমি যে ঠকতে চাই।
—কী হেঁয়ালি করছ? ভরসা রাখতে পারছ না?
—না… আমি সেজন্যে বলিনি।
— তবে?
—আসলে, ভীষণ ব্যস্ততার কারণে আপনি তো নির্দিষ্ট দিনে দিতে পারেন না, সেটাই স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তাই এবার যদি ওই দিনেই দিয়ে দেন, সেটা তো এক অর্থে আমার ঠকে যাওয়া হবে। কিন্তু, তাতেই লাভ। তাই বললাম ঠকতে চাই।
— বড় ভালো বললে তো হে।
এরকম প্রতিনিয়তই হয়। ঠকে যাওয়া যে কতভাবে আমাদের আনন্দ দেয়, তা খেয়াল হয় না। ঠকে যাওয়া মানে তো এক অর্থে বোকা বনে যাওয়া। সেই বোকা হওয়া অনেকক্ষেত্রেই সুন্দরের জন্ম দেয়। প্রাপ্তিযোগ ঘটায়। অর্থের দিক থেকে নয়। জীবনের নিরিখে। আমরা ‘ঠকা’ মানে একটি নির্দিষ্ট ধারণা নিয়ে চলি। কিন্তু খেয়াল করি না, কতরকমভাবে কত বৈচিত্রের ঠকে যাওয়াকে আমরা জীবনে বরণ করে নিই। সেগুলি তৃপ্তি দেয় আমাদের। প্রকৃতি তো অহরহ ঠকায়। এত আধুনিকতা, প্রযুক্তির রমরমা— তবু প্রকৃতির কাছে এখনও আমরা দাসানুদাস। কখন কী ঘটিয়ে দেবে, কেউ জানে না। পূর্বাভাসের সঙ্গে প্রকৃতির লুকোচুরি খেলাটা তো এই উপগ্রহ-ব্যবস্থার মধ্যেও প্রায়শই ঘটে চলে।
ধ্বংসাত্মক রাগের কথা ধরছি না। কিন্তু, অনুমানের বাইরে গিয়ে প্রকৃতি নানাভাবে সুন্দরকে সামনে এনে আমাদের তো বোকা বানিয়েই চলে। আমরা তা উপভোগও করি। বোকা হতে ভালো লাগে। পূর্বাভাস ছিল নিম্নচাপের। শুরু হল মুষলধারা। জনজীবন অতিষ্ঠ। সরকার থেকে সাধারণ লোক, সবাই সামলাতে ব্যস্ত। বিপর্যস্ত। আশঙ্কা, আরও ২/৩ দিন এই বিরক্তিকর অবস্থা চলবে। গাছ ও মাছের হয়তো দারুণ আনন্দ। আমাদের অবস্থা সঙ্গীন। পরের দিন সকালে জানলা দিয়ে মুখের ওপর রোদ পড়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আকাশ ঝকঝকে তকতকে। কীরকম হল? সূয্যিমামা হাসছেন কী করে? তার তো মেঘের আড়ালে থাকার কথা ছিল। আনন্দে মন ভরে গেল। কী ঠকানোটাই না ঠকালো প্রকৃতি। ভাগ্যিস!
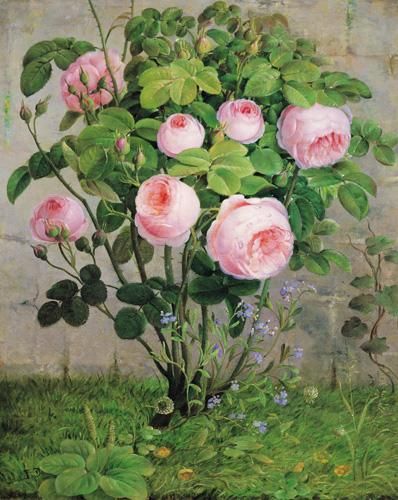
বহু যত্নে গোলাপগাছ বসিয়েছেন। দিনরাত তার পরিচর্যা। অবশেষে কুঁড়ি এল। কী আনন্দ! কিন্তু, ঝরে গেল যে! যাকগে, পরেরবার নির্ঘাৎ ফুল হবে। হল না। একটার পর একটা কুঁড়ি আসে আর ঝরে যায়। ক্রমশ সেটাই ধরে নেওয়া অভ্যেস হয়ে গেল। ওমা, আজ এ কী কাণ্ড! কুঁড়ি যে গোলাপ ফুল হয়ে আলো ছড়াচ্ছে! প্রাণভরে গন্ধ-পান, আর চোখ জুড়িয়ে রূপদর্শন। কী সুন্দরই যে বোকা বানালো গাছটা! আহা!
ছেলেটা দাঁড়িয়েই থাকে। রোজ বিকেলে পড়তে যাবার সময়, এই জায়গাটায় এলেই পা আর চলে না। জানে দেরি হয়ে যাচ্ছে। স্যার বকবে। একদিন বকেছেনও। তবুও…। মেয়েটা ঠিক এখনই সামনে দিয়ে যায়। মুখচোরা লাজুক ছেলেটার রাস্তা দিয়ে গেলে চোখই ওঠে না। সেদিন কী যে হল! একঝলক চোখ গেল। আর মেয়েটা কীসব করে দিল। বুকে হামানদিস্তের আঘাত লেগেছিল। তারপর থেকে এখানে এলেই ক্ষণেকের থমকে যাওয়া। রোজ মনে হয়, আজ কি দেরি হয়ে গেল?
না, কোনওদিনই হয় না। মেয়েটা তার দিকে তাকায় না। তা নিয়ে ছটফটানিও যে হয় ছেলেটার, তাও নয়। শুধু তার দৃষ্টিতে রোজ ধরা দিক সে। একমাত্র এই নিয়েই তার নিজের চোখ, মন, ইচ্ছের ঠোকাঠুকি। অন্য কিছু ঘটতে পারে, ভাবতেই পারত না। মেয়েটা কোথায় যায়, কী করে— তা নিয়েও কোনও আগ্রহ নেই। শুধু এই সময়টায় এই জায়গায় যেন তার দৃষ্টি শূন্য না থাকে। একদিন সত্যিই শূন্য রইল। এল না মেয়েটা। পা আর এগোতেই চাইছে না ছেলেটার। কী হল? না, কোনও শরীর খারাপ-টারাপের চিরাচরিত প্রেমজনিত আশঙ্কা মেয়েটির সম্পর্কে তার হয়নি। শুধু কেন সে দেখতে পাচ্ছে না, তা নিয়েই যত ছটফটানি। নিজেকে টানতে টানতে স্যারের বাড়ি। ঢুকেই চমকানির বিস্ফোরণ। মেয়েটা ওখানে! ও ঢুকতেই তার দিকে তাকিয়ে। এই প্রথম! মুখে আলগা হাসি।

স্যার আলাপ করিয়ে দিলেন সবার সঙ্গে। ছেলেটির সম্বন্ধে অকুণ্ঠ প্রশংসা। পড়াশুনায় দারুণ ভালো যে সে। সত্যিই তাই। কলেজেও খুব সুনাম। পড়ে ফেরার সময় মাথায় ঘোর লাগছিল। হঠাৎ পেছন থেকে আওয়াজ
—এই যে শুনছ?
ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটার চোখাচোখি—
—আমাকে?
—হ্যাঁ, তোমাকেই তো। আমি নতুন এসেছি এখানে। তোমাদের কলেজে ভর্তি হয়েছি। তোমার নাম কলেজে সবার মুখেমুখে…
একনাগাড়ে বলে গেল মেয়েটা।
— আমি কী করব তার জন্যে?
— কী আবার করবে? তোমাকে আমি তো অনেকবার দেখেছি মোড়ের ওই সাইকেলের দোকানের সামনে।
—ও তা হবে।
—শোনো, আমার কিছু অসুবিধে হলে তোমাকে কিন্তু ডিসটার্ব করবো। দরকার হলে, তোমার বাড়ি গিয়েও পড়া বুঝে আসব। কোথায় তোমার বাড়িটা?…
এইরকম চলতে চলতে ভালোবাসা একদিন দখল করল তাদের। তখন একদিন মেয়েটা বলেছিল, — আমি অনেক আগে থেকেই তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।
ছেলেটা ভাবল, মেয়েটা নয়। তার নিজের দৃষ্টিকেই একসময় বুঝতে পারেনি সে। আচ্ছা ঠকিয়েছে। ভালোই করেছে।
রমাপ্রসাদ বণিকের লেখা নাটক— ‘খেলাঘর’। সদানন্দ ও কলাবতী বাবা-মেয়ে। এককালে বিরাট রমরমা ছিল। এখন হতদরিদ্র হয়ে কলকাতায় কোনওরকমে বেঁচে থাকা। সদানন্দ নেশাভাঙ করে। কলাবতী সর্বক্ষণ বাপের বাপান্ত করছে। তারা ঠিক করল গ্রামে যে পরিত্যক্ত বিশাল বাড়িটা রয়েছে— সেটা বেচে দিলে কেমন হয়? সেই মতো বিশলাখ টাকা বাড়ির দাম হেঁকে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিল। দু’জনে গ্রামে চলে গেল ওই বাড়িতে থাকতে। খদ্দের এলে তো সেখানেই আসবে। ধূলিধূসর কিছু জিনিসের মধ্যে সদানন্দ তার বাবার একটা ডায়রি খুঁজে পেল। তা পড়ে বাপ-মেয়ের দৃঢ় বিশ্বাস হল, এ বাড়িতে কোথাও গুপ্তধন পোঁতা আছে, যার ছক রাখা আছে কোনও গোপন জায়গায়। সদানন্দর বাবার এক খাস সাকরেদ ছিল নীলরতন। সে-ই নির্ঘাৎ তাঁকে খুন করেছে গুপ্তধনের আশায়। কিন্তু, ছকটা খুঁজে পায়নি হয়তো। তাই এই বাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপন দেখে অবশ্যই নীলরতনের আসার সম্ভাবনা প্রবল।
আরও পড়ুন: বাংলালাইভের বিশেষ ক্রোড়পত্র: সুরের সুরধুনী
বাবা-মেয়ের মতলব অন্যদিকে মোড় নিল। প্রথম খদ্দের এল। নাম— নীলাঞ্জন। আকাঙ্ক্ষিত লোকের কাছাকাছি নাম। বেশি কিছু না বলেই সে বিশলাখ টাকার চেক কেটে দিল। সন্দেহ আরও পাকা হল এতে। তাকে অনুরোধ করে এ বাড়িতেই রেখে দিল সদানন্দ-কলাবতী। নীলাঞ্জন সুদর্শন। রোম্যান্টিক। সুন্দর গানের গলা। সবসময় একটা ডায়রিতে কীসব লেখে। পরিকল্পনা মতো একদিন বাবা-মেয়ে মিলে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে দিল নীলাঞ্জনকে। হেঁচকি তুলতে তুলতে বাথরুমে আছড়ে পড়ল সে। মিশন সাকসেশফুল। দুজনেই আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু নীলাঞ্জনের ডায়রি পড়ে জানা গেল ও নীলরতন নয়। বাড়িটা কিনে একটা অনাথ-আশ্রম করবে ভেবেছিল। কলাবতীর প্রেমেও পড়েছিল। বাপ-মেয়ের হাহাকার শুরু হল। নীলাঞ্জন কিন্তু মরেনি, অনেক বমি হওয়ায় বেঁচে গেল। স্বস্তি এল দুজনের। বাড়িতে গুপ্তধন বলেও কিছু নেই। ছকটা পড়ে সেটাও জানা গেল। তার মানে সব ধরে নেওয়াগুলো উলটো ফল দেখাল। যা আনন্দের। তাই তো, নাটকের একেবারে শেষে সদানন্দ বলে উঠল, ‘ঠকে যাওয়ার মধ্যেও যে এত সুখ, তা আগে বুঝিনি।’
‘খেলাঘর’ নিয়ে ব্যক্তিগত কথাও আছে, যেখানে চরম ঠকার এক অদ্ভুত মুহূর্ত এসেছিল সামনে। তখন চুঁচুড়ার ‘সারথি’ দলে রয়েছি। ‘খেলাঘর’ নাটক নিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তর চষে বেড়াচ্ছি। নভেম্বর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় নাট্য-প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে মার্চের প্রথম দিক অবধি চলত। এখনও হয়। সে এক উন্মাদনামুখর পরিবেশ। প্রত্যন্ত গ্রাম। সন্ধে হল কি হল না, কাতারে কাতারে মানুষের কলরোলে ভরে উঠল ফেলেন প্যান্ডেল। মাটি থেকে উঠে আসা এইসব মানুষদের সঙ্গে শহুরে বোদ্ধামহলের বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটাও সম্পর্ক নেই। আছে শুধু নিখাদ ভালবাসা। এর ধরন ঠিকঠাকভাবে বোঝা, আমাদের মতো প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিতদের কাছে বোধহয় দূর-অস্ত।
একবার আমরা গেছি বর্ধমানের বড়শূল গ্রামে। নাটক হয়ে গেছে। বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। উদ্দেশ্য হল, দর্শকরা কে কী বলতে বলতে যাচ্ছেন, তা শোনা। একটু আগেই অভিনয় করেছি। মানুষজন তাই আমার দিকে তাকাচ্ছেন। ভালোই লাগছে। নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হচ্ছে। হঠাৎ কাছে এগিয়ে এলেন একটি বউ। উঁচুতে পরা শাড়ি। কোলে একটি আধন্যাংটা বাচ্চা। হাতে ধরা আরেকটি ছেলে। খালি পা। সব মিলিয়ে চরম দারিদ্র্যের এক জ্বলন্ত প্রমাণ যেন সামনে দাঁড়িয়ে। কড়া ঠাণ্ডা। তখন বাজে ৮টা-সাড়ে ৮টা। তার মধ্যে শীত ঢাকার সামগ্রীর এই ভয়াবহ ব্যবস্থা! বউটি কী যেন বলতে চায় আমাকে। আমি তো ‘শিক্ষিত’ বাবু! তাই পাত্তা দিচ্ছিলাম না।
এবার তিনি বলে উঠলেন— ‘কী ভালো গান গাইলে গো।’ আসলে, নাটকে আমার অনেকগুলো টুকরো টুকরো গান ছিল। বউটির কথা শুনে শহুরে তাচ্ছিল্যে জবাব দিলাম- ‘হুম’।
— তোমরা তো সারথি। গতবারে করেছিলে এই নাটক, তার আগে এই…, তার আগেরবার…। এবার আমার অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার দশা! এক মুহূর্তে নিজেকে অশিক্ষিত মনে হল। অভাব যাদের চিরসঙ্গী, নিত্যজীবন কষ্টে জর্জরিত— থিয়েটারের প্রতি তাদের এই ভালোবাসা আসে কোথা থেকে? কলকাতা ও অন্যান্য শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলো তো গ্ল্যামারওলা নাটক ছাড়া ফাঁকা পড়ে থাকে। সেখানে গ্রামের প্রান্তিক মানুষেরা ভিড় জমাচ্ছেন অনামী দলের নাটক দেখতে! মনে মনে সেদিন প্রণাম জানিয়েছিলাম সেই বউটিকে। পরমহংসদেবের বলা ‘থিয়েটারে লোকশিক্ষে হয়’ কথাটির সার্থক রূপ বোধহয় একেই বলে। সেদিনের সেই গাঁয়ের বধূর কাছে যা ঠকেছিলাম, ভুলতে পারবো না কোনওদিন। যা একইসঙ্গে যত তৃপ্তি দিয়েছিল, তার সঙ্গে নিজের ব্যাপারে এক চরম লজ্জারও মুখোমুখি করেছিল। চারপাশ দেখে যেসব সিদ্ধান্তে আমরা দ্রুত পৌঁছে যাই, তার মধ্যে যে কত ভুল থাকে, এই অভিজ্ঞতা ডাহা বোকা বানিয়ে এক সত্যের শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিল সেদিন।
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে ছবি করলেন তরুণ মজুমদার— ‘দাদার কার্তি’। ক্যাবলাকান্ত কেদার পরীক্ষায় বারেবারে ফেল করে। একদিন রেগেমেগে তার বাবা তার দাদার বাড়ি শিমুলতলায় পাঠিয়ে দিলেন কেদারকে। সেখানে বাড়িভর্তি লোক আর অফুরন্ত আনন্দ। কেদারের এক ভাই কলেজে পড়ে। তার বিয়ে ঠিক হয়ে আছে প্রতিবেশীর মেয়ে বীণার সঙ্গে। বীণার এক দিদিও আছে। সরস্বতী। ভীষণ রাশভারি। ছেলেরা কাছে যেতে সাহস পায় না। দুই বোনই সুন্দরী। পাড়ার ছেলেদের মধ্যে ভোম্বল হচ্ছে সর্দার। কেদারকে বোকাসোকা দেখে ভোম্বলের তার পেছনে লাগার ইচ্ছে জাগল।
একদিন কেদার মর্নিংওয়কে বেরিয়েছে। বীণাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে কানে এল দু’টি নারীকণ্ঠের এক অপূর্ব গান। ভোরের সঙ্গে যেন মিশে যাচ্ছে সুর। কেদার দাঁড়িয়ে পড়ল। ভোম্বলও তার দলবল নিয়ে মর্নিংওয়কে বেরিয়েছে। কেদারকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তার বদমায়েসি বুদ্ধি মাথায় খেললো। কেদারকে টেনে নিয়ে গেল সরস্বতীদের বাড়ির ভেতরে। তারপর, কেদারের সম্বন্ধে বানিয়ে বানিয়ে একগাদা ভালো ভালো কথা বলতে লাগলো ভোম্বল। কেদার নাকি পড়াশুনায় খুব ভালো। সবেতে ফার্স্ট। সর্বগুণে গুণান্বিত। এইসব ডাহা মিথ্যেগুলো তার সম্বন্ধে শুনে কেদার ভীষণ বিব্রত। অবাক! কিন্তু সে যে বোকাসোকা। সোজা হয়ে প্রতিবাদও করতে পারল না।
ভোম্বল বলে বসলো কেদার নাকি অসাধারণ গানও করে। সবাই অনুরোধ করলো একটা গান শোনানোর জন্য। কেদার সঙ্কুচিত। দর্শকেরা যারা প্রথমবার ছবিটা দেখেছিলেন, তারাও আশঙ্কিত কী কেলেঙ্কারি হবে, তা নিয়ে। ভালোমানুষ ছেলেটা দারুণভাবে অপদস্থ হতে চলেছে এবার। সরস্বতী পিয়ানোয় হাত রাখলো। কেদারকে ভোম্বল দাঁড় করিয়ে দিল তার পাশে। ফিসফিস করে বিদ্রুপ করলো তাকে। হঠাৎ, সব দর্শক এবং ভোম্বলকে চমকে দিয়ে, কেদার অসাধারণভাবে গেয়ে উঠল— ‘চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে…’ (হেমন্ত মুখোপাধ্যায়) । দর্শকরা যতটা ঠকলেন, তার চেয়েও বেশি মোহিত। তাঁরা সকলেই তৃপ্ত কেদারের জিতে যাওয়া দেখে। ভোম্বল ততক্ষণে পগারপার। দর্শক হিসেবে নিজেও মনে করতে পারি, কেদারের কাছে সুরময় ঠকে যাওয়াটা সেদিন কত মধুর লেগেছিল।
দুঃখও মাঝেমাঝে ঠকে যায়। তীব্র যন্ত্রণার অপেক্ষায় থাকা মন যখন বোকা বনে যায়, তা অপূর্ব আনন্দ দেয়। মৃত্যুপথযাত্রী নিকটজন। ডাক্তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন। চিকিৎসাশাস্ত্র, তার শেষ চেষ্টা অবধি করেও হার মেনেছে। এক মর্মান্তিক অবস্থায় রয়েছেন কাছের মানুষেরা। হঠাৎ পরপারের দিকে মুখ করে থাকা মানুষটি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন এপারের দিকে। মরণ থেকে জীবনের দিকে চলে এলেন তিনি। চিকিৎসাশাস্ত্র কোনও উত্তর পেল না। কীভাবে সম্ভব হল এটা! নিকটজনেরাও অভাবনীয় প্রাপ্তিতে আলোড়িত। তাঁরা যে কান্নাকে গলায় চেপে, ধরেই নিয়েছিলেন চিরবিচ্ছেদকে। এক অর্থে ঠকলেন তাঁরাও। কিন্তু, এই ঠকে যাওয়া যেন বারবার আসে, তাও তো চাইবেন সকলে।
দাদাস্থানীয় বন্ধু মধুময় পালের কাছে শোনা একটা ঘটনা। একে ঠকার আনন্দ, না দুঃখ… না কী যে বলা যায়, তা ঠিক করা বেশ শক্ত। মধুময়দা লেখালেখি করেন বহুদিন থেকেই। সেইজন্য একসময় যেতেন ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার অফিসে। তখন সম্পাদক আবদুর রউফ। জমাটি আড্ডা বসত তাঁর টেবিলে। মধুময়দা একদিন গেছেন। রয়েছেন আরও কয়েকজন। কিছুক্ষণ বাদেই এলেন লম্বা দোহারা চেহারার এক পরিচিত লেখক। গল্পে যোগ দিয়ে একথা-সেকথার পর সেই লেখক বলতে লাগলেন তাঁর ছেলের কথা। ছেলে আমেরিকাবাসী। বিয়েও করতে চলেছে এক বিদেশিনীকে। ভদ্রলোকের আফসোস, নাতি-নাতনি হলে, তাদের সঙ্গে প্রাণভরে সময় কাটাতে পারবেন না। এইসব নানা কথা বলে সেখান থেকে চলে গেলেন সেই লেখক।
যেই তিনি বেরিয়েছেন, আব্দুর রউফ বলে উঠলেন— ‘আজ ফার্স্ট এপ্রিল’। সবাই জিজ্ঞেস করল, এ কথা বলার মানে কী? তাহলে এতক্ষণ ওই লেখক যা বলে গেলেন সব বাজে কথা? আজকের দিনে ঠকাবার জন্যে বললেন? রউফসাহেব বললেন, বছরখানেক হল এই ভদ্রলোকের ছেলে মারা গেছে। উনি কিন্তু মানসিক ভারসাম্যহীন নন। রীতিমতো লেখালেখি করেন। কিন্তু, ছেলের ব্যাপারে উনি বাস্তব-অবাস্তব-পরাবাস্তব মেশানো এক অদ্ভুত দুনিয়ায় থাকেন। কী বিস্ফোরক বোকা বনে যাওয়া! মধুময়দা আমায় বলেছিলেন, ‘সেদিন থেকে আমি মনে মনে চেয়েছি ভদ্রলোক যেন এইভাবেই তাঁর ছেলের ব্যাপারে নিজেকে ঠকিয়ে চলেন। তাতে তাঁর মনটা অন্তত শান্তিতে থাকবে।’
উনিশ শতকের শেষের দিকে তো আচ্ছা ঠকেছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বড়রা। প্রতিভার ঠাসাঠাসিতে তো তখন হাঁসফাঁস অবস্থা ঠাকুরবাড়ির। শিক্ষা-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির হেন ক্ষেত্র নেই, যেখানে এই বাড়ির রত্নেরা তাঁদের জেল্লা দেখাচ্ছেন না। তারই মধ্যে একটি বালক ছন্নছাড়া। স্কুলে যেতে চায় না। বাড়িতে মাস্টারমশাইয়েরা পড়াতে এলেও পড়তে বসতে ইচ্ছে করে না। জানলায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতি দেখে উদাস চোখে। বাড়িতে থাকা অগুনতি চাকর-বাকরদের পেছনে ঘুরঘুর করে তাদের রকমসকম দেখতে ভালবাসে। কখনও বারান্দার রেলিংগুলোকে ছাত্র বানিয়ে পড়ায়। বেত দিয়ে বেদম মারতে ভালবাসে সেগুলোকে। অভিভাবকেরা ধরে নিল এ ছেলে বখাটে না হয়েই যায় না। ভালো কিছু এর সম্বন্ধে আশা করা বৃথা। কিন্তু, পরে কী হল? তা কি আর বলতে হবে? অত প্রতিভার মধ্যেও সর্বোচ্চ স্তম্ভটি হল এই বালকই। ঠাকুরবাড়ির গরিমার সাম্রাজ্যে সম্রাট তো একজনই—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ঠাকুরবাড়ির অভিভাবকদের ঠকে গিয়ে যে পরিমাণ প্রাপ্তি হয়েছিল, তার আঁচ তো আমরা আজও অনুভব করে চলেছি।
উনিশ ও বিশ শতরে একটা বিরাট সময়জুড়ে বাংলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোনার মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল ঝাঁকে ঝাঁকে। সে এক স্বর্ণক্ষণ। আজকের এই পচা-গলা সমাজে দাঁড়িয়ে আমরা বোধহয় স্বপ্ন তো দূরের কথা, মনগড়া স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না, ওই মাপের কাছাকাছি কোনও ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব সম্ভব বলে। কিন্তু, যদি ঘটে যায়? এইসময়ে যদি এসে যান কিছু মহান মানুষ? আমরা অবশ্যই ডাহা ঠকব। কিন্তু, প্রার্থনা জানাতে ইচ্ছে করছে সেই ঠকবার জন্যেই। আমরা এই ঠকাটা ঠকতে চাই। সমাজকে যদি বাঁচাতে হয়, যদি শুভ-লক্ষ্যে মানবজগতকে পথ দেখাতে হয়, আমাদের ঠকিয়ে কয়েকজন মহান ব্যক্তিত্বের আগমন হোক আজকের সময়ে।
*ছবি সৌজন্য: Pinterest, National world
জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।

























