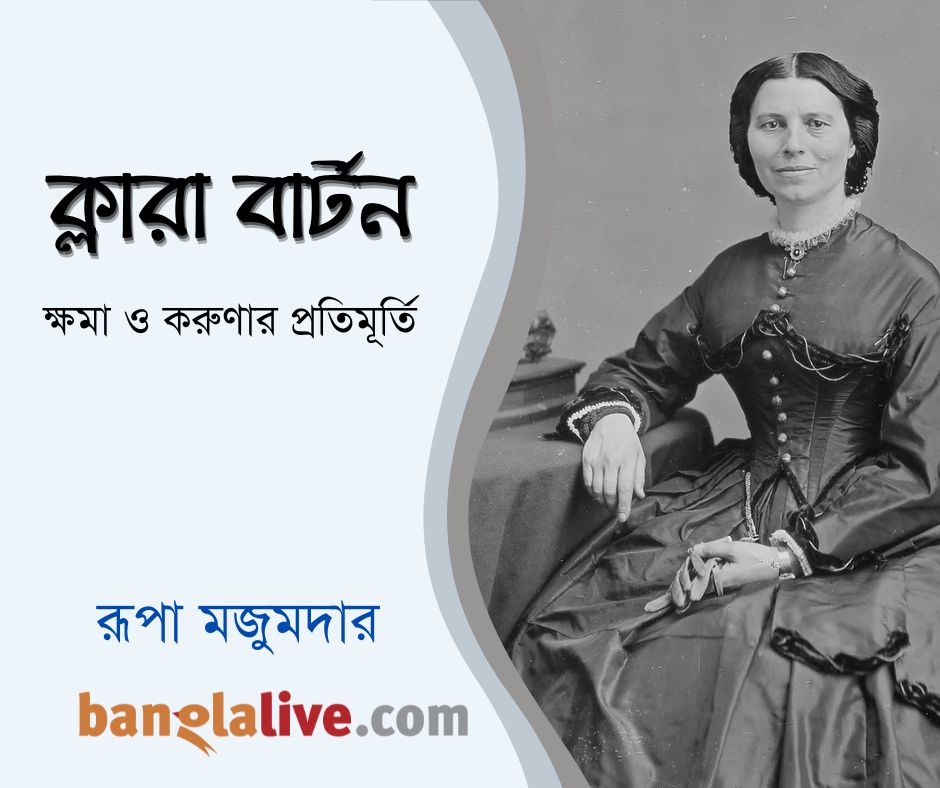ইউরোপে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময় আহত সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য নতুন নার্সিং পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল আর যুদ্ধকালীন সেই সেবিকার কাজের জন্য তিনি লেডি উইথ দ্য ল্যাম্প আখ্যায় ভূষিত হয়েছিলেন। এর আগে আহত সেনাদের জন্য সেবার কোনও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। তিনি শুধু সেনাদের সেবার দায়িত্বই নেননি, নিজের জীবন বিপন্ন করে রাতের বেলাতেও আলো হাতে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে বেড়াতেন। যদি কোনও সৈনিক আহত অবস্থায় জীবিত থেকে থাকেন, যদি তার জীবন বাঁচানো যায়, এমনই ছিল আহত মানুষদের জন্য তাঁর মমত্ববোধ। এইরকমই আরেক স্বেচ্ছাসেবিকা ছিলেন মিস ক্লারা বার্টন (Clara barton)।
আমেরিকার নর্থ অক্সফোর্ডের এক গণ্যমান্য কৃষক পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে ক্লারা জন্মগ্রহণ করেন ১৮২১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর। বাবা ক্যাপ্টেন স্টিফেন বার্টন ছিলেন প্রাক্তন সেনা, কৃষক এবং একজন সফল অশ্বব্যবসায়ী। ছেলেবেলা থেকেই লেখাপড়ার সঙ্গে খেলাধুলা ঘোড়ায় চড়া সবেতেই পারদর্শী ছিলেন ক্লারা। পড়েছিলেন দর্শনশাস্ত্র, রসায়নবিদ্যা ও ল্যাটিন ভাষা।
ছেট থেকেই বাবার কাছে শুনতেন যুদ্ধক্ষেত্রের নানা গল্প– সেনাদের আত্মত্যাগের গল্প,যুদ্ধে আহত হয়ে উপযুক্ত সেবার অভাবে কষ্ট পাওয়ার কথা, সময়মতো ত্রাণ সামগ্রী না মেলায় খাদ্যাভাবে কষ্ট পাওয়ার কথা, মৃত সেনাদের দেহ খুঁজে না পাওয়ার কথা, তাদের পরিবারের মানুষের অসহায়তার কথা। শুনতে শুনতে ধীরে ধীরে সেবার মনোবৃত্তি তৈরি হতে থাকে ক্লারার। তার এই সেবার মনোবৃত্তি পরিচয় পাওয়া গেল প্রথমে নিজের বাড়িতেই। একদিন দাদা ডেভিড গোলাবাড়ির চাল সরাতে গিয়ে মাটিতে পড়ে সাংঘাতিক চোট পেল। ডাক্তাররাও ডেভিডের ভাল হয়ে ওঠার আশা ছেড়ে দিলেন। আশা ছাড়লেন না কেবল ১১ বছরের ক্লারা। সব কাজ সরিয়ে রেখে দৃঢ় সংকল্পে দাদার সেবা করতে লাগলেন। ডাক্তারদের ধারণা ভুল প্রমাণ করে অতন্দ্র সেবায় দাদাকে সুস্থ করে তুললেন। ডাক্তার ব্যাপারটাকে মিরাকেল আখ্যা দিলেন।
এভাবেই শুরু হল আজীবন সেবার কাজ। মাত্র ১৭ বছর বয়সেই মাসাচুসেটস ওরসিস্টার কান্ট্রি স্কুলে শিক্ষিকা চাকরি পান। ১০ বছর চাকরি করার পর আরও পড়াশোনা করার জন্য অ্যান অ্যাডভান্স স্কুল ফর ফিমেল টিচার্স এ ভর্তি হন। এখানে থাকতেই ফরাসি ভাষা শিখতে শুরু করেন এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পড়া শেষ করে শিক্ষিকার চাকরি নিয়ে চলে যান নিউ জার্সি। সেখানে বাড়ির কাছে নিজে একটা অবৈতনিক স্কুল খুললেন যেখানে ছাত্র সংখ্যা অচিরেই ৬০০ ছাড়িয়ে গেল। এই সময়ে
স্কুল বোর্ড একজন মহিলাকে প্রধানের পদে না রেখে একজন পুরুষ শিক্ষককে সেই পদে বসানোর সিদ্ধান্ত নিলে, প্রতিবাদে কাজ ছেড়ে ক্লারা ওয়াশিংটন ডিসিতে ফিরে গেলেন। সেখানে যোগ দিলেন পেটেন্ট অফিসে পেটেন্ট কমিশনার পদে। কিন্তু এখানেও দেখা দিল সেই একই সমস্যা। এমন একটা উঁচু পদে একজন সামান্য মহিলা পুরুষ সহকর্মীর সমান বেতন নিয়ে কাজ করবেন সেটা অনেকের মনঃপূত হলো না। অতএব রাজনৈতিক চাপে তাকে কমিশনার থেকে একেবারে কেরানির পদে নামিয়ে দেওয়া হলো। আসলে ক্লারা ছিলেন ক্রীতদাস প্রথার বিরোধী আর পেটেন্ট অফিসার কর্তাব্যক্তিরা ছিলেন দাস প্রথার পক্ষপাতি। এটাই তার পদাবনতির কারণ। চার বছর সেখানে কাজ করার পর ১৮৬০ সালে তিনি ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে যান।

ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (American Civil War) শুরু হয়। ক্লারা নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুদ্ধের ফ্রন্টে কাজ শুরু করলেন। যুদ্ধে আহত বিদ্ধস্ত সেনাদের সেবাই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। হাতের কাছে খাদ্য, তুলো, ব্যান্ডেজ, তোয়ালে, রান্নার জ্বালানি, কিছুই ছিল না। সামান্য কিছু জিনিস নিজের ছিল, আর কিছু নাগরিকদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে জোগাড় করতে পেরেছিলেন। তাই দিয়ে আহতদের সেবার কাজে লাগালেন। পুরনো চাদর ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বানাতেন, বড় টুকরো করে তোয়ালে হিসেবে ব্যবহার করতে নিতেন,অবশিষ্ট অংশ রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতেন। দৈনন্দিন সামগ্রীর জন্য সাধারণ জনগণের কাছে আবেদন রাখতে শুরু করলেন। বিখ্যাত “প্রথম বুল রান” (First Battle of Bull Run) যুদ্ধের পর সৈন্যদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাবের বিষয় বিশেষ রিপোর্ট পেয়ে তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে যুদ্ধে আহত সেনাদের ও ক্ষতিগ্রস্ত সাহায্যের জন্য মানুষের কাছে আবেদন রাখলেন।
ক্লারার এই আকুল আবেদনের ফল মিলল হাতে হাতে। এত সাহায্য আসতে শুরু করল যে তা ঠিকঠাক ভাবে রাখার জন্য এবং বিতরণের জন্য সঙ্গীদের নিয়ে একটা সংস্থা খুললেন। প্রমাণ করলেন মানুষের সেবার কাজের জন্য কখনও অর্থের অভাব হয় না, শুধু প্রয়োজন আন্তরিক ইচ্ছা ও সুযোগ খুঁজে নেওয়ার সদিচ্ছা। স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে আহত সেনাদের যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় জিনিস জোগাতেন এবং নিজের হাতে আহতদের শুশ্রুষাও করতেন। কাজটা তিনি করতেন কোনও সরকারি সাহায্য ছাড়াই। একবার এরকম এক সৈনিকের মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় একটা গুলি এসে ক্লারার জামার হাতায় লাগে। একটুর জন্য তিনি বেঁচে যান, তবুও কখনও ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া বন্ধ করেননি।
ইতিমধ্যে ১৮৬১ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ক্লারা নিজের কাজ ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে যুদ্ধের ফ্রন্টে কাজ শুরু করলেন। যুদ্ধে আহত বিদ্ধস্ত সেনাদের সেবাই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। হাতের কাছে খাদ্য, তুলো, ব্যান্ডেজ, তোয়ালে, রান্নার জ্বালানি, কিছুই ছিল না। সামান্য কিছু জিনিস নিজের ছিল, আর কিছু নাগরিকদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে জোগাড় করতে পেরেছিলেন। তাই দিয়ে আহতদের সেবার কাজে লাগালেন। পুরনো চাদর ছিঁড়ে ব্যান্ডেজ বানাতেন, বড় টুকরো করে তোয়ালে হিসেবে ব্যবহার করতে নিতেন,অবশিষ্ট অংশ রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করতেন।
শুধু সেবা করেই ক্লারা থেমে থাকেন নি। মৃত নিখোঁজ সেনাদের খবর খুঁজে বার করে আত্মীয়দের কাছে পৌঁছে দেবার কাজ শুরু করলেন। যুদ্ধ শেষে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে একটি “হারানো মানুষের দপ্তর” খুললেন। এইখানে তিনি হারানো সেনাদের খুঁজে পাওয়ার জন্য এক অভিনব কায়দা তৈরি করলেন। সেটা হল চিঠি লেখা অভিযান। উত্তরে তার কাছে হারানো স্বজনদের খুঁজে দেয়ার জন্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রচুর আবেদন পত্র আসতে লাগল। গৃহযুদ্ধের সময় জর্জিয়াতে ইউনিয়ন পক্ষের যেসব সেনা বন্দি ছিলেন ও যারা বন্দি অবস্থায় মারা যান তাদের খোঁজে সরেজমিনে তদন্ত করতে তিনি নিজেই জর্জিয়া যান ও ইউনিয়ন পক্ষের হাজার হাজার মৃত সেনার অচিহ্নিত গণকবর খুঁজে বার করেন। তার মধ্যে প্রায় ১৩০০০ সেনা তীব্র শীতে অসুখে ও খিদেয় মারা গিয়েছিলেন। ক্লারা সেই হতভাগ্য সেনাদের নামের তালিকা খবরের কাগজে ছাপতে থাকেন। এর ফলে অনেক পরিবার তাদের হারানো পরিজনের খোঁজ পায়। ঐতিহাসিকরা বলেন একক চেষ্টাতেই ১৮৬৭ সালে ওই অফিস বন্ধ হওয়া পর্যন্ত ৬৩১৮৩ জনের চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন ক্লারা এবং প্রায় ২২০০০ হারানো মানুষের খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। নিখোঁজ সেনাদের মা, স্ত্রী ও সন্তানদের অসহায় অবস্থা লক্ষ্য করে তিনি তাদের সুরক্ষা ও অধিকারের জন্য সরব হন। মেয়েদের অধিকারের সংগঠন তৈরি করেন।
অপরিসীম পরিশ্রমে একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়েন ক্লারা। যুদ্ধের শেষে ডাক্তারের নির্দেশে স্বাস্থ্যের কারণে ইউরোপ যেতে হয়। কিন্তু সেখানে গিয়েও জড়িয়ে পড়লেন যুগান্তকারী কাজের সঙ্গে। ফ্রান্স ও জার্মানির সংঘর্ষের সময় খুব কাছ থেকে দেখলেন জেনেভা চুক্তির (Geneva Convention) উপকারিতা এবং আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা রেড ক্রসের (Red Cross) কাজ। আমেরিকায় রেড ক্রস প্রতিষ্ঠা করার এবং জেনেভা চুক্তিতে আমেরিকাকে সই করানোর প্রতিজ্ঞা নিয়ে দেশে ফেরেন ক্লারা।

দেশে ফিরে লাগাতার চেষ্টা চালিয়ে ১৮৮১ সালে আমেরিকায় ন্যাশনাল সোসাইটি অফ রেড ক্রস (National Society of Red Cross) গঠন করেন এবং আমেরিকা ১৮৮২ সালে জেনেভা চুক্তিতে সই করে। শুরু থেকে ১৯০৪ পর্যন্ত রেড ক্রসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার কার্যকালে আন্তর্জাতিক রেড ক্রসের ইতিহাসে আমেরিকা গুড সামারিটন অফ নেশনস আখ্যায় ভূষিত হয়।
তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৮৮১ সালে ৪ ঠা সেপ্টেম্বরে অসামরিক ক্ষেত্রে ত্রাণ পাঠানো হয় মিশিগানের ভয়ংকর দাবানলের ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০০ এর ওপর মানুষকে। ১৮৮৯ সালে ৩১ শে মে আমেরিকার জনস্টাউন বন্যা কবলিত অঞ্চলে এবং তৃতীয়বার ১৮৯৩ সালে ২৭শে আগস্ট সাউথ ক্যারলিনার সমুদ্র দ্বীপগুলিতে যেখানে ভয়ংকর ঘূর্ণীঝড়ে ৩০০০০ মানুষ গৃহহারা হয়েছিলেন।
এইরকম বহু ত্রাণকার্যে ক্লারা নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে। অবশেষে ১৯০৪ সালে প্রেসিডেন্টের পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি।
তারপর আরও আট বছর জীবিত ছিলেন কর্মক্ষম অবস্থায়। ১২ ই এপ্রিল ১৯১২ সালে সামান্য অসুখে কাউকে সেবা করার সুযোগ না দিয়েই মারা যান। তাঁর লেখা বইগুলোর মধ্যে অন্যতম “হিস্ট্রি অফ দি রেড ক্রস”, (History of the Red Cross) “রেড ক্রস ইন ওয়ার এন্ড পিস”, “দি স্টোরি অফ মাই চাইল্ডহুড”।
১৯৭৫ সালে তাঁর স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে “ক্লারা বার্টন ন্যাশনাল হিস্টোরিক সাইট” (Clara Barton National Historic Site) স্থাপিত হয় তাঁর মেরিল্যান্ডের বাড়িতে। আমেরিকায় কোন মহিলাকে এমন সম্মান দেখানো সেই প্রথম। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস পত্রিকা তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করে লিখেছিল, বর্তমানকালের যুদ্ধ আর যোদ্ধারা জেনেছে –
“একমাত্র তিনিই ছিলেন ক্ষমা ও করুণার সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি।”
ছবি সৌজন্য: Red Cross
প্রকাশক, সমাজসেবক ও শিক্ষাবিদ। নানা ক্রিয়েটিভ কাজকর্মে জড়িয়ে থাকতে
ভালবাসেন, আর ভালবাসেন নিজস্ব লেখালিখি।