বাংলার রাজপাট: চতুর্থ পর্ব
গৌড়ের ভারতের অংশতে এবং পাণ্ডুয়াতে যে ধ্বংসাবশেষ এখন দেখতে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই হল মসজিদ। সেই সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকটা প্রবেশপথ, নগরপ্রাচীর এবং একটা রাজপ্রাসাদের সামান্য অংশ। এ ছাড়াও রয়েছে একটা মিনার বা টাওয়ার।
ফিরোজ মিনার
‘বড় সোনা মসজিদ’ বা ‘বারোদুয়ারী’-র পূর্ব দিকের রাস্তা ধরে খানিকটা এগিয়ে গেলেই সামনে পড়বে পাথর ও ইট দিয়ে তৈরি এক বিশাল মিনার। এর কিছু ইট বা টালিতে ফিরোজা বা ঈষৎ নীল রঙের আভা দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম মিনারটাকে ‘ফিরোজ টাওয়ার’ (Firoz Minar) বলে উল্লেখ করেছিলেন। যদিও তাঁর অনেক আগেই হেনরি ক্রেইটন ওই মিনার ফিরোজ শাহর তৈরি অনুমান করে ‘ফিরোজ মিনার’ নামেই চিহ্নিত করে গেছেন তাঁর বইতে। আনুমানিক ১৪৮৮ সাধারণাব্দে নির্মিত ওই মিনারটাকে তিনি নব্বই ফুট উঁচু ও কুড়ি ফুট পরিধির বলে উল্লেখ করেছেন। বারো-কোণ বিশিষ্ট ওই চোঙাকৃতি মিনারের উপরে ওঠার জন্য তিয়াত্তরটা সিঁড়ির ধাপ আছে। মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচু জমির উপরে প্রতিষ্ঠিত ওই মিনারের শীর্ষে আগে একটা চুড়োও ছিল, সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের কোনও সময়ে সেটা ভেঙে যায়।

পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে গৌড়ের সিংহাসনে বসেছিলেন দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী রাজবংশের সুলতান জালালউদ্দিন ফতে শাহ। তাঁরই শাসনকালে, ১৪৮৬ সাধারণাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন বিশ্বম্ভর মিশ্র তথা গৌরাঙ্গ। ১৫১০ সাধারণাব্দে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁর সন্ন্যাস-নাম হয় কৃষ্ণচৈতন্য ভারতী। তিনি অবশ্য বেশি পরিচিত ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু নামেই।
যাই হোক, জালালউদ্দিন ফতে শাহ কিন্তু একেবারেই সুশাসক ছিলেন না। স্বেচ্ছাচারী এবং অমিতব্যয়ী হওয়ার ফলে প্রজাদের উপরে জবরদস্তি করে টাকা সংগ্রহ করতেন তিনি, পাশাপাশি রাজকর্মচারীরাও প্রজাদের উপরে নানা অত্যাচার করত। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসনকর্তার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা অন্য ধর্মের প্রজাদের অসন্তোষ বাড়িয়ে তুলেছিল। এই রকম এক নৈরাজ্যে গৌড়ের সুলতানিতে ঘটে গেল এক নতুন ঘটনা।
হাবশি সেনাদের বিদ্রোহ
গত পর্বের আলোচনায় আমরা জানিয়েছিলাম যে আফ্রিকার আবিসিনিয়া থেকে আনা ক্রীতদাসদের হাবশি বলা হত। অসম্ভব পরিশ্রমী ও শক্তিশালী ওই ক্রীতদাসদের সেনাবাহিনী এবং রাজপ্রাসাদ প্রহরার কাজে নিযুক্ত করা হত। সাধারণভাবে হাবশি পাহারাদারেরা ‘প্রভুভক্ত’ হলেও তার ব্যতিক্রমও ছিল। জালালউদ্দিন ফতে শাহর অপশাসনের সুযোগে স্থানীয় জমিদারদের সহায়তায় বাংলার বিভিন্ন জায়গায় হাবশি সেনারা বিদ্রোহ করতে আরম্ভ করে। বেশ কিছু জায়গায় তারা সুলতান নিয়োজিত শাসনকর্তাকে সরিয়ে নিজেদের লোক বসায় এবং নিজেদের নামে মুদ্রাও প্রবর্তন করতে আরম্ভ করে। এই আঞ্চলিক বিদ্রোহ এক সময়ে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ১৪৮৭ সাধারণাব্দে, শাহজাদা বারবাক নামে এক নপুংসক খোজা হাবশি সেনানায়ক জালালউদ্দিন ফতে শাহকে হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করলেন। সেই সঙ্গে গৌড়ে সূচনা হল হাবশি সুলতানীয় যুগের।

বারবাক শাহ সুলতানি তখ্তে বসলেন বটে, কিন্তু তিনি একে হাবশি, তার উপর খোজা অর্থাৎ নপুংসক। কাজেই গৌড়ের উচ্চবংশীয় আমির-ওমরাহরা তাঁকে মেনে নিতে পারলেন না। অল্প দিনের মধ্যেই মালিক আন্দিল নামে আরেক হাবশি তাঁকে রাজপ্রাসাদের মধ্যেই হত্যা করে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন।
বাংলার প্রথম হাবশি সুলতান বারবাক জালালউদ্দিন শাহ ফতে শাহ সিংহাসনে বসবার পর থেকেই রাজপ্রাসাদে তাঁকে ঘিরে তাঁর পরিচিতজনেদের যাতায়াত বাড়তে লাগল, কিন্তু সেটা আবার গৌড়ের তৎকালীন অভিজাত শ্রেণির পছন্দ হল না। একে তো বারবাক শাহ বিদেশ থেকে আসা ক্রীতদাস, তার উপরে তাঁর গাত্রবর্ণ আফ্রিকানদের মতো কালো। সব মিলিয়ে সুলতান ও গৌড়ের অভিজাত শ্রেণির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ক্রমে ঘনীভূত হতে লাগল।
গৌড়ের তৎকালীন অভিজাত শ্রেণির মধ্যে স্থানীয় লোকজন যেমন ছিলেন, পাশাপাশি কিছু হাবশিও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন— মালেক আন্দিল। বারবাক শাহের আমল থেকে হাবশি দাসেদের সেনাবাহিনীর উচ্চপদে নিয়োগ করা শুরু হয়। সেই সময়ে তিনি সেনানায়ক পদে উন্নীত হয়েছিলেন, কিন্তু পরবর্তী সুলতান ফতে শাহর আমলে হাবশিদের ক্ষমতা হ্রাস করা হলে মালেক আন্দিল গৌড় ছেড়ে অন্যত্র বসবাস আরম্ভ করেন।

বারবাক শাহ বা সুলতান শাহজাদা সিংহাসনে বসলেও তিনি স্বজাতীয় আরেক হাবশি মালেক আন্দিলকে ভয় করতেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল ওই প্রাক্তন হাবশি সেনানায়ক তাঁর সিংহাসন দখল করে নিতে পারেন! তাই তিনি কৌশলে মালেক আন্দিলকে গৌড়ের রাজসভায় আমন্ত্রণ জানালেন। মালেক আন্দিল সুলতানের আমন্ত্রণে গৌড়ে গেলেও সুলতানের মতলব বুঝে খুব সাবধানে থাকতেন, যাতে কোনও ছলছুতোয় সুলতান তাঁকে কারারুদ্ধ করতে না পারেন। সুলতান শাহজাদাও কোনওভাবে মালেক আন্দিলকে কারারুদ্ধ করতে না পেরে শেষে তাঁকে দিয়ে কোরান ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে, শাহজাদা যতক্ষণ সিংহাসনে থাকবেন, ততক্ষণ মালেক আন্দিল তাঁর কোনও ক্ষতি করবেন না।
এক দিন সুলতান শাহজাদা প্রচুর মদ্যপান করে মহিলাদের পোশাক ও অলংকার পরে সিংহাসনে শুয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরে নর্তকীরা নাচগান করছিল। সুলতানকে বেসামাল মনে করে সুলতানের উপরে অসন্তুষ্ট কিছু প্রহরী মালেক আন্দিলকে ডেকে নিয়ে এল। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মালেক আন্দিল সিংহাসনে শুয়ে থাকা সুলতানকে হত্যা করতে রাজি হলেন না।
মালেক আন্দিল সুলতানের আমন্ত্রণে গৌড়ে গেলেও সুলতানের মতলব বুঝে খুব সাবধানে থাকতেন, যাতে কোনও ছলছুতোয় সুলতান তাঁকে কারারুদ্ধ করতে না পারেন। সুলতান শাহজাদাও কোনওভাবে মালেক আন্দিলকে কারারুদ্ধ করতে না পেরে শেষে তাঁকে দিয়ে কোরান ছুঁইয়ে শপথ করিয়ে নিলেন যে, শাহজাদা যতক্ষণ সিংহাসনে থাকবেন, ততক্ষণ মালেক আন্দিল তাঁর কোনও ক্ষতি করবেন না।
এমন সময়ে মদের ঘোরে থাকা সুলতান হঠাৎই সিংহাসন থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। মালেক দেখলেন, এই সুযোগ। সুলতান সিংহাসনে নেই, অতএব, এমন অবস্থায় তাঁকে বধ করলে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ হবে না। তিনি তখন শাহজাদাকে আঘাত করলেন। কিন্তু আঘাতে তেমন জোর না থাকায় সুলতানের মদের ঘোর কেটে গেল এবং তিনি সম্বিত ফিরে পেয়ে লাফিয়ে উঠে মালেক আন্দিলের বুকের উপরে চেপে বসলেন। আন্দিলের এক অনুগত কর্মচারী তখন সুলতানকে আঘাত করে এবং তিনি মারা গিয়েছেন ভেবে ঘরে ফেলে রেখে সকলে চলে যায়। কিন্তু খানিক পরে তিনি তখনও বেঁচে আছেন জানতে পেরে মালেক আন্দিল সেই ঘরে গিয়ে আহত সুলতান শাহজাদাকে হত্যা করলেন।

সুলতান ফিরোজ শাহ
মালেক আন্দিলের পুরো নাম সুলতান সাইফুদ্দিন আবুল মুজফফার ফিরোজ শাহ। সুলতান শাহজাদাকে হত্যা করলেও তিনি প্রথমে নিজে সুলতান হতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু মৃত শাহজাদার মহিষী ও অন্যান্য অভিজাতদের অনুরোধে ফিরোজ শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন।
ফিরোজ শাহ হাবশি হলেও খোজা অর্থাৎ নপুংসক ছিলেন না। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য জায়গায়! তুরস্ক, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে আসা পূর্ববর্তী প্রায় সব শাসকেরই গায়ের রং ছিল ফর্সা, কিন্তু আফ্রিকার আবিসিনিয়ার (বর্তনাম নাম ইথিয়োপিয়া) আদিবাসী গোষ্ঠী থেকে ভারতে পাচার হয়ে আসা ক্রীতদাসদের বংশধর হিসেবে তাঁর গায়ের রং ছিল কালো। ফলে অভিজাত মুসলিম আমিরদের অনেকেই তাঁকে পছন্দ করত না। তিনি সেই সমস্যা দূর করতে এবং নিজের গ্রহণযোগ্যতাকে শক্তিশালী করতে ‘খলিফৎ আল্লাহ-বিল-হুজ্জতে ওয়াল বুরহান’ উপাধি গ্রহণ করেন। এর অর্থ হল, ‘দলিল সাক্ষ্য-মতে আল্লাহর খলিফা।’

সুলতান হওয়ার পর একবার তিনি গরিব প্রজাদের জন্য রাজকোষ থেকে এক লক্ষ মুদ্রা দান করবার আদেশ দিলেন। এরকম তিনি আগেও করেছেন। কিন্তু তাঁর এই দানশীলতা এক শ্রেণির আমিরের পছন্দ হত না। তাঁরা বলাবলি করতেন যে গরিব ক্রীতদাস থেকে সুলতান পদে উন্নীত হয়ে তাঁর মাথা ঘুরে গেছে। তিনি টাকার মূল্য বোঝেন না তাই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করে নষ্ট করছেন…
আড়ালে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলেও সুলতানের সামনে সে সব কথা বলার সাহস তাঁদের ছিল না। তাই তাঁরা একটা কৌশল করলেন। যেসব কর্মচারীর উপরে দানের টাকা বণ্টন করবার ভার ছিল, তাঁদের মাধ্যমে সুলতানের যাওয়া-আসার পথের সামনে দানের জন্য রাখা মুদ্রাগুলো রেখে দিলেন। যাতায়াতের পথে মুদ্রাগুলো সুলতানের নজরে পড়ল। তিনি কর্মচারীদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘এগুলো কীসের মুদ্রা, এভাবে সামনে রয়েছে?’’ কর্মচারীরা উত্তর দিলেন যে ওগুলো দানের জন্য রাখা হয়েছে। সুলতান ফিরোজ শাহ তখন বললেন, ‘‘এত কম মুদ্রা দান করা হচ্ছে? ওগুলো দ্বিগুণ করে দাও।’’ আমিররা বিস্মিত হলেও প্রতিবাদ করবার সাহস তাঁদের ছিল না ফলে সুলতানের দান করা আটকাতে তাঁদের কৌশল আর খাটল না!
সুলতান ফিরোজ শাহের উদ্যোগে গৌড়ে একটা জলাশয়, একটা মসজিদ এবং ফিরোজ মিনার নির্মিত হয়েছিল। ফিরোজ শাহর রাজত্বকালে গুয়ামালতী কুঠির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মুকালিশ খাঁ একটা মসজিদ নির্মাণ করেন। এখন অবশ্য শুধু তার কয়েকটা স্থম্ভ অবশিষ্ট আছে।

ফিরোজ মিনার ঠিক কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন এটা কোনও জয়স্তম্ভ, আবার সম্ভবত মিনারের শীর্ষে বাতি জ্বালানো হত বলে স্থানীয় হিন্দুরা একে ‘চেরাগদানি’ও বলে।
ফিরোজ শাহ মিনার নিয়ে একটা জনশ্রুতি আছে। বলা হয়ে থাকে, মিনারের কাজ শেষ হলে সুলতান স্থপতি রাজমিস্ত্রিকে সঙ্গে করে মিনারের শীর্ষে উঠলেন। এসময় রাজমিস্ত্রি অহংকার করে বলে ফেলেন, ‘‘আমি এর থেকেও উঁচু মিনার তৈরি করতে পারতাম।’’
সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘করনি কেন?’’
রাজমিস্ত্রি উত্তর দিলেন, ‘‘উপযুক্ত মালমশলা পাইনি বলে…’’
সুলতান তখন জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘চাওনি কেন?’’
তখন রাজমিস্ত্রি আর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁকে নিরুত্তর দেখে সুলতান রেগে গিয়ে ওই রাজমিস্ত্রিকে উপর থেকে ফেলে দেওয়ার আদেশ দিয়ে নীচে নেমে এলেন। সুলতানের আদেশে প্রহরীরা রাজমিস্ত্রিকে উপর থেকে ফেলে দিল। অহংকার করতে গিয়ে তাঁর প্রাণ চলে গেল!

এদিকে সুলতান মিনার থেকে নীচে নেমে এসে হিঙ্গা নামের এক পাইককে দেখতে পেয়ে রাগের মাথায় হুকুম দিলেন, ‘‘হিঙ্গা তুই মোরগা যা…’’ সুলতানের রাগি চেহারা দেখে হিঙ্গাও আর কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেলেন না। তিনি সোজা মোরগার পথ ধরলেন। সেখানে গিয়ে সনাতন নামে এক ব্রাহ্মণের বুদ্ধিতে মোরগা থেকে রাজমিস্ত্রি নিয়ে গৌড়ে ফিরলেন।
হিঙ্গাকে রাজমিস্ত্রি সঙ্গে নিয়ে ফিরতে দেখে ফিরোজ শাহ অবাক হলেন! কারণ তিনি রাগের মাথায় সব কথা হিঙ্গাকে বলেননি, অথচ হিঙ্গা ঠিক কাজটাই করেছে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করাতে হিঙ্গা সনাতনের কথা সুলতানকে জানালেন। সুলতান তখন সনাতনকে রাজদরবারে আমন্ত্রণ জানালেন। কেউ কেউ বলেছেন, তিনিই পরবর্তীকালে সনাতন গোস্বামী নামে গৌড় রাজসভায় পরিচিত হন। সুলতান হিঙ্গার আনা রাজমিস্ত্রিকে দিয়ে মিনারের শীর্ষের চুড়োটা তৈরি করালেন। সেটা অবশ্য পরবর্তীকালে ভেঙে পড়ে।
এই আখ্যানের সূত্র ধরেই, কোনও কারণ না জানিয়ে কাউকে কোনও কাজ করতে বললে, ‘‘হিঙ্গা তুই মোরগাঁ যা’’ —এই বাক্যবন্ধের উৎপত্তি হয়েছে। মালদহ জেলায় এখনও এই প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়।
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সনাতন গোস্বামীর লেখা ‘শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ’ গ্রন্থের অবতরনিকা অংশের লেখক হরিদাস দাস অবশ্য ওই সুলতানকে হুসেন শাহ বলে উল্লেখ করেছেন।
গ্রন্থঋণ:
১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে‘জ পাবলিশিং কলকাতা ৭০০০৭৩
২। মালদহ: জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র
৩। মালদহ চর্চা (১), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল
৪। মালদহ চর্চা (২), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল
৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা
৬। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা
৭। কেদারনাথ গুপ্ত, গৌরবময় গৌড়বঙ্গ, সোপান, কলকাতা
৮। সুস্মিতা সোম, মালদহ ইতিহাস-কিংবদন্তী, সোপান কলকাতা
৯। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা
১০। প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস: প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা
১১। সিদ্ধার্থ গুহরায়, মালদা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা
১২। কমল বসাক, শ্রীশ্রীরামকেলিধাম রূপ-সনাতন ও মালদহের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, উৎসারিত আলো প্রকাশনী, মালদহ বুক ফ্রেন্ড, মালদহ
১৩। সনাতন গোস্বামী, শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ, শ্রীনবদ্বীপ হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ
১৪। Creighton Henry, The Ruins of Gour described and represented in eighteen views; with a topographical map, Londan
*পরবর্তী অংশ প্রকাশ পাবে ২৭ অক্টোবর, ২০২৩
গৌতম বসুমল্লিকের জন্ম ১৯৬৪ সালে, কলকাতায়। আজন্ম কলকাতাবাসী এই সাংবাদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার সুবাদে। মূলত কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও, এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন’ [UGC, Human Resource Development Centre (HRDC)]-র আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন দীর্ঘকাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো’।




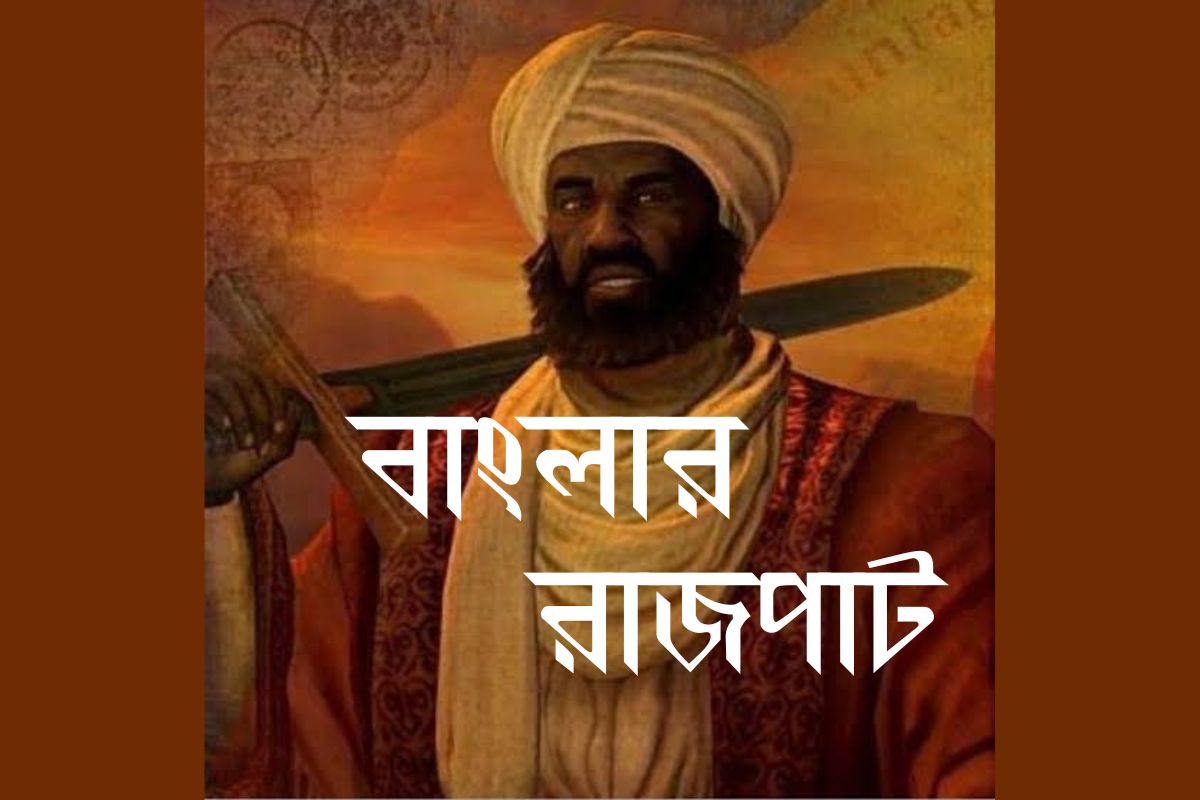





















One Response
দারুণ তথ্যসমৃদ্ধ লেখা, বাংলার ইতিহাস তেমনভাবে সচরাচর এত সুন্দর ও সাবলীল ভাবে পাওয়া যায় না ও প্রচলিত নয়… অসংখ্য ধন্যবাদ 🙏