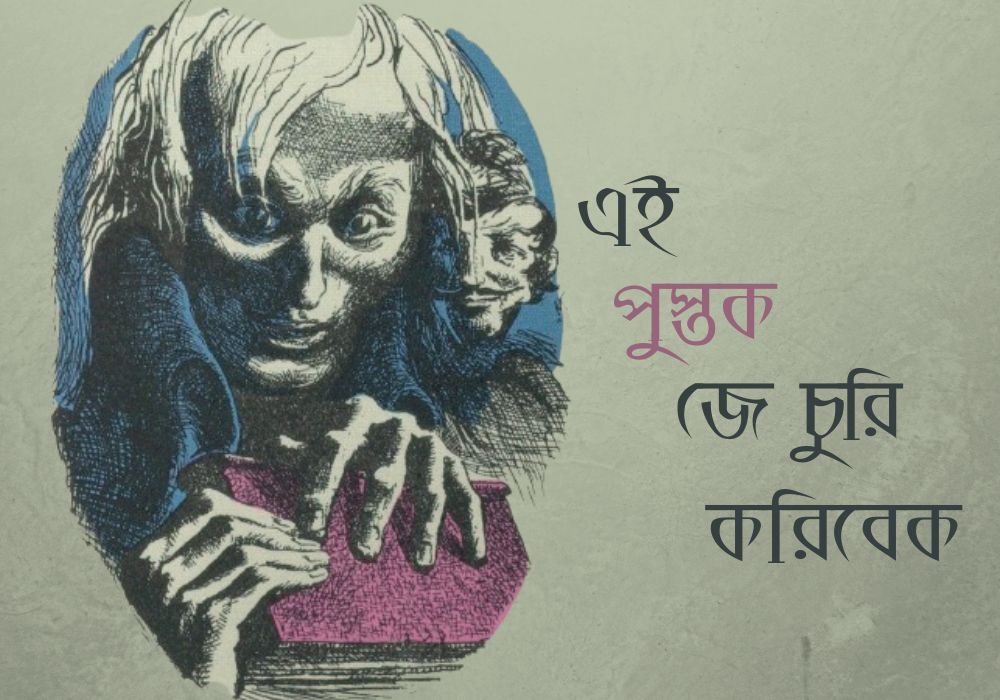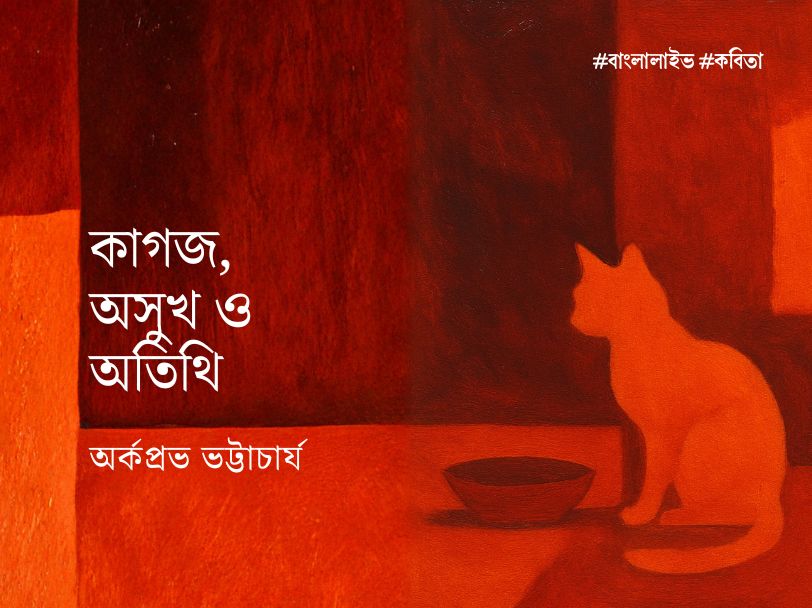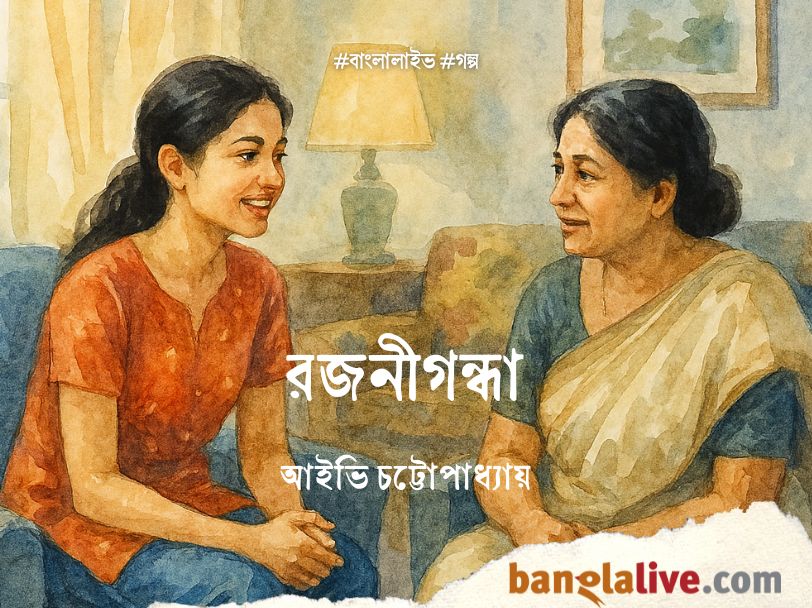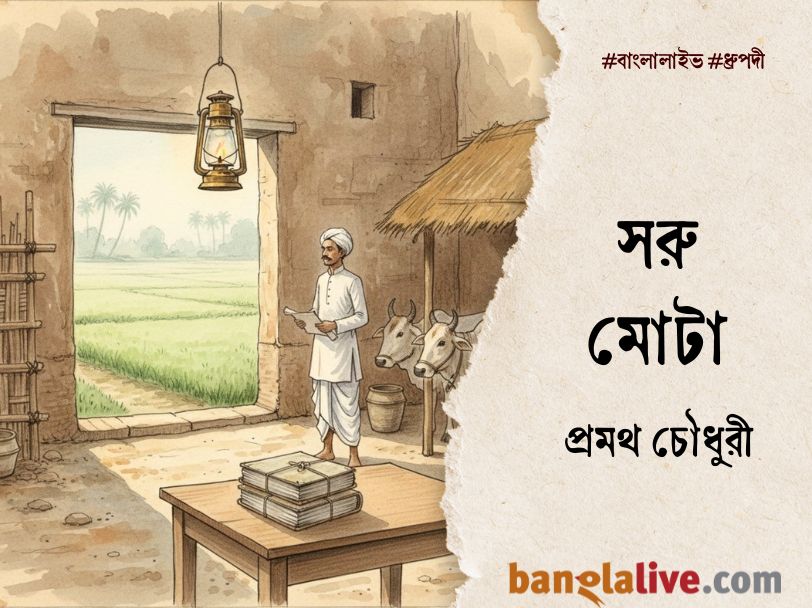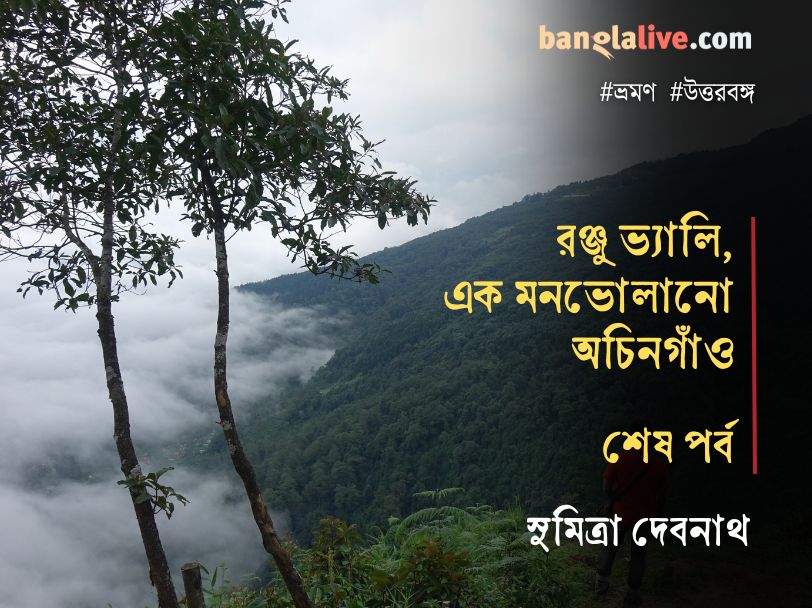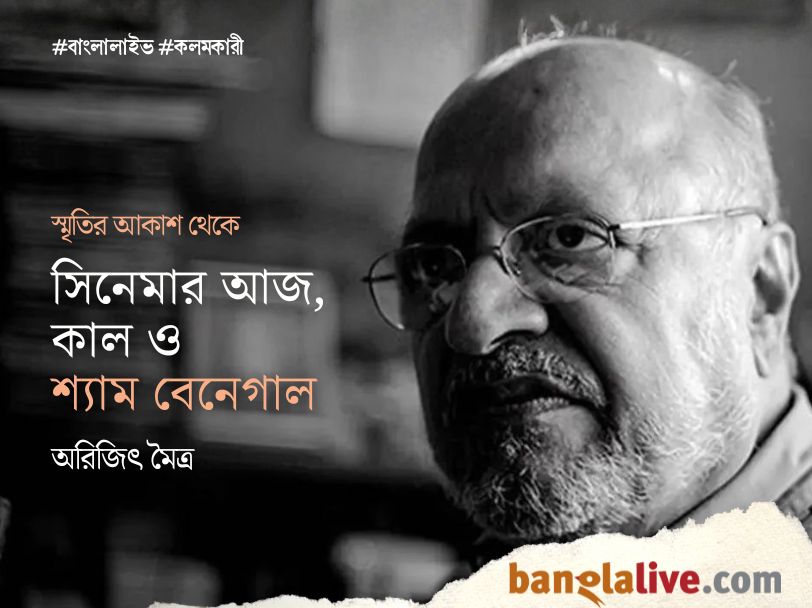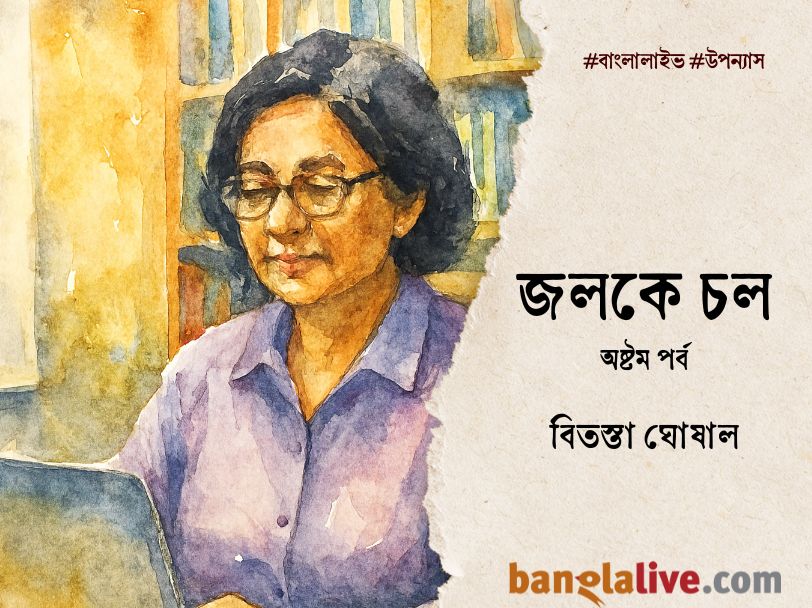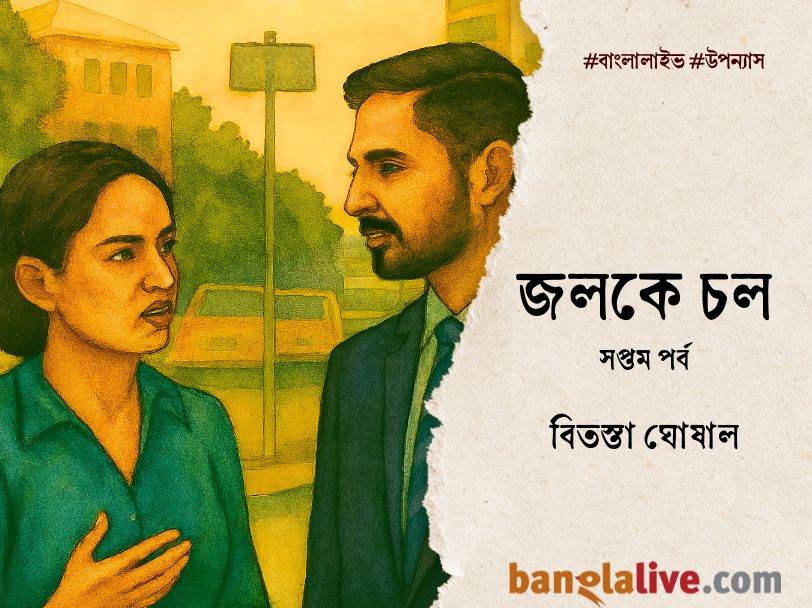মার্ক টোয়েনের লাইব্রেরির গল্প দিয়েই শুরু করা যাক। ভদ্রলোকের বইয়ের কালেকশান ছিল দেখার মতো। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত স্তরে স্তরে বই আর বই। এমনকি মেঝেও ছাড় পায়নি। ঘরে হাঁটা মুশকিল। এক বন্ধু শেষে বাধ্য হয়েই বললে “এভাবে বইগুলো নষ্ট না করে শেলফ জোগাড় করে আনলেই তো হয়!”
মাথা-টাথা চুলকে টোয়েন উত্তর দিলেন “তা তো হয় ভাই, কিন্তু যেভাবে বই জোগাড় করেছি, শেলফ তো আর সেই কায়দায় জোগাড় করা যায় না। আর ধার চাইলে বন্ধুরা শেলফ দেবেই বা কেন?”
মুজতবা আলি একেবারে ঠিক লিখেছেন “যে মানুষ পরের জিনিস গলা কেটে ফেললেও ছোঁবে না, সেই লোকই বইয়ের বেলায় সর্বপ্রকার বিবেক-বিবর্জিত।” আলি সায়েব এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা বুঝেছেন, তা হল জ্ঞানার্জন ধনার্জনের চেয়ে মহত্তর। তাই এই মহৎ কাজে কোনও পন্থাই দোষের না। সপ্তম শতকের লেখক টেলমা দে র্যু তো জোর গলায় বলেই গেছেন “বই চুরি কিছুতেই দোষের না, যদি না সেই বই কেউ বিক্রির জন্যে চুরি করে।”
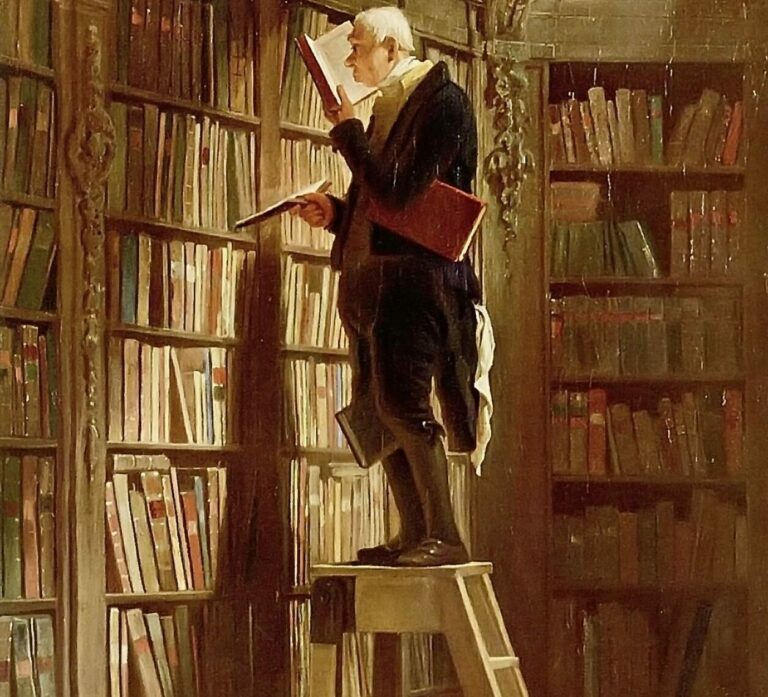
বইচুরির এই প্রবণতা আজকের না। আলবের্তো মাঙ্গেল পড়তে গিয়ে দেখলুম বইচুরি (যার গালভরা নাম বিব্লিওক্লেপ্টোম্যানিয়া)র উৎপত্তি মানব সভ্যতার একেবারে শুরুর দিনের গ্রিক কিংবা প্রাচ্যের লাইব্রেরিগুলো থেকে। রোমানদের লাইব্রেরির বেশিরভাগ বইই ছিল গ্রিক, কারণ গ্রিস জয়ের সময় তারা লাইব্রেরির সব বই লুটেপুটে নিয়ে চলে এসেছিল। (Bibliokleptomania) ইতিহাসের পাতায় তৃতীয় শতকের এক সাধু প্যাকোমিয়াসের নাম পাই, যিনি সেই কবেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন কীভাবে লাইব্রেরি থেকে বই চুরি ঠেকানো যায়। অ্যাংলো স্যাক্সন যুগে ইংল্যান্ডে যখন ভাইকিংরা আক্রমণ করল, শুরুতেই তাদের নজরে এল সেখানকার বিরাট বিরাট সব লাইব্রেরিগুলো। ছাপা বইয়ের কাল তখনও আসেনি। বর্বরগুলো বইয়ের বাঁধাই আর ভিতরের ছবির সোনার জল থেকে সোনাটুকু নিয়ে বইগুলোকে বেমালুম পুড়িয়ে দিত।
রোমানদের লাইব্রেরির বেশিরভাগ বইই ছিল গ্রিক, কারণ গ্রিস জয়ের সময় তারা লাইব্রেরির সব বই লুটেপুটে নিয়ে চলে এসেছিল। ইতিহাসের পাতায় তৃতীয় শতকের এক সাধু প্যাকোমিয়াসের নাম পাই, যিনি সেই কবেই নির্দেশ দিয়ে গেছেন কীভাবে লাইব্রেরি থেকে বই চুরি ঠেকানো যায়।
মজা হয়েছিল কোডেক্স অরিয়াসের বেলায়। একাদশ শতকে সোনায় মোড়া এই বইটি লাইব্রেরি থেকে চুরি যায়। চোরেরা দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে খরিদ্দার না পেয়ে শেষে আসল মালিকের কাছেই এসে বলে “আমাদের ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করে দিন। তবে কিছু পয়সাকড়ি যদি দিতেন। মেলা খরচা হয়ে গেছে এদিক ওদিক করতে করতে।”

রেনেসাঁস যুগে তো বই চুরি একেবারে শিল্পের পর্যায়ে চলে গেল। পোপ চতুর্থ বেনেডিক্ট বাধ্য হয়ে প্যাপাল বুল চালু করলেন। যে বই চুরি করবে, তার উপরে ভগবানের অভিশাপ নেমে আসবে। চোরেদের তাতে ঘণ্টা। সান পেদ্রোর মঠের লাইব্রেরিতে গেলে দেখতে পাবেন, এখনও খোদাই করা আছে “যে ব্যক্তি পুস্তক চুরি করিবেন অথবা ধার লইয়া ফিরত দিবেন না, পরম করুণাময় ঈশ্বরের অভিশাপে তাহার হস্ত কালসর্পে পরিণত হইয়া তাহাকেই দংশাইবে…”
ঠিক এইখানে একেবারে দেশি কিছু অভিশাপের কথা মাথায় এল। বাংলায় মধ্যযুগের কিছু পুথির শেষে চোরেদের উদ্দেশ্যে মহা মহা সব গালি লেখা থাকত। এতদিন বাদে পড়লে তূরীয় আনন্দ পাওয়া যায়। কয়েকটা বলি (বানান মূলানুগ)-
• এ পুস্তক যে চুরি করিবেক কিম্বা মাগিয়া লয়্যা জায় যদ্যপি নাই দেই তাহাকে গো হর্ত্তা ব্রহ্মহত্তার পাপ লাগে এবং মাত্রিহরণ করে এইমত তাল্লাক॥
• যতনে লিখিলাম পুঁথি চুরি করে জে সুকর তাহার পিতা গাধা হঅ সে।
• এই পুস্তক যে ছাপিবেন (অর্থাৎ গোপন করবেন) সে ব্যক্তি হিন্দু হইয়া মুসলমান হইবেক… আর সুরাপান করিবেক॥
• এ পুস্তক জে ব্যক্তি চুরি করিবে সে সাসুরে হইবেক আর পুত্রবধূকে হরণ করিবেক।
• যে এই পুথি চুরি করিবে সে বোবা হইবে।
• এই পুস্তক জে চুরি করিবেক আর জে চুরি কোরে না দিবেক শে মাতৃহরণ করিবেক আর পুথী পড়িতে আর জে লিখীতে নিএ জে দিবেক নাই সে গুরুপত্নী করিবেক ইহাতে ভেদ নাই॥
• এ পুস্তক চুরি করি যিনি নিবেন তাহার এই বেবথা…. তিনি মসাএর স্থানে বেতগাবে আর আমিহ কান মলিএ দিব আর এবং তাহার মাতা ধরে কিল হাড়িতে মারিবে এবং ইতি॥
• এ গ্রন্থ যে চুরি করিবেক শে আপনার সাশুড়িকে লইবেক।
এটুকু বলে রাখি, সেই বহুবিবাহের কালে প্রায়ই শাশুড়িরা জামাইয়ের সমবয়সী বা ছোট হতেন। বরং বউ হত একেবারে নাবালিকা। ফলে সাসুরে বা শাশুড়ির সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক খুব একটা অচেনা কিছু ছিল না।

গালি দেওয়া একরকম, কিন্তু বই চুরির জন্য খুন অবধি করা একেবারে অন্য স্তরের ব্যাপার। তাও হয়েছে। ভদ্রলোকের নাম ডন ভিনসেন্ট। স্পেনের এক মঠের সাধু। দিনরাত পড়ে থাকতেন মঠের দুষ্প্রাপ্য সব বই দিয়ে সাজানো গ্রন্থাগারে। ১৮৩০ নাগাদ তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। মঠের থেকে দামি দামি সব বই চুরি করে পালিয়ে গেলেন বার্সেলোনা। সেখানেই এক বই বিক্রেতা হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হল। আজকের দিন হলে কী হত জানি না, তখন অবশ্য বই চুরিকে তেমন অপরাধ হিসেবে দেখা হত না। তবে ভিনসেন্টের আগ্রহ বই বিক্রির দিকে কম, বই কেনার দিকে বেশি ছিল। যখনই কোনও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধান পেতেন, যত দামই হোক না কেন, তাঁর সেটা কেনা চাই। তাঁর দোকানটিও ছিল অদ্ভুত। বেশিরভাগ বই তিনি বিক্রি করতেন না। বইয়ের গায়ে লেখা থাকত “শুধুমাত্র বিক্রেতার ব্যবহারের জন্য। বিক্রির জন্য নহে।”
১৮৩০ নাগাদ তিনি আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। মঠের থেকে দামি দামি সব বই চুরি করে পালিয়ে গেলেন বার্সেলোনা। সেখানেই এক বই বিক্রেতা হিসেবে তাঁর জীবন শুরু হল।
১৮৩৬ সাল নাগাদ তিনি খোঁজ পেলেন এক নিলামঘরে ১৪৮২ সালে ছাপা ‘Edicts for Valencia’ বইটা নিলাম হবে। বইটি ঐতিহাসিক, কারণ এটি ছেপেছিলেন স্পেনের প্রথম মুদ্রাকর লাম্বেরতো পালমার্ট। ভিনসেন্ট স্থির করলেন যে কোনও উপায়ে এ বই তাঁকে পেতেই হবে। তাঁর বিশ্বাস, পৃথিবীতে এই একটি বই অবশিষ্ট আছে। নিজের সব সম্বল নিলামে লাগালেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর! নিলামে তাঁকে হারিয়ে বই কিনে নিলেন অন্য এক বই বিক্রেতা অগাস্টিনো প্যাক্সটট।
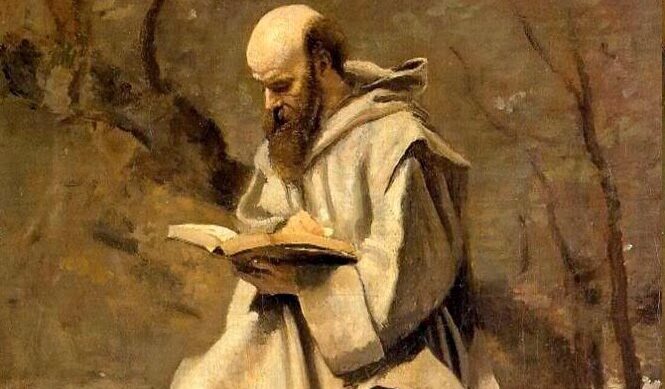
ভিনসেন্ট ব্যাপারটা মোটেই ভালোভাবে নিলেন না। তিনদিন বাদে প্যাক্সটটকে নিজের বইয়ের দোকানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। দোকানে শুধু একটি জিনিসই চুরি গেছে, পালমার্টের সেই বইখানা। খুব স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ এল ভিনসেন্টের উপর। তাঁর দোকানে তল্লাশি চালিয়ে শুধু সেই বইটিই পাওয়া গেল তা নয়, পাওয়া গেল মঠে হারানো সব কটি দুষ্প্রাপ্য বই। ভিনসেন্ট একটিও বিক্রি করেননি, যদিও যেকোনও একটি বিক্রি করলেই তিনি প্রচুর টাকা পেতেন।
বিচার শুরু হল ভিনসেন্টের। বারবার তিনি দাবি করলেন, তিনি চোর বা খুনি নন। বইগুলো তাঁর কাছেই সবচেয়ে যত্নে থাকবে, তাই তিনি এগুলো নিজের কাছে এনে রেখেছেন। নিজের কাজের সপক্ষে এই ছিল তাঁর যুক্তি। গল্প এখানেই শেষ না। বিচারের শেষ দিকে তাঁর উকিল প্যারিস থেকে “Edicts for Valencia” র আরও একটা কপি খুঁজে বার করে প্রমাণ করতে চাইলেন ভিনসেন্টের কাছে থাকা বইটাই যে প্যাক্সটটের বই তার কোনো মানে নেই। এই ঘটনা ভিনসেন্টের মন ভেঙে দিল। তিনি কেমন একটা পাগলমতো হয়ে গেলেন। দিনরাত শুধু বলতেন “আমার বইটা একমাত্র নয়!” এরপর খুব বেশিদিন বাঁচেনওনি তিনি। বইয়ের শোকেই তাঁর মৃত্যু ঘটল।

তবে বইচুরির ঘটনা না ঘটলে সেকেলের কলকাতায় একটা বড় বদল হয়ত হতই না। দেড়শো বছরের কিছু আগে, ১৮৫৭ তে জেমস লং দুঃখ করে লিখছেন “কলকাতায় কোনও বইয়ের দোকান নেই, আছে শুধু ফেরিওয়ালা। তাঁরা মাথায় ঝাঁকা নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বইফিরি করে বেড়ায়।” এই কায়দাও অবশ্য নতুন কিছু না। ইউরোপে বই ছাপা শুরু হলে ভাল বইয়ের এত দাম ছিল, যে সাধারণ মানুষ তা কিনে পড়তে পারতেন না। তাঁদের জন্য ছিল সস্তা কাগজে বাজে ছাপা কিছু বই। এদের বলা হত চ্যাপবুক। চ্যাপবয় নামে ছেলেরা কয়েক পেনির বদলে পাড়ায় পাড়ায় এদের ফেরি করে বেড়াত। কলকাতায় সবেধন নীলমণি হিসেবে লালদিঘির পাশে ‘সেন্ট অ্যান্ড্রুজ’ নামে একটা বিলিতি বইয়ের দোকান ছিল। লন্ডন থেকে জাহাজে করে বই এলে সাহেব মেমসাহেবরা এই দোকান থেকে বই কিনতেন। ১৭৭৮ সালে প্রথম বাংলা বই হলহেডের ব্যাকরণ ছাপা হলে তা এই দোকান থেকেই বিক্রি হত। এদিকে শ্রীরামপুর প্রেস থেকে সাহেবদের নেটিভ ভাষা শেখানোর জন্য দেদার বাংলা বই ছাপা হতে লাগল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে রীতিমতো গ্রন্থাগার স্থাপন হল। মুশকিল হল যেহেতু খোলা বাজারে সেসব বই পাওয়া যায় না, তাই বই চুরি হতে শুরু করল আর কালোবাজারে বিকোতে লাগল দশগুণ দামে। কলেজ কাউন্সিল ঠিক করলেন, তাঁরা নিজেরাই বই ছাপিয়ে সাধারণ মানুষের জন্য ন্যায্য দামে বেচবেন। কলকাতা নতুন এক ব্যবসার নাম শুনল। বই ব্যবসা।
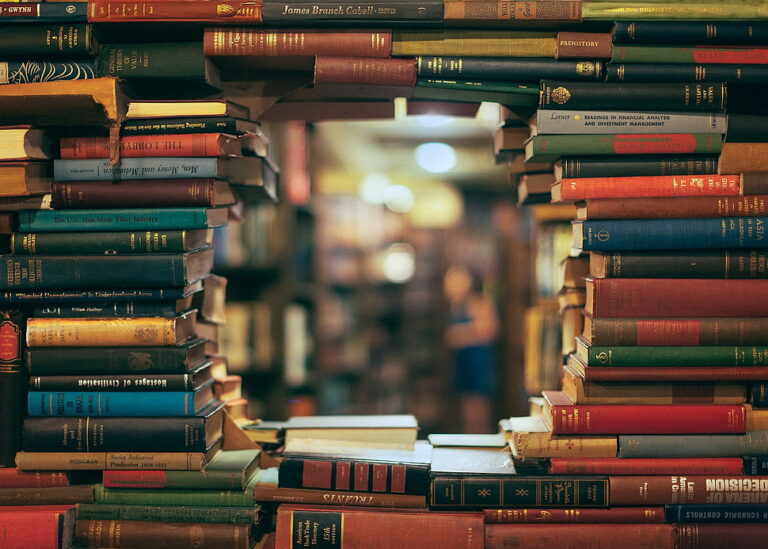
শেষ করি এক লেখকের বই চুরির অভিজ্ঞতা দিয়ে। ভদ্রলোক টোয়েনের পথে বিশ্বাসী। বন্ধুদের থেকে বই চেয়ে আনেন। প্রথমেই পড়েন না। কিছুদিন আলমারিতে শোভা পায়। তারপর সাহস করে একদিন বাঁধিয়ে নিয়ে আসেন। আরও কয়েকমাস বাদে, যখন তিনি নিশ্চিন্ত, যে বন্ধু বইয়ের কথা ভুলেই গেছে, তখন বইয়ের প্রথম পাতায় নিজের নামটি লিখে দেন। ব্যাস! বই নিজের। এবার পড়া শুরু। এভাবেই তাঁর লাইব্রেরি বাড়ছিল।
একবার এক বন্ধুর থেকে একখানি দামি বই এনেছেন। ছয় মাসের মধ্যে বন্ধু সে বইয়ের খোঁজ করে না। বাড়ি এলেও সে বুক শেলফের দিকে তাকায় না। নয় মাসের মাথায় চামড়া দিয়ে বই বাঁধানো হল। এক বছর পূর্তিতে তিনি নিজের নাম বইতে লিখলেন।
সেদিনই সেই বন্ধু এসে হাজির। আর এসেই সোজা শেলফের সামনে।
“এই তো ভাই, যে বইটা নিয়েছিলে, খুব সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিয়েছ দেখছি। আসলে চামড়ায় বাঁধাইয়ের যা দাম! তবে তুমি কারও থেকে বই নিলে বাঁধিয়ে দাও এটা অন্যদের মুখে শুনেছিলাম। রোজই আসি আর ভাবি কবে বইটা বাঁধানো দেখব। ওমা! আবার প্রথম পাতায় নিজের নাম লিখেছ? ও কিছু না। আমি তুলে দেব। অনেক ধন্যবাদ ভাই। আজ তবে আসি” বলে বই নিয়ে সটান রওনা হল সে।
জন্ম ১৯৮১-তে কলকাতায়। স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি-তে স্বর্ণপদক। নতুন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কারক। ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়ায় বৈজ্ঞানিক পদে কর্মরত। জার্মানি থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা গবেষণাগ্রন্থ Discovering Friendly Bacteria: A Quest (২০১২)। তাঁর লেখা ‘কমিকস ইতিবৃত্ত’ (২০১৫), 'হোমসনামা' (২০১৮),'মগজাস্ত্র' (২০১৮), ' জেমস বন্ড জমজমাট'(২০১৯), ' তোপসের নোটবুক' (২০১৯), 'কুড়িয়ে বাড়িয়ে' (২০১৯) 'নোলা' (২০২০) এবং সূর্যতামসী (২০২০) সুধীজনের প্রশংসাধন্য। সম্পাদনা করেছেন ‘সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রবন্ধ সংগ্রহ’ (২০১৭, ২০১৮)'ফুড কাহিনি '(২০১৯) ও 'কলকাতার রাত্রি রহস্য' (২০২০)।