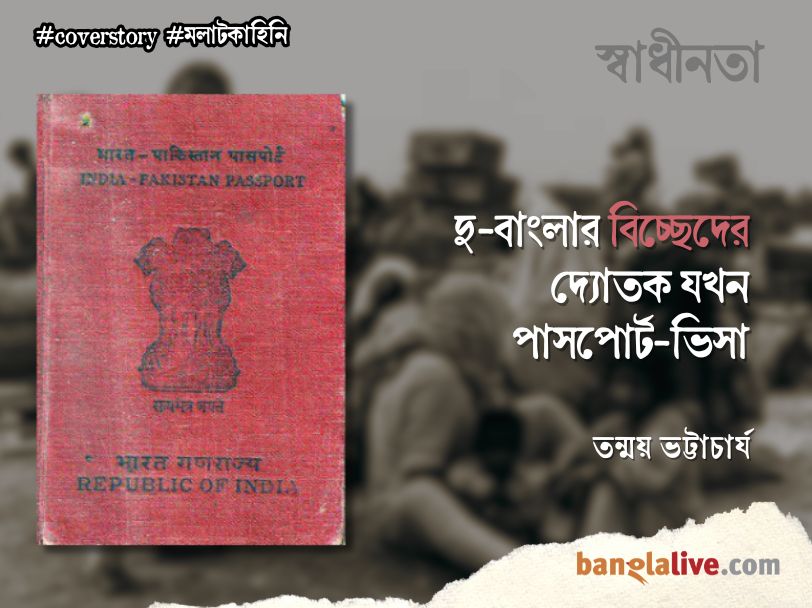‘স্বাধীনতা’ শব্দটির অর্থ একমুখী নয়। ব্যক্তি ও ভূগোলভেদে বদলে যায় তার গুরুত্ব ও অভিঘাত। পশ্চিমবঙ্গে শব্দটি ঐতিহাসিকভাবে ১৯৪৭-এর ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসকেই অনুসরণ করে। আর সেই সূত্রেই হাজির হয় আরেক শব্দ— ‘দেশভাগ’। এদের চলন কখনও পিঠোপিঠি, কখনও আবার প্রথমটির তুলনায় ভারী হয়ে ওঠে দ্বিতীয়টিই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এক-থাকা বঙ্গীয় ভূখণ্ড যখন বিচ্ছিন্ন হয়, বৃহৎ সংখ্যক মানুষের কাছে প্রশ্নের মুখে পড়ে ‘স্বাধীনতা’-র অর্থই। অবিশ্বাস্যও ঠেকে বইকি! এই বিচ্ছেদ যে অপরিবর্তনীয়— কালক্রমে টের পাওয়ার পর, জন্মায় বিবিধ প্রতিক্রিয়া। সেইসব প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, চুঁইয়ে নামে সাহিত্যেও। ঘটনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠে বিভিন্ন মোটিফ। শুধু সমকালে নয়, সময়সরণি বেয়ে তার রেশ ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তী দশকগুলিতেও। তেমনই একটি মোটিফ— ‘পাসপোর্ট’ (Passport) নিয়ে এই আলোচনা, যা এক অর্থে প্রশ্নের মুখে ফ্যালে যাতায়াতের স্বাধীনতাকেও।
ব্রিটিশ ভারতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সীমিত কয়েকটি দেশে যাতায়াতের জন্য প্রথম পাসপোর্ট পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু আম বাঙালির জীবনে পাসপোর্টের গুরুত্ব অনুভূত হয় স্বাধীনতা তথা দেশভাগের পর, ১৯৫২ সালে। তার আগে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের (পূর্ব পাকিস্তান) মানুষের যাতায়াত ও মাইগ্রেশন ছিল ‘বর্ডার পাস’-এর ওপর নির্ভরশীল। বর্ডারে পৌঁছে, অপর দেশে প্রবেশের ছাড়পত্র সংগ্রহ করা। এতে নিয়মগতভাবে অন্য-কোনো কড়াকড়ি বিশেষ ছিল না বললেই চলে। অবশ্য গোড়ার দিকে বর্ডার পাসের বালাইও ছিল না, বর্তমান নিবন্ধকারকে এমনটাই জানান অধ্যাপক পবিত্র সরকার (৮৭)। ১৯৪৭-এর নভেম্বরেই পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসেন তিনি। তাঁর স্মৃতি অনুযায়ী, সেই সময়ে বর্ডার পাসের প্রয়োজন তো হয়ইনি, এমনকি পরবর্তী দু-বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ পর্যন্ত একাধিকবার যাতায়াতের সময়েও সে-নিয়ম দেখেননি তিনি।
১৯৫২ সালে ভারত ও পাকিস্তান সরকার যৌথভাবে পাসপোর্ট ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারিখ ঠিক হয় সে-বছরের ১৫ অক্টোবর। ঘোষিত হয়, পাসপোর্ট ব্যবহার করে র্যাডক্লিফ লাইনের অপর পাড়ে যাতায়াত করতে পারবেন উদ্বাস্তুরা। তবে একদেশ থেকে অপর দেশে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দেওয়া হত বর্ডারেই।
এই প্রসঙ্গে বর্ষীয়ান নাগরিক রথীন্দ্রমোহন গোস্বামীর (৮৮) বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে আসেন তিনি। স্মৃতিচারণায় বর্তমান নিবন্ধকারকে তিনি জানান, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র ঢাকাতেই ছিল পাসপোর্ট অফিস। নিজেদের গ্রাম (ময়মনসিংহের যশোদল) থেকে ডাকযোগে ঢাকায় পাসপোর্টের আবেদনপত্র পাঠান তাঁরা, পাসপোর্টও হাতে পৌঁছোয় ডাকযোগেই। তারপর সেই পাসপোর্ট নিয়ে দর্শনা হয়ে (মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট সহ) ভারতে প্রবেশ করেন তাঁরা। রথীন্দ্রবাবুর থেকে এ-ও জানা যায় যে, ভারত থেকে কেউ পাসপোর্ট ব্যবহার করে পূর্ব পাকিস্তানে সাময়িকভাবে গেলে, স্থানীয় থানায় উক্ত ব্যক্তির আগমন ও বসবাসের বিবরণী ইত্যাদি নথিভুক্ত করার নিয়ম ছিল।
উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের সচিব হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন, পাসপোর্ট-প্রথা চালু হওয়ার খবর শুনে ১৯৫২ সালে উদ্বাস্তুদের ঢল নামে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে জুলাই-অক্টোবরে। ভয় ছিল, পাসপোর্ট চালু হলে বোধকরি উভয় দেশে যাতায়াত আর সহজ হবে না ততটা। যাতায়াতের ‘স্বাধীনতা’-টুকুও হারানোর যে ভয়, তা গ্রাস করেছিল অসংখ্য বাঙালিকে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ওই চার মাসে প্রায় বাষট্টি হাজার মানুষ বর্ডার পেরিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রবেশ করেন পশ্চিমবঙ্গে।
এই পাসপোর্টই কালে-কালে দুই বঙ্গের বিচ্ছেদ ও গমনাগমনে বাধার ক্ষেত্রে ‘আইকনিক’ হয়ে ওঠে। অনাদিকাল ধরে যে যাতায়াত ছিল সহজ, দেশ-বিভাজনে তাতে জড়িয়ে দেয় নিয়মের শিকল। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার পাশাপাশি, কবিতাতেও প্রতিফলিত হয় সেই বাধা ও তজ্জনিত প্রতিক্রিয়া। কবিতায় প্রথমদিকের উল্লেখগুলি দেশভাগের প্রত্যক্ষ আঘাতজনিত হলেও, পরবর্তীতে প্রাধান্য পেয়েছে দুই বাংলার বিচ্ছেদ ও ঐক্যের সুরই।
যেমন অন্নদাশঙ্কর রায়, তাঁর ‘এপার থেকে ওপার বহু দূর’ কবিতায় সরাসরি তুলে ধরেছেন যাওয়ার বাধা— ‘প্রদেশ একদা ছিল, আজ পরদেশ/ পাসপোর্ট, ভিসা বিনে নাইকো প্রবেশ।’ যে পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) এককালে অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের অংশ ছিল, দেশভাগের ফলে তা ‘পরদেশ’, সেই ব্যথাই জড়িয়ে কবিতাটির সর্বাঙ্গে। আবার, বেণু দত্তরায় ‘মা ভাগ হয় না’ শীর্ষক কবিতায় লেখেন— ‘পাসপোর্ট ও ভিসার বাইরে দাঁড়িয়ে আছি/ আমার চোখে কোনো জল নেই/ মাটি ভাগ হয় মা ভাগ হয় না’। বস্তুত, পাসপোর্ট-ভিসার জটিলতাকে অস্বীকার করতে চাইছেন তিনি মনে-মনে। যে-জন্মভূমি ‘মা’, কোনো কাঁটাতার বা নিয়মের বিধিনিষেধ তাকে সন্তানের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না।
পাসপোর্ট যে এক অর্থে বাঁধনের চিহ্ন, বিশেষত যদি প্রসঙ্গ হয় ফেলে-আসা দেশের, তা বুঝিয়ে দেন কমলেশ পাল, তাঁর ‘চেকপোস্ট’ কবিতায়। ‘নিজের মোকামে যেতে মানুষের পাসপোর্ট লাগে/ পাখির লাগে না’— লেখেন তিনি। বাধাহীনভাবে যাতায়াতের প্রতীক হিসেবে পাখিকে ঈর্ষা করেছেন বহু কবিই, ব্যতিক্রম নন কমলেশও। একই কথা ধ্বনিত হয় অরণি বসুর কবিতা ‘বর্ডার’-এ— ‘পাখির কোনো পাসপোর্ট লাগে না।/ শুকনো পাতা সেও অনায়াসে পার হয়ে যেতে পারে—/ শুধু মানুষকেই সীমান্ত মেনে চলতে হয়।’
অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর ‘পাসপোর্টবিহীন বাংলাদেশ’ কবিতায় যে-বাংলাদেশ কাঁটাতার-পূর্ব, আবহমানকালের, তাতে বিচরণের স্বপ্ন দ্যাখেন— ‘যে দিকে তাকাই, শুধু বাংলাদেশ।/ এ-আত্মীয়তায় আমি পাসপোর্টবিহীন হাঁটি/ পুরনো পল্টনে’। এ-কবিতা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে লেখা, যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে উদ্বেল হয়েছিলেন এপার বাংলার অজস্র কবি। তবে সার্বিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের কবিদের (বিশেষত যাঁদের শিকড় ওপার বাংলায়) কবিতায় স্বাধীন যাতায়াতের বাধা হিসেবে পাসপোর্ট-ভিসার উল্লেখই সর্বাধিক। যেমন পার্থ বসু ‘বিবাহ প্রস্তাব’ শীর্ষক কবিতায় লেখেন— ‘এপারে হিঙ্গলগঞ্জ ওপারে বসন্তপুর তবু যাওয়া আসা/ নদীর ইচ্ছায় নয় যেতে চাই ভিসা ও পাসপোর্ট।’ ‘শরণার্থী’ কবিতায় সজল দে তুলে ধরেন সব-হারানো নথিহীন মানুষের জবানি— ‘সীমানা পেরিয়ে ঢুকেছি যেন তস্কর/ ভীত খুব, আমার কোনও পাসপোর্ট-ভিসা নেই।’
দেখা যাচ্ছে, পাসপোর্টের সঙ্গে ভিসাও সমানতালে উচ্চারিত হচ্ছে বেশিরভাগ কবিতায়। বস্তুত, ভারত-পাকিস্তান পাসপোর্ট-ব্যবস্থা চালু হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই ভিসাও চালু হয়। আগে শুধুমাত্র সীমান্তে পাসপোর্ট দেখিয়েই যাতায়াত করা যেত, এবার আগাম অনুমতি নিতে হবে ভিসা অফিসে গিয়ে। এই বর্ণনাই ফুটে উঠেছিল পঞ্চাশের দশকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘ভিসা অফিসের সামনে’ কবিতায়, যেখানে ‘দুটি মানুষ দুই পথে চলে গেল/ যতক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়/ ওরা অপেক্ষা করেছিল।’ কবিরুল ইসলামের ‘মোহাম্মদ মতিউল্লাহ প্রিয়বরেষু’ কবিতায় বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে-আসা এক বন্ধুর সুবাদে ফিরে দেখা দুই বাংলার বিচ্ছেদ— ‘এতো কাছে, তবু এতো দূর—/ পাশপোর্ট ও ভিসা আপিসের জটিল জঙ্গলে ঘুরে/ আমাদের পরস্পর পরিচয়পত্র তাই লটকে আছে নো-ম্যান্স-ল্যাণ্ডের/ শিশু গাছে।’
শুভেন্দু পাল তাঁর ‘বর্ডার’ কবিতায় ফেলে-আসা দেশে মা-বাবার ফিরে যাওয়ার কল্পনা করেন— ‘রাস্তা চেনা নেই, ভিসা নেই/ পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে কবে/ তবু দুপায়ে জড়িয়ে নিয়ে কৌতূহলী ধুলো/ তারা আজো চুপিচুপি বর্ডার পেরোল।’ এই যে ফেরার আর্তি, তা দেশভাগ-সংক্রান্ত কবিতার অন্যতম উপজীব্য। সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পাসপোর্ট’ শীর্ষক কবিতায় ফুটে ওঠে সমকালীন বাংলাদেশ ভ্রমণের স্মৃতি, যেখানে পাসপোর্ট-অস্বীকার হয়ে ওঠে মিলনের বার্তাবাহী— ‘ভাষা দিয়ে পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলা যায়।’
দেশভাগ-কেন্দ্রিক গানের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। তার ওপর, সেইসব গানে পাসপোর্টের উল্লেখ বিরল। একটিমাত্র গান চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, যেটিতে উল্লেখ আছে পাসপোর্টের (পাশফুট)। পরিচয়ে সেটি লোকসঙ্গীত (অষ্টক), গীতিকার দুলাল চক্রবর্তী। তিনি লেখেন— ‘স্বাধীনতার পাশফুট হয় চুয়ান্ন সনে।/ হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানে যাওয়া যায় না পাশফুট বিনে,/ ওরে পাশফুট হয়ে মনের শান্তি নাই।।’ পাসপোর্ট ছাড়া দু-দেশে যাতায়াতের বাধার কথাই প্রতিফলিত হয়েছে এই গানে। চুয়ান্ন সন অর্থাৎ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে (১৯৪৭ খ্রি.) দেশ স্বাধীন হয়, সে যেন খোদ স্বাধীনতারই পাসপোর্ট প্রাপ্তি— পরাধীনতা থেকে মুক্তির দিকে আগমন। অথচ সদ্য ভাগ-হওয়া দুই দেশ হিন্দুস্তান আর পাকিস্তানে পাসপোর্ট ছাড়া যাতায়াতের উপায় নেই; এতদিনের আদানপ্রদান আটকে গেল এক লহমায়, ফলে এমন নিয়ম আখেরে অশান্তিই নিয়ে এল। সহজ কথাটি সহজভাবে বলে দেওয়ায় জুড়ি নেই এ-গানের।
পশ্চিমবঙ্গের কবিদের লেখা দেশভাগের কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে বিভিন্ন মোটিফ উঠে আসে, যেগুলির মাধ্যমে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্তারে ব্যাখ্যা সম্ভব। ‘কাঁটাতার’, ‘বর্ডার’, ‘উদ্বাস্তু’, ‘বাস্তুহারা’, ‘ভিটে’, ‘দেশের বাড়ি’, ‘শিকড়’ ইত্যাদি এই-বিষয়ক কবিতায় বহুব্যবহৃত। এছাড়া নদীর নাম, জেলার নাম ইত্যাদি তো আছেই! পাসপোর্ট ও ভিসা তেমনই দুই মোটিফ। বিশ্বনাগরিকত্বের দর্শন-অনুসারে পাসপোর্ট-ভিসার অসারত্বের তত্ত্ব অচর্চিত নয়। তবে তার থেকেও ব্যঞ্জনাবাহী হয়ে ওঠে দু-বাংলার মধ্যে পাসপোর্ট-ভিসাহীন যাতায়াতের দাবি, যা ধ্বনিত হয় মাঝেমধ্যেই। ভাষা, সংস্কৃতি ও আরও অজস্র মৌলিক বৈশিষ্ট্যের যে-মিল, তাতে কাঁটাতারের দু-পারের বাঙালিরই উত্তরাধিকার। ৭৭ বছরের বিভাজন উপড়ে ফেলতে পারে না হাজার হাজার বছরের যৌথতার ইতিহাস। ফলে যাতায়াতের এই ‘পরাধীনতা’-ও যে প্রবলভাবে বাস্তব, পাসপোর্ট-ভিসার সূত্রে একপ্রকার বুঝিয়েই দিয়েছেন কবিরা।
আর, অনথিভুক্ত থেকে গেল যে-সমস্ত মানুষের স্মৃতি, বেদনা ও অভিমান, এ-কথা তাঁদের একাংশেরও কি নয়?
জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।