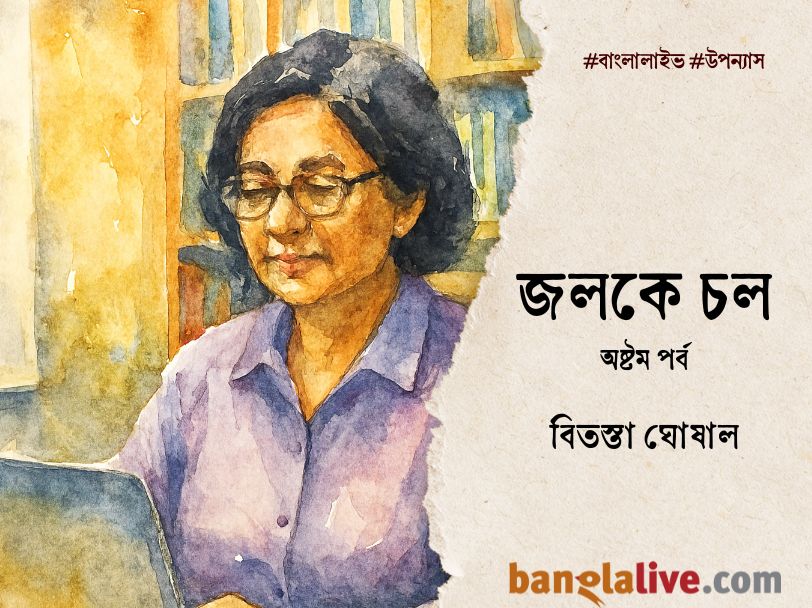“ওখানে কে রে?“
মাঠের উপর জমে থাকা ঘন কুয়াশার পর্দা ভেদ করে কথাগুলো এল উত্তর দিক থেকে । ঐ দিকে বয়েজ স্কুলের দক্ষিণের সীমানা বরাবর এক বেমক্কা, বিশাল পাঁচিল। নিকষ কালো অন্ধকার জমে আছে সেখানে। এখন ভোর সোয়া পাঁচটা। গরমকাল হলে এখানে এতক্ষণে ফুটবলে লাথি পড়ে যেত। পাস, ড্রিবল, শট – হই হই, চিৎকার। ফ্রি কিক না ফাউল তা নিয়ে হুলুস্থুল বেঁধে যেত। কিন্তু মধ্য জানুয়ারির এই ঠান্ডায় এখন ঘুমিয়ে আছে পাড়া। ভোর রাতের এই নীল অন্ধকারে শুধু জেগে আছে মাঠের এ ধারে ও ধারে জনাকয়েক ছেলেপুলে আর চঞ্চলদা। আর এই প্রশ্নবাহী চিৎকার যে চঞ্চলদার, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। (Old Games)
গরমকাল হলে এখানে এতক্ষণে ফুটবলে লাথি পড়ে যেত। পাস, ড্রিবল, শট – হই হই, চিৎকার।
চঞ্চলদা মানুষটা রোগাসোগা বেঁটে খাটো হলে কী হবে পায়ে বল পেলে বাঘের বাচ্চা! আর শুধু ফুটবল কেন, আমাদের সেই দক্ষিণ শহরতলির অখ্যাত ক্লাবের ক্রিকেট থেকে ক্যারাম, টেবল টেনিস থেকে হাডুডু – সব খেলাতেই চঞ্চলদার উপস্থিতি। সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যা – যে কোনও সময়ে তাকে পাওয়া যাবে। বয়সীদের ব্রিজ অথবা দাবা খেলার পার্টনার এদিক ওদিক হলেই খোঁজ পড়ত “আরে চঞ্চল কই?” কোনও এক সরকারি অফিসের খাতায় নাম থাকলেও – ক্লাব আর মাঠই ছিল চঞ্চলদার যাকে বলে প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি! এমনও নাকি হয়েছে অফিস যাওয়ার পথে ক্রিকেট টিমের ওপেনারের পেট খারাপ হওয়ার খবর শুনে চঞ্চলদা অফিস কামাই করে ব্যাট ধরেছে। আর এ তো আমার নিজের চোখে দেখা – পাঁচদিন মাঠে যাইনি বলে একদিন গভীর রাতে, চঞ্চলদা মুরারি ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। “কাল থেকে যাব” এই বলে সে যাত্রা পার পেয়েছিলাম।

আশি নব্বইয়ের দশক জুড়ে আমাদের সেই শহরতলির অতিব সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনে খেলাধুলা নিয়ে যে ধরণের মাতামাতি ছিল তাতে এই ধরণের একজন মানুষের উপস্থিতিকে কোনও অভিভাবক কোনওদিন খারাপ চোখে দেখেননি। বরং সে ছিল তাঁদের ভরসার জায়গা। চঞ্চলের চেলা হলে অন্তত ছেলে গোল্লায় যাবে না এ বিশ্বাস তাঁদের ছিল। আসলে এই চঞ্চলদারা আস্তে আস্তে হারিয়ে গেছে আমাদের জীবন থেকে। তার সঙ্গে হারিয়ে যেতে বসেছে খেলা বা খেলার অভ্যাস যা হয়তো কোনও এক সময়ে জড়িয়ে ছিল আমাদের জীবনযাত্রার পরতে পরতে।
শৈশবের নানা ধাপ বেয়ে আমাদের বেড়ে ওঠা। দোলনায় শুয়ে হাত পা ছুঁড়ে আমরা জানান দিই সতেজ প্রাণের অস্তিত্ব। রঙ বেরঙের ঝুমঝুমি বাঁধা দোলনা শিশুর প্রথম খেলাঘর।
আরও পড়ুন: চলচ্ছবির প্রতিবেশীরা
মনের অপরিপক্কতা যেমন আবিষ্কার করতে শেখায় জীবনকে, তেমনই খোঁজ দেয় এক কল্পজগতের ঠিকানার; এই দু’য়ের মাঝে সেতুবন্ধন করে নানা ধরণের খেলা বা ক্রীড়া। আমাদের ছোটবেলা জুড়ে এরকম নানা ধরণের খেলা ছিল যা এক হিসেবে শিশুমনের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়। এসবের জন্য দামি সরঞ্জামেরও খুব একটা প্রয়োজন ছিল না। নিতান্তই আটপৌরে পরিবেশে ঘণ্টা কয়েক সময় কাটানোর জন্য এই সব খেলার জুড়ি মেলা ভার। লুকোচুরি, চোর –পুলিশ, কুমিরডাঙা, রাজা সেনাপতি, পিট্টু, ডাংগুলি, এক্কাদোক্কা (বা কিৎ কিৎ), কানামাছি, রুমাল চোর, কবাডি (নামভেদে হাডুডু বা দাড়িয়াবান্ধা) এরকম কত রকমের বৈচিত্র্যময়তায় ঘেরা ছিল ছোটোদের জগত। ঘুড়ি, মার্বেল, লাট্টু (লাটিম), ইও ইও – ছুটির অলস দুপুর জুড়ে এদের যাতায়াত নেহাৎ কম নয়। খেলা আমাদের শারীরিক এবং মানসিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, খেলার সম্ভাব্য হারজিতের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বাচ্চার মানসিক প্রতিক্রিয়া ও প্রস্তুতি তৈরি হয় – খেলায় দক্ষতা লাভ করে সে। কর্ম এবং পরিণতির একটি ধারণা স্থাপন করে নেয় সে মনের মাঝে।
কানামাছি, রুমাল চোর, কবাডি (নামভেদে হাডুডু বা দাড়িয়াবান্ধা) এরকম কত রকমের বৈচিত্র্যময়তায় ঘেরা ছিল ছোটোদের জগত।
খেলার মাধ্যমে আমরা এক পরিপূর্ণ “ব্যক্তি” হয়ে উঠতে শুরু করি। এখানেই ক্রীড়া বিনোদনের স্বার্থকতা।
কমবয়সী ছেলেপুলেদের মধ্যে অলস অবসর যাপনের সঙ্গী হিসেবে আরও কিছু দেশজ খেলা প্রচলিত ছিল, যেমন “ইকির মিকির”, “রস কষ সিঙ্গারা বুলবুলি” অথবা “রাজা-চোর-মন্ত্রী-সেপাই”। এ সব খেলা ঘিরে ভাঙনকীর্ণ একান্নবর্তী পরিবারের অন্দরমহলে তখনও শোনা যেত সমস্বরে কচি কলতান। স্কুলের গণ্ডির মাঝে আউটডোর গেমস হিসেবে ক্রিকেট, ফুটবল বাদ দিলে ক্লাসরুম কেন্দ্রিক কিছু খেলা জমে উঠেছিল। এর মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয় ছিল “বুক ক্রিকেট”, “ম্যাপ পয়েন্টিং”, “ব্যাটেলশিপ”, “ডটস অ্যান্ড বক্স” এবং “টিক–ট্যাক-টো” বা নিছক “কাটাকুটি খেলা”। এছাড়াও ছিল ক্রিকেটের কিছু সরলীকৃত সংস্করণ যেমন “ফ্রেঞ্চ ক্রিকেট” অথবা “ওয়ান টিপ ওয়ান হ্যান্ড” (One-tip-one-hand)! একঘেয়েমি কাটানোর জন্য বাজি রেখে টেবিল টেনিসের ব্যাটে পিং পং বলের বাউন্স করানোর মধ্যে যে উত্তেজনা তা এক কথায় অনন্য।
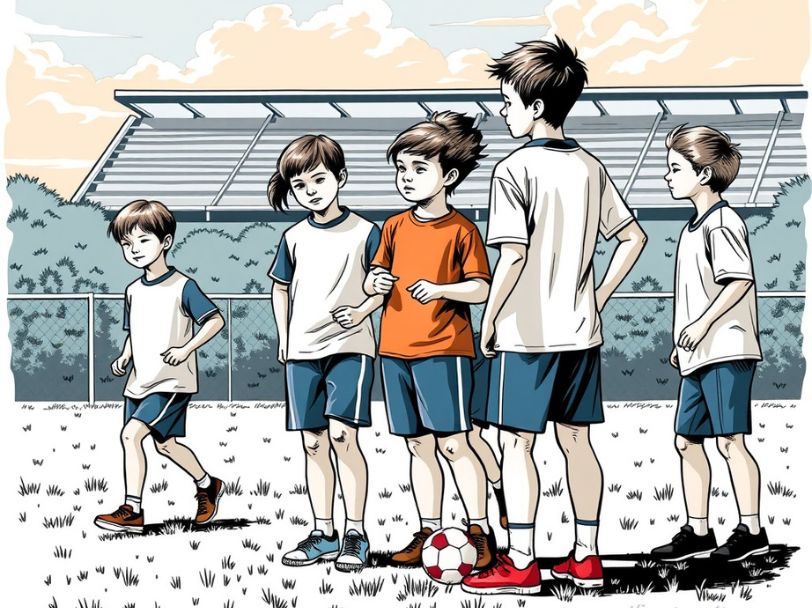
আরেকটু সময়কাল পেরিয়ে আসি। সর্বজনীনভাবে সম্মিলিত বিনোদন ছিল “অন্তক্ষরি” এবং “কুইজ”! এই দুটি খেলা গণ মাধ্যমের কল্যাণে ছড়িয়ে যায় একটা সময়ে। “অন্তক্ষরি”–র উল্লেখ নাকি আছে রামায়ণের পাতায়। সে ছিল ঋষি মুনিদের ব্যাপার – এ দিকে তার প্রচার প্রসারের দায় দায়িত্ব পুরোটাই কাঁধে নিয়েছিল বলিউড! আর “কুইজ” মনে করিয়ে দেবে সত্তর আশির দশকে রবিবাসরীয় রেডিও অনুষ্ঠানের কথা – হামিদ ও আমিন সায়নির অননুকরণীয় কণ্ঠ ও পরিবেশন!
তাসের প্যাকেটেও হাত পড়েছিল সে বয়েসে। প্রথম জীবনে “রংমিলান্তি” এবং খানিক বয়সকালে “ফিস” অথবা “পেসেন্স” (যাকে আমরা এখন সলিটায়ার হিসেবে জানি)। তবে এসব কিছু ছাপিয়ে ছিল ক্যারাম বোর্ড ঘিরে এক আসক্তিপূর্ণ বিনোদন।
আর ছিল নানা ধরণের বোর্ড গেম বা ফলক ক্রীড়া যা আসলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, দুই সভ্যতার মিশেলের প্রতিভূস্বরূপ। লুডো (যার একটি বিশাল ডিজিটাল পুনরুজ্জীবন হয়েছে আজকাল), দাবা, চাইনিস চেকার, বাগাটেলি, মনোপলি ইত্যাদি ঘরোয়া খেলার মধ্যে ডুবে থাকত আমাদের মন – অলস সময় অতিবাহন এবং বিনোদনের যৌথ প্রয়াসে। তাসের প্যাকেটেও হাত পড়েছিল সে বয়েসে। প্রথম জীবনে “রংমিলান্তি” এবং খানিক বয়সকালে “ফিস” অথবা “পেসেন্স” (যাকে আমরা এখন সলিটায়ার হিসেবে জানি)। তবে এসব কিছু ছাপিয়ে ছিল ক্যারাম বোর্ড ঘিরে এক আসক্তিপূর্ণ বিনোদন। ক্লাবঘরের এক পাশে সিলিং থেকে ঝোলানো হলদে আলোর নীচে তার মায়াময় উপস্থিতি। লাল ঘুঁটিকে কেন্দ্র করে সাদা কালোর ব্যূহ রচনা। আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা খেলোয়াড়দের মুখ দেখা যায় না; তাদের আঙুল খেলা করে দৃশ্যমান বোর্ডের উপরে। আমাদের চঞ্চলদার মতো কেউ একজন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ায়, ফিসফিসিয়ে বলে “ডানদিক থেকে ঐ সাদা দুটোকে টিপ কর- জোরে মার রেড টাকে কভার করে”!
“জীবন গিয়েছে চ’লে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার”।

খেলার সঙ্গে ধূলার সম্পর্কে লেগেছে বিভেদ। জয়ের উল্লাস – হারের অবসাদ, নেই দু’য়ের বহিঃপ্রকাশ।
শৈশবের খেলা আজ মাঠের পরিবর্তে উঠে এসেছে স্মার্টফোন অথবা কম্পিউটারের পর্দায়। খেলার সঙ্গে ধূলার সম্পর্কে লেগেছে বিভেদ। জয়ের উল্লাস – হারের অবসাদ, নেই দু’য়ের বহিঃপ্রকাশ। সবই যেন আজ অন্তর্লীন হয়েছে মনের গভীরে। ডিজিটাল গেমের আধিক্য ও আবেদনে এই দুনিয়ার শিশুদের শৈশবের এপিটাফ লেখা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শারীরিক তো বটেই, মানসিক উন্নয়নের জন্য খেলা গুরুত্বপূর্ণ। জীবনের চলার পথে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একজন মানুষের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিৎ তার শিক্ষা দেয় খেলা, কল্পনা প্রকাশের একটি ক্যানভাস প্রদান করে। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা জানান দেয় “For the very young, it helps in the development of motor skills, of being able to navigate one’s environment, by providing them with an unstructured set of activities.”
ডিজিটাল গেমের আধিক্য ও আবেদনে এই দুনিয়ার শিশুদের শৈশবের এপিটাফ লেখা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শারীরিক তো বটেই, মানসিক উন্নয়নের জন্য খেলা গুরুত্বপূর্ণ।
আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের সেতু গড়ে খেলোয়াড়ি মন। জীবন যে শুধু নিয়ম আর প্রোটকলের চৌহুদ্দি আর সরলরেখায় বাঁধা নয় – “ব্যতিক্রম”ও যে সেই নিয়মের অংশ – এটাই বোঝার।
কিন্তু ফোন বা কম্পিউটারের পর্দায় আটকে থেকে আসলে হারিয়ে যাচ্ছে এই প্রজন্মের শৈশব! পারিপার্শ্বিক ভুলে আমরা বুঁদ হয়ে আছি ফোনের পর্দায়। মানসিক তৎপরতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বৃদ্ধি করার দাবী আংশিকভাবে স্বীকার্য হলেও algorithem এর ছাঁচে ঢালা ভিডিও গেমস, অজান্তে তৈরি করছে এক বিচ্ছিন্নতার অনুভূতি। টেলিভিশন থেকে ওটিটি – অনলাইন ক্লাস থেকে অনলাইন বাজার কম বেশি সবকিছুই বাড়াচ্ছে এই বিচ্ছিন্নতা সমাজ এবং প্রকৃতি থেকে – যার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হয় না।
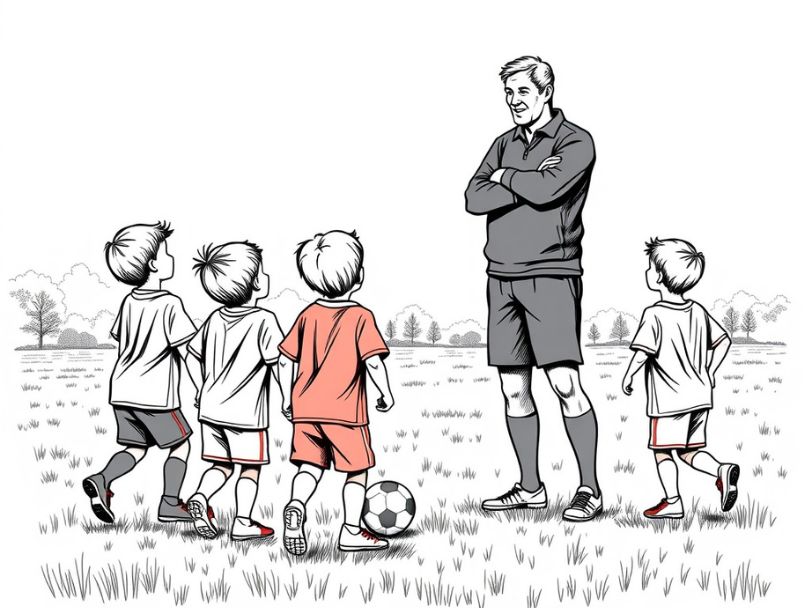
খেলা এবং কাজের ধর্ম আসলে পরস্পরবিরোধী। উভয়ের সঙ্গেই যদিও কিছু শারীরিক এবং মানসিক কার্যকলাপ জড়িত – প্রকৃতিগত ভাবে তারা ভিন্ন। কাজের ক্ষেত্রে আমাদের মেনে নিতে হয় নিয়মের অধীনতা – ত্যাগ করতে হয় সুখানুভবতার আয়েশ। পক্ষান্তরে খেলা বা ক্রীড়ার হাত ধরে ওড়ে ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার কেতন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, জীবন ও জীবিকা কেন্দ্রিক কর্মব্যস্ততার কারণে, অবকাশ আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠে আমাদের কাছে। খেলার আনন্দ হারিয়ে যেতে বসে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমাদের একবার চোখ পড়ে খোলা জানালার বাইরে। উপায় আর উপশম খুঁজি মানসিক স্বস্তির সবুজ প্রান্তরের প্রান্তে। ভেতরের শিশুটা হাত পা ছুঁড়তে থাকে। মনে পড়ে সেই পুরনো গুরুবচন, “all work and no play makes Jack a dull boy, all play and no work makes Jack a mere toy!”
কুয়াশা ভরা গাঢ় নীল অন্ধকারে কোথা থেকে চঞ্চলদার গলার স্বর ভেসে আসে “ওখানে কে রে! – টেন ল্যাপ কুইক – ওয়ান, টু, থ্রি…”।
অলংকরণ- আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।