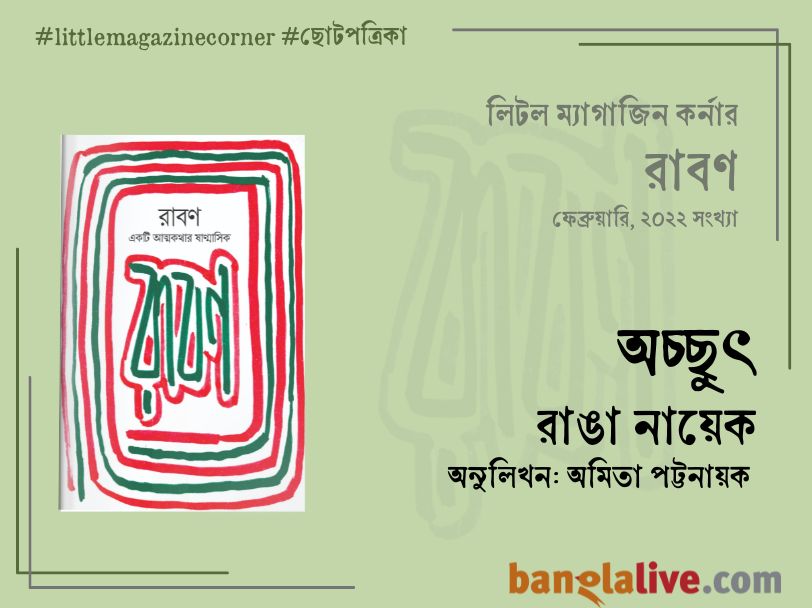১৯৮২-র শীতে শ্বশুরবাড়িতে আসার পর ভোরবেলা ঘুম ভাঙত সুইপারদের রাস্তা ঝাঁটানোর খবর আওয়াজ আর টাইমকলের জল তোলার বালতির চড় চড় শব্দে। তার সাথে কানে আসত ঠেলাগাড়ির গড়গড় আওয়াজ। জানালা দিয়ে দেখতাম ঢাকনা দেওয়া চকচকে অ্যালুমিনিয়ামের বড়ো বড়ো দুটো করে ক্যান হাত ঠেলায় বসিয়ে ঠেলতে ঠেলতে কয়েকজন নারী-পুরুষ (নারী বেশি পুরুষ কম) চলছে রাস্তার পুবদিক থেকে পশ্চিমদিকে। (Little Magazine)
শহরের খাটা পায়খানাগুলোর কাঁচা গু নিয়ে গুইয়াবাড়ি (ট্রেঞ্চে) ফেলতে যাচ্ছে। ভাগ্যিস শ্বশুরবাড়ির কাউকে দুধের কথাটা বলিনি। হাসির খোরাক হতাম। অফিসিয়ালি এদের পরিচয় হরিজন’ হলেও শহরবাসীর কাছে পরিচয় মেঘর-মেথরানি। হাতে ‘অ্যুৎ। শহরের নোংরা আবর্জনা নর্দমা, রাস্তা, খাটা পারখানার কাঁচা ও পরিষ্কার করে। তখনও শহরতলির মানুষজনদের ঢল আসেনি শহরে থাকার জন্য। শহরে লোকজন কম। পরিবার ভিত্তিক শহর। আলাদা করে বিভিন্ন মানুষকে চলনে বলনে পোশাকে তাদের কম সহজে চেনা যেত। মেথরদের চেহার পোশাক কথাবার্তা অন্যরকম। পুরুষেরা বেশ স্বাস্থ্যবান, ঘনকালো তেল চুকচুকে চুল। জাপান খেয়ে ঠোঁটগুলো টুকটুকে লাল। পরনে লুঙ্গি বা গামছা। গায়ে সাদা স্যান্ডো গেঞ্জি। প্রায় সময় নেশায় বুদ, চোখ রাঙা। রেগে গেলে বুনো মোষ। সহজে লোকে ওদের ঘাঁটায় না। ওরা রাগলে শহর পরিষ্কার রাখবে কে? মেয়েদের গোড়ালির উপর উঁচু করে পরা শাড়ি। আঁচলটা কোমরে টাইট করে জড়ানো। মাথায় চুড়ো খোঁপা।
গালের একপাশে গোঁজা সুগন্ধি পান। কাজের সময় সবার কোমরে শাড়ির উপর গামছা ঘুরিয়ে জড়ানো। যাতে শাড়িতে ময়লা না লাগে। ওরাও ওদের মেজাজ নিয়ে চলে। চলায় বাস্ততা নেই। অকারণে চঞ্চলতা নেই। নিজেদের মধ্যেই থাকে। মাতৃভাষা ওড়িয়ায় কটর-মটর কথা বলে। ছেলেমেয়েরা কেউ স্কুলে যায় না। দরকারও নেই। না পড়েই ওরা চাকরি পায়। শহরের দুটো হরিজনপল্লিতে থাকে। যাকে ওরা নিজেদের গেরাম (গ্রাম) বলে পরিচয় দেয়। শহরবাসীর কাছে মেঘরপাড়া। পল্লি মিউনিসিপ্যালিটির অফিস, মদ-তাড়ির দোকান আর সিনেমাহল— এই ওদের দুনিয়া।
সে সময় তমলুক শহরের সারাবছরের বিনোদন বলতে বর্ষাকালে রাখাল মেমোরিয়াল ফুটবল গ্রাউন্ডে ফুটবল খেলা, দুর্গাপূজা, পৌষে রারুনিমেলা, শীতে টিকিট কেটে যাত্রা থিয়েটার, মাঝে মাঝে সার্কাস, চৈত্র মাসে চড়ক মেলা আর দুটো সিনেমাহলের চারখানা শো। এরমধ্যে শহরবাসীর একটা উপরি পাওনা ছিল মঙ্গল সংক্রান্তিতে মেথরদের মঙ্গলচণ্ডীর ঘট-ডোবানোর নজরকাড়া শোভাযাত্রা। সোমবারের একটু গভীর রাতে দূর থেকে ভেসে আসত চাঙ্গুর (ঢাক) মিষ্টি শব্দ। রাতের ভাতঘুম ভেঙে রাস্তার দু-পাশের বাড়িগুলোর দরজা খুলে লোকেরা বারান্দায় ছাদে দাঁড়ায় মেথরদের শোভাযাত্রা আসছে দেখবে। এদের অনেক বউ-ঝি দেখতে বেশ সুশ্রী। শ্যামলা রঙের মুখের গড়ন ভারি সুন্দর। চোখ টেনে রাখে। মাথাভর্তি কোঁকড়ানো একঢাল চুল। শোভাযাত্রার দিন পল্লির সমস্ত বউ-ঝিদের পরনে নতুন লালপাড় সাদা খোলের শাড়ি কুঁচি দিয়ে পরা। টান টান করে বাঁধা বিরাট খোঁপায় গোঁজা ফুল। নাকে কানে ভারী ভারী সোনার গয়না। গলায় ভারী রূপার হার। হাতে শাঁখা- পলার সাথে গোছা গোছা লাল চুড়ি। মাথায় লম্বাগলা মাটির ঘটে লম্বা লম্বা ঝাঁটাকাঠিতে গাঁথা কাঠকক্ষে ফুলের ঝাড়। কিছু মেয়েদের হাতে থালায় সাজানো জ্বলন্ত প্রদীপ। কোনো হই-চই নেই। চুপচাপ শান্তভাবে লাইন করে সামনে বাজন্ম বাজিয়ে হ্যাজাক লাইটের আলোয় শহরের এক রাস্তা দিয়ে রূপনারায়ণের খাঁড়িতে ঘট ডুবিয়ে আর এক রাস্তা দিয়ে ফেরে। এরকম সুন্দর শান্ত নজরকাড়া শোভাযাত্রা অনেকদিন পর্যন্ত আর কেউ করত না। এখন যে কোনো সার্বজনীন অনুষ্ঠানে ওদের মতো করে মেয়েরা মাথায় ফুলের ঘট, হাতে প্রদীপের থালা সাজিয়ে চমকদার শোভাযাত্রা বের করে। তবে ওদের নিজস্বতাটাই আলাদা।
দিন বদলেছে। হরিজনদেরও আমূল পরিবর্তন। আগের সেই অচ্ছুৎ মানুষজন প্রায় কেউ নেই বললেই চলে। দু-একজন মহিলা আছে। এদের একজন রাঙাদি। বয়স প্রায় চুরানব্বই বছর। শক্ত সমর্থ চেহারায় বয়স কাবু করতে পারেনি। এখনও ওদের একটা পল্লির মোড়ল, বিকাল হলে কপালে তিলক কেটে রাস্তার ধারে নিজের দোতলা বাড়ির রোয়াকে বসে মালা জপে আর গাড়ি-ঘোড়া পথের মানুষজন দেখে। কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবেনি মাথার উপরে বাবুদের বাড়ির মতো পাকা ছাদ হবে। বন্ধ করে পাখা ঘুরবে। ঘরে বসে টিভিতে সিনেমা দেখবে। মাস গেলে ঘরে বসে কড়কড়ে নোটের পেনশন পাবে। ঘরের মধ্যে স্যানিটারি পায়খানা-বাথরুম হবে। যে পায়খানার কাঁচা গু পরিষ্কার করতে করতে পূর্বপুরুষদের সারা জীবন আর নিজের জীবনের অর্ধেক কেটেছে। মাঝে মাঝে স্মৃতিতে ভেসে ওঠে সেই দিনগুলো।
ছিলাম অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ জাত। চলতে হত বাবুদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। এখন আর নেই জাত-অজাতের ভেদাভেদ। নেই ছোঁয়া-ছুঁয়ি। আমাদের অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ ছোটো জাতের ছেলেমেয়েরা বাবুদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সাথে বড়ো বড়ো স্কুলে পড়বে, একসাথে খেলবে, ভালো ভালো জামাকাপড় পরবে, বড়ো বড়ো চাকরি করবে, বাবুদের সাথে এক টেবিলে বসে খাবে— এ আমাদের কাছে স্বপ্ন।
বাপের কাছে গল্প শুনেছিলাম— আমাদের আদিবাড়ি ছিল উড়িষ্যার বহরমপুরের গজ্ঞামগ্রামে। কবে যে ঠাকুরদা, তার বাপ ঠাকুরদা তমলুক শহরে এসেছিল কেউ জানে না। তখন আমাদের মাত্র দু-ঘর বসতি। পরে পাঁচ-ঘর হয়। সব রাস্তার ধারে ঝুপড়ি বানিয়ে থাকত। ধীরে ধীরে শহর বাড়ে। বাড়িঘর লোকজন বাড়ে। মেথর কম পড়ায় মেদিনীপুর, উলুবেড়িয়া, কলকাতার মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জাতভাইয়েরা এল। তমলুক মিউনিসিপ্যালিটি আনায়, তাদের ছেলে-মেয়ে নাতি-পুতি বাড়তে বাড়তে এখন অনেক।
স্বাধীনতার আগের কথা। বাবাকে এক ডাকে শহরের সবাই চিনত। নাম কন্তু ভাঙ্গারী। আমরা চারবোন পাঁচভাই। বাবা-মা মিউনিসিপ্যালিটির খাটাপায়খানার গু পরিষ্কার করত। পরে দাদা-দিদিরাও করত। উঁচু উঁচু খাটটাপায়খানা গুলোর তলায় বসান থাকত মাটির গামলা। সারাদিনের বাবুদের বাড়ির লোকেদের পেচ্ছাব-মল ওই গামলায় জমা হত।
পায়খানার পিছনে থাকত মেথরদের যাওয়া আসার আলাদা রাস্তা। খুব ভোরবেলা সেই রাস্তা দিয়ে গিয়ে গামলা থেকে মল টিনে ভরে মাথায় চাপিয়ে নিয়ে শশ্মানের কাছে ফেলতে হত। এক একদিন ভিতরে কেউ পায়খানায় বসেছে আর নীচে গামলা নেওয়ার জন্য যেই মাথা ঢুকিয়ে হাত বাড়িয়েছে, আর অমনি ওপর থেকে কাঁচা গু এসে পড়ত হাতে মাথায়। অনেক সময় গামলা ভর্তি গু-জল তুলতে গিয়ে গামলা যেত হড়কে। মাটির গামলা ভেঙে, জলে চারিদিক ভাসত। বাবুরা দেখার আগে তাড়াতাড়ি করে তাকে দু-হাত দিয়ে আঁজলা করে তুলে টিনে ভরে নিত। বাবুরা দেখলে নাকে কাপড় চাপা দিয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিত। মিউনিসিপ্যালিটিতে জানাত— ‘মেথররা রাস্তায় গু ফেলতে ফেলতে যায়।’ চেয়ারম্যান বলত— ‘তোরা টিনে একটু কম করে ভরতে পারিস না। সারা গায়ে গু মেখে রাস্তায় ছড়াতে ছড়াতে যাস।’ মেথররা বিনয়ের সাথে বলত— বাবু,
ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না।’
মেথররা গু ঘাঁটার কাজ করলে কী হবে মাইনে সবাই খুব ভালো পেত। নগদ টাকার লোভে নোংরা কাজকে নোংরা মনে করত না। বাবা তিনটাকা মাইনে পেত। স্বাধীনতার আগে তখনকার বাজারে ওই টাকাটা অনেক। অনেক বাবুদের বাড়িতে মাসে নগদ তিনটাকা আয় ছিল না। পরে বাবা গু পরিষ্কারের কাজ ছেড়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করত। সমস্ত জঞ্জাল নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটির মহিষের গাড়িতে চাপিয়ে খালে ফেলত। জোয়ারের জলে সব জঞ্জাল ভেসে যেত। তখন খালের উপর ষোলোফুকার (লকগেট) হয়নি। রূপনারায়ণের জোয়ারের জল ঢুকে শহরের অনেক রাস্তাঘাট ডুবিয়ে দিত। পরে বাবা জমাদার হল। মাইনে বাড়ল। তখন গোরুর গাড়ি মহিষের গাড়ি মালপত্র বইত। বাবার উপর দায়িত্ব ছিল ওই গাড়িগুলো দেখার। রাস্তা দিয়ে গাড়ি গেলেই বাবা হেঁকে বলত— ‘অ্যাই, তোদের লাইসেন্স আছে তো?’ কোনো কোনো গাড়ি বলত — ‘না, দাদা নেই। তুমি একটু পার করে দাও। তোমাকে খেতে (তাড়ি) দেব।’ বাবা খুব তাড়ি খেত। মেথররা সবাই তাড়ি খেত। তাড়ির লোভে বাবা গাড়িগুলো ছেড়ে দিত। তাছাড়া উপরি নগদত্ত ছিল। গাড়োয়ানেরা গাড়ি মহিষ নিয়ে থাকত শালগেছিয়ায়। ওরা সব আমাদের জাতভাই। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে, পরে মহিষের গাড়ি, গোরুর গাড়ি উঠে গেল। ওখানেই মিউনিসিপ্যালিটি জাতভাইদের থাকার ব্যবস্থা করে দিল। চাকরির ব্যবস্থা করে দিল। ওটা হল আমাদের দ্বিতীয় গেরাম।
শহর বাড়ল। মেথর-সুইপার বাড়ল। বাবা হল এদের জমাদার। বাবাকে দেখতুম মাসের শেষে অফিসের বারান্দায় ভাগ ভাগ করে টাকা সাজিয়ে বসতে। দশ-বিশ-তিরিশ। যার যেমন বেতন। সুইপারদের বেতনও বেশ ভালো। যে যার গিয়ে টাকা নিত। বাবারও তখন অনেক বেতন। চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকার মতন। আমাদের এত বড়ো সংসারে ওই টাকা বেশি হয়ে যেত। মাইনে ছাড়া ছিল সরকারি ডোল। অভাব ছিল না। অভাব ছিল মনের। ছোটোবেলা থেকে দেখতুম ভদ্দরলোকেরা আমাদের ঘৃণা করত। আমরা গু ঘাঁটার কাজ করতুমতো, আমাদের দেখলে নাকে কাপড় চাপা দিত। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলত। যেন আমাদের গায়ে সব সময় গু মাখা। যদি কারোর গায়ে ছুঁয়ে ফেলতুম গালি-গালাজ দিয়ে স্নান করে ঘরে ঢুকত। ছেলেবেলায় দেখতুম আমরা চায়ের দোকানে গেলে দোকানদার কোনোদিন দোকানের গ্লাসে চা দিত না। বলত— ‘অ্যাই, তোরা যে চা খাবি গেলাস আনছ? গেলাস লিয়ায় চা দেব’। আমরা ঘর থেকে বড়ো গেলাস নিয়ে দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতুম। দোকানি আমাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে উঁচু করে গেলাসে চা ঢেলে দিত। বাড়িতে নিয়ে এসে সবাই মিলে ভাগ করে খেতুম। আমাদের নগদ পয়সার অভাব নেই । মাও গু-পরিষ্কারের কাজ করে। বাবার কাছে পয়সা নিয়ে ছুটতুম দোকানের খাবার খেতে। খুব ইচ্ছে করত বাবুদের মতো দোকানের টেবিল চেয়ারে বসে প্লেটে খাবার নিয়ে চামচে করে খাই। চেয়ারে বসে প্লেটে খাব কী, কোনোদিন দোকানি তার দোকানে ঢুকতে দিত না। বলত— ‘অ্যাই, তোরা সব বাইরে দাঁড়া। খাবার দিচ্ছি।’ বাইরে দাঁড়িয়ে জামা, গামছা বা আঁচল পাততুম। দোকানি তাতে ঢেলে দিত। নয়তো দোকানি ঠোঙায় খাবার ভরে ঠোঙাটা বাইরে রেখে দিত। হাতে দিত না। আমরা তুলে নিতুম। পয়সা দিলে হাতে নিত না। সামনে রেখে দিতে বলত। পরে ধুয়ে তুলে রাখত। মনটা খুব খারাপ করত। বাবাকে বলতুম — ‘বাবা, আমাদের কেন দোকানে বসে খেতে দেয় না। বাইরে কেন খাবার রেখে দেয়। পয়সা দিয়ে তো কিনি।
বাবা বোঝাত— মা, আমরা অস্পৃশ্য অচ্ছুৎ ছোটোজাত, নোংরা পরিষ্কার করি তাই দেয় না। ভাবতুম, সত্যিই তো। আমরা বাবুদের কাঁচা ও হাত দিয়ে তুলে মাথায় করে নিয়ে পরিষ্কার করি। নর্দমা পরিষ্কার করি। রাস্তার জঞ্জাল আবর্জনা সাফ-সাফাই করি, তায় মূর্খ ছোটোলোক। তাইতো লোকে আমাদের ঘৃণা করে। এইজন্য আমরা আমাদের মতন থাকতুম। বাবুদের বাড়ির
ছেলেমেয়েদের সাথে মিশতুম না। ওরাও মিশত না। আমাদের লিখাপড়া নাই। সেজন্য ছোটো ছেলেরা খায় দায় আর সারাদিন লাটাই নিয়ে ঘুড়ি ওড়ায়। গুলি, ডাংগুলি খেলে। মরদেরা সকালবেলা কাজ করে তাড়ি খেয়ে পড়ে থাকে। তবে কেন জানি না বাবা সেজদাদাকে স্কুলে ভর্তি করেছিল। খড়ের ছাউনি স্কুলে দাদা পড়তে যেত। আমরা অচ্ছুৎ, তাই দাদা অন্য ছেলেদের থেকে দূরে চাটাই পেতে বসত। তখন সবাই নীচে চাটাই পেতে বসত। দাদাকে কেউ ছুঁতো না। এক দু-কেলাস (ক্লাস) পড়েছিল। পরে বাবা সুইপারের কাজে ঢুকিয়ে দেয়।
মনে পড়ে ছোটোবেলায় একবার যুদ্ধ লেগেছিল। মাতঙ্গিনী বুড়ি কোর্ট- পাড়ায় বানপুকুরের ধারে গুলি খেয়ে মরে গেল। আমরা দেখিনি। ঘরে বসে শুনেছি। মা আমাদের বেরোতে দেয়নি। ঘরে বসেই দেখছি চারদিকে কী গণ্ডগোল! লোকজন পুলিশের সে কী দৌড়াদৌড়ি! রাজবাড়ির ওইদিকে মানিকতালার রাস্তায় বন্দুক চলছিল— ঢ্যার্ ঢ্যার্ করে। বন্দুক হাতে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। ভয়ে সব ঘরে ঢুকে পড়ি। তখন আমরা ক’ঘর মাত্র। লাশঘর তখন কলেজপাড়ায়। কলেজ তখন হয়নি। ফাঁকা জায়গা সেই লাশঘর থেকে তিন-চারদিন পর যখন বুড়িকে বের করল পচে ফুলে গেছে। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। ধারে কাছে যাওয়া যাচ্ছে না। অনেক ধূপ-ধুনো দিয়ে নিয়ে গেল। সাথে বাবাকে নিয়ে গেল দাহ করার জন্য। বাবা একপেট তাড়ি খেয়ে দাহ করতে গেল। খুব গণ্ডগোল হচ্ছিল তো। ওরা এখানে অনেকদিন ছিল। তাঁবু খাটিয়ে থাকত। ওদেরকে আমরা কাঠকুটো কুড়িয়ে দিতুম রান্না করার জন্য। পরিবর্তে ওরা আমাদের অ্যাতো অ্যাতো রুটি দিত। ভয়ে নিতুম না। ওদের কাছে বন্দুক ছিল। ওরা বলত,— ‘লে বেটি, রোটি খালে। ডরো মৎ।’
উনপঞ্চাশ সালে ভয়ংকর ঝড়জল বন্যা হল। বড়োবাজারের কাঠের পোল ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বন্যার পরে পাকা পোল হয়। চারদিক জলে ভেসে গেল। হাজার হাজার মানুষ মরল। কত পচা গোরু ছাগল মানুষের মড়া ভেসে এল। চারিদিকে পচা দুর্গন্ধে টেকা দায়। তখন এই অচ্ছুৎ মেথর সুইপাররা আধপেটা খেয়ে চারদিকের নোংরা আবর্জনা সরিয়ে সব পরিষ্কার করল। তারাও আর পারছে না। কত করবে! বন্যার পর মানুষের দুর্দশার শেষ নেই। পেটে ভাত নেই । পরনে কাপড় নেই। আমরাও খেতে পেতুম না। বর্গভীমা মন্দির থেকে রিলিফের খিচুড়ি দিত। ক’টি গামলা নিয়ে ধরনা দিতুম। খিচুড়ি ভরতি গামলা মাথায় করে
নিয়ে এসে ঘরে সবাই ভাগ করে খেতুম। মনু বোস তখন চেয়ারম্যান। সুইপাররা ঝামেলা করছে। খাবার চাই। না হলে কাজ করবে না। মনু বোস বলল- আমার সুইপাররা না খেয়ে কাজ করতে পারবে না। পরাউফ (খাদ্য দপ্তর) তখন ঘাটাল ব্যাঙ্কের কাছে ছিল। ওখান থেকে চাল, ডাল, ছোলা নিয়ে আমাদের গেরামে পৌঁছে দিত। আমাদের এই গেরামের জায়গাটা রাজাদের পতিত পড়েছিল। এখানে এক যোগী থাকত। তার অনেক চ্যালা চামুণ্ডা ছিল। সন্ধেবেলা ধুনি জ্বালিয়ে সব গাঁজা-ভাং খেত। যোগী মারা যেতে খানিকটা জায়গা ধোপাপাড়া নিল। বাকি জায়গাটার মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের থাকতে দিল। বস্তি বানিয়ে থাকতুম। তার আগে আমরা টাউনস্কুলের ধারে, রাজবাড়ির পুকুরের ধারে, এদিক ওদিক রাস্তার ধারে সবাই ঝুপড়ি বানিয়ে থাকতুম। পরে সরকার থেকে ঘর করে দিল ১৯৮৭ সালে।
আমার যখন বারো-তেরো বছর বয়স তখন আমার খুব জলবসন্ত হয়। অ্যাত্তো বড়ো বড়ো। জ্যাঠাইমা, মামিমারও হয়েছিল। মা-মামা মুখে খড়ের টুকরো নিয়ে মন্দিরে ধরনা দিত। তখন তো এ অসুখের কোনো ডাক্তার-বদ্যি-ওষুধ ছিল না। মা ঘুঁটে পোড়ানো টাটকা ছাইকে পিষে জালি ন্যাকড়ায় ছাঁকত। ঘরের এক কোণে মোটা করে কলাপাতা পাতত। পাতায় গুঁড়ো ছাই বিছিয়ে তার উপরে খালি গায়ে শুইয়ে রাখত। মামিমা জেঠিমাকে ওই ভাবে রেখেছিল। গুঁড়ো ছাই বসন্তের সব রস শুষে নিয়ে ঝরে যেত। গায়ে কাপড় দিত না। রসে কাপড় জড়িয়ে যাবে। ওই করে সব ভালো হয়ে গেলুম। সেই বসন্তের দাগ এখন সারা মুখময়। তখন কলেরা হত খুব। খাবার জল বলতে বড়ো বড়ো বাঁধানো পুকুরের জল। আমাদের কখনও জলে হাত দিতে দিত না। পুলিশ পাহারায় থাকত। কলসি নিয়ে যেতুম। লোকেরা জল তুলে আমাদের কলসি ভরে দিত। আমরা ধাঙ্গড় জাত। আমাদের ছোঁয়া জল কেউ খেত না। একবার আমাদের গেরামে সতীশ সামন্ত (প্রাক্তন এম. পি) অজয় মুখার্জী (প্রাক্তন সেচমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী (প. ব.) এসে বললেন— ‘এই সুইপাররা, তোরা জল ধরে রাখবি। আমরা তোদের হাতে জল খাব।’ ওঁদের সাথে অনেক লোকজন আসতেন। হাতে পতাকা। সব বলত ‘বন্দে মাতরম্, বন্দে মাতরম্’। ওঁরা এসে আমাদের হাতে জল খেলেন। সাথে লোকেরাও আমাদের হাতে জল খেলেন।
আমাদের হাতের মেয়েদের খুব কম বয়সে কারোর বিয়ে হয়নি। সবার চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে বিয়ে দিত। এখানে আমাদের জাতের লোক কম। তাই নিজেদের জ্ঞাতি কুটুমদের সাথে বিয়ে-শাদি হত। দিদিদের কয়েকজনের
এখানে, কয়েকজনের খঙ্গাপুরে বিয়ে হয়েছে। ওরাও সব বাবুদের খাটা পায়খানার ও বইত। তবে এইসব কাজ কমে আসছিল। বেশিরভাগ বাড়িতে স্যানিটারি পায়খানা করে নিচ্ছিল। তার আগে মিউনিসিপ্যালিটিতে ডোকে ডেকে কাজ দিত। ষোলো বছর বয়সে আমার বিয়ে হল। বিয়ের আগে আমি কখনও পায়খানা পরিষ্কারের কাজ করিনি। বিয়ে হল হাওড়ার আমতায়। আমার ননদ এখানে থাকত। সে-ই সম্বন্ধ করল। বর দোজবরে। আগের বউ বাচ্চা হতে গিয়ে মরে গেছে। তার আর একটা বাচ্চা ছেলে আছে। বর আমতা ডিস্ট্রিকট বোর্ডের সুইপার। ওখানে সরকারি ঘরে আমাদের তিনজনের সংসার। সংসারে অভাব অনটন কিচ্ছু ছিল না। তবে মানুষটা বড্ড বেশি নেশাভাং করত। অন্য কোনো কাজকর্ম নাই। লিখাপড়া নাই। নাই পেটে বিদ্যাবুদ্ধি। হাতে নগদ পয়সা। ভালোমন্দ খাবার, মাছ, মাংস, মদ ছাড়া মুখে রোচে না। বারণ করলে বলে- ‘আমি আমার রোজগারের পয়সায় খাই। তোর কোনো অভাব রেখেছি। যখন তোর কোনো অভাব রাখব তখন বলবি।’
তবে মানুষটা খারাপ ছিল না। আমাকে খুব ভালোবাসত। বিয়ে করে নিয়ে যাওয়ার পর আমাকে বলে— ‘সারাদিন ঘরে বসে বসে কী করবি? লিখাপড়া কর। লিখাপড়া না করলে ভদ্দরলোকেদের সাথে মিশতে পারবি না। শুনে আমি তো লজ্জায় মরি। বাপের জনমে শুনিনি আমাদের জাতের মেয়েরা কখনও লিখাপড়া করেছে। ছেলেরা দু-চারজন দু-এক কেলাস পড়েছে। আমি বিরকে মানা করি। বর শোনে না। আমার জন্য এক খিস্টান দিদিমণি ঠিক করল। দিদিমণি রোজ বাড়িতে পড়াতে আসত। আমি পড়তুম। ওই বয়সে কী লেখাপড়া হয়। আমাদের রক্তে লিখাপড়া নাই। তাও অনেক কষ্টে পড়লুম। তিনবছর পড়ার পর দিদিমণি বলল— ‘কী রকম লিখাপড়া শিখেছ বাবা-মা কে চিঠি লিখ।’ চিঠি লিখলুম। বাবা-মা তো চিঠি পেয়ে অবাক। কার চিঠি ? নিজেরা তো পড়তে জানে না। সেজদাদা পড়ে শোনায়। শুনে বাবা-মা খুশিতে পাগল। মাটিতে যেন পা পড়ে না। গেরামের সকলকে ডেকে ডেকে চিঠি দেখায় আর বলে— ‘আমাদের রাঙা বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতো লিখাপড়া শিখেছে। অচ্ছুৎ ধাঙ্গড় জাতের মেয়ে লিখাপড়া শিখে চিঠি লিখেছে।’ গেরামের সবাই অবাক হয়ে সে চিঠি দেখে। তারা নিজেদের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। মা বলে— ‘জামাই আমাদের কত ভালোমানুষ। কত উঁচু মন। মেয়ে এই বয়সে লিখাপড়া শিখিয়েছে।’
১৩৫
সব ভালো চলছিল। অতিরিক্ত নেশাভাং করার জন্য বর অসুখে মারা গেল। খুব কান্নাকাটি করলুম। খুব দুঃখ হয়েছিল। আমি ওখানে রাজরানির মতো ছিলুম। বর মরে যেতে আমরা একা। সতীনের ছেলেটাকে তার মামারবাড়ি থেকে নিয়ে গেল। আমাকে আমার বাবা মা ভাই গিয়ে নিয়ে এল। বাপের বাড়িতে থাকি। আমার তখন খুব দুঃখ। দিদিরা সব শ্বশুরবাড়িতে। মা মিউনিসিপ্যালিটিতে কাজ করছে। মা বলল— ‘দুঃখ করিসনি। তুই আমার কাছে থাক। আমি মরে যাওয়ার আগে তোকে আমার কাজটা দিয়ে যাব। দাদারা আমার আবার বিয়ে দিতে চায়। আমি না করলুম। একটা বিয়ে করে সুখী হতে পারলুম না। অকালে বিধবা হলুম। আবার বিয়ে করে কি সুখী হতে পারব? চোখের সামনে দেখেছি নেশাভাং করে কীভাবে দিনের পর দিন মানুষটা পড়ে থাকত। নেশা করে করে জীবনটা শেষ করে দিল। আবার একজনকে বিয়ে করলে সে যে নেশাভাং করবে না কে বলতে পারে? শেষে মায়ের সাথে কাজে বেরুলুম। মা টিনে গু ভরে দিত। মাথায় করে সবার সাথে ট্রেঞ্চে নিয়ে যেতুম। ট্রেঞ্চে ফেলার পর কংগ্রেস অফিসের রাস্তার ধারে বাঁধানো পুকুরে সবাই স্নান করতুম। ওই পুকুরের পাশেই শিশুরক্ষা ছিল। অনেক গরিব ছেলেরা ওখানে থেকে লিখাপড়া করত। পুকুরে স্নান করে কাপড় ছেড়ে মেয়েরা বাড়ি যেতুম। পুকুর থেকে একটু এগিয়ে শিশুরক্ষা ছাড়িয়ে গেলে বাঁ- হাতি অশ্বথ-তলায় মিউনিসিপ্যালিটির তাড়ি দোকান। মরদেরা তাড়ি দোকানে ঢুকত। লম্বা গলা হাঁড়িতে এক হাঁড়ি তাড়ি নিয়ে একটা করে গ্লাস নিয়ে গোল হয়ে ঘিরে বসত। হাঁড়ি থেকে তাড়ি ঢেলে ঢেলে খেত।
কয়েকদিন কাজ করার পর কী মন খারাপ করত। শুধু কান্না পেত। যাই হোক একটু লিখাপড়া শিখেছি। খুব অপমান বোধ হত। ইচ্ছে করত অন্যরকম কাজ করতে। আগে পরিবারের লোকের এই কাজ করা দেখে ভাবতুম এটাই আমাদের কাজ। লিখাপড়া শিখার পর বাবাকে বললুম— ‘এ গু ঘাঁটার কাজ করতে পারব না। তোমরাও কোরো না। এই কাজ আমরা করি বলে ভদ্দরলোকেরা আমাদের ঘৃণা করে। ওরা বোঝে না ওরা ভালো থাকবে, ওদের বাড়ি ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে বলে আমরা এই কাজ করি। আমরা ও পরিস্কার না করলে ওরা ওই গু-এর মধ্যে পড়ে থাকবে।’ শুনে বাবা বলত- “মা, আর কী কাজ করব? বাপ ঠাকুরদাকে দেখে এসেছি এই কাজ করতে। অন্য কাজ শিখিনি। লিখাপড়া জানি নি। এ কাজ না করলে খাব কী?
সংসার চলবে কীসে? এতে পয়সা আছে। সরকারি ডোল আছে। কাপড়জামা আছে। ঘরবাড়ি আছে। চাকরি আছে। সরকারি কত সুবিধা আছে?’ মা-ও বোঝাল, — আমরা মরে গেলে তোকে কে দেখবে? তোর কীসে চলবে? সবাই এ কাজ করছে। তোকেও করতে হবে।’ কী করি! মনের দুঃখ মনে চেপে কাজে লেগে গেলুম। খুব ভোরে রাস্তা দিয়ে টিন ভর্তি গু মাথায় করে নিয়ে যেতুম। রাগে দুঃখে অপমানে কান্না পেত। মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করত। এই জন্যেই লোকে আমাদের ঘৃণা করে। আমাদের ছোঁয় না। আমাদের ছোঁয়া কোনো জিনিস খায় না। আরো খারাপ লাগত যখন লোকে দেখে হাসত। ঘৃণায় মানুষ হয়েও লোকে মানুষ ভাবে না। ভালো মানুষদের সাথে মিশতে পারতুম না। ঘৃণায় দূরে সরে যেত… গন্ধে নাকে মুখে কাপড় চাপা দিত। বাচ্চারা টিটকারি দিয়ে বলত, ‘মেথরানি গু বয়।’ তখন রাগে গালাগালি দিতুম। মনে মনে যে, কী কষ্ট হত সে বলার নয়। । এটাই সবচেয়ে দুঃখের। তেষ্টা পেলে কারোর বাড়িতে জল চাইলে গেলাসে জল দিত না। গেটের বাইরে কিংবা উঠানে ‘দাঁড়িয়ে হাত পাততুম। বাড়ির কেউ উঁচু করে হাতে জল ঢেলে দিত। আমাদেরও এই ভাবে খাওয়াটা অভ্যাস হয়ে গেছিল। আসলে আমরা দশবাড়ির গু ঘাঁটতুম তো সেজন্য ভদ্দরলোকেরা ভাবত আমাদের ছুঁয়ে দিলে ওদের গায়ে গু লেগে যাবে। ওনারা কোনোদিন ভাবেনি ওনাদের ভালো থাকার জন্য তো আমাদের পায়খানা, নর্দমা পরিস্কার করতে হয়। অনেক বাবুদের বাড়ির প্রাইভেট পায়খানা নর্দমা পরিস্কার করতে হত। তার জন্য আলাদা পয়সা দিত। সেইসব বাবুদের বাড়ির বিয়ে-শাদী অন্নপ্রাশন পূজাপার্বনে আমাদের নিমন্ত্রণ করত। দল বেঁধে যেতুম। তবে বলত— ‘তোরা সব বাইরে দাঁড়া।’ দাঁড়িয়ে থাকতুম। সকলের খাওয়ার শেষে ওখানেই আমাদের খেতে দিত। খেতুম, আবার বাড়ির জন্য বেঁধে আনতুম। তখন টেবিল-চেয়ারে খাওয়ার চল হয়নি। নীচে বসে বাবুরা সবাই লাইন করে খেত। আমরাও লজ্জা পেতুম বাবুদের সাথে এক লাইনে বসে খেতে।
বাবা নেশাভাং করে অসুখে মরে গেল। মা-ও মরে গেল। ভাইদের কাছে রইলুম। মায়ের চাকরিটা আমি পেলুম। ভালো মাইনে। ষাট টাকা। চল্লিশ টাকা সংসারে খরচ করতুম। কুড়ি টাকা বেঁচে যেত। পূজার সময় নতুন শাড়ি, জামা পরে ঠাকুর দেখতে যেতুম। দূর থেকে সব দেখতুম। (মণ্ডপের কাছে যেতুম না। সিনেমাহলে গিয়ে খুব সিনেমা দেখতুম।) বেশি যেতুম রূপশ্রী হলে, চেয়ারে কেউ বসতুম না। সামনে চটপাতা থাকত। চটের টিকিট কেটে সব পা ছড়িয়ে বসে পড়তুম। তিনআনা টিকিট। হাফ-টাইমের সময় মুড়ি, কাঁচালঙ্কা, আলুরচপ, বেগুনি কিনে সব হলে বসে খেতুম। আমি রাজেন্দ্রকুমার বৈজয়ন্তীমালার সিনেমা দেখেছি। দেবানন্দের সিনেমা দেখেছি। তখন কী যে ভালো লাগত কী বলব! বয়সটাতো কম ছিল। কিন্তু কাজে সুখ পেতুম না। একটু লিখাপড়া শিখেছি। কাজ করি। মন মানে না। একদিন সবাইকে নিয়ে চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন করলুম— ‘বাবু, টিনে আর গু বইতে পারব না। গায়ে মাথায় পড়ে। লোকে দেখে হাসে। আমাদের ঘৃণা করে। তাছাড়া আমরাও তো মানুষ। কত আর বাবুদের কাঁচা গু–পেচ্ছাপ গায়ে মাথায় মাখি।’ চেয়ারম্যান অভয় দিলেন কিছু একটা করবে। অনেকদিন পর গু বওয়ার জন্য ‘বারো’এল।অ্যালুমিনিয়ামের ঢাকনা দেওয়া ক্যান। তার সাথে ঠেলাগাড়ি। একটু স্বস্তি পেলুম। ক্যানে ভরে ঠেলাগাড়ি করে ট্রেঞ্চে ফেলতুম। কয়েকবছর পর খাটাপায়খানা উঠে গেল। বাড়ি বাড়ি স্যানিটারি পায়খানা হল। তখন থেকে কাঁচা গু ঘাঁটার কাজের অবসান হল।আমাদের সবাই স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, মিউনিসিপ্যালিটিতে সুইপারের কাজ পেল।
পার্টি করতুম। সতীশ সামন্ত, রজনী প্রামানিক, অজয় মুখার্জীর পার্টি। পরে বিশ্বনাথ মুখার্জী, গীতা মুখার্জীর পার্টি। অজয়বাবু জিতে গিয়ে গদ্দারি করল। আমাদের দেখল না। কথা দিয়ে কথা রাখল না। সেই রাগে ওই পার্টিতে (সি পি আই) চলে গেলুম। সবাই গেল না। এ পার্টি গরিবের পার্টি, ছোটোলোকদের পার্টি। ঝান্ডা কাঁধে নিয়ে মিছিলে সব যেতুম। পাঞ্জাব গিয়েছিলুম সম্মেলনে বিশ্বনাথবাবু, অরুনাবলি (অরুনা আসফ আলি) এসেছিল। গীতা মুখার্জীর সাথে। সম্মেলনে অনেক মেয়েরা এসেছিল। আমাকে মাইক দিল তমলুকের হরিজনদের অবস্থার কথা বলতে। আমি বাংলায় বললুম— ‘ওখানে আমাদের সবাই ঘৃণা করে। আমাদের হাতে জল খায় না। আমাদের কাছে বসায় না। অথচ আমরা ওদের পায়খানা, ড্রেন, রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে সাফ করি।’ আমার কথাগুলো একজন হিন্দিতে বলে দিল। খুব হাততালি পড়েছিল। সেই সব কথা মনে হলে আজও মনে মনে খুব আনন্দ হয়। আমার সাথে কত বড়ো বড়ো লোকের পরিচয় হয়েছিল। যখন কংগ্রেস করতুম, সে সময় তমলুকে ইন্দিরা গান্ধী আসবেন। চেয়ারম্যান আমাকে ডেকে বলল— ‘রাঙা, প্রধানমন্ত্রী আসবেন। তোদের উৎসবে যেমন মাথায় ঘট ফুল সাজিয়ে প্রসেশান্ বের করিস, প্রধানমন্ত্রী এলে সেই রকম প্রসেশান্ বের করবি। হরিজনদের প্রসেশান্ দেখে ইন্দিরা গান্ধী খুব খুশি। চেয়ারম্যান আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে ইন্দিরা গান্ধী আমার হাতে হাত মেলালেন। কী ফর্সা সুন্দর দেখতে! আমার তো খুব আনন্দ হল। আমার মতো অদ্ভুতের হাতে হাত মেলালেন। আমাকে বললেন— ‘সুইপাররা খুব ভালো করেছে। তোমার নাম কী ?” ‘রাঙা নায়েক।’ শুনে— ‘ও গুড় গুড়’ বলল। উনি হিন্দিতে বলছিলেন। একজন আমাকে বাংলায় বলে দিচ্ছিলেন। রাজীব গান্ধী (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) আসতে রাজবাড়ির মাঠে মিটিং হল। তার আগে মিউনিসিপ্যালিটিতে ছোট্ট মিটিং হল। আমার সাথে হিন্দিতে কথা বললেন— “মা, তুমি কাজ করছ ভালো, কাজ করো। কংগ্রেস যেন জিততে পারে।’
একটু লিখাপড়া জানার সুবাদে আমি মিউনিসিপ্যালিটির বাবুদের সাথে বেশি মিশি। কথা বলি। পার্টি করতুম তো। আমার খুব তেজ ছিল। সুইপারদের দাবি-দাওয়া মাইনে বাড়ানোর জন্য কোমরে কাপড় জড়িয়ে চেয়ারম্যানের টেবিল চাপড়ে কথা বলতুম। আমাকে ভয় পেত সব। বলত— ‘এ কী মেয়েরে বাবা! চেয়ারম্যানের টেবিল চাপড়ে কথা বলে।’ বলত— ‘রাঙা, তুই সুইপারদের বোঝা।’ আমি বোঝাতুম। কী করলে ভালো হবে। এমনিতে ওরা খুব গোঁয়ার। রেগে গেলে বুনো মোষ। হুঁশ-জ্ঞান থাকে না। তবে সুইপাররা আমাকে খুব মান্য করে। গেরামের মোড়ল মানে। আমার কথা অমান্য করে না। গেরামের মরদগুলো যখন তাড়িমদ খেয়ে মারামারি করত তখন আমি কোমরে শাড়ির আঁচল জড়িয়ে লাঠি নিয়ে মেরে ওদের ছাড়াতুম। আমাকে ভয় করত সব। ছাড়িয়ে দিলে চুপচাপ সব চলে যেত। এখনও মারামারি করে। তবে আমি বুড়ো হয়েছি। বয়স হয়েছে। ছাড়াতে গেলে বলে— “পিসি, তুমি আমাদের মধ্যে আসবে না। সরে যাও।’ কী আর করি। সরে যাই। বুড়ো হয়েছি। কোথায় লেগে যাবে। ডাক্তার হাসপাতাল করতে হবে।
তবে এখন বুঝি, আগে অচ্ছুৎ অশুচি ছিলুম অনেক ভালো ছিলুম। ঘৃণার কাজ করতুম বটে, চাকরির কোনো চিন্তা ছিল না। ডেকে ডেকে চাকরি দিত। ঘর, ডোল, কাপড় পেতুম। লিখাপড়া নাই। সেজন্য লিখাপড়ার কোনো খরচ ছিল না। অনেক ভদ্রলোকদের চেয়ে আমরা ভালো ছিলুম। অফিসের কর্মচারীদের চেয়ে আমাদের বেতন বেশি ছিল। বেশি বেতনও আমাদের কাল ছিল। শস্তাগন্ডার বাজার। প্রায় সময় তো আমরা খাসির মাংস, ভাত খেতুম।
শুয়োর মাংস খেতুম। শাক-সবজি কেউ খেত না। মরদেরা তাড়িমদের সাথে মাংসের চাঁট খেয়ে বুড়ো হওয়ার অনেক আগেই সব অকালে মরে গেল। কমবয়সি ভাইপোগুলোও তাড়িমদ খেয়ে মরল। আমি সরকারি ঘর ছেড়ে দোতলা বাড়ি করেছি। সেখানে এক ভাইয়ের নাতির সাথে থাকি। এখন ছেলেমেয়েরা আগের মতো চাকরি পাচ্ছে না। কী করে পাবে? বাবুদের বাড়ির পাশকরা ছেলেরা সুইপারের কাজ করছে আমাদের ছেলে-মেয়েদের পেট মেরে। দুশো পনেরো টাকা যখন মাইনে তখন রিটায়ার করি। এখন মাইনের চেয়ে পেনশন বেশি পাই। প্রতিদিন সন্ধেবেলা মহাপ্রভু মন্দিরে যাই। সবার সাথে বসি। আরতি দেখি। ঠাকুরনাম করি। সবাই আমাকে ভালোবাসে। ‘রাঙাদি’ বলে ডাকে। এটাই তো চাই।
রাঙা নায়েক হরিজন: জন্ম— পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক শহরে। বয়স প্রায় চুরানব্বই। প্রথমে তমলুক মিউনিসিপ্যালিটিতে খাটা পায়খানা পরিষ্কারের কাজ করতেন। পরে করতেন সুইপারের কাজ।
অমিতা পট্টনায়ক: ১৯৬০ সালের পয়লা জুন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ডায়মন্ড হারবার শহরে মামার বাড়িতে জন্ম অমিতা পট্টনায়কের। পৈতৃক নিবাস ওই জেলারই নামখানা থানার দেবনগর গ্রাম। ১৯৮২ সালে বিবাহ। বর্তমানে মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা।
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।