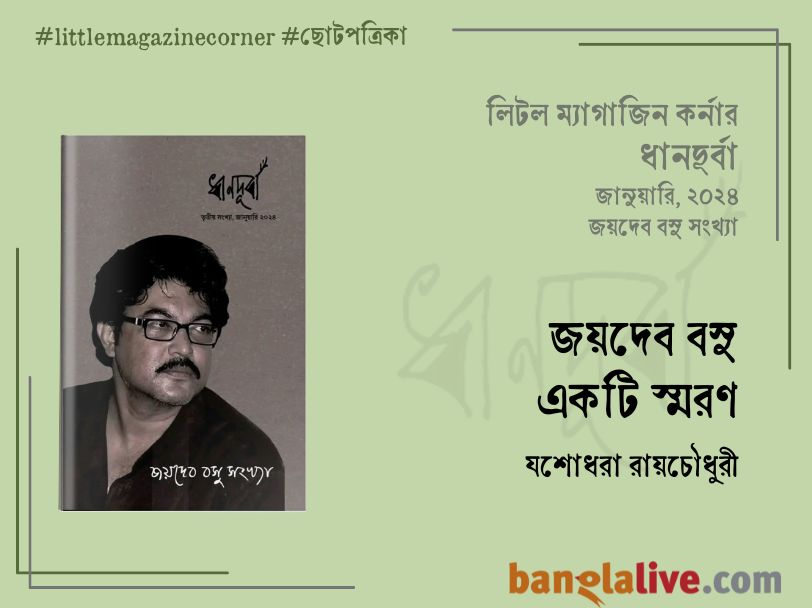পঞ্চাশের কবিতা নিয়ে কোন লেখা যদি তৈরি করতে হয়, সে লেখার শীর্ষ হতেই পারে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের তৈরি শব্দগুচ্ছঃ সত্যবদ্ধ অভিমান। আটের দশকের কবিতা কি আছে সেরকম কোন কয়নেজ? এই দশক নিয়ে কি সেই প্রত্যয় নিয়ে লেখা চলে, এ দশক, জনগণতান্ত্রিক কবিতার ইশতেহার? জয়দেব বসুর লাইনটি আজো শিরোধার্য রাখার। (Little Magazine)
আটের দশক কবিতায় সত্তরের প্রচ্ছায়ায় থাকেন নি। সত্তরের গর্জন, সত্তরের অসহায়তা ও উচ্ছ্বাস, অনাশ্রয়, নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চিতির পাশাপাশি আত্মউন্মোচনের প্রত্যয়, সত্তরের ধ্বংসাত্মক নির্মাণশীলতার পরবর্তী এই দশকটি।
এভাবেও ভাবা যায় যে এই দশকে, প্রতিমুহূর্তের বেঁচে থাকা থেকে অন্তর্হিত হচ্ছে অস্বস্তিকর প্রশ্ন, নিরাপত্তাহীনতা অথবা সে-অর্থে শহরবাসী কবিরা অন্ততঃ স্পৃষ্ট হচ্ছেন না কোন বিশাল পরিবর্তনের ঢেউয়ে। নকশাল আন্দোলনের শেষ হয়ে যাওয়া একটা নস্টালজিয়া দিচ্ছে, স্মৃতিকাতরতার উষ্ণতা থাকলেও ধার নেই। আছে নতুন কিছু গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট সমস্যাহীন পরিবেশ। বাম আদলে ভাবনা ভেবে হৃদয় শুকায় জেনে কাজ করে যাওয়া। (Little Magazine)
এই সময়, জয়দেব বসুর মত কয়েকজন ঘোষিত রাজনৈতিক কবিকে বাদ দিলে, বাকিদের উদবুদ্ধ করছে অ-রাজনৈতিক কবিতাই। ব্যক্তিজীবনে প্রত্যেকেই রাজনৈতিকভাবে সচেতন, কিন্তু সচেতনে ল্যাংগুয়েজ থেকে মেটাল্যাংগুয়েজের দিকে হেঁটে গেছেন তাঁরা। তাঁরা সামগ্রিকভাবে দেখলে আত্মস্থ ঢের বেশি, একইসঙ্গে লেখালেখিতে সংহত। (Little Magazine)
জয়দেব বসুকেও একমাত্র ‘রাজনৈতিক কবি’র সংজ্ঞায় স্থিত করে, আঁটিয়ে দিতে চাওয়া আদ্যন্ত ভুল। কারণ ভাষার দিক থেকে অত্যন্ত সংযত, একপ্রকার কবিতানিমগ্নতার জন্ম যে দশকে, জয়দেব সেই দশকের অন্যতম। আশির কবিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বিক্ষুব্ধ নন তাঁরা, জীবনযাপন তাঁদের কাছে আশ্রয়হীন নয়। এঁরা অধিকাংশ শহরবাসী, এবং শিক্ষিত। প্রায়শই উচ্চশিক্ষিত। (Little Magazine)
এঁদের কবিতায় র্যাবোকথিত ‘আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়ানোর’ প্রয়াস আমরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারি। শব্দের নিজস্ব গ্রন্থনে এঁরা সকলেই বুঁদ, এবং এই শব্দ আসছে এঁদের পুরাবাহিত দীর্ঘ এক শব্দ অববাহিকা থেকেই। ধারাবাহিক ভাষা অনুশীলনের স্পষ্ট ছাপ প্রায় সকলের লেখাতেই অপর্যাপ্ত।
এঁরা তাৎক্ষণিক ধাক্কা, জাঁকজমক চাননি প্রায়শই। চেয়েছেন ধ্যানের বিন্দু, শান্ততা, স্থিরতা, কবিতার প্রতি নিবেদন। প্রায়শই শব্দ, ছন্দ, প্রচুর চিত্রকল্প, ভাষাশৈলীর ভেতরে ডুব দেবার জন্য বদ্ধপরিকর। জয়দেবের কবিতায় এই প্রতিটি যুগলক্ষণ বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়। (Little Magazine)
২
যাদের যখন যাবার কথা নয়, তারা তখন চলে গেলে একটা অদ্ভুত অস্বস্তিকর শূন্যতার সৃষ্টি হয়। বিশেষত জয়দেব বসুর মত কবি, যিনি ছিলেন সর্ব অর্থেই সর্বত্রগামী, নিজের প্রজন্মের মধ্যে প্রধান, নিজের মণ্ডলীর ভেতরে একটা আলাদা অভিভবের অধিকারী। উল্লেখ্য নাম, যাকে ঘিরে বিস্ময় জুগুপ্সা নানাধরণের অনুভূতি নিয়ে খেলা চলত। বিতর্ক উঠত। লেখা ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার দিক থেকে শুধু নয়, নানা ক্ষেত্রেই জয়দেব ছিলেন বিশিষ্ট অনেক অর্থে। (Little Magazine)
বিদায় নিয়েছেন অভিমানী জয়দেব, বাংলা কবিতার এই মঞ্চ, এই এরিনায় অনেক যুদ্ধ জয়ের পর। সেইসব যুদ্ধের চিহ্নসকল তাঁর কবিতাগুলি। তাঁর ক্ষুরধার শাণিত গদ্যও। অথচ, জয়দেব বসুর মৃত্যু কিন্তু আত্মহত্যা নয়, সমসময়ে প্রমোদ বসুর মত, অথবা তাপসকুমার লায়েকের মত। অসুস্থতায়, আকস্মিক হৃদযান্ত্রিক গোলযোগে চলে গেছেন অকালে জয়দেব। ৫০ বয়সে। অথচ তাঁর অনুজ তরুণ কবিরা তাঁকে ঘিরে অবিচুয়ারি কবিতা লিখেছেন এমন, যার নির্যাস, জয়দেব অভিমানে, স্বেচ্ছায় প্রস্থান করেছেন। আসলে চিরকাল এমনই ইচ্ছাময় ছিলেন, যে জয়দেব মৃত্যুর পরও নিজের ভাগ্যবিধাতা, নিজের কাহিনির নির্মাতা থেকে গেছেন অনুসারীদের চোখে। একজন মানুষের ছায়া কতটা বিস্তারিত হলে এমন হয়। অভিমানী জয়দেব, আত্মউপেক্ষাকারী জয়দেব, অগোছালো এলোমেলো একাকী জয়দেব আমাদের সকলকে অনেকটা বিষণ্ণ, অনেকটা বিপন্ন করে রেখে গেছেন। আসি তাঁর কবিতার কথায়। (Little Magazine)
আবার আসিব ফিরে, ধানসিঁড়িটির তীরে/কুয়াশা আবরিত এ বাংলায় হয়ত একাকী নয়, হয়তো আস্তিনে জড়ানো থেকে যাবে চাবুকদাগ হয়তো শহরগ্রাম প্লাবিত কল্লোলে জাগবে উতরোল এই স্বদেশ ফিরব আমিও ঠিক সুকেশী সন্ধ্যায় অথবা ভোররাতে পুনর্বার
(উত্তরমেঘ, ৭১ নং)
এই ধরণের চমৎকারী লাইনে পূর্বজ কবিদের, বা বাংলার সমস্ত কবিতাকে, আত্মীকরণ করতে করতে, অধিকার করতে করতে, জয়দেবের নিজ কবিতার মর্দানি। একইসঙ্গে পুনরাবিষ্কার ‘মেঘদূত’কে। প্রতিটি লেখায় মেধাচমক আর আবহমান কবিতার প্রতিষ্ঠানকে ভাঙচুর করতে করতে ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণ, এমন এক মাপ নিয়েই তাঁর নিজের কাব্যভাষার আত্মপ্রকাশ।
নদীপথ ধরে ঢোকো, ষোড়শ অঙ্গের দারুণ সমাহার আমার দেশ তোমাকে চেনাব সব, যেভাবে চিনে নেয় মডেলভঙ্গিমা চিত্রকর অথবা লাশের ঘরে যেমন ছাত্রেরা নিপুণ বিভাজন করে দেহের যেভাবে স্থাপন করো নিজের মনোযোগ, শ্যামল বর্ণের অলকা এই…
এভাবেই ইনি পশ্চিমবঙ্গের শবব্যবচ্ছেদ করে দেখান আমাদের। আদ্যন্ত সমাজসচেতন, বামপন্থী এই কবির সমস্ত লেখাতেই চুঁইয়ে পড়ে আত্মসচেতন এক ভাষানির্মাণ। নিজ দেশ কাল সম্বন্ধে ইতিহাস চেতনা। একইসঙ্গে এক পৌরুষ, সাহস, অ্যাটিচ্যুড। প্রেমের কবিতা হোক বা প্রতিবাদের, একই তীক্ষ্ণ শাণিত ভাষা। যে ভাষা পড়তে পড়তে পরতে পরতে খুলে আসবে শ্লেষ, ব্যঙ্গ, রাগ, তিক্ত কযায় সমসময়ের দাগ।
বরং কৌতূহলে তাকালে ডানদিকে দেখবে গঞ্জের পোয়াতি বউ আলের উপর দিয়ে হাঁটছে সাবধানে, পরনে ফ্লেশ-টিন্ট সিন্থেটিক চোখের তারায় তার হলুদ ছোপ, ক্ষীণ বুকের থেকে সব ক্যালসিয়াম নিয়েছে রেশম চাষ শোষণ করে তাই ভ্রূণের গোপনীয় আর্তনাদ
সরল ভাষা মানুষের কাছাকাছি পৌঁছয়। যে সরলভাষা অনেক অধ্যয়নে অর্জন হয়, কিন্তু ব্যবহার হয়ে মানুষের জন্য। সেই ভাষাছন্দ, যা সবার। কিন্তু কবির ক্ষেত্রে এ এক চ্যালেঞ্জও বটে। কনস্ট্রেন্ট বা আগল। যার ভেতর দিয়ে, তিনি দেখিয়ে দিতে চান, নিজের ক্ষমতা। বাধাকে সৃষ্টি করেন আরোপিতভাবে, নিজের সৃষ্টিশীলতার সীমানা চিহ্নিত করতেই। আমার কব্জির জোর আমি প্রমাণ করব এখানেই। মনে পড়বে সমসময়ের, আশির দশকের, আর এক প্রখ্যাত কবি জয়দেব বসুর কাজ, ‘মেঘদূত’। সমসময়ের নতুন ‘মেঘদূত’ এটি। পূর্ব নির্ধারিত একটি খাঁচায় বা ছাঁচে পুরে নতুন কিছু পেশ করা। নতুন ভাঙাচোরা সময়, অসুন্দর, আপাতভাবে কবিতার থেকে এতদিন দূরে থাকা, দূরে রেখে দেওয়া কিছু কথা, কিছু ভাবনা, কিছু শব্দ ব্রহ্ম।
মেঘদূতের পাঠ থেকে যে জয়দেবকে পাই, সেই জয়দেবই পূর্বজদের লেখাকে ফেলাছড়ার জিনিসের মতো করে ব্যবহার করেন। একটা কবিতার বইয়ের নাম হয় তাই, ‘জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়’। কাব্যগ্রন্থের এক পর্বভাগের নাম ‘আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি’ একটি কবিতার শেষ দুটি লাইন উৎপলকুমার বসুর এক জনপ্রিয় বহু আলোচিত লাইনের প্যারডি।
সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির কবিতায় জয়দেব নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন অনন্যতায়। অথচ প্রেমের কবিতাতেও সেই জয়দেবই মারাত্মক। সেখানে পাচ্ছি দোলায়মান ছন্দের আলোড়ন, বলছেন কোন নারীকে, ‘তোমায় দেখি, তোমার কথা ভাবি/ তোমায় মারি, তোমায় নাকছাবি/পরাই মনে মনে/হায় মেয়ে তোর রূপের গাঙে রূপ ভেসে যায় অনেক/ দূরে দূরে দূরে দূরে…/ তোমায় খাই, তোমায় খাই কুরে’
যে জৌলুস ছিল জয়দেবের হাতে, যে জৌলুস তাঁর লেখায়, তা যেন শুধু কব্জির জোর, শুধু হৃদয়ের উত্তাপই নয়, তা এক শবসাধনাও বটে। ‘উদর আঁট করে বসেছি ঠাকরুন, খাদ্য দাও কিছু আদ্যা মা/উপোসে বমি পায়, পিত্তরক্ষায় পারলে দুই মুঠো ভাত দে মা’ (লুপ্ত পূজাবিধি) এই কবিতার
সবটুকুই তুলে ধরতে ইচ্ছে করে… ‘কুলুঙ্গিতে জমা নিকষ অমা, ওমা, নিষ্কাশনে ঝরে অশ্রু’ এমন অত্যাশ্চর্য শব্দখেলায় আমরা জব্দ হতে থাকি ক্রমশ। আদি অকৃত্রিম বঙ্গঐতিহ্যে, কালী করালীর সাধনার ধারায় যে ভাষা আমরা সহজেই পেয়েছি, আত্তীকরণ করেছি তারই অমোঘ ব্যবহারকে সমসাময়িক করে তুলতে পারেন জয়দেব এভাবেই।
উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কেবলই ‘ধান্ধাবাজ এ শহরে’ জহর ছড়িয়ে দিতে তাঁর প্রবণতা গুণে গেঁথে রাখি। আত্মসমালোচনার আরকে চুবিয়ে ধরেন তিনি পাঠককে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কূটকচালির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন, অতীত ও ভবিষ্যতের সঙ্গেও এভাবেই, বলা যায়, রচনা করতে সক্ষম হন একশো পঞ্চাশ বছরের পুরনো এক মাস্টারপিস বইয়ের সমকালীন, ভারতীয় ক্রিটিক- যে বইয়ের নাম কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো। বাংলার মর্মে মিশে থাকা বামপন্থী ভাবাবেগও তাই কবিতায় আসে নানা ক্ষত, প্রশ্ন আর বিভ্রান্তি নিয়ে। লেনিন মূর্তি ভূপতিত হবার পনেরো বছর পরেও, শ্রেণীসম্পর্কের সহজ হিসেবে না আঁটা শিরদাঁড়া আর পাকস্থলীহীন মানুষের মিছিল রচনা হয় তাঁর কবিতায়। উদ্ভট অথচ বাস্তব, পরাবাস্তব যেই সব কথন। ‘আমার পুরুষকার’, ‘আমার লোকাল কমিটি’, ‘আমার পুরসভা অঞ্চল’, এজাতীয় কবিতায় আমরা পাই এক মর্মছোঁওয়া বিবমিষ। ‘এল-সি বলেছে, ঝামেলায় জড়াবেনা/ এল-সি বলেছে তোমার জন্য প্রায়ই/ সমস্যা হয় আমাদের সকলের/এল-সি বলেছে, এল-সি বলেছে তাই।’
সব মিলিয়ে এই কবির রাজনীতিবোধ হয়ত বা, এই প্রজন্মে, একমেবাদ্বিতীয়ম্। জয়দেবের হাত ধরেই যে বাংলা কবিতা সাবালক হয়ে উঠেছে, অন্তত বাংলা কবিতায় এমন লাইন লিখিত হয়েছে, ‘প্রতিটি কবিতার জন্ম, তুমি চাও বা না-চাও, হয় রাজনীতি থেকে।/প্রতিটি শিশুর জন্ম, সঙ্গমের ফলে শুধু নয়, নিবিড় নিবিড়তম রাজনীতি থেকে।’
কিন্তু রাজনীতির দিকটি অতিকথনের মত জয়দেবকে ঘিরে ছিল বলেই আমরা উপেক্ষা করে যাই ভাষা নিয়ে তাঁর অনন্য সব কাজ।
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।