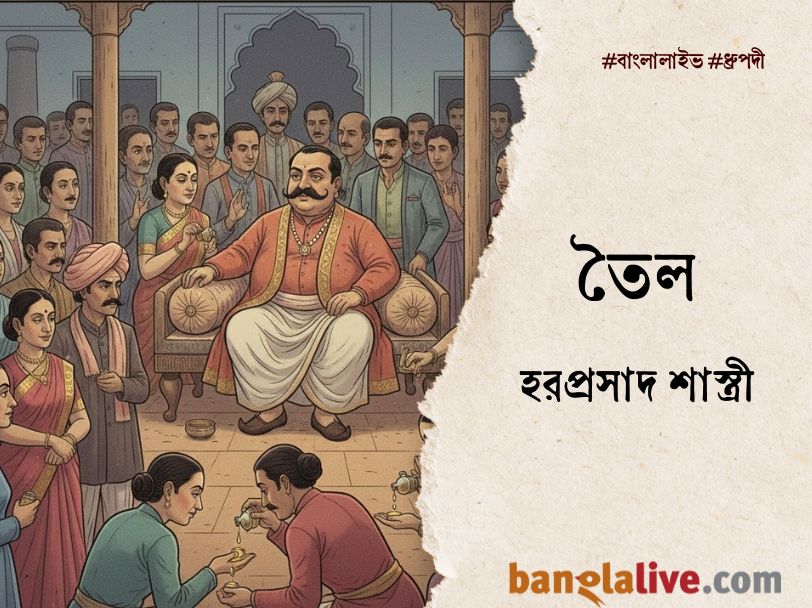(Ranna Puja)
প্রতিবছর ভাদ্রের সংক্রান্তিতে গৃহপরিচারিকাদের দুটোদিন ছুটি নেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয় তাঁদের রান্না পুজোর কথা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অধিবাসীরা অধিকাংশই যদিও ‘আন্না পুজো’ উচ্চারণ করে থাকেন। তাই রান্নাপুজো এলেই মনে মনে হেসে উঠি আর মা মনসার প্রতি প্রণতি জানাই সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠির কথা ভেবে যাদের অবিরত ভরা বর্ষায় জলে জঙ্গলে কাটাতে হয় আর তাও আমাদেরই জন্য। কৃষির স্বার্থে, মৎস্য চাষ করতে, ফসল ফলানোর লক্ষ্যে অবিচল তাঁরা। (Ranna Puja)
আসলে কৃষি যাঁদের উপজীবিকা তাঁদের এই ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসার উদ্দেশ্যে রান্নাপুজোই যেন ভরা ভাদ্রের আউস ধান তথা নানাবিধ ফসল ফলানোর কারণেই একপ্রকার ধন্যবাদ জ্ঞাপন বা থ্যাংক্সগিভিং। শুধু ধান আর ফসলই নয় দক্ষিণবঙ্গের মৎস্যচাষের ভরভরন্ত ফলন তো সর্বজনবিদিত, আর তাই রান্নাপুজোয় মরশুমি সব মাছের ভোগ নিবেদনও আবশ্যিক। রাঢ়বঙ্গে আবার শ্রাবণ সংক্রান্তিতে হয় রান্নাপুজো। দক্ষিণবঙ্গে ভাদ্রসংক্রান্তিতে। (Ranna Puja)
এবার কেন মনসা পুজোয় এই অরন্ধনের রীতি?
শহরে সেদিন বিশ্বকর্মা পুজোর ধুম আর গ্রামে মনসাপুজোয় বাঙালির হেঁসেলে এলাহি আয়োজন রান্নাপুজোর। উত্তর কলকাতার বনেদি বাঙালিদেরও দেখছি বহুপার্বণের মধ্যে এই অরন্ধন উত্সব অন্যতম। ভাদ্র মাসের শেষ ও আশ্বিন মাসের প্রথম দিনেই পালিত হয় এই অরন্ধন পুজো। ভাদ্রে রান্না আশ্বিনে পান্না। অর্থাৎ ভাদ্রসংক্রান্তিতে রান্না করে আশ্বিনের প্রথম দিনে পান্না বা সেই বাসি পান্তা খাওয়ার রীতি। এই পান্তা বা ঠাণ্ডা খাওয়া আধুনিককালে কতটা পুষ্টিকর তা আমরা জানি। সেখানে ঋতুপরিবর্তন বা ভাদ্রের পচা গরম গিয়ে আশ্বিনের হাওয়া গায়ে মাখলেই শরীর খারাপ হওয়ার প্রবণতা হয় তাই বুঝি আগাম সুরক্ষা কবচ স্বাস্থ্যকর পান্তা খেয়ে ও সবাইকে খাইয়ে। মনসার সঙ্গে এর একাধিক সংযোগ। ((Ranna Puja)

একসময় মাটির উনুনে রান্না হত তাই সেই গর্ত মানে যেখানে সাপেদের বাস সেখানেই দেবী মনসা অধিষ্ঠান করেন বলে মনে করা হয়। বছরের প্রতিটি দিন এই উনুনেই রান্না তাই উনুনকে উপাসনা করতে এই পুজোর আয়োজন। মা চন্ডীর অবস্থান নাকি এই রান্নাঘরেই। তাই চন্ডীশাল বলে উনুনকে। চণ্ডী হলেন রন্ধনশালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাঁর সুদৃষ্টির ওপরেই রান্নাঘরের উৎকর্ষ নির্ভর করে। তাই অনেক অনুষ্ঠান বাড়িতে রান্নার আগে রান্নার স্থানে চন্ডীর ঘট পেতে পুজো করে নেওয়ার রেওয়াজ ছিল। (Ranna Puja)
আর শিবঘরণী চন্ডীর প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় শিবের মানসকন্যা মনসার সঙ্গে তাঁর সৎ মায়ের সেই দ্বৈরথ। মনসা লৌকিক দেবী। সমাজের মূলস্রোতে পুজো পাওয়ার জন্য মরিয়া। তাই বুঝি শিবের কন্যা রূপে প্রবেশাধিকারের চেষ্টা। কিন্তু চন্ডীর তাতে ঘোরতর আপত্তি থাকায় ঘর গেরস্থালির বাসনকোসন ছুঁড়ে অবৈধ এই কন্যাটির একটি চোখ তিনি কানা করে দেন। (Ranna Puja)
“যাদের ঘরে মনসা গাছ নেই তারা নিজের ঘরের সামনের মাটিতে এই সিজের ডাল পুঁতে সেখানেই নৈবেদ্য নিবেদন করে। আসলে নাগমাতা মনসাদেবী নিজে নাগ না হয়েও সর্পরাজ্ঞী। উর্বরতার প্রতীক।”
তবে মনসাপুজো এই প্রচলিত রান্না উত্সব পরম্পরা মেনেই। উনুন সেদিন বাস্তুর প্রতিনিধি, মনসার প্রতীকি। আর অরন্ধনে নাগের অর্ঘ্য শীতলতা। আগুনের উত্তাপ কাম্য নয়। তাই সবকিছু ঠাণ্ডা। আর মনসার যারা চ্যালাচামুন্ডা মানে সমগ্র সর্পকুলের দেহগত কারণে তাত মোটেও সয় না বরং শীতলতাই পছন্দের। (Ranna Puja)
এযাবৎ গৃহসহায়িকা ও বন্ধুদের মুখ থেকেই ঘরে বসে বসে এই রান্নাপুজো নিয়ে আমার ক্ষেত্রসমীক্ষা আজও অব্যাহত। ওদের মুখেই শোনা সিজ বা মনসা গাছের নীচেই দেবীর অধিষ্ঠানের কথা। যাদের ঘরে মনসা গাছ নেই তারা নিজের ঘরের সামনের মাটিতে এই সিজের ডাল পুঁতে সেখানেই নৈবেদ্য নিবেদন করে। আসলে নাগমাতা মনসাদেবী নিজে নাগ না হয়েও সর্পরাজ্ঞী। উর্বরতার প্রতীক। আবার বাংলায় সাপের ভয় পায় না এমন লোক বিরল। (Ranna Puja)
জলজঙ্গল অধ্যুষিত অঞ্চলে সাপের কামড়ে এযুগেও প্রচুর লোকের মৃত্যু হয়। সেই ভয় থেকেই ভক্তি হয়তো, তবে মনসা কিন্তু শুধুই সাপের দেবী নন। মূলতঃ কৌমসমাজের ‘প্রজনন শক্তির পূজা’ থেকেই মনসা-পূজার উদ্ভব আর তা থেকে তিনি এখন ‘সিজের’ (মনসা গাছের) ডালে অধিষ্ঠিতা। তিনি প্রজননের দেবী, বৃষ্টির তথা শস্যেরও দেবী কিন্তু এতসব গাছ থাকতে সিজ বা কাঁটা যুক্ত মনসা গাছের থানেই দুধ কলা সহ অরন্ধনের জন্য খাদ্য দ্রব্য উৎসর্গ করা হয় কেন? বৌদ্ধধর্মে যে বিষহরি দেবীকে জাঙ্গুলী তারা বলা হয়, তিনিই আমাদের মনসা। বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসা বিজয়ে আছে “জাগিয়া জাগুলি নাম সিজ বৃক্ষে স্থিতি”।(Ranna Puja)
“আগের দিন সূর্যাস্তের পর রান্না শুরু হয় শুদ্ধাচারে। তার আগেই বাজারহাটের জোগাড়। তারপর বটিতে কুটনো কোটা, শিলে বাটনা বাটা, রান্নাঘরের মাটির মেঝে গোবর দিয়ে নিকিয়ে উনানের কাঠকুটো জোগাড়যন্ত করে তারা।”
আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক সুপ্রাচীন। উভয়েই উর্বরতা শক্তির প্রতীক। তাই বৃক্ষ ও সাপের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আদিম ফারটিলিটি কাল্ট বা উর্বরতাবাদের সম্পর্কটি সুস্পষ্ট। কোথায় যেন বৃক্ষ উপাসক ও সর্পোপাসক মিলেমিশে একাকার। তাই মনসা বৃক্ষ আর সর্পমঙ্গলা মনসা যেন সেখানেই একাত্ম। সংস্কৃতে এই মনসা বা সিজ গাছের নাম স্নূহী যার বিষ প্রতিষেধক গুণের কথা আছে আয়ুর্বেদে। তাই বুঝি এত শ্রদ্ধাস্পদ সেই গাছ। (Ranna Puja)
তবে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে করতে হয় এই রন্ধনকার্য। বিন্দুমাত্র খামতি বা অবিশ্বাস থাকলে মনসা কুপিত হন এবং যদি রান্নাবান্নায় কোনও অসংগতি থাকে কিম্বা পরিচ্ছন্নতায় দোষত্রুটি থাকে তবে ঐ দিন মনসাদেবী সাপকে পাঠিয়ে সব খাবার বিষাক্ত করে দেন আর মনসার অভিশাপে সে বাড়িতে রান্নাপুজো বন্ধ হবে জন্মের মতো। এই পুজোর নিষ্ঠা চোখে দেখবার মতো। (Ranna Puja)

মনসাদেবীকে উত্সর্গ করে তারপর দিন সব ঠান্ডা খাবে তারা। তারা কাঁটা মনসার ঝোঁপেঝাড়ে এখনও রেখে আসে দুধের বাটি আর কলা। ঘরের উঠোনের সামনের মাটিতে একটি মনসা গাছের ডাল পুঁতে রাখার রীতি। সেখানেও নিবেদন করা হয় কিছু রান্নাপুজোর ভোগদ্রব্য। পচা গরমে, কখনও রোদ, কখনও বৃষ্টি। অগাধ বিশ্বাস নিয়ে তারা সেই ব্যঞ্জন নিবেদন করে মনসা ঠাকুরাণী আর তাঁর চ্যালা নাগনাগিনীদের… দক্ষিণবঙ্গের গ্রামের বাসিন্দা অমিতা মণ্ডল জানালেন। আগের দিন সূর্যাস্তের পর রান্না শুরু হয় শুদ্ধাচারে। তার আগেই বাজারহাটের জোগাড়। তারপর বটিতে কুটনো কোটা, শিলে বাটনা বাটা, রান্নাঘরের মাটির মেঝে গোবর দিয়ে নিকিয়ে উনানের কাঠকুটো জোগাড়যন্ত করে তারা। (Ranna Puja)
রান্না শেষ হতে হতে ভোর হয়ে যায়। তারপর মাটির উনানের ওপর আতপ চালের ভাত ভর্তি মাটির হাঁড়ি রেখে তাকে মনসার প্রিয় শাপলা ফুলের বেষ্টনী দিয়ে রাখা হয়। সেটিই তাদের আরাধ্যা মা মনসা সেদিন। থরে থরে সব ব্যাঞ্জন রাঁধাবাড়া হয় সেই রাতে। গ্রামশুদ্ধ সকলে রাঁধে আগের দিনে আর বাসি খায় পরদিনে। সংক্রান্তি এমনই এক পুণ্য তিথি। দুই মাসের সন্ধিক্ষণ। (Ranna Puja)
“এরপরেই আশ্বিনে শুরু হয় উৎসবের প্রস্তুতি। বর্ষার বিদায়ে সাপেরা তখন মনের আনন্দে ফিরে যাবে যার যার ডেরায়। শুরু হবে তাদের শীতঘুম।”
বিশ্বাসে তাদের প্রত্যেকের ঘরের নীচের বাস্তুসাপের নজরদারিতে তারা সারাবছর বেঁচেবর্তে থাকে তাই তাকে বছরের একটা দিন মনে করে পুজো করা। মা মনসা তুষ্ট হলে তবেই সাপেরা উত্পাত করবে না। গোবরছড়া দিয়ে রান্নাঘর, উঠোন নিকোনো, শুকনো করে, ধোয়ামোছা করে, ঘর রং করে ষোড়শোপচারে এই রান্নাবান্না পরিবেশের পরিচ্ছন্নতার বার্তাও দেয়।এরপরেই আশ্বিনে শুরু হয় উৎসবের প্রস্তুতি। বর্ষার বিদায়ে সাপেরা তখন মনের আনন্দে ফিরে যাবে যার যার ডেরায়। শুরু হবে তাদের শীতঘুম। (Ranna Puja)
আমার গৃহসহায়িকা অমিতা মণ্ডলের বাড়িতে মোট ২৬ রকমের পদ নিবেদনের রীতি। স্নান সেরে, নতুন শাড়ি পরে শুরু হয় ভোগ রান্না। আর সে এলাহি ভোগের পঞ্চব্যাঞ্জনের যা ফিরিস্তি দিলেন তিনি, তাতে মনে হয় সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় বুঝি কম সময়। ভোগের রকমফের হয়। কারও বেশি, কারও কম। নানাবিধ আনাজপাতি ভাজার মধ্যে সজনে শাক, নারকোল, আলু, পটল, উচ্ছে, চিচিঙে, ঝিঙে, ঢেঁড়স, বেগুন, ওল, লাউ, কচুরমুখী, কুমড়ো, চালকুমড়ো, কাঁচকলা, পেঁপে, উচ্ছে, করলা থাকবেই। ইচ্ছানুযায়ী আরও ভাজা দেয় অনেকে। কেউ নাচারে ৫ভাজা দেয়। (Ranna Puja)
ডালের মধ্যে কেবল খেসারির ডালই রান্না হয় আর তা সংরক্ষণের কারণে ডালচচ্চড়ি রূপে। পাঁচফোড়ন, শুকনো লংকা আর তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে একেবারে ডাল বসানো হয়। ডাল সেদ্ধ হয়ে গেলে জিরে-গোলমরিচ বাটা দিয়ে নেড়ে নেড়ে একদম শুকনো করে নামানো হয়। (Ranna Puja)
তরকারির মধ্যে চিংড়িমাছ দিয়ে পুঁইশাক-কুমড়ো চচ্চড়ি, ছোলা দিয়ে কচুর শাক আর মাছভাজার মধ্যে রুই, ইলিশ আর কুচোচিংড়ি… যার যেমন নিয়ম। এরপর অম্বলের মধ্যে সর্ষে, শুকনো লংকা ফোড়নে কাঁচা তেঁতুল দিয়ে চালতার টক, ইলিশ মাছ বা চিংড়ি অথবা চুনোমাছের টক। দেবীর ভোগের মধুরেণ সমাপয়েত পায়েস পিঠে দিয়ে। চিনি, নারকেলকোরা, দুধ ও আতপচাল দিয়ে পায়েস আর মালপোয়ার মতো গুড়পিঠে আর কলার বড়া। (Ranna Puja)

এবার আসি কলকাতার কয়েকটি বনেদি ঘটিবাড়ির নিরামিষ রান্নার রেসিপিতে।
পান্তাভাত, পাঁচভাজা, কচুশাক, ডালচচ্চড়ি, আলুপোস্ত বা আলুর দম, ইলিশভাজা, ভাপা ইলিশ, তেঁতুল দিয়ে ইলিশের টক, চালতা বা টমেটোর চাটনি, পায়েস থাকবেই অরন্ধনের পদে… জানালেন বেলঘরিয়ার বিখ্যাত নস্যিবাড়ির বৌ শ্রীমতি দোলন মুখোপাধ্যায়। অরন্ধনের পান্তাভাত, সারারাত জলে ভিজে থাকলেও একদমই জলঝরানো, হালকা, ঝরঝরে থাকবে। আর ইলিশের টক ছাড়া বাকিসব একেবারে শুকনো করা হয়। অরন্ধনের নিরামিষ ভোগের অভিনব কচুশাক রেসিপিও দিলেন তিনি। (Ranna Puja)
“যেদিন রান্না হবে সেদিন রাতে গরম ভাত খেতে হবে তাঁদের আর পরের দিন মানে অরন্ধনের দিন মাটির উনুনের ভেতরে মনসা গাছ দিয়ে সমস্ত রান্না নিবেদন করে মা মনসাপুজো হয়।”
আঁশ ছাড়িয়ে কেটে রাখা কচুশাক খুব ভালোভাবে ধুয়ে, তারপর আবারও গরম জলে ধুয়ে বড় ডেকচিতে ভাপিয়ে নিয়ে জল ঝরিয়ে, কড়ায় সর্ষের তেল গরম হলে তেজপাতা ও শুকনোলঙ্কা ফোড়ন, তারপর জল ঝরানো কচুশাক দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করতে, করতে জল কমে পরিমাণ কমে এলে পরিমাণমত লবণ, আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা ছোলা, নারকেল কোরা। কেউ সামান্য হলুদ দেন। নাড়াচাড়া করতে, করতে মাঝে মাঝে সামান্য সর্ষের তেল ছড়াতে হবে। একেবারে শুকিয়ে আসার আগে খুব সামান্য রাঁধুনিবাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে, অল্প ঘি ছড়িয়ে নামাতে হবে।(Ranna Puja)
অনেকের বাড়িতে ডালবড়া, উচ্ছেচিংড়ি, গাঁটিকচুর দম, নারকোল কোরা, সর্ষে-বাটা আর সর্ষের তেল দিয়ে মাখা ঘেঁটুফুল ও কচুপাতা বাটা, সর্ষে দিয়ে কচুর লতি আর শাপলা ডাঁটার ডাল দেওয়ার নিয়ম থাকে। (Ranna Puja)
উত্তরকলকাতার বনেদি লাহাবাড়ির কন্যা, কবি সুস্মেলী দত্তর শাশুড়িমা শ্রীমতী রেবা দত্ত জানালেন তাঁদের রান্নাপুজোয় আলু, বেগুন, পটল, ঢেঁড়স, ওল ভাজার সঙ্গে ইলিশমাছ ভাজা, বাগদা চিংড়ির ঝাল, চালতা দিয়ে চিংড়ি মাছের টক, চালতা দিয়ে গুড় অম্বল, মুসুরডাল ভাতে, ইলিশ মাছের মুড়ো দিয়ে কাঁচা তেঁতুলের টকের কথা। পান্তা ভাতের পাশে এক টুকরো গোঁড়া লেবুও নিবেদন করার রীতি।(Ranna Puja)
যেদিন রান্না হবে সেদিন রাতে গরম ভাত খেতে হবে তাঁদের আর পরের দিন মানে অরন্ধনের দিন মাটির উনুনের ভেতরে মনসা গাছ দিয়ে সমস্ত রান্না নিবেদন করে মা মনসাপুজো হয়। (Ranna Puja)
“৩০০ বছরের পুরোনো এই বাড়ির মেয়ে আমার কলেজবান্ধবী, অধ্যাপক সুনন্দা হালদারের কাকিমা অশীতিপর গৃহবধূ শ্রীমতি অসীমা দত্ত এখনও রান্নাপুজো পালন করেন নিষ্ঠার সঙ্গে।”
উত্তরকলকাতার তালতলার দত্ত পরিবারের মেয়ে ছন্দা বিয়ে হয়ে এলেন বড়বাজারের কালাকার স্ট্রীটের রায়বাহাদুর শিবচন্দ্র নন্দী খ্যাত নন্দীবাড়িতে। দুই বাড়িতেই নানান পালাপার্বণের মধ্যে রান্নাপুজোর মহা ধূম। শ্বশুরবাড়িতে একটু বেশিই। কারণ সেখানে আবার অন্নপূর্ণা পুজো হয় বিশাল। বড়বাজারের বাড়িতে এই অরন্ধনে দেড়-দু’কেজির ইলিশই আসত ৭-৮টা। বউমাদের বাপের বাড়ি থেকেও রান্নাপুজোয় ইলিশের তত্ত্বের রেওয়াজ ছিল। (Ranna Puja)
এহেন ঘটিবাড়ির বৌ ছন্দাদের অরন্ধনে নারকেল কুমড়ি, নারকেল কোরা দিয়ে মুগ ডাল, কাঁচা ইলিশ ভাপা, ইলিশের ঝাল, আমড়ার টকের সঙ্গে আলু, পটল ইত্যাদি ৯ রকম ভাজার মধ্যে বড়িভাজা আর মেচো শশা বা মাচায় বেড়ে ওঠা শশা ভাজা দিতে হয়। তাঁদের কোনও রান্নায় শুকনোলংকা পড়ে না। কেবল কাঁচালঙ্কা। ছাঁচি কুমড়ো ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়ে ভাপিয়ে জল ফেলে দিয়ে প্রথমে সর্ষের তেল গরম করে নারকেল কোরা ভেজে তুলে নিতে হবে। এরপর কাঁচালংকা, জিরে, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে ছাঁচি কুমড়ো সেদ্ধ, নুন, হলুদ আর দরাজ হাতে চিনি দেওয়ার নিয়ম। ঘটিবাড়ির রান্না বলে কথা। জল মরে গেলে নারকেল ভাজা দিয়ে খটখটে করে শুকিয়ে নিতে হবে। (Ranna Puja)

উত্তরকলকাতার খাস ঘটিপাড়া কলেজস্ট্রিট বেনিয়াটোলা লেনের ৩৭ নম্বর বাড়িটি ‘ডাক্তার বাড়ি’ নামে দোলদুর্গোৎসবের জন্য খ্যাত। সূতানুটি, গোবিন্দপুর, কলকাতা এই তিন গ্রাম নিয়ে যে কলকাতা শহর সেই গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদার গোবিন্দরাম দত্তের বংশধর তাঁরা। ৩০০ বছরের পুরোনো এই বাড়ির মেয়ে আমার কলেজবান্ধবী, অধ্যাপক সুনন্দা হালদারের কাকিমা অশীতিপর গৃহবধূ শ্রীমতি অসীমা দত্ত এখনও রান্নাপুজো পালন করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। তাঁদের বাড়িতে নিয়ম পান্তার সঙ্গে ৫ভাজা, নারকোল দেওয়া চাপ চাপ মুগ ডাল, ছাঁচি কুমড়ো, কচুর তরকারি, ইলিশ আর চালতার টক। তাঁদের ছাঁচিকুমড়োর রেসিপিতে আবার ফোড়নের মধ্যে জিরে, তেজপাতা ছাড়াও শুকনো লংকা ও গরমমশলা পড়ে আর চিনির ব্যাপারে তাঁরা অন্যান্য ঘটিবাড়ির মতোই দরাজ। নারকোল কোরা কিন্তু এই ছাচিকুমড়োর ঘন্টেও মাস্ট। (Ranna Puja)
“বিশ্বের কৃষিকর্মের সূচনা করবেন বিশ্বকর্মা তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি দিয়ে। ধরিত্রী শস্যশ্যামলা না হলে দেবী মহাশক্তির আবির্ভাব হবে কী করে? আর তাই মা মনসাকে সব ধরণের আনাজপাতি, মাছ নিবেদন। মনসাও তো শাকম্ভরী দুর্গার অংশ।”
বরানগরের ব্যাবসায়ী অধ্যুষিত শ্রীমানি মার্কেটের কাছেই আমার স্কুলের বন্ধু অদিতি শ্রীমানি জানালেন এই ছাঁচি কুমড়োয় বিনা হলুদে ঘিয়ে ফোড়ন আর চিনির বদলে গুড় দেওয়ার রীতি। বাকিসব এক। (Ranna Puja)
এই ভাদ্রসংক্রান্তির দিনেই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুজো। পুরাণে বিশ্বকর্মা হলেন, ‘বর্ষাকালীন সূর্য’। সূর্যের তাপে মেঘ সৃষ্টি করে বর্ষণের মাধ্যমে কৃষিকর্ম সম্পাদন করেন বলেই তিনি বিশ্বকর্মা। সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্ক আর চাষাবাদ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভাদ্রের আগমনে শরতের প্রবেশ, বর্ষার ইতি। ভাদ্রের উত্তাপে বর্ষার আর্দ্র মাটি শুষ্ক, রুক্ষ। আবার শুরু হবে রবিশস্যের জন্য নতুন করে জমিতে হলকর্ষণ। (Ranna Puja)
আরও পড়ুন: মুক্তিরূপেণ সংস্থিতা
বিশ্বের কৃষিকর্মের সূচনা করবেন বিশ্বকর্মা তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রপাতি দিয়ে। ধরিত্রী শস্যশ্যামলা না হলে দেবী মহাশক্তির আবির্ভাব হবে কী করে? আর তাই মা মনসাকে সব ধরণের আনাজপাতি, মাছ নিবেদন। মনসাও তো শাকম্ভরী দুর্গার অংশ। আরেক কৃষি উৎসবের শুভ লগ্ন ঘোষণার আগেভাগে মনসাও যেন কৃষিদেবীর মতো মূর্ত হয়ে ওঠেন। তাই বুঝি এই ভাদ্র সংক্রান্তির নাম কন্যাসংক্রান্তি বা সুপর্বা আর সেই সূত্র ধরে এইদিন ‘রান্নাপুজো’ও প্রাচীন কৃষি উৎসব একেবারেই অমূলক নয়। তাইতো অরন্ধন বা রান্নাপুজোর সঙ্গে কৃষির দেবতা বিশ্বকর্মা, মনসাপুজো মিলেমিশে এক হয়ে যান।(Ranna Puja)
“অরন্ধন” এক মিলনোৎসব। আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী সকলে মিলে হইহই করে খাওয়াদাওয়া… সেটাই হল রান্নাপুজোর সর্বকালীন আবেদন। (Ranna Puja)
* শুভশ্রী- খাবারের স্বাদকাহন / রান্নাঘর আর সোনার থালায় ভাত খাওয়ার গল্প / শ্রীধরকথক
বিশেষ ধন্যবাদ অমিতা মণ্ডল, দোলন মুখোপাধ্যায়, সুনন্দা হালদার, সুস্মেলী দত্ত, অদিতি শ্রীমাণি ও ছন্দা নন্দীকে রান্নাপুজোর রান্নাবান্না নিয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য।
মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অলংকরণ- আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।