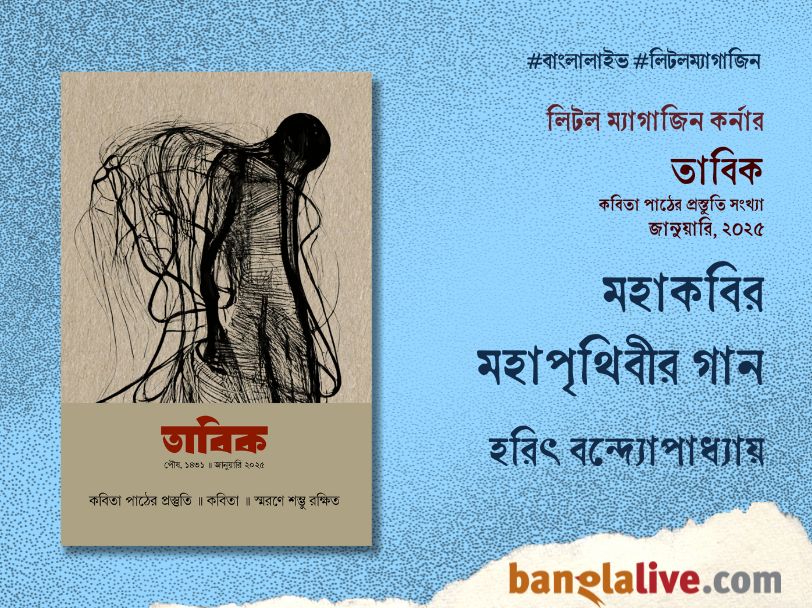(Little Magazine)
শম্ভু রক্ষিত সম্পর্কে একটি গল্প (সচেতনভাবে ’গল্প’ শব্দটিই লিখলাম কারণ এমন ঘটনা অনেক মানুষের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে না৷) প্রচলিত আছে, পৌরসভা থেকে তাঁর বিরিঞ্চিবেড়িয়া গ্রামের রাস্তায় ইলেকট্রিকের আলো লাগানো হয়েছে৷ এই ঘটনা শম্ভু রক্ষিত জানেন না৷ পরে যখন তিনি গ্রামে এসে সবকিছু দেখলেন তখন পৌরসভায় গিয়ে একাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিটিকে যারপরনাই তিরস্কার করেছিলেন৷ কে না চাইবেন তার গ্রাম আলোয় আলো হয়ে উঠুক৷ শুধু তাই নয়, একাজের জন্যে সরকারি লোকজনদের কত না ধরাকরা৷ কিন্তু শম্ভু রক্ষিত চাননি৷ কারণ তিনি মগ্ণতায় বিশ্বাসী ছিলেন৷ আমার গ্রাম তার নিজস্ব ঢঙেই বিরাজমান থাকুক৷ তুমি হঠাৎ করে এসে তার ধ্যান ভাঙাতে পারো না৷ কেননা এই কাজের মধ্যে যত না প্রাণের টান তার থেকে অনেক অনেক বেশি নিজ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ৷ মানুষের এহেন আচরণকে কবি ঘৃণা করতেন৷ মানুষ শম্ভু রক্ষিত এবং কবি শম্ভু রক্ষিতের মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল না ৷ (Little Magazine)
১৯৮৫ সালে কলকাতার রবীন্দ্রসদনে একটি স্মরণসভা চলছে৷ শম্ভু রক্ষিত কবিতা পড়তে উঠলেন৷ ঠিক ওইসময় অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন একটি জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচরিত বাণিজ্যিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক৷ শম্ভু রক্ষিতের কবিতা পাঠ শেষ হল৷ আর সেই সম্পাদক কবির কাছ থেকে পঠিত কবিতাগুলি চাইলেন কারণ তিনি সেগুলি তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করবেন৷ শম্ভু রক্ষিত মুখের ওপর না বলে দিলেন৷ তাঁর এইসমস্ত পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের বিন্দুমাত্র কোনো আগ্রহ নেই৷ যদিও পরে সম্পাদক একপ্রকার জোর করেই তাঁর পত্রিকায় কবিতাগুলি প্রকাশ করেছিলেন৷ অর্থাৎ কবি তাঁর প্রত্যেকটি আচরণের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি শম্ভু রক্ষিত৷ তাঁকে কেনা যাবে না৷ তাই তাঁর তুলনা শুধুমাত্র তাঁকে দিয়েই দেওয়া যেতে পারে ৷ (Little Magazine)
আরও পড়ুন: ভ্রমি: স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড- ভাস্কর দাস
শম্ভু রক্ষিত কবিতা লেখার একেবারে শুরুর দিকে মামার বাড়িতে থাকতেন এবং সেখানে তাঁর একটি নিজস্ব ঘর ছিল৷ তিনি আশা করেছিলেন ওই ঘরটুকু অন্ততঃ তার হবে৷ কিন্তু দিদিমা মারা যাওয়ার পর মামারা তাঁকে ওই বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন৷ কবি নিজে এজন্য অনেক লড়াই করেন৷ কিন্তু কোনো লাভ হয়নি৷ শেষ পর্যন্ত তাঁকে ওই বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয় ৷ (Little Magazine)
১৯৬৩-৬৪ সাল নাগাদ যখন কবি মামার বাড়ি হাওড়ার কদমতলায় থাকতেন ৷ সেইসময় হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন৷ এই আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল এবং সেই কারণে তিনি এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের কথা মাথায় রেখে ‘ব্লুজ’ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতে শুরু করেন৷ পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা থেকেই কবির প্রতিষ্ঠান ভাঙার তীব্র ইচ্ছাকে লক্ষ করা যায়৷ হাংরি আন্দোলন তখন জোর কদমে চলছে ৷ সেই সময় শম্ভু ‘জেব্রা’ নামের একটি পত্রিকায় ‘আমি স্বেচ্ছাচারী’ নামে একটি কবিতা লেখেন— ‘এইসব নারকেল পাতার চিরুনিরা, পেছন ফিরলে, এরাও ভয় দেখায়৷/ কিছুই, এক মিনিট, কিছুই জানি না, সাম্যবাদী পার্লামেন্টে জনশ্রুতি সম্পর্কে বা/ চণ্ডাল কুকুরদের আর্তনাদ আমাকে ঘিরে— এবং আমাকে আলবৎ জানতে হবে, আলবৎ আমাকে/ ডুবতে দিতে হবে, যেতে দিতে হবে যেখানে যেতে চাই না, পায়চারি করতে দিতে হবে৷’ বোঝাই যায় এখান থেকেই তাঁর রাস্তা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে৷ তাঁর হাত ধরেই বাংলা কবিতা যেন এক নতুন রূপ পরিগ্রহণ করলো ৷ (Little Magazine)
এই কবিতাটিরই শেষ কয়েকটি লাইন পড়লে আমাদের চমকে উঠতে হয় — ‘হু হু করে জেটপ্লেনে আমি যেতে চাই যেখানে যাবো না, এর ভেতর দিয়ে/ ওর ভেতর দিয়ে— আর৷ হুম৷ একধরনের ছেনি-শাবল আমার চাই—/ যা কিছুটা অন্যরকম, রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দের নয়—ঠিক খেলার মাঠে স্টার্টারের পিস্তলের মতো—রেডি— আমি বাঘের মতন লাফিয়ে পড়ব৷ খবরদার৷’ ষাটের দশকের শুরুতেই শম্ভু রক্ষিত জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব রাজ্যের কথা৷ বলাই বাহুল্য শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘আমি স্বেচ্ছাচারী’ শম্ভুর পরে লেখা ৷ (Little Magazine)
“তিনি কবিতা লেখার শুরুতে নিজেই নিজের একটি পৃথিবী তৈরি করে তবে কবিতার রাজ্যে পা রেখেছিলেন৷ তাই প্রথম থেকেই তাঁর কবিতা একেবারেই তাঁরই মতো ৷”
হাংরি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে লালবাজার থেকে শম্ভু রক্ষিতকে ডেকে পাঠানো হয় এবং এর পরে মামলার কারণে ‘ব্লুজ’ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়৷ এর বেশ কিছু সময় পরে শম্ভু ‘মহাপৃথিবী’-র প্রকাশ শুরু করেন৷ ইন্দিরা গান্ধীর এমারজেন্সির সময়ে শম্ভুকে জেলে যেতে হয়৷ জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি ‘রাজনীতি’ নামে এই কবিতাটি লেখেন— ‘চ্যান্টার অশ্ব আর গ্রহদের নিয়ে আমি এখন আর পালিয়ে বেড়াই না/ নির্র্দেষদের বন্দি করার নীতি ধ্বংস করে আমি আমার খনন শুরু করি/ এবং বস্তুতঃ এমন একটা বক্তব্য উচ্চন্ট্রে তুলে ধরতে চেষ্টা করি/ ঐন্দ্রজালিক উদোম ন্যাংটো সব বিশ্লেষণকে যা আগেই এড়িয়ে যায়/ আমি চিন্তানায়কদের দিকে কখনও তাকাইনি, এখনও তাকাচ্ছি না/ তবে জেলের টাইপরা সুপারকে কয়েকবার বলেছি/ আপনাদের শ্রুতিঘোড়াটি একমাত্র ‘সর্বশক্তিমান’ নয়, আপনিও!/ বন্দিনিবাসেও দু-দশদিন অন্তর তাই আমার চামড়া ভাঁজ করে শুকিয়ে ফেলা হয়/ ভোঁ ভোঁ ও অশান্ত অঞ্চল গান শব্দে ‘পাগলি’ বেজে ওঠে৷’ কারাবাস সম্পর্কে শম্ভুর এক অসাধারণ উক্তি আছে—দেখুন জেল খুব ভালো জায়গা৷ এই জেলখানাতে খুব সহজে যাওয়া যায় না আপনার টাকাপয়সা থাকলে আপনি পৃথিবী ভ্রমণ করতে পারবেন, কিন্তু আপনি ইচ্ছেমতো জেলখানায় যেতে পারবেন না৷ আমার তো জেলখানা খুব ভালো লেগেছে৷ আমার মনে হয় প্রত্যেক কবি যদি একবার করে জেলখানায় ঘুরে আসতে পারতেন তো খুব ভালো হত৷’ (Little Magazine)
একজন কবি যখন কবিতা লিখতে আসছেন তখন তিনি নিশ্চয়ই কিছু পড়াশোনা করে আসছেন৷ অবশ্যই তাঁর কোনো প্রিয় কবি থাকবেন এবং লেখার সময় সেই কবির অল্পবিস্তর প্রভাব তাঁর কবিতায় এসে পড়বে৷ এটাই স্বাভাবিক৷ কিন্তু শম্ভুর ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনি৷ তিনি কবিতা লেখার শুরুতে নিজেই নিজের একটি পৃথিবী তৈরি করে তবে কবিতার রাজ্যে পা রেখেছিলেন৷ তাই প্রথম থেকেই তাঁর কবিতা একেবারেই তাঁরই মতো ৷ এখানে আরও একটা কথা বলে রাখা ভালো, একজন পাঠক যখন কোনো কবিকে পড়তে যাচ্ছেন তখন পাঠক মনে মনে একটা লাইন ঠিক করে ফেলছেন যে, তিনি কি পড়তে যাচ্ছেন এবং সেই কবির কবিতায় তাঁরই কোনো প্রিয় বিষয় গুরুত্ব পাবে— এই কারণের জন্যেই তো সেই কবিকে ভালোবেসে ফেলা৷ কিন্তু শম্ভুর কবিতা পড়তে যাওয়ার আগে কোনে পাঠক এমন কোনো লাইন টানতে পারবেন না৷ কারণ শম্ভুর কবিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কোন পথে হেঁটে যাবে এবং তার চলার গতিই বা কেমন হবে তা সত্যিই এক রহস্য৷ পাঠক শম্ভুর কবিতা পড়ছেন কিন্তু কিছুতেই ধারণা করতে পারছেন না এই কবিতা তাকে কোন পথে নিয়ে যাবে৷ সম্পূর্ণ ছবি গড়ে ওঠার আগেই তিনি অন্য ছবিতে চলে যাচ্ছেন৷ প্রতি মুহূর্তে তাঁর কবিতা বাঁক বদল করে৷ দশক অনুযায়ী যদি আমরা ভাবি তাহলে ষাট সত্তর আশির দশকে যে ধরনের কবিতা লেখা হয়েছে তার সঙ্গে শম্ভুর কবিতার কোনো মিল নেই ৷ (Little Magazine)
“এই কাব্যগ্রন্থটিরই ‘মুক্তিবাদ’ কবিতাটি পড়লে আমরা কবি শম্ভু রক্ষিতকে অনেকটাই খুঁজে পাব৷ তাঁর কবিতায় লোকদেখানো মেকি জিনিসটাই নেই৷ তাঁর নিজস্ব পৃথিবীতে তিনি একাই রাজা ৷”
তিনি তাঁর কবিতায় কিভাবে বাক্য সাজাবেন, এমনকি কোন কোন শব্দ তিনি তাঁর কবিতায় আনবেন তাও তিনি তাঁর নিজের তৈরি পৃথিবীতেই অন্বেষণ করেন৷ আমৃত্যু তিনি এই পথেই হেঁটে গেছেন— ‘যারা তাকে দেখেছিল, তারা কেউ আর আর্ত-হাত বাড়াবে না/ তারা ধরিত্রীর মৃত-পিতৃপুরুষ, তারা পরিপুষ্ট শস্যবীজের মধ্য দিয়ে উঠে আসে/ আদি জলরাশির অন্তরে; অন্যজন্ম জন্মান্তর গ্রহ-উপগ্রহে শব্দের প্রকাশে/ যারা থাকে শুয়ে; অকস্মাৎ এই পরবাসী অধ্বর্যুদের ভিড়ে নিজেদের দ্যাখা/ পেয়ে কেঁপে ওঠে যারা; যারা মন্ত্রবলে হালকা মেঘের ভেলায় চেপে/ অবলীলাক্রমে স্বর্ণপদক যাবে; যারা দেবতাদের অস্ত্রাগার থেকে অমোঘবজ্র আর / অনির্বাণ বহ্ণিশিখা সংগ্রহ করে আনবে; যারা অমৃতভৃঙ্গার নিয়ে সুরাসুরের/ মধ্যে বন্টন করে চায় সূর্য ; যারা নোঙর তুলে/ গলুই-এর আগায় প্রতিহিংসা গুটিয়ে নেয়/ প্রাত্যহিক সুখে দুঃখে শোকে ঈশ্বরের মহিমময়লোকে বাতি জ্বলে/ কণারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে থাকে৷’ (Little Magazine)
আমরা যখন কোনো কবির (তিনি যদি নতুন না হন) কবিতা পড়তে যাই তখন আগে থেকেই তার একটা আসন আমাদের হৃদয়মন্দিরে পাতা থাকে৷ যত সময় যায় তত সেই কবির প্রতি আমাদের দুর্বলতা গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে৷ এইরূপ দুর্বলতার পরে যদি সেই কবি তার কোনো কোনো কবিতায় নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য (যা পূর্বসূরীদের কাছ থেকেই পাওয়া, তার সঙ্গে কিছু নতুনত্ব মিশিয়ে একটা ভিন্ন রূপ দেওয়ার চেষ্টা) দেখাতে নাও পারেন আমরা তার প্রতি দুর্বলতার কারণে সেগুলিকে বড় করে দেখি না এবং সেগুলি আমাদের মনের মধ্যে কোনো দাগও রাখে না৷ কিন্তু শম্ভুর কবিতা পড়তে গিয়ে আমার বারবার মনে হয়েছে এমন কোনো সুবিধা তিনি কোনোদিনই পাননি৷ বলা ভালো তিনি পেতে চাননি৷ আসলে পাঠক শম্ভুর কবিতা পড়ে নিজের মনের মধ্যে কোনো জমি তৈরি করতে পারেন না, যে জমির ওপর দাঁড়িয়ে অর্থাৎ একটা অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তিনি পরের দিনের শম্ভু পাঠ শুরু করবেন৷ এটাই শম্ভুর বড় মৌলিকতা— একমাত্র বাংলা ভাষার কবি যাঁকে পড়তে গিয়ে পাঠককে প্রতিদিন শূন্য থেকে শুরু করতে হয়৷ প্রত্যেক দিন নতুন নতুন দিক অন্বেষণ—পাঠক হিসাবে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ৷ (Little Magazine)
একদিন আমার হাতে এসে পড়ল শম্ভু রক্ষিতের ‘আমি কেরর না অসুর’ কাব্যগ্রন্থটি৷ প্রথমেই নামে আটকে যাই৷ ‘কেরর’ মানে কি? না, কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না৷ কোনো অভিধানে নেই৷ শম্ভু তাঁর কবিতায় এমন কিছু শব্দ এনেছেন যার মানে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না৷ এগুলি সবই শম্ভুর নিজস্ব সৃষ্টি৷ এর পাশাপাশি আমি এটাও বিশ্বাস করি এইসব শব্দ শম্ভুর অন্তর্জগতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ৷ তাঁর কবিতার নিজস্ব চলন সে কথাই বলে৷ তবে কাব্যগ্রন্থটির নাম-কবিতার শেষ লাইনটির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে ‘কেরর’-এর অর্থের একটা হদিশ আমরা পেতে পারি— ‘আমি দেহ না আত্মা বদ্ধ না মুক্ত আমি কেরর না অসুর৷’ (Little Magazine)
“প্রতি মুহূর্তে এই যে নিজেকে ভাঙাগড়ার কাজে ব্যস্ত রাখা— এইভাবেই তো কখন যেন সময় চলে যায়৷ কত না যত্নে, কত কষ্টের চেষ্টায় নিজেকে একটা কোনো ইতিবাচক পরিধির মধ্যে ব্যাপৃত রাখা ৷”
এই কাব্যগ্রন্থটিরই ‘মুক্তিবাদ’ কবিতাটি পড়লে আমরা কবি শম্ভু রক্ষিতকে অনেকটাই খুঁজে পাব৷ তাঁর কবিতায় লোকদেখানো মেকি জিনিসটাই নেই৷ তাঁর নিজস্ব পৃথিবীতে তিনি একাই রাজা ৷ শুধু তাই নয় আমৃত্যু তিনি নিজেই নিজের প্রতিযোগী৷ শহুরে সাজানো কবিদের দিকে তিনি আঙুল তুলে বলেন— ‘যারা আমাকে ডিগডিগে/ আমার রুহে যুদ্ধের হিরো/ আমার ঈশ্বরকে অনিষ্টজনক/ আমার কবিতাকে/ চাকচিক্যময় আভিজাত্য বা বিক্ষিপ্ত প্রলাপ মনে করে আহভাইরে/ তারা বাণিজ্যের অযথার্থ ক্ষমতা দিয়ে/ তাদের নাক মুখ কান দখল করে / এই শক্তিশালী প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের/ অস্তিত্ব রক্ষা করুক/ যারা বালি ফুঁড়ে/ আমাকে বাল্যপাঠ শেখাচ্ছে/ আহভাইরে/ তারা মেকি সুন্দরের মিথ্যা সীমারেখা প্রত্যাখ্যান করে/ অন্তত একটা ছোটখাটো দেবদূতের সন্ধান করুক/ অকেজো জ্যুকবক্সে স্থির ডিস্ক/ জীবনের আর ভাঙা ইঁটের/ অশুভ যুদ্ধপরা যন্ত্রণায় আন্তর্জাতিক কোরাস/ আহভাইরে/ কবরখানা আর টাউনশিপের সুড়ঙ্গের মধ্যে গুঞ্জন করা/ আস্তাবলের ধূর্ত পিটপিটে মায়া/ মধ্যে মধ্যে ফ্যাঁকড়া/ আহভাইরে/ কাঁধে অগ্ণিবর্ণের ক্যামেরা/ হাতে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট ট্রানজিস্টার/ অন্য সম্রাটের দায় যাতে মেটে/ মাংস ভেদ করে সচল ফ্রেস্কোর মতো/ এইসব রেডিয়ো-টিভি-অ্যাকটিভ যুবশক্তি/ মুক্তিবাদে এবং জাঁকজমক খুঁড়ে নৈশস্তব্ধতা/ আহভাইরে’ ভয়ঙ্কর এক বিদ্রূপ সমগ্র কবিতাটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে৷ যদিও শম্ভুর সব কবিতাতেই এই বিদ্রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করি৷ প্রাতিষ্ঠানিক কবিদের নিয়ে তিনি রঙ্গরসিকতা করেছেন৷ ‘আহভাইরে’ বারবার উচ্চারণ করে তিনি তাঁদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন৷ শুধু তাই নয় তাদের কাজকর্ম কতটা হাস্যকর তা কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়৷ এমন একটি কবিতা লেখার জন্য যে মেরুদণ্ডের দরকার তা শম্ভু রক্ষিতের ছিল৷ আজকের সময়ে কবির এই মানসিকতার কথা আমরা ভাবতেও পারি না৷ এইজন্যই তিনি বাংলা কবিতার জগতে বিরলতম চরিত্র ৷ (Little Magazine)
এই কাব্যগ্রন্থেরই ‘প্রায় প্রজল্প’ কবিতাটি পড়তে গিয়ে দেখি কবি লিখেছেন ‘আমরা প্রবলতর ভাবে নিজেদের দ্বারা নির্মিত, সমাজের বহির্ভূত ও স্বাধীন৷’ আত্মনির্মাণের গভীর পদ্ধতির কথাই এখানে উঠে আসতে দেখি৷ ‘আমরা এই মুহূর্তে মরবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি/ আমরা যে বিরাট দৈত্যের দম্ভকে অস্বীকার করেছি/ তার নৌকাগুলোকেও থামাতে বাধ্য করেছি/ আমরা এই মুহূর্তে আমাদের চোখের নীচের ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছি’— এ যেন আমাদেরকে নতুন রূপে দেখা৷ অন্য কেউ নয়, নিজের ভেতরেই ঘুমিয়ে থাকা এক অন্য আমি৷ এই কবিতাটিরই শেষ স্তবকে কবি আত্মখননে মত্ত৷ একটা সময়ে মনে হতো ভেতরের আমি-টাকে রোজ একটু একটু করে বদলে ফেলবো৷ রোজ সকালে নতুন করে বেঁচে উঠবো৷ আজ ঘুমিয়ে পড়ার আগে পর্যন্ত আমি-র যে নেতিবাচক অংশটুকু আমাকে তৃপ্তি দিল না পরের দিন সেই অংশটুকু আমি-র মধ্যে না রাখার আপ্রাণ চেষ্টাই হবে আমার সারাদিনের কর্মসূচি৷ অথবা এমন কিছু ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য যা আমার মধ্যে ঘুমিয়ে আছে তাকে খুঁড়ে বের করার একটা চেষ্টা৷ এইভাবেই তো তৈরি হতে পারে নতুন আমি৷ ‘আমরা নিজেদের খুঁড়ে বের করছি৷ আবার নিজেদের হারাচ্ছি / নিজেদের হারাচ্ছি, নিজেদের খুঁড়ে বের করছি…’ (Little Magazine)
আরও পড়ুন: মথ: প্রতিচ্ছবি ও প্রতিধ্বনির গল্প- অমিতাভ মৈত্র
প্রতি মুহূর্তে এই যে নিজেকে ভাঙাগড়ার কাজে ব্যস্ত রাখা— এইভাবেই তো কখন যেন সময় চলে যায়৷ কত না যত্নে, কত কষ্টের চেষ্টায় নিজেকে একটা কোনো ইতিবাচক পরিধির মধ্যে ব্যাপৃত রাখা ৷ আবার দেখা গেল কোনো একদিনের হঠাৎ ঝঞ্ঝায় অনেকদিনের বেড়ে ওঠা গাছ একধাক্কায় ভেঙে গেল৷ আমরা যে খুব একটা সাবধান হয়েছিলাম তা নয় কারণ সাবধান হলে ঝঞ্ঝার বিপরীতে গাছটা হয়ত বাঁচানো যেত না কিন্তু একটা প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেত৷ এই প্রতিরোধটাই হতো আগামী দিনের আমি-র বাঁচার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ৷ (Little Magazine)
কোনো কোনো দিন সকালে অথবা নির্জন দুপুরে আমরা সেই বিন্দুতে হাজির হতে পারি যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা আমাদের হেঁটে আসা পথ অথবা নিজেরই হাতে তৈরি করা আগামীর পথকেও দেখে নিতে পারি৷ একদিন যে মানুষের জন্যে আমরা দিনরাত এক করে ফেলেছি অথবা একমুহূর্তের দুপুরের ছোঁয়ায় সারা জীবন আলো হয়ে উঠেছে সে-ই আবার কখন যেন আমাদের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে৷ হয়ত আমরাই তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়েছি৷ কত কত দিন খুঁড়ে খুঁড়ে তবে জীবনের একটা গভীর স্তরে গিয়ে পৌঁছানো৷ আবার কেনই বা সেখান থেকে উঠে আসা! বড় জানতে ইচ্ছা করে জীবনের কোন মুহূর্তে এই রকম অনুভূতি হয়? দীর্ঘ খনন প্রক্রিয়া চালানো আমি ঠিক কতখানি বদলে গিয়ে নিজেদের হারানোর পথে যাই? হৃদয়ঘরে সত্যিই কি খুব ভয়ানক ডামাডোল চলতে থাকে যেখানে অবস্থান করে মনে হয় এই হারানোর মধ্যে দিয়ে একটা ভারসাম্য আসুক? এসবই আমাদের কাছে অজানা— ‘তবে আমরা জানি না কেন আমরা নিজেদের হারাচ্ছি?/ নিজেদের কেন খুঁড়ে বের করছি…’ (Little Magazine)
নিজেদের ভেতর থেকে যখন কিছু খুঁজে বের করতে পারি তখন এক অসাধারণ আনন্দে আমাদের মন প্রাণ ভরে ওঠে৷ আমাদেরই শরীর জাত কোনো অনুভূতি যা আমাদেরই অসচেতনতায় শরীরেরই কোনো কন্দরে ঘুমিয়ে ছিল একদিন কোনো এক নির্জন মুহূর্তে তার সঙ্গে আমাদের চোখাচোখি হলো৷ সারা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল আলো৷ তখন মনে হয় সকালের আলোয় কে যেন ছড়িয়ে দিয়ে গেছে রাশি রাশি সোনা, মনে হয় দুপুরের অনন্ত প্রবাহের দিকে তাকিয়েই থাকি৷ নতুন আলোকচ্ছটায় নিজেদের মূল্যায়নের ধারও বদলে যায়৷ মনে হয় সে এক নতুন জীবন— ‘কিন্তু আমরা যখন নিজেদের খুঁড়ে বের করি/ এক অনির্বচনীয় শান্ত আনন্দে ভরে যায় আমাদের অন্তর’ ‘তুমি ঈশ্বরকন্যা, তুমি আমাকে বিশুদ্ধ কবির জনক হতে সেদিন শেখালে/ ব্যক্তিগত মৌলিক দৃশ্য থেকে ধূসর বিষয় নিয়ে আমি, ব্যক্ত অব্যক্তের/ অবাস্তব মুহূর্তের স্বতন্ত্র আমি, আমার গভীরতর সাম্রাজ্যে/ তুমি আছো, তুমি নেই— ‘প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না’ কাব্যগ্রন্থ শুরু হচ্ছে ঠিক এইভাবেই৷ কবির বয়স তখন মাত্র তেইশ৷ সমস্ত গাণিতিক সমীকরণ মিথ্যে করে দিয়ে তিনি আসছেন৷ তাঁর পূর্বসূরি সেই অর্থে কেউ নেই ৷ (Little Magazine)
“সেইকারণেই তো কবিতা লেখার শুরুতে কবিকে হাজার প্রশ্ণের মুখোমুখি হতে হয় ৷ কারণ কলকাতার কবিতার যাঁরা পিতা তাঁদের বোধে শম্ভুর কবিতা কোনো সাড়া দিতো না ৷”
তিনি নিজের থেকেই নিজে গ্রহণ করছেন৷ ‘তুমি স্থির, নিঃশব্দ রক্তমাংস, তোমার যৌনাঙ্গকে আমার প্রণতি/ তোমার উন্মুখ স্তনে মুখ দিয়ে আমি ব্যবধানহীন বেঁচে রয়েছি/ আমি এতদিন আত্মাতে বিশ্বাসী ছিলাম, তোমায় গর্ভবতী করে রেখেছিলাম/ আমি চন্দ্রমাশীতলরাত্রে খুঁজেছিলাম তোমার গাল আমার গালের পাশে/ আমি উত্তরঙ্গ জলোচ্ছ্বাসে তোমাকে ভাসিয়ে দিয়ে বলেছিলাম:/ সব মানুষ জন্মকাল থেকে সমান’— তেইশ বছর বয়সের এই রচনায় যাঁরা চমকে ওঠার উঠুন, আমি বিন্দুমাত্রও চমকাই না৷ কারণ একটাই, কবির নাম শম্ভু রক্ষিত৷ আর পৃথিবীতে একজন মাত্রই শম্ভু রক্ষিত জন্মগ্রহণ করেন৷ কবি তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থের উৎসর্গপত্রে লেখেন— ‘ঈশ্বরের রোষ থেকে মানুষকে ত্রাণ করবার জন্য আর এক ঈশ্বর-পুত্রের আত্মাহুতি ও রক্তদান’—এইরূপ বক্তব্য পড়ে যে কেউ প্রশ্ণ করে উঠবেন, তাহলে কি কবি নিজেকে ঈশ্বর-পুত্র যীশুর সঙ্গে একই আসনে বসিয়েছেন? অসম্ভব কিছুই নয়, যাঁরা শম্ভু রক্ষিতকে চেনেন তাঁরা খুব ভালো মতোই জানেন এরকম বলিষ্ঠ উচ্চারণ তাঁর চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ৷ (Little Magazine)
এই কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ১০৬ টি কবিতা আছে৷ কোনো কবিতারই আলাদা কোনো নাম নেই৷ কোনো কবিতারই নির্দিষ্ট কোনো পরিমাপ নেই৷ পাঠক যেখান থেকে খুশি পড়তে পারেন৷ কেউ কেউ আবার এগুলিকে আলাদা আলাদা কবিতা মনে করতে পারেন৷ কেউ কেউ আবার সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিকেই একটি দীর্ঘ কবিতা মনে করতে পারেন৷ কোনো কিছুতেই কোনো অসুবিধা কিছু নেই৷ তবে আমি ব্যক্তিগত এই কাব্যগ্রন্থটিকে একটি মহাকাব্য ভাবতেই বেশি ভালোবাসি ৷ তিনি অনন্ত পথের যাত্রী ৷ পথ চলতে চলতে চোখের সামনে যা কিছু দেখেছেন তাকেই তিনি তাঁর গভীর আত্মোপলব্ধির দ্বারা জারিত করে একান্ত নিজস্ব পথে ভাষারূপ দিয়েছেন ৷ তবে এরকম একটি কবিতার বই আমাদের সামনে রেখে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, এটাই তাঁর পরিচয়— যার সবটুকু আদ্যন্ত মৌলিক৷ তিনি একাই এসেছেন ৷ নিজের খুশিমতো একাই ঘুরেছেন ৷ তাঁর জীবনে নিষেধ বলতে কিছু ছিল না৷ আবার যখন ইচ্ছা গেছে তখন তিনি এখান থেকে সরে পড়েছেন ৷ (Little Magazine)
“মহানগরের মানুষজন জানেন কালবৈশাখী কাকে বলে? এখনই সবাই রে রে করে ছুটে আসবেন, জানি না মানে? বলতে বলতে তাঁরা সাদা পাতায় লিখে দেবেন একশ একটা কালবৈশাখীর সংজ্ঞা ৷”
শম্ভুর সব কবিতাতেই বিশেষ করে ‘প্রিয় ধ্বনির জন্য কান্না’-য় তিনি যে ধরনের শব্দচয়ন, ছন্দের ব্যবহার, ভাষার অলংকরণ করেছেন— সবই তাঁর নিজস্বতায় ভরা৷ নিজের কবিতা সম্পর্কে শম্ভু বলেছেন— ‘আমি ‘‘নেহাত কবিতা’’ নির্মাণ করি না এই কারণে যে আমি জানি, আমার যা বিশ্বাস যা আমি হঠাৎ হঠাৎ করি, তার মধ্যে বেঁচে-থাকার একটি মুক্তি আছে৷’ তাঁর প্রতিটি কবিতাতেই আমরা দেখি তিনি এই মুক্তিকেই খুঁজে বেড়িয়েছেন৷ দেখাটা যদি আমার নিজস্ব হয় তাহলে কবিতার প্রকাশ কেন সেই সনাতন পথ ধরে হবে? তাই তিনি কোনো শর্তেই বিশ্বাসী ছিলেন না৷ ‘আমি কেরর না অসুর’ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার দিকে দৃষ্টিপাত করলে কবির পরিচয় অনেকটাই নির্দিষ্ট হবে— ‘আমি বস্তুর চেয়ে নেগ্রিটিউড, রাষ্ট্র ধর্ম শিক্ষা সমাজ বা প্রেম পোয়েট্রি/ সব থেকেই আমি মুক্ত হতে ক্রমাগত বিলীয়মান দিকরেখায় মিলিয়ে যাই/ আমি সৌন্দর্যের এক ধাপে দাঁড়িয়ে গাই মানুষের নীলেরই সমান্তরাল/ আমি প্রতিধ্বনিত শব্দের মতো বৃহৎ দৃষ্টি নিয়ে চিত/ আমি মকরুহ পাহাড় নিয়ে বত্তৃণতা দিই/ মাইসিনাসবাদ ভানে দুঃখকে উপাসনা করি/ আমি উদ্ভিদের প্রশান্ত পাতার বর্ণনা দিতে ভালোবাসি৷’ এই কবিতাটিরই শেষ কয়েকটি লাইন এইরকম— ‘আমার বৈকালিক ভ্রমণের জন্য একটি প্যালিওযোইক যুগও কিনেছি/ মানবতার পক্ষে হাত তুলতে স্টোভ নাইপে যেতে উৎসাহ পাচ্ছি না আর/ কেননা আমি আমার মাথার মধ্যে/ আমার চৈতন্য এক এবং ক্রমশ আরও একত্বে ঘনীভূত হচ্ছে/ এসো স্তন্যপায়ী জীবশ্রেণী, থুতু ছিটোই আর হয়ে উঠি এমন মানুষ৷’ (Little Magazine)
শম্ভু রক্ষিতের সামনের মানুষজন এবং তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকা মানুষেরা কবিকে ঠিক কতখানি চিনতেন? এই চেনা মানে ঠিকানা আর পিতার নাম যে নয় তা বলাই বাহুল্য ৷ একজন কবিকে চেনা মানে তো তাঁর সৃষ্টির মৌলিকতা দিয়ে তাঁমকে চেনা ৷ এই চেনা কবিকে ক’জন চিনতেন আমার খুব সন্দেহ আছে৷ বিশেষত এই চেনার ক্ষেত্রে শম্ভু রক্ষিতের মতো মানুষকে তো মুহূর্তে উড়িয়ে দেওয়া যায় এবং দিয়েছেনও বেশিরভাগ মানুষ৷ কারণ তাঁর চেহারা মোটেই সমীহ আদায় করার মতো নয়, বরং অনেক বেশি চাষাভুষো৷ তাই এরকম একটা আটহাতি কাপড়ের মানুষ কবিতা আর কতটুকুই বা বুঝবে! কবিতা লেখা তো অনেক পরের ব্যাপার ৷ (Little Magazine)
সেইকারণেই তো কবিতা লেখার শুরুতে কবিকে হাজার প্রশ্ণের মুখোমুখি হতে হয় ৷ কারণ কলকাতার কবিতার যাঁরা পিতা তাঁদের বোধে শম্ভুর কবিতা কোনো সাড়া দিতো না ৷ কিন্তু তা তো আর প্রকাশ্য দিবালোকে স্বীকার করা যায় না, তাহলে তো সিংহাসন টলে যাওয়ার ভয় থাকে৷ তার চেয়ে বরং অনেক সহজ বলে ফেলা— এগুলো কোনো কবিতাই নয়— ‘এই উৎসব আপনার জন্য নয়৷ তবে এই সংকেতলিপি কলকাত্তাইয়া ভাষায় বিয়াল্লিশটি বাগরীতির সমন্বয়ে গঠিত৷ এর মুফত গোপনতা আছে৷ যেমন, চারটি আঞ্চলিক দর্ভটচিত্র নিয়ে এই সংকেতলিপি৷ এর নির্মাণকার্যে কোনো অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যকোণ দেখতে পাওয়া যাবে না৷ সর্বত্রই একটু সুগোল করে বানানো৷ শিল্পীরা যেমন স্তরবিন্যাস বা খুঁটির ওপর ঘরবাড়ির ছবি আঁকেন, সেরকমও এখানে নেই ৷’ (Little Magazine)
“শম্ভুর কবিতা যদি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ত তাহলে আজকে তৈরি হতো শম্ভুর উত্তরসূরী এবং তাতে বাংলা কবিতার একটা আমূল বদল ঘটত ৷”
মহানগরের মানুষজন জানেন কালবৈশাখী কাকে বলে? এখনই সবাই রে রে করে ছুটে আসবেন, জানি না মানে? বলতে বলতে তাঁরা সাদা পাতায় লিখে দেবেন একশ একটা কালবৈশাখীর সংজ্ঞা ৷ যাঁরা মুখোমুখি কালবৈশাখীর সঙ্গে লড়াই করেছেন তাঁরা পর্যন্ত চমকে উঠবেন এবং অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করবেন নিজের মেকিত্ব ঢাকতে কিভাবে তাঁরা শব্দের শরীরে অলংকার পরিয়েছেন৷ মহানগরের স্বঘোষিত কবিতার রাজ্যের দাদারা কেনোদিনও জানবেন না, হ্যারিকেন বা লম্ফর আলোয় কিভাবে মহাকাব্য লেখা হতে পারে; সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর খড়ের বা খোলার বা টালির চালের জলপড়া ঘরে কিভাবে না ঘুমিয়ে কবিতা লিখতে হয়৷ তাই তাঁরা কি করে বুঝবেন শম্ভুর কবিতার গতিপ্রকৃতি ! (Little Magazine)
শম্ভু জানতেন মহানগরের এক টুকরো মাটির জন্যে কবিদের সে কী হুড়োহুড়ি (পড়ুন মারামারি), সেখানে কবিতা লিখতে জানাটা কোনো শর্তই নয়, বরং অনেক অনেক বেশি দরকারী কার কত বড়ো হাত এবং শেষ পর্যন্ত সেটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে৷ শম্ভু মহানগরের এই আবহাওয়া সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে তিনি ওই মাটি কোনোদিন মাড়াতে যান নি৷ সবসময় দূরে থাকাই স্বাস্থ্যকর বলে মনে করতেন— ‘আপনি সময় সময় নিজের প্রদর্শনশালার ভেতর তীব্রদৃষ্টি দিয়ে দেখুন৷ আর যদি অজানা বঙ্গের কোনো গ্রামে আপনার বাড়ি থাকে, তাহলে বেশি করে বিশ্রাম করুন৷ দর্শনে অভিনিবেশ করুন৷ প্রকৃতির কোলে সময় কাটান৷ আর অভিনয়ের দিকে ঝোঁক থাকলে সেখানে প্রাণখুলে স্বীকারোক্তি করুন৷ কিন্তু সেখানে কথা থাকবে না, অভিব্যক্তি ঘটবে দেহভঙ্গির মাধ্যমে৷ অন্যথায় হীনভাব, প্যাংক্রিয়াস, স্নায়ুর চাপ যা পৌষে শুরু হয়েছিল, তা আপনাকে ছেড়ে যাবে না ৷’ (Little Magazine)
ঠিক এই জায়গায় এসে প্রকাশদার (শিল্পী প্রকাশ কর্মকার) একটা কথা খুব মনে পড়ছে৷ রামকিঙ্কর সম্পর্কে উনি একবার আমাকে বলেছিলেন— ‘এই পোড়ার দেশে জন্মেছিলেন বলেই কিঙ্করদার কোনো মূল্যায়ন হলো না৷ কিন্তু বিদেশে চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণীর শিল্পীদেরও যা বইপত্র আছে তা দেখলে মনে হবে তাঁরা বোধহয় বিরাট মাপের কোনো শিল্পী ৷ অথচ আমাদের দেশে কিঙ্করদার ওপর একটাও কোনো ভালো বই নেই৷’ রামকিঙ্কর সম্পর্কে আমার নিজেরও একটা বক্তব্য আছে৷ মাধ্যমিক পাশের পর থেকেই রাঙামাটির সঙ্গে আমার সখ্য৷ শান্তিনিকেতনের যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু রামকিঙ্কর৷ কী ভালো যে লাগে! যথার্থ মানুষকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—তোর নিজের মতো করে শান্তিনিকেতনকে তুই সাজিয়ে দে ৷ এর পাশাপাশি আরও একটা কথা আমার বারবার মনে হয়, দেশ বিদেশ থেকে লোক এসে দেখে শুধুই রামকিঙ্কর৷ এটা কি কম যন্ত্রণার ছিল সেই সময়কার শিল্পীদের কাছে৷ কারণ রামকিঙ্কর ছাড়া কি দেশে আর কোনো শিল্পী নেই? বাইরে থেকে সবাই এসে কেন জানবে শুধুই রামকিঙ্কর? এই প্রশ্ণ কি তৎকালীন শিল্পীরা করেননি? তাই তাঁরা যদি সুযোগ পেতেন তাহলে রাতারাতি রামকিঙ্করের সমস্ত সৃষ্টিকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে একমুহূর্তও দেরি করতেন না ৷ (Little Magazine)
আরও পড়ুন: ‘আমি আর লীনা হেঁটে চলেছি’: কবিতা— ছাগলের তৃতীয় সন্তান- জাজরা খলিদ
আমার বক্তব্য যদি কেউ ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেন তাহলে আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করব, জীবদ্দশায় রামকিঙ্করের জীবন চূড়ান্ত অশান্তিতে ভরিয়ে দিয়েছিল কারা? শম্ভু রক্ষিত সম্পর্কেও আমার একই বক্তব্য৷ সবাই তাঁকে চিনতেন, তাঁর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে সকল কবিই পূর্ণ ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং তাঁরা প্রায় সকলেই একটি মাত্র বাক্যে তা স্বীকার করে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন৷ কেউ তো আর বলতে পারবেন না আমরা তাঁর কথা বলিনি৷ একটি বাক্যে প্রণাম সেরে দূরে সরিয়ে রেখেছি৷ যেহেতু একটি মাত্র বাক্য তাই কোটি কোটি বাক্যের ভিড়ে আজকের প্রজন্ম শম্ভুকে খুঁজে পায়নি৷
অবশ্যই সেটা শিবহীন যজ্ঞের মতোই৷ ব্যক্তিগত আগ্রহ ছাড়া শম্ভু রক্ষিতের চর্চা কোথায়? বিশেষ সংখ্যার তো ছড়াছড়ি৷ কিন্তু কোথায় শম্ভুকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা? এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও না৷ অবশ্যই আমরা নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি৷ কারণ শম্ভু রক্ষিতের এতে কোনো ক্ষতি হয়নি৷ যাঁরা পড়ার তাঁরা হাজার অকবিতার মধ্যে ঠিকই তাঁকে পড়ে নিচ্ছেন৷ আজকের বাংলা কবিতার যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা অবশ্যই সম্পূর্ণ নয় ৷ শম্ভুর কবিতা যদি দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ত তাহলে আজকে তৈরি হতো শম্ভুর উত্তরসূরী এবং তাতে বাংলা কবিতার একটা আমূল বদল ঘটত ৷ ‘আমার কবিতা অন্তরের স্বর্গীয় ভাবধারার আবিষ্কার৷ কবিতা ছাড়া অন্য কোনো পবিত্রতায় আমার বিশ্বাস নেই’— এমন এক কবিকে সচেতনভাবে দূরে ঠেলে আমরা বাংলা কবিতাকে অনেকখানি পিছিয়ে দিয়েছি ৷ (Little Magazine)
(বানান অপরিবর্তিত)
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।