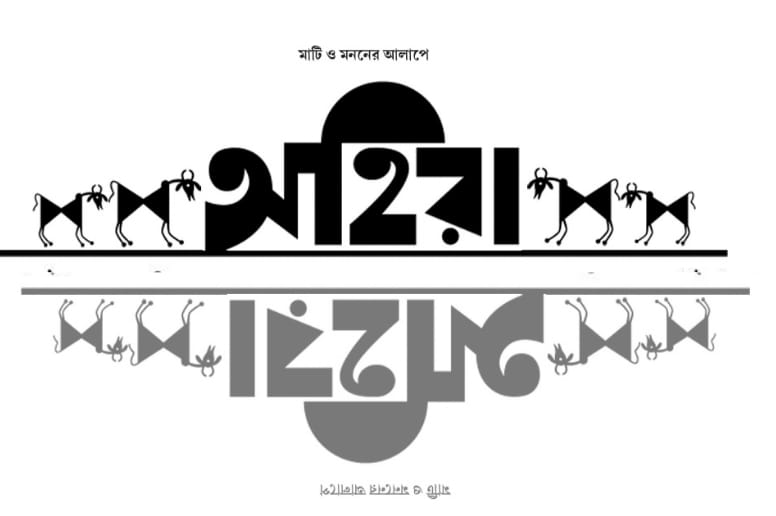ঈশান দেব
 প্রায় সাড়ে চারশো বছর পূর্বের এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত, বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্য মল্লভূমের গভীর জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে চলেছেন, তার পিছন পিছন চলেছেন পালকি-বোঝাই পুঁথিপত্র কাঁধে চারজন মানুষ। তাঁরা আসছেন সুদূর বৃন্দাবন থেকে, গন্তব্য গৌড়। পথশ্রমে জড়িয়ে আসছে পা। এসময় মল্লরাজ বীর হাম্বিরের সৈন্যবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে প্রমাদ গুনলেন শ্রীনিবাস ও তাঁর সঙ্গীরা। রাজার সৈন্যবাহিনী কেড়ে নিল শ্রীনিবাসের অমূল্য পুঁথিপত্র, এমনকি পাথেয়টুকুও। সারারাত অস্থির শ্রীনিবাস পুঁথিপত্রের চিন্তা মাথায় নিয়ে খোলা আকাশের নীচে কাটালেন। পরেরদিন প্রভাতে রাজসভায় শ্রীনিবাস আচার্য রাজা ও সভাসদদের সম্মুখে ভাগবতের যে অসাধারণ ব্যাখ্যা দিলেন তাতে নড়ে গেল রাজার অন্তরাত্মা। তিনি শ্রীনিবাসকে শুধুমাত্র পুঁথিপত্রই ফেরত দিলেন না, দিলেন অগাধ ধন-সম্পত্তি, এমনকি বিসর্জন দিলেন পরম্পরাগত শাক্তধর্মটুকুও। সদ্য বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হাম্বির বিষ্ণুপুরকে ‘দ্বিতীয় বৃন্দাবন’ করার তাগিদে নিয়োজিত হলেন মন্দির নির্মাণে। সেনাবাহিনীও যুদ্ধ জয়ের পরিবর্তে মন্দির নির্মাণে ব্রতী হলেন। আজকের বিষ্ণুপুর সেই মন্দির নগরীর নিদর্শন হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিত। এর পাশাপাশি রাজা তাঁর সেনাবাহিনীর অন্যতম সেরা পটুয়া কার্তিক ফৌজদারকে লাগিয়ে দিলেন দশাবতার তাস তৈরির কাজে। আসলে কার্তিকের ‘মৃন্ময়ী পট’ রাজাকে সম্মোহিত করেছিল, তিনি তো এমন শিল্পীই চেয়েছিলেন তাস তৈরির কাজে। দূরদর্শী রাজা ভালোই বুঝেছিলেন, এই পেশায় জীবিকা নির্বাহ ভীষণ কষ্টকর, তিনি জানতেন ‘আর চিন্তা যেমন তেমন, অন্ন চিন্তা চমৎকারা’। কার্তিককে যাতে অন্নচিন্তায় মগ্ন হতে না হয় তাই রাজা তাঁকে নিষ্কর জমি দান করেন।
প্রায় সাড়ে চারশো বছর পূর্বের এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। শ্রীচৈতন্যের পরম ভক্ত, বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্য মল্লভূমের গভীর জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে চলেছেন, তার পিছন পিছন চলেছেন পালকি-বোঝাই পুঁথিপত্র কাঁধে চারজন মানুষ। তাঁরা আসছেন সুদূর বৃন্দাবন থেকে, গন্তব্য গৌড়। পথশ্রমে জড়িয়ে আসছে পা। এসময় মল্লরাজ বীর হাম্বিরের সৈন্যবাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে প্রমাদ গুনলেন শ্রীনিবাস ও তাঁর সঙ্গীরা। রাজার সৈন্যবাহিনী কেড়ে নিল শ্রীনিবাসের অমূল্য পুঁথিপত্র, এমনকি পাথেয়টুকুও। সারারাত অস্থির শ্রীনিবাস পুঁথিপত্রের চিন্তা মাথায় নিয়ে খোলা আকাশের নীচে কাটালেন। পরেরদিন প্রভাতে রাজসভায় শ্রীনিবাস আচার্য রাজা ও সভাসদদের সম্মুখে ভাগবতের যে অসাধারণ ব্যাখ্যা দিলেন তাতে নড়ে গেল রাজার অন্তরাত্মা। তিনি শ্রীনিবাসকে শুধুমাত্র পুঁথিপত্রই ফেরত দিলেন না, দিলেন অগাধ ধন-সম্পত্তি, এমনকি বিসর্জন দিলেন পরম্পরাগত শাক্তধর্মটুকুও। সদ্য বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হাম্বির বিষ্ণুপুরকে ‘দ্বিতীয় বৃন্দাবন’ করার তাগিদে নিয়োজিত হলেন মন্দির নির্মাণে। সেনাবাহিনীও যুদ্ধ জয়ের পরিবর্তে মন্দির নির্মাণে ব্রতী হলেন। আজকের বিষ্ণুপুর সেই মন্দির নগরীর নিদর্শন হিসেবে সারাবিশ্বে পরিচিত। এর পাশাপাশি রাজা তাঁর সেনাবাহিনীর অন্যতম সেরা পটুয়া কার্তিক ফৌজদারকে লাগিয়ে দিলেন দশাবতার তাস তৈরির কাজে। আসলে কার্তিকের ‘মৃন্ময়ী পট’ রাজাকে সম্মোহিত করেছিল, তিনি তো এমন শিল্পীই চেয়েছিলেন তাস তৈরির কাজে। দূরদর্শী রাজা ভালোই বুঝেছিলেন, এই পেশায় জীবিকা নির্বাহ ভীষণ কষ্টকর, তিনি জানতেন ‘আর চিন্তা যেমন তেমন, অন্ন চিন্তা চমৎকারা’। কার্তিককে যাতে অন্নচিন্তায় মগ্ন হতে না হয় তাই রাজা তাঁকে নিষ্কর জমি দান করেন।
এ তো গেল প্রচলিত গল্পগাথা। এবারে বরং ইতিহাসে চোখ রাখা যাক—
আজ থেকে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে মল্লরাজ বীর হাম্বির (১৫৬৫-১৬২০ খ্রিস্টাব্দে) মুঘল সম্রাট আকবরের কাছে থেকে পেশকুষের জমিদারি লাভ করেন। আকবর ছিলেন মুঘল-গঞ্জিফা তাসের গুণগ্রাহী। কচ্ছপের খোলা, হাতির দাঁত, সোনা-রুপা, কাগজের মণ্ড ইত্যাদিতে নির্মিত ‘গঞ্জিফা’-তে মূলত সৈন্যদলের পদবিন্যাস, পশুপাখির ছবি আঁকা থাকত। বাবর-কন্যা গুলবদন বেগমের ‘হুমায়ুন-নামা’ ও আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’র মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে গঞ্জিফা-র উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন ভাবনা প্রচলিত যে, গঞ্জিফা তাসের শৈল্পিক ধারণা দশাবতার তাস তৈরির ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হয়েছে। এই মতাবলম্বীদের মতে, বিষ্ণুপুরী এই দশাবতার তাসে আছে ওড়িয়া ও মুঘল শিল্পরীতির পরোক্ষ প্রভাব। কল্কি ব্যতীত বাকি নয়টি অবতারের গঠনশৈলী ও বস্ত্রের পারিপাট্য ওড়িয়া শিল্পরীতির হলেও কল্কি ও তার পার্শ্বচরদের বেশভূষা মুঘল শিল্পরীতির খুব কাছাকাছি। যদিও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, মল্লভূমে দশাবতার তাসের আবির্ভাব খ্রিস্টীয় পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি, যে সময় বুদ্ধকে পঞ্চম অবতার এবং পদ্মফুলকে তাঁর প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হত। বিরুদ্ধবাদী গবেষক মানিকলাল সিংহ তাঁর ‘পশ্চিম রাঢ় সংস্কৃতি’ গ্রন্থে জানালেন, বিষ্ণুপুরের দশাবতার তাসে বুদ্ধের পরিবর্তে আছেন নবম অবতার জগন্নাথ। খ্রিষ্টীয় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণকালে জগন্নাথের দেবমহিমা ছড়িয়ে পড়ে। অতএব, একথা বলাই বাহুল্য, খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা পরে এই তাসের প্রচলন। দশাবতার তাসের আবির্ভাব ও বিবর্তন ঘিরে যাবতীয় তরজাকে সরিয়ে রাখলে এটুকু বলা যায়, দশাবতার তাস রাজ-অনুগ্রহ পেয়েছিল প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগে রাজা বীর হাম্বিরের শাসনকালেই।

ফসিল হয়ে যাওয়ার পূর্বে যাতে ‘অহিরা’র পাতায় রয়ে যায় দশাবতার তাদের পদচিহ্ন, তাই ‘ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে’ ভাবধারায় বিশ্বাসী আমরা এক শনিবার বেরিয়ে পড়লাম বিষ্ণুপুরের উদ্দেশ্যে। এক দশাবতার তাস শিল্পীর নাগাল না পেয়ে শরণাপন্ন হলাম বিবেকের, বিবেক মানে বিষ্ণুপুর নিবাসী বিবেক সিংহ, কর্মসূত্রে উৎপলদার পড়শি। কী অদ্ভুত! মুশকিল আসানও হলো। বিবেকের পক্ষ থেকে পূর্বাভাস ছিল আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে পারে জাত-শিল্পী বিদ্যুৎ ফৌজদারের। বিষ্ণুপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে রিক্সায় সওয়ারী হয়ে জানতে চাইলাম, দশাবতার তাসের কথা, কোথায় পাওয়া যাবে শিল্পীদের? কিন্তু রিক্সাওয়ালার মৌনতা লক্ষ্য করে ফৌজলার পাড়ার কথা বলতে উত্তর এল — “ওটা আসলে ওস্তাদ-গলি”। অতএব, এখন আমাদের গম্ভব্য শাঁখারীপাড়া, মনসাতলা ওরফে ওস্তাদগলি।
বিরামহীন ছুটে চলেছে রিক্সা। রাস্তার দুপাশে হঠাৎ নজরে আসা শাঁখার কাজ জানান দিচ্ছে আমাদের গন্তব্য আর বেশিদূর নয়। রিক্সা থামাতেই চোখে পড়লো দশাবতার তাসের বিজ্ঞাপন, আমরা যেন আর্কিমিডিস। শুধু মুখ ফুটে বেরিয়ে এল না ‘ইউরেকা’। তার বদলে যাকে আবিষ্কার করা গেল সে আমাদের নিয়ে যাবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে। গলি উজিয়ে আমরা পৌঁছালাম একটি শীর্ণকায় বাড়ির সামনে। গৃহকর্ত্রীর আমন্ত্রণে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে জানতে পারলাম আমাদের সামনে দণ্ডায়মান বিদ্যুৎ ফৌজদার। মানুষটির অতি সাধারণ চেহারা দেখে আঁচ করবার উপায় নেই এই অসাধারণ শিল্পকর্মের তিনি বর্তমান প্রতিভূ। দুধসাদা দাড়ি, সৌম্যকান্তি চেহারা আর শৈল্পিক পোশাক-আশাক না থাকলেও তাঁর আছে শিল্পীসুলভ দুটি চোখ। শিল্পীটির মতোই বাড়ির অন্দরসজ্জাও ভীষণই অকিঞ্চিৎকর। কেবলমাত্র মাটির দেওয়ালে ঝুলতে থাকা দশাবতার তাসের দশটি ছবি অসাধারণত্বের জানান দেয়। এটি আসলে বিদ্যুৎ ফৌজদারের প্রয়াত পিতা কার্তিক ফৌজদারের অন্তিম স্মারক।
আকবর ছিলেন মুঘল-গঞ্জিফা তাসের গুণগ্রাহী। কচ্ছপের খোলা, হাতির দাঁত, সোনা-রুপা, কাগজের মণ্ড ইত্যাদিতে নির্মিত ‘গঞ্জিফা’-তে মূলত সৈন্যদলের পদবিন্যাস, পশুপাখির ছবি আঁকা থাকত। বাবর-কন্যা গুলবদন বেগমের ‘হুমায়ুন-নামা’ ও আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’র মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে গঞ্জিফা-র উল্লেখ পাওয়া যায়। এমন ভাবনা প্রচলিত যে, গঞ্জিফা তাসের শৈল্পিক ধারণা দশাবতার তাস তৈরির ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হয়েছে। এই মতাবলম্বীদের মতে, বিষ্ণুপুরী এই দশাবতার তাসে আছে ওড়িয়া ও মুঘল শিল্পরীতির পরোক্ষ প্রভাব। কল্কি ব্যতীত বাকি নয়টি অবতারের গঠনশৈলী ও বস্ত্রের পারিপাট্য ওড়িয়া শিল্পরীতির হলেও কল্কি ও তার পার্শ্বচরদের বেশভূষা মুঘল শিল্পরীতির খুব কাছাকাছি।
কথা হচ্ছিল বিদ্যুৎ ফৌজদারের সঙ্গে। তিনি জানালেন, এই পরিবার এখনো বছরে তিনবার মৃন্ময়ীর পট বানায়। রাজার আদেশে তারা এখনও দশাবতার তাস বানালেও, রাজ-অনুগ্রহে পাওয়া জমি-জিরেত আর নেই। বিদ্যুৎবাবুর স্ত্রী শম্পা ফৌজদার জানালেন, জমি-জিরেত থাকলে হয়তো দারিদ্রের দংশন জ্বালা এভাবে সহ্য করতে হত না এই পরিবারকে— “কত কষ্ট করে এই তাস বানাই জানেন! হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। অথচ সেই পরিশ্রমের মূল্য যখন পাঁচ হাজার হয়, খদ্দের ফিরিয়ে নেয় মুখ।” আমাদের ঔৎসুক্যে ২০১০-এ বিবাহসূত্রে বাঁকুড়ার সূত্রধর পরিবার থেকে বিষ্ণুপুরের ফৌজদার পরিবারে আসা শম্পা জানালেন দশাবতার তাসের নির্মাণ-কৌশল— বৈশাখের খর রোদে মেলে দেওয়া মাদুরের উপর রাখা হয় সুতির কাপড়ের প্রথম পরত। এবার প্রথম পরতের সঙ্গে তেঁতুল বীজের আঠা দিয়ে লাগানো হয় দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পরত। তারপর, তিনভাগ খড়িমাটির সঙ্গে একভাগ তেঁতুল বীজের আঠা দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয় সেই কাপড়ের পরতে। এভাবে প্রলেপ দেওয়া চলতেই থাকে যতক্ষণ না অর্জিত হয় কাঙ্ক্ষিত ঘনত্ব। এরপর শুকনো হয়ে যাওয়া মোটা কাপড় ৮-১০ ইঞ্চি মাপে বর্গাকারে কেটে নেওয়া হয়। কাঁচির সৌজন্যে বর্গক্ষেত্র পরিণত হয় বৃত্তাকারে। এবার বৃত্তাকার কাপড়খণ্ডটির একপিঠ ঝামা পাথরে ঘসে তৈরি হয় মসৃণ জমিন, শুরু হয় জমিন রাঙানোর কাজও। প্রতিটি অবতার অঙ্কনের পূর্বে এর পশ্চাৎপট অর্থাৎ জমিনে রঙের ব্যবহার ভিন্ন। মৎস্য অবতারের পশ্চাৎপটে ওঠে কালো রং, কূর্মে বাদামি, বরাহ ও বলরামে সবুজ, বামনে আকাশি, নরসিংহে ধূসর, পরশুরামে সাদা এবং রাম ও কল্কি অবতারের জমিনে থাকে লাল রঙের ব্যবহার। এরপর এই রঙিন বৃত্তগুলিতে একে একে ফুটে ওঠে দশাবতারের অবয়ব। অঙ্কন ও অলঙ্করণ শেষে শুরু হয় পালিশের কাজ। দশাবতার ছাড়াও এই তাসে থাকে একজন রাজা ও একজন মন্ত্রী। শম্পা ফৌজদার জানালেন, এই কাজে পূর্বে প্রাকৃতিক রং ব্যবহৃত হলেও, এখন বাজারি রঙের ব্যবহার। তবে অবতার অঙ্কনে এখনো ছাগ-লোমের তুলির ব্যবহার থেকেই গেছে।
বিদ্যুৎবাবু কথায় কথায় জানালেন, ১২ টি অবতারের দাম ১২০০ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, খেলার জন্য ব্যবহৃত ১২০ টি অর্থাৎ এক প্যাকেট তাসের মূল্য ৫০০০ টাকা কেন! আমাদের সঙ্গী সুশান্ত নন্দীর কথাতে জানা গেল, বাকি কয়টি সেটে দশাবতারের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় অবতারের প্রতীক-চিহ্ন। অর্থাৎ মৎস্যে মাছ, কূর্মে কচ্ছপ, বরাহে শঙ্খ, নরসিংহে চক্র, বামনে কমণ্ডলু, পরশুরামে কুঠার, রামে তির, বলরামে গদা, জগন্নাথে পদ্মফুল ও কল্কিতে তরোয়াল বা খড়্গ। এক থেকে দশ নম্বর সেট পর্যন্ত প্রতীকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। অবতার অঙ্কনের তুলনায় প্রতীক অঙ্কন সহজসাধ্য হওয়ায় দামের এই ফারাক।

বিষ্ণুপুরের শেষ রাজা কালীপ্রসন্ন সিংহ ঠাকুর ও পারিষদবর্গের মধ্যে খেলাটির প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এটি বিলুপ্তির পথে। সুশান্ত নন্দীর কথায়, একমাত্র রঞ্জিত কর্মকার ব্যতীত বর্তমানে এই খেলাটি প্রায় কেউই জানেন না। আরও জানা গেল, ১২০ টি তাসের এই খেলায় পাঁচজন খেলোয়াড়ের কেউই কারও সঙ্গী নয়। রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত এই খেলাটিতে খেলোয়াড়ের বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি প্রকৃতি ও সময়ও ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক — দিনের খেলায় রাম অবতার, গোধূলিতে নরসিংহ, বৃষ্টিদিনে কূর্ম এবং বৃষ্টিরাতে মৎস্য অবতার প্রধান ও শক্তিধর হয়ে ওঠে।
আরও পড়ুন- অহিরা: এই আমি (কবিতা বিষয়ক গদ্য)
প্রকৃতি ও অবতারদের সম্মিলিত ঐশ্বরিক শক্তি কতদিন এই খেলাটিকে বাঁচিয়ে রাখবে তার উত্তর কালের গর্ভে জমা থাক। ভবিষ্যতের কথা না ভেবে আমরা শম্পার কথায় আসি— “জানেন, ভারি অনিয়মিত রোজগার এই পেশায়! সারাবছর তাস বানালেও শীতকালে গুটিকয়েক বিদেশি পর্যটকের দিকে চেয়ে হা-পিত্যেস করে বসে থাকতে হয় এবং তারাই কিনে নিয়ে যান এই তাস।” অবাক হওয়ার পালা। আরও একবার প্রমাণিত হল গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। তাই দেশের মাটিতেই ব্যাঙ্গালোর, কলকাতা বা দিল্লির বিভিন্ন হস্তশিল্প মেলায় শম্পা, বিদ্যুৎ বা বাঁশরী ফৌজদারদের শুনতে হয়, ‘এ তাস কী কাজে লাগে?’ কাজের কথা বলতে গিয়ে বলা প্রয়োজন, এই তাস কলকাতার বিভিন্ন পূজা প্যান্ডেলের অলঙ্করণে ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল। এছাড়া জানা গেল, শম্পার মতো কারিগরেরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিকে থাকার জন্য আপন বুদ্ধিমত্তায় তাসের ব্যবহারে এনেছে ভিন্নমাত্রা। দেশলাই কাঠির সৌজন্যে সেজে ওঠা তাস এখন দেওয়াল-সজ্জায় ব্যবহৃত হয়। অনিয়মিত রোজগার এবং বরাতের অনিশ্চয়তা পরিবারের অন্যান্যদের পেশা বদলে বাধ্য করেছে। বিদ্যুৎবাবুর দুই দাদা চাকরি করলেও ছো্ট দুই ভাই প্রশান্ত ও গণেশ পেটের তাগিদে মৃৎ-প্রতিমা বানায়। তাই বিদ্যুৎবাবুর আক্ষেপ, ‘ছো্টবেলায় তুলি না ধরে, হয়তো কলম ধরলেই ভালো হত।’
প্রতিটি অবতার অঙ্কনের পূর্বে এর পশ্চাৎপট অর্থাৎ জমিনে রঙের ব্যবহার ভিন্ন। মৎস্য অবতারের পশ্চাৎপটে ওঠে কালো রং, কূর্মে বাদামি, বরাহ ও বলরামে সবুজ, বামনে আকাশি, নরসিংহে ধূসর, পরশুরামে সাদা এবং রাম ও কল্কি অবতারের জমিনে থাকে লাল রঙের ব্যবহার। এরপর এই রঙিন বৃত্তগুলিতে একে একে ফুটে ওঠে দশাবতারের অবয়ব। অঙ্কন ও অলঙ্করণ শেষে শুরু হয় পালিশের কাজ। দশাবতার ছাড়াও এই তাসে থাকে একজন রাজা ও একজন মন্ত্রী।
যখন মাউস-এর একটি ক্লিকে হাতের মুঠোয় দুনিয়া, তখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের পত্রমিতালি বা তাস-পাশা খেলার সময় কোথায় আমাদের? আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের বোয়া উপজাতির শেষ প্রতিনিধির মৃত্যুতে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ভাষাটির মতোই, রঞ্জিত কর্মকার-পরবর্তী সময়ে দশাবতার তাসের খেলাও কি হারিয়ে যাবে, সে প্রশ্নই এখন জাজ্বল্যমান বিষ্ণুপুরের আকাশে। খেলাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সফরসঙ্গী রাজীব ঘোষালের দাওয়াই, “কোনো সংস্থার মোটা টাকায় স্বত্ব কিনে আধুনিক প্রযুক্তিতে তাসটিকে বাজারজাত করা প্রয়োজন।” কিন্তু সুশান্ত নন্দীর মতে, এর ফলে হারিয়ে যাবে বহু বছর ধরে প্রবহমান ঐতিহ্য। আমরা বরং মধ্যপন্থায় আসি। দশাবতার তাদের মূল ১২টি তাস বাদে অন্য তাসগুলিকে প্রযুক্তির আওতায় এনে বাজারজাত করা হোক, যাতে থাকবে হাতে আঁকা বারোটি তাস, প্রযুক্তির সন্তান ১২০টি তাস এবং খেলার নিয়মাবলী-সম্বলিত পুস্তক। একটি অসাধারণ প্যাকেজ! যা বাঁচিয়ে দিতে পারে একটি ঐতিহাসিক খেলা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানুষজনকে।
যেভাবে বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণীকে আনা হচ্ছে সংরক্ষণের আওতায়, যেভাবে বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী দেব-দেউলের ভার নিয়েছেন ‘আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া’, সেভাবেই কি এই ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম এবং খেলাটিকে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা যায় না! আমাদের সম্মিলিত প্রশ্ন থাক, থাক উত্তরের আশাও।
বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।